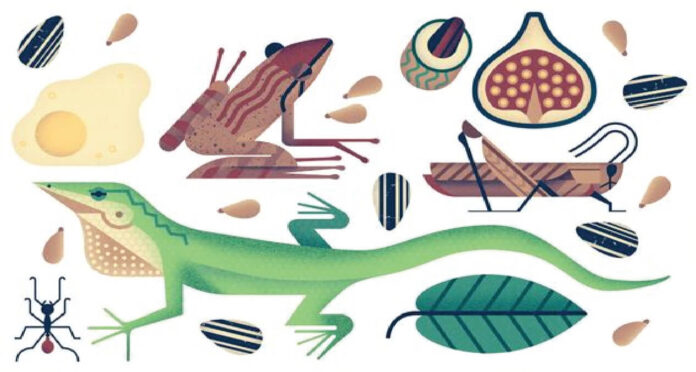১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের বাঙালিদের জন্য এক গৌরবজনক অধ্যায়। নয় মাস রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের স্বাদ পায় বাঙালি।এ যুদ্ধে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত আমাদের সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করলেও মূলত লড়াইটা ছিল একান্তই আমাদের। মুষ্টিমেয় কিছু বিশ্বাসঘাতক রাজাকার, আলবদর,আলশামস ছাড়া আপামর বাঙালি এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল কোনো না কোনোভাবে। কেউ হয়তো অস্ত্রহাতে রণাঙ্গনে শত্রুর মোকাবেলা করেছে। আবার কেউ পরোক্ষভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছে।
তবে আপাতদৃষ্টিতে এ যুদ্ধকে নয় মাসের মনে হলেও,ইতিহাস বলে বাঙালির স্বাধীনতার সংগ্রাম অনেক বছরের। এ সংগ্রামে তিতুমীর, নুরলদীন, ঋষি অরবিন্দ, বাঘা যতীন যেমন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে অবদান রেখেছিলেন, তেমনি মাস্টারদা সূর্য সেন তাঁর প্রশিক্ষিত সৈন্যদল নিয়ে বৃটিশদের বিরুদ্ধে সম্মুখ লড়াই করে বিজয়ী হয়ে চট্টগ্রামকে চারদিনের জন্য স্বাধীন রেখেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এ চট্টগ্রামে উড়েছিল স্বাধীনতার পতাকা। তবে শেষ পর্যন্ত এ বিজয় ধরে রাখা না গেলেও বৃটিশরা বাঙালি জাতির মন থেকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে মুছে দিতে পারেনি শত নির্যাতনের ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়েও।
৪৭ এর দেশবিভাগের মাধ্যমে এ দেশের মানুষ বৃটিশ শাসকদের দুঃশাসন থেকে মুক্তি পেলেও সেই মুক্তির স্বাদ ম্লান হতে বেশিদিন লাগেনি। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে ৪৮ সাল থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের বিরোধ চরমে ওঠে। পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালিরা পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে তাদের অনাস্থা জানিয়ে দেয়। এরই সূত্র ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন গড়ে ওঠে। ৫৪,৫৮,৬২,৬৬,৬৮,৬৯ এর একেকটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথ ধরে অবশেষে ১৯৭০ সালের ০৭ই ডিসেম্বরের নির্বাচন। এটাই অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রথম এবং শেষ নির্বাচন। এ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ছয়দফার পক্ষে রায় দিয়ে আপামর বাঙালি জানিয়ে দিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রতি তাদের কোনো আস্থা নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা থাকলেও নানা টালবাহানার পর ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১লা মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ২রা মার্চ ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ান। ৩রা মার্চ তাঁরা বঙ্গবন্ধুর হাতে সে পতাকা তুলে দেন। এ পতাকার নকশা করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিব নারায়ণ দাশ। মূলত আলাদা পতাকা উড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা সেদিনই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে যে ভাষণ দেন,তা ছিল বাঙালির প্রাণের দাবীর প্রতিফলন। সেদিন রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ জনতার উল্লাসধ্বনি পাকিস্তান সরকারকে ভীত করে তুলেছিল। তারা বুঝে গিয়েছিল এ বাংলার জনগণ স্বাধীনতার নেশায় উন্মাতাল হয়ে উঠেছে। তাই ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে যখন অপারেশন সার্চলাইট এর মাধ্যমে তারা বাঙালি নিধনে নামলো,তখন তারা হয়ে উঠেছিল হায়েনার মতো ভয়ংকর। কারণ তারা জানতো বাঙালি স্বাধীনচেতা জাতি।এ জাতি কখনো রক্তচক্ষুকে ভয় পায়নি। মোগল,পাঠান,বৃটিশ সব আমলেই বাঙালি অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে।
তাই বীর বাঙালির মনোবলকে ধ্বংস করে দিতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা প্রথম থেকেই গণহত্যায় মেতে উঠেছিল। অপারেশন সার্চলাইট নামক এ হত্যাযজ্ঞে পরিকল্পনা অনুযায়ী দুটি সদরদপ্তর স্থাপন করা হয়। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর তত্ত্বাবধানে প্রথম সদরদপ্তরটি গঠিত হয়। এখানে ৫৭তম ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার আরবাবকে ঢাকা নগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় এবং মেজর জেনারেল খাদিম রাজাকে প্রদেশের অবশিষ্টাংশে অপারেশনের দায়িত্ব দেয়া হয়। অপারেশনের সার্বিক দায়িত্বে থাকেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান। এদের ওপর আদেশ ছিল সব বাঙালিকে মেরে হলেও এ ভূখণ্ডকে দখলে রাখতে হবে। উল্লেখিত জেনারেলরা নির্দেশ অনুসারেই কাজ করেছিল। নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে তারা এ সোনার বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছিল। ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইলের ছোট্ট এ ভূখণ্ডটির প্রতি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লেগে আছে রক্তের দাগ। এ মাটির তলায় মিশে আছে তিরিশ লক্ষ শহিদের হাঁড়গোড়।১৯৭১ এ সাড়ে সাতশ নদনদীর স্রোত স্থবির হয়ে গিয়েছিল লাখো শহিদের লাশের কারণে।এ প্রবন্ধের লেখকও সেই তিরিশ লাখ শহিদ পরিবারের একজন। মুক্তিযুদ্ধে আমি হারিয়েছি আমার বাবা,কাকা,দুই মামাকে। আমি জানি না কোথায় তাঁদের সমাধি। কারণ তাঁদের পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ধরে নিয়েছিল ঠিকই,কিন্তু এরপর তাঁদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাঁরা আর কেউ ফিরে আসেননি। শুধু আমরা নই,আমাদের মতো এমন লক্ষ লক্ষ পরিবার রয়েছে,যাঁরা জানেন না কোথায় সমাহিত করা হয়েছে তাঁদের স্বজনদের।
১৯৭১ এ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের দোসররা এ দেশে রক্তের হোলিখেলায় মেতে উঠেছিল। পরবর্তীতপ শুধু এ চট্টগ্রাম মহানগরীতেই চিহ্নিত করা গেছে ৭৭টি বধ্যভূমি। বধ্যভূমি বলতে আমরা বুঝি যেস্থানে বধ বা হত্যা করা হয়। আমাদের দেশে বধ্যভূমি বলতে আমরা সেসব স্থানকেই বুঝি, যেসব স্থানে ১৯৭১ সালে নির্বিচারে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। এসব স্থানে মুক্তিযোদ্ধা এবং সাধারণ জনগণকে ধরে এনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং রাজাকার আলবদররা নির্মমভাবে হত্যা করে মাটি চাপা দিয়েছে,কখনো বা উন্মুক্ত ফেলে রেখে শিয়াল,কুকুর,শকুনের খাদ্যে পরিণত করেছে। চট্টগ্রামেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ গবেষক সাখাওয়াত হোসেন মজনুর “চট্টগ্রাম শহরের বধ্যভূমি” বইয়ে ৫১টি বধ্যভূমির কথা বলা হয়েছে। তবে লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন কোনো স্মৃতিচিহ্ন না থাকাতে সব বধ্যভূমি চিহ্নিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি আমরণ মুক্তিযুদ্ধ,মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবার নিয়েই গবেষণা করে গেছেন। এরকম আরেকজন গবেষক ড.গাজী সালেহউদ্দিন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।
তিনিও মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের অবদান নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর “প্রামাণ্য দলিল:মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম” বইটিতে চট্টগ্রাম শহরে ৭৭টি বধ্যভূমির কথা উল্লেখ করেছেন।
এ পর্যন্ত যাঁরাই চট্টগ্রামের বধ্যভূমি নিয়ে কাজ করেছেন, তাঁদের সবাই স্বীকার করেছেন চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় বধ্যভূমি পূর্ব পাহাড়তলীতে অবস্থিত।পাহাড়তলীর ওয়ারলেস কলোনির মোড়ে টিএন্ডটি অফিসে ছিল বেলুচ রেজিমেন্টের ক্যাম্প। এর কাছাকাছিই ছিল জল্লাদখানা। এখানে প্রায় ১০,০০০ বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এ হত্যাযজ্ঞ চলে। এ হত্যাযজ্ঞে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে বিহারিরাও অংশ নেয়। দোহাজারি, নাজিরহাটের ট্রেন থামিয়ে নিরীহ বাঙালিদের ধরে এনে এখানে হত্যা করা হতো। বিভিন্ন জায়গা থেকে বাঙালি মেয়েদের ধরে এনে ধর্ষণের পর এ স্থানে হত্যা করা হতো। দুঃখের বিষয় এ বধ্যভূমিটাকে এখনো সংরক্ষণ করা হয়নি।
১৯৯৮ সালে “প্রজন্ম ৭১” নামে একটি সংগঠন এ বধ্যভূমিটির আদ্যোপান্ত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এটি সংরক্ষণের দাবী জানান। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বধ্যভূমি সংরক্ষণের নির্দেশ দেন। তারই প্রেক্ষিতে ১ দশমিক ৭৫ একর জমি অধিগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেই সময়ে এই প্রকল্পের জন্য ৯৪ লক্ষ টাকা দেয়াও হয়েছিল। কিন্তু ২০০৫ সালে চারদলীয় জোট সরকার ওই প্রকল্প বাতিল করে। সরকারের ওই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে দেশের আটজন বিশিষ্ট নাগরিক হাইকোর্টে রিট করে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন লেখক অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল, গবেষক অধ্যাপক ড. মুনতাসির মামুন, গবেষক অধ্যাপক ড. গাজী সালেহ উদ্দিন, মিলি রহমান প্রমুখ। ২০১১ সালের ১৬ জানুয়ারি হাইকোর্ট রিট নিষ্পত্তি করে দেয়। আবেদনকারীরা এরপর আপিল বিভাগে যান। ওই আবেদনের শুনানি নিয়ে আপিল বিভাগ সরকারকে এক সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে এর নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেন। সাবেক সেনাপ্রধান কে এম সফিউল্লাহকে নিয়ে ওই কমিটি গঠিত হয়। কমিটি ওই বধ্যভূমি চিহ্নিত করে তা সংরক্ষণের সুপারিশ করেন। ২০১৪ সালের ১৭ মার্চ রিট আবেদনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে বধ্যভূমিটি সংরক্ষণের চূড়ান্ত আদেশ আসে। সুখের কথা বর্তমান সরকার পাহাড়তলী বধ্যভূমিটি সংরক্ষণের জন্য ১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।
এই বধ্যভূমিটি ছাড়াও চট্টগ্রাম শহরে আরও ৭৬টি বধ্যভূমি রয়েছে। যদিও সরকারি হিসাবে ৬১টি বধ্যভূমি চিহ্নিত করা গেছে।সরকারি হিসাবে যে ৬১টি বধ্যভূমি চিহ্নিত হয়েছে তার পরিসংখ্যান হলো পাহাড়তলীতে ১৫টি,লালখানবাজারে ৬টি,হালিশহরে ৫টি,গোসাইলডাঙ্গায় ৫টি,আন্দরকিল্লায় ৪টি,বাকলিয়ায় ৩টি,রহমতগন্েজ ২টি,কাট্টলীতে ২টি,পতেঙ্গায় ২টি,বন্দর এলাকায় ২টি,কাটগড়ে ২টি,মুরাদপুরে ২টি,নাসিরাবাদে ২টি,মাদারবাড়িতে ২টি,পাঁচলাইশে ২টি এবং চন্দনপুরা,জয়পাহাড়,চান্দগাঁও,ষোলশহর,
রামপুরায় ১টি করে। কিন্তু এগুলো ছাড়া প্রত্যক্ষদর্শী এলাকাবাসীদের তথ্যানুযায়ী চট্টগ্রাম শহরে আরও বধ্যভূমি রয়েছে।পরিতাপের বিষয় তিনটি বধ্যভূমি ছাড়া আর একটিতেও কোনো স্মৃতিচিহ্ন নেই। যে তিনটিতে স্মৃতিচিহ্ন আছে তা হলো পূর্ব পাহাড়তলী বধ্যভূমি,মধ্যম হালিশহর নাথপাড়া বধ্যভূমি ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের পেছনে অবস্থিত বধ্যভূমি। মেডিকেল কলেজসংলগ্ন বধ্যভূমিটিতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মীয়মাণ।
এ তিনটি বধ্যভূমি ছাড়াও শহর জুড়ে যে বধ্যভূমিগুলো ছড়িয়ে আছে তার কয়েকটি হলো মহামায়া ডালিম হোটেল, গুডসহিল, পশ্চিম পাহাড়তলী, দক্ষিণ বাকলিয়া মোজাহের উলুম মাদরাসা, জেনারেল হাসপাতাল, জয়পাহাড়, আগ্রাবাদ জাম্বুরী মাঠ, ১ নম্বর জেটি থেকে ১৫ নম্বর জেটি, জামালখানের হোটেল টাওয়ার, চাক্তাই খালপাড় চামড়ার গুদাম, তুলসীধাম সেবায়েত মন্দির,লালখান বাজার হাইওয়ে প্লাজা,বাটালি পাহাড়ের রেলওয়ে বাংলো,পাঁচলাইশ সড়ক,চট্টগ্রাম জেনারেল পোস্ট অফিস,সিআরবি,চন্দনপুরা,সার্কিট হাউজ,বন্দর আর্মি ক্যাম্প,প্রবর্তক সংঘ,সদরঘাট রাজাকার ক্যাম্প, ঝাউতলা বিহারি কলোনি,গোসাইলডাঙ্গা নৌবাহিনী ক্লাব, সিভিল গোডাউন দেওয়ানহাট,চট্টগ্রাম সেনানিবাস, কালুরঘাটস্থ রেডিও সমপ্রচারভবন, টাইগারপাস নৌঘাঁটি,পতেঙ্গাস্থ নৌবাহিনী সদরদপ্তর, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ,দেওয়ানহাট ফায়ারব্রিগেড,মদুনাঘাট পাওয়ার স্টেশন, পাহাড়তলি সিডিএ মার্কেট, পাহাড়তলী হাজিক্যাম্প, সল্টগোলা ক্রসিং সীম্যান্স হোস্টেল, আমবাগান রেলওয়ে ওয়ার্কশপ,ফিরোজ শাহ কলোনি,বন্দরটিলা ক্রসিং, অঙিজেন মোড় রাজাকার ক্যাম্প,ঈদগা রেডিও স্টোর ক্যাম্প,ইস্টার্ন রিফাইনারি ক্যাম্প,কাট্টলী বঙ্গোপসাগরের পাড়, পাকিস্তান বাজার,ইস্টার্ন ক্যাবলস এর অভ্যন্তর, হালিশহর চৌধুরীপাড়া সাগরপাড়,ড্রাইডক ইয়ার্ডের অভ্যন্তর,মাঝিরঘাট লবণঘাটা,গরীবুল্লাহ শাহর মাজারের নিকটস্থ কবরস্থান, কালুরঘাট সেতু,বন্দর কলোনি, নাসিরাবাদ পাহাড়ি এলাকা, শেরশাহ কলোনির পূর্বদিকের পাহাড়,গোল্ডেন টোবাকোর পাশের পাহাড়গুলো,পতেঙ্গা বিমানবন্দরের সর্ব দক্ষিণ পাড়,বন্দরটিলার সাগরতীরের পোড়াবাড়ি,কাট্টলী জেলেপাড়া,মদুনাঘাট গৌরাঙ্গবাড়ি,চট্টগ্রাম কোর্টবিল্ডিং,মোহসিন কলেজসংলগ্ন পাহাড়,পশ্চিম রামপুরা,পদ্মা অয়েল কোম্পানি। এসব বধ্যভূমি ছাড়াও চট্টগ্রাম শহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের অনেকগুলো নির্যাতনকেন্দ্র ছিল।
চট্টগ্রাম শহর ছাড়াও তারা চট্টগ্রামের বিভিন্ন গ্রামেও হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে রাউজানের ঊনসত্তর পাড়া ও বোয়ালখালী শাকপুরা গ্রামের নির্বিচারে গণহত্যার কথা স্মরণ করা যায়। এ প্রসঙ্গে ঘৃণার সাথে বলতে হয়, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তো এ দেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলো চিনতো না, তাহলে তারা গ্রামগুলোতে এমন ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালালো কী করে? উত্তর খুব সহজ,মীরজাফরের বংশধর এ দেশীয় রাজাকার, আলবদর,আলশামস তাদেরকে এ দেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলো চিনিয়ে দিয়েছিল। তাদেরই সহযোগিতায় পাকিস্তানি হায়েনার দল চট্টগ্রামের গ্রামগুলোতে নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েছিল। তাদের প্রধান টার্গেট ছিল হিন্দু জনগোষ্ঠী। এর পরেই তাদের টার্গেট ছিল আওয়ামীলীগ নেতাকর্মী। তারা প্রায় প্রতিটি উপজেলায় বধ্যভূমি তৈরি করেছিল। কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে তা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে।
এখনো মুক্তিযুদ্ধের পূর্ববর্তী প্রজন্মের অনেকেই বেঁচে আছেন বলে আমরা সে স্থানগুলো চিহ্নিত করতে পারি।কিন্ত এমন দিন আসবে যখন কেউ চিনিয়ে দিতে আসবে না,কোথায় নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল এ দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষদের। তাই অচিরেই এসব বধ্যভূমি চিহ্নিত করে তা সংরক্ষণ করা জরুরি।
একটা জাতি কতটুকু সভ্য তা নির্ধারণ করা হয় তার ইতিহাস-সচেতনতা দেখে। তাই যুগে যুগে দেশে দেশে তাদের জাতীয় বীরদের সম্মান জানানো হয়। সংরক্ষণ করা হয় তাঁদের স্মৃতিচিহ্নগুলো। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বাধীনতা পেয়েছি। এ স্বাধীনতার জন্য আমাদেরকে অনেক বেশি দাম দিতে হয়েছে। তিরিশ লক্ষ শহিদ আর দুই লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের ওই লাল-সবুজের পতাকা। তাঁদের প্রতি অসম্মান জানালে ইতিহাস আমাদের কখনো ক্ষমা করবে না। তাই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা শপথ নিই আমাদের বধ্যভূমিগুলো সংরক্ষণ করার। যেন আগামী প্রজন্ম শহিদানের স্থানগুলোতে গিয়ে সশরীরে সম্মান জানাতে পারে আমাদের জাতীয় বীরদের। শহিদ স্মৃতি অমর হোক।
লেখক : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ; কথাসাহিত্যিক।