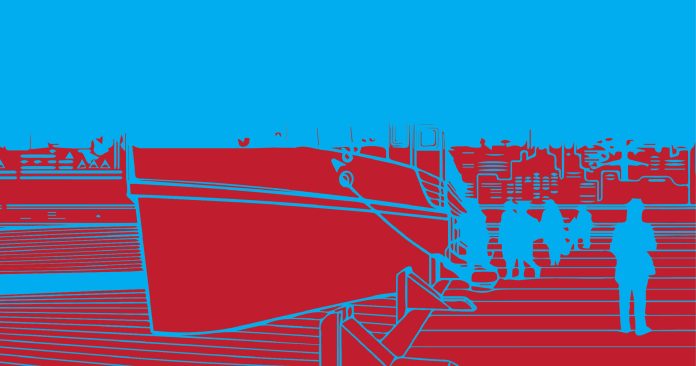আজ এতদিন পরে কেবিন নম্বরটা আর মনে নেই; স্মৃতির পাতায় অনেক হাতড়ে, অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করে, হাসপাতালটাকে শনাক্ত করতে পেরেছি রিভারসাইড রিজিওনাল মেডিকেল সেন্টার। এখানে আমার জীবনের একটা সংকটময় সময় কাটিয়েছিলাম। প্রায় এক মাসের উপর। জাহাজে গরম তেলে ঝলসে যাওয়াতে ইমার্জেন্সি বেসিসে আমাকে নিউ পোর্ট নিউজ বন্দরে নামিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে ডাক্তার পরীক্ষা করে আমাকে ঘুমের ঔষধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। ঔষধের কারণে কতক্ষণ যে মড়ার মতো ঘুমিয়েছিলাম, তা জানি না। ঘুম ভেঙে নিজেকে একলা একটা কেবিনের বেডে আবিষ্কার করলাম।
নার্স এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এবং আমার ভালো–মন্দ জিজ্ঞেস করতে করতেই অনেক পরীক্ষা–নিরীক্ষা করলেন, ভাইটাল সাইনগুলো রেকর্ড করলেন। তারপরে জানালেন ডাক্তার আসবেন আমাকে দেখতে। ঠোঁট–জিহ্বা–গলা বারেবারে শুকিয়ে যাচ্ছে। নার্স আমাকে স্ট্র লাগানো মাঝারি সাইজের পানির জগ দিলেন, সেটা থেকেই ডাইরেক্ট চুমুক দিয়ে খাচ্ছি। তিনি খাবার চয়েসের জন্যে একটা মেন্যু দিলেন। অ্যামেরিকার প্রতিটা হাসপাতালেই রোগীদের জন্যে রীতিমত একটা রেস্টুরেন্ট টাইপের কিচেন আছে। তিনবেলা সেখানে সব ধরনের রান্নাই হয়। রোগীরা আগে থেকে সিলেক্ট করে দেয়; আর সময়মতো সেগুলো বেডে বেডে সার্ভ করা হয়। কারো বাধানিষেধ থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী মেন্যু দেওয়া হয়। আর নার্সরা তো সাহায্য করার জন্যে সেখানে চব্বিশ ঘণ্টাই আছেন। আরো দেখলাম অনেক সাধারণ পাবলিক, হাসপাতালে ভলান্টিয়ার করেন। তাদেরকে স্ক্রিনিং করে, ভালোমতো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে বাছাই করা হয়। মেডিকেল প্রফেশনের না হলেও চলবে–যে কোনো কেউই ভলান্টিয়ার হতে পারেন। এই যেমন আমার পানি ফুরিয়ে গেলে জগ ভর্তি করে দেওয়া। গুরুতর রোগী না হলে হুইলচেয়ারে করে আনা–নেওয়া করা, নন–মেডিকেল কাগজপত্র গোছগাছ করা ইত্যাদি। রোগীর প্রাইভেসির কারণে তারা মেডিকেল রেকর্ড করতে পারবেন না। হাইস্কুলের ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক ৫০ ঘণ্টা ( কম–বেশি), সমাজে যে কোনো জায়গায় ভলান্টিয়ারের কাজ করতে হয়। অনেকেই হাসপাতালে করেন। কেউ করে চার্চে, মসজিদে, শহরের পার্কে, আত্মীয়স্বজনদের অফিসে।
ঘণ্টাখানেক পরে ডাক্তার এলেন। ইনি হাসপাতালের ডাক্তার। আমার ফাইল পড়ে দেখে নার্সকে বললেন কী করতে হবে। আমাকে জানালেন, পুড়েছে, তবে জীবন–শঙ্কা তো নেই–ই এবং অঙ্গহানিরও তেমন শঙ্কা নেই। গলা ও কাঁধে যেখানে প্রথম তেলের ধারাটা পড়েছিল, সেখানে বেশ কিছুটা জায়গায় থার্ড ডিগ্রি বার্ন; আশেপাশে গড়িয়ে গিয়ে বুকে–পিঠে–হাতে সেকেন্ড ও ফার্স্ট ডিগ্রি। আর সৌভাগ্যবশত মুখে, কপালে ফার্স্ট ডিগ্রি সুপারফিশিয়াল বার্ন। অল্পের জন্যে চোখ রক্ষা পেয়েছে; আমার চশমাই মনে হয় চোখ দুটোকে সরাসরি তেল থেকে রক্ষা করেছে। কারণ, আমার মনে পড়ছে, জাহাজে আমার এক সহকর্মী চশমাটা খুলে নিয়েছিলেন এবং পরে পরিষ্কার করেছিলেন। তাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিলেন সেটা থেকে তেল পরিষ্কার করতে।
ডাক্তার আরেকটা নির্দেশ দিলেন, আমার কেবিনে বা বাথরুমে কোনো আয়না রাখা যাবে না বা থাকলেও সেগুলোকে ঢেকে দিতে হবে। প্রথমে আমি খেয়াল করিনি বা বুঝতেও পারিনি–আমি তো তখন প্রায় বেডরিডেন। বাথরুমের দরকারে দিনের বেলা নার্সরা ধরে ধরে নিয়ে যেতেন আর রাতে বেডপ্যান দিতেন। সে অবস্থায় বাথরুমের আয়নার দিকে খেয়ালও করিনি। পরে একদিন নার্সদের সঙ্গে কথায় কথায় বুঝলাম যে, আমার মানসিক শক এড়ানোর জন্যই ওই নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি নিজের বিকৃত মুখ হয়তো সহ্য করতেই পারতাম না। ডাক্তার আমার মুখে কসমেটিক সার্জারির কথাও চিন্তা করেছিলেন। তবে, আল্লাহর অশেষ রহমতে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মুখের অবস্থা ঠিক হয়ে গিয়েছিল আর আয়নার নিষেধাজ্ঞাও তুলে নিয়েছিলেন। আর আমার চেহারাবদন এমন আহামরি কিছুই না যে, পুড়ে গিয়ে আরো নষ্ট হবে। কসমেটিক সার্জন হয়তো আমার এই চাঁদপনা মুখের সৌন্দর্যবর্ধনের কথা চিন্তা করে হেসেই খুন হতেন।
ডাক্তার প্রতিদিন সকালে রাউন্ড নিয়ে দেখে যেতেন। ক্ষতস্থান দেখে ব্যান্ডেজ বদলে দিতেন, ঔষধের মাত্রা ঠিক করতেন। দুই–তিন দিনের মাথায় ব্যথার ঔষধ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছিল–যেটা খুবই ভালো। তা না হলে, সেটার উপরে নির্ভরশীল (বা এডিক্ট) হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রতিদিনই যে একই ডাক্তার আসেন তা নয়– দুই–তিনজন আছেন। ঘুরেফিরে তারাই ডিউটি দেন। একজন আবার একটু বেশি দয়ামায়াহীন–তিনি আমার ক্ষতস্থানের ব্যান্ডেজ খুলে জোরে ঘষে ঘষে দেখেন সেটা ঠিকমতো শুকাচ্ছে কিনা। কী যে ব্যথা লাগত! আমি প্রায়ই তার হাত চেপে ধরতাম, যাতে আর ব্যথা না দিতে পারেন।
দ্বিতীয় দিনেই নার্সরা আমার সারা শরীর ভালোমতো গরম পানি দিয়ে ধুইয়ে দিয়েছিলেন। যাক বাবা, এর ফলে সেই উৎকট হেভি অয়েলের চিটচিটে ভাব ও গন্ধ দূর হয়েছিল। নিজেকে ভদ্র ধোপদুরস্ত মনে হয়েছিল। সুগন্ধি সাবান–শ্যাম্পুর গন্ধ অনেকদিন পরে ভালো লাগল। এর মাঝে ডাক্তারে নির্দেশ দিলেন আমাকে ক্লিনসিং অ্যান্ড হিলিং একুয়া–বাথ নিতে হবে। সেটা একটা পন্থা বটে। আমাকে হুইলচেয়ারে ঠেলে ঠেলে হাসপাতালের সেই সেকশনে নিয়ে যেত। সেখানে অনেকগুলো বড় বড় চৌবাচ্চা আছে। ভিতরের পানি উষ্ণ, ক্রমাগত পাম্প করেই চলেছে। আমাকে একটা স্ট্রেচারে শুইয়ে, কপিকল ও ক্রেনের মাধ্যমে স্ট্রেচারসহ ছাদের দিকে লিফট করে, তারপরে ধীরে ধীরে একটা চৌবাচ্চায় নামানো হয়। আমি কিন্তু শোওয়া অবস্থাতেই পানিতে আধা ডুবে যাই। আমাকে নামানোর আগে পানিতে কী কী সব ঔষধ বা কেমিক্যাল মিশায়, যেগুলো আমার চামড়া সেরে ওঠার জন্যে দরকারি। আমার গায়ে কোনো কাপড়ই থাকে না; শুধুমাত্র কোমরে একটা তোয়ালে, কোনোমতে নেংটির মতো দিয়ে রাখে। আমি দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে সেটাকে জায়গামতো রাখার চেষ্টা করি। তা না হলে সেই নেংটিও চৌবাচ্চার পাম্পের পানির তোড়ে না জানি কোথায় চলে যায়! প্রায় আধা ঘণ্টাখানেক আমাকে সেই পানিতে কান পর্যন্ত চুবিয়ে রাখা হতো। এরপরে সেখানকার নার্স বা টেকনিশিয়ান, চিমটা দিয়ে দিয়ে আমার শরীর থেকে মড়া চামড়া তুলতেন। তিনি বেশ সাবধানে করতেন, যাতে ব্যথা না পাই। নিষ্ঠুর ডাক্তারটার মতো একদমই না।
আমি ধীরে ধীরে আমেরিকার হাসপাতালের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করলাম। বিছানাটাই যেন একটা মেশিন–কত রকম করে যে ওঠানামা করা যায়, ভাঁজ করা যায়। সেইসঙ্গে তো আরো কত রকমের যন্ত্রপাতি স্ক্রিন–মনিটর, এলার্ম ইত্যাদি। ফ্লুইড–লসের ভয়ে আমাকে প্রথমে স্যালাইন দিয়েছিল। এরপরে আমি স্টেবল হলে সেটাও বন্ধ করল। বিছানার সঙ্গে একটা রিমোট, সেটা দিয়েই টিভি চলে, বিছানা ওঠানামা করে এডজাস্ট করতে পারি, আবার নার্সদের কল করতেও পারি। বাথরুমেও নার্স কল করার ব্যবস্থা রয়েছে। ইমার্জেন্সি তো বাথরুমেই বেশি হয়। বাংলাদেশ থেকে সদ্য আগত আমি, এগুলো আমার কাছে বেশ মজাই লাগত। তবে, সবচেয়ে অদ্ভুত ছিল রোগীদের গাউন। পাতলা ও লম্বা, কটনের গাউন দুই হাত গলিয়ে উল্টো শার্টের মতো পরতে হয়। পিছে দুই–তিনটা মাত্র ফিতা থাকে, সেগুলো লাগানো কষ্টের। আর এর ফলে প্রায়শই পুরা পশ্চাৎদেশ উন্মুক্ত হয়ে থাকে–গলা থেকে পিঠ হয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সবকিছুই। কি লজ্জার ব্যাপার!
হাসপাতালে থাকা অবস্থায় আমার সদ্যবিবাহিত সেজভাই ও ভাবী, প্রায় দুইশ মাইল ড্রাইভ করে আসলেন আমাকে দেখতে। বিদেশের হাসপাতালে ভিজিটর পাওয়াই ভাগ্যের ব্যাপার; আর ভিজিটর যদি নিজের আপন ভাই–ভাবী হয়, তাহলে ঈদের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো। ভাই এসে দেশে ফোন করে আব্বা–আম্মার সাথে কথা বলিয়ে দিলেন। নব্বই সালে তো সেলফোন, স্মার্টফোন ছিল। আমার বেডে ফোন ছিল, সেটা দিয়ে দেশে করলে যে চার্জ আসবে, আমার দুয়েক মাসের বেতনের সমান হবে। ভাই টেলিফোন কার্ড দিয়ে সস্তায় করে দিলেন। আরেকদিন নর্থ ক্যারোলিনা থেকে এলো আমার খালাতো বোন ঊষা। সঙ্গে তার ফুপাতো ভাই নন্দন ভাই–ভাবী। উনাদের কখনো চিনতামই না; আমার খবর পেয়ে উনি ঊষাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। নার্সরা অবাক এবং সেই সঙ্গে খুশিও। এই ভিনদেশি নাবিকেরও ভিজিটর আছে!
মাসখানেক কেটে গেল। সব চিকিৎসা চলছে। ঘা–ক্ষতস্থান শুকিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। তবে বাম কাঁধ, গলা, হাতের উপরের অংশ এখনো ঠিকমতো সেরে উঠেনি। হঠাৎ একদিন ডাক্তার ঘোষণা দিলেন, সুখবর, তোমাকে ডিসচার্জ করে দেওয়া হবে। তুমি দেশে ফিরে যেতে পারবে শীঘ্রই। শুনে তো আমি আকাশ থেকে পড়লাম। আমি ডাক্তার না, বুঝতে পারছিলাম না এই অবস্থায় প্লেনে আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ এত লম্বা জার্নির ধকল সহ্য করতে পারব কিনা। বা পারলেও শরীরের কী অবস্থা হবে; ক্ষতস্থানগুলোর কী অবস্থা হবে? তারপরে দেশে পৌঁছলে কীরকম চিকিৎসা পাব তা–ও জানি না। বরং এখানে বেস্ট অফ দি বেস্ট ট্রিটমেন্ট পাচ্ছি। আমি রিকোয়েস্ট করলাম সম্পূর্ণ না সেরে উঠলে আমাকে ডিসচার্জ না করতে। ডাক্তার ‘ঠিক আছে’ বলে চলে গেলেন। দুদিন পর এসে একই কথা। এবার টের পেলাম, এটা উনি করছেন না, জাহাজ কোম্পানির ইনস্যুরেন্স এটা করাচ্ছে। দিনের পর দিন আমেরিকার মতো ব্যয়বহুল দেশে হাসপাতালের বিল দেওয়ার ব্যাপারে সকলেই কৃপণ। কিন্তু আমি তখনো ঘাড় ঘুরাতে পারি না, সেখানে ক্ষতটা এখনো দগদগে, শুকায়নি। প্লেনে–এয়ারপোর্টে কীভাবে চলব? আর দেশের ধুলাবালিতে তো আবারো ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে।
অনেক বলা–কওয়ার পর ঠিক করা হলো, হাসপাতাল থেকে হোটেল এবং সেখান থেকে আমার ভাইয়ের বাসায়। সেইমতোই সব ব্যবস্থা করে, ডিসচার্জের সময়ে প্রচুর পরিমাণে ঔষধ, অয়েন্টমেন্ট ও ব্যান্ডেজ দিয়ে দিল আমার জন্য।
(চলবে)
টলিডো, ওহাইও, ২০২৩
refayet@yahoo.com