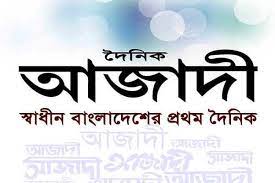মুক্তিযুদ্ধ যেকোন জনপদের সবচেয়ে গৌরবের দিক। আর বীর মুক্তিযোদ্ধারা হলেন ইতিহাসের নির্মাতা। ইতিহাসের শিক্ষার্থী হিসেবে জানি, ইতিহাস নিজ দায়িত্বে এরকম সন্তানদের ধারণ করে এবং জীবন্ত রাখে। বাবাকে নিয়ে তাই কখনো লিখতে প্রয়োজনবোধ করিনি। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিকালে স্থানীয় কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধার অনুরোধে কিছু লিখতে হচ্ছে।
বাবার মুখ : হয়তো এটা পুরানো শুনাবে। কিন্তু বলতেই হবে, বাবা হিসেবে দক্ষিণ চট্টগ্রামের ডা. শামসুল আলম পৃথিবীর সেরা বাবাদের একজন ছিলেন। পটিয়ার ঐ জনপদ জানে ব্যক্তি হিসেবে তিনি চারপাশকে আকর্ষণ করার যাদু জানতেন। আমাদের খুব কম বয়সে মা দূর আকাশে তারা হয়ে গেলেন। চার ভাই-বোনকে বাবা তাৎক্ষণিকভাবে বাড়তি যত্নে বুকে তুলে নিয়েছিলেন।
মা, বাবা, বন্ধু, শিক্ষকরা সাধারণত জীবনের পাঠশালায় পদপ্রদর্শক। ডা. শামসুল আলম এর বেশি কিছুই ছিলেন। তিনি নেই বহুদিন। কিন্তু এখনও স্থানীয় মানুষের কাছে চিকিৎসক হিসেবে শামসুল আলম দক্ষিণ চট্টগ্রামে কিংবদন্তিু হয়ে আছেন। এলাকার প্রথম ‘এমবিবিএস’ তিনি। কেবল শেখা বিদ্যা দিয়ে নয়- মমতা, ধৈর্য্য আর আন্তরিকতা দিয়ে চিকিৎসা করতেন। তাঁর বেশীর ভাগ রোগী ছিল গ্রামের দরিদ্রজন এবং সেটা বিনামূল্যে। এলাকার বৃদ্ধ নারী-পুরুষ কারো কাছে তিনি ছিলেন ‘ধর্ম-বাবা’, কারো কাছে ‘ধর্ম-ছেলে’। এসব আর কিছু নয়- সম্পর্কের গভীরতা নির্দেশ করতো মাত্র। হিন্দু, বৌদ্ধ অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে বিশেষভাবে মানুষ তাঁকে আপন ভাবতো, ভরসা পেতো, ভালোবাসতো।
বিনিনিহেরার গর্ব : পটিয়ার বিনিনিহেরা গ্রামে ১৯৪১ সালে ডা. শামসুল আলমের জন্ম। পিতা আলী আকবর ও মাতা গোলতাজ খাতুনের চতুর্থ সন্তান তিনি। তাঁর অনুপ্রেরণার জায়গা ছিল বড় ভাই ড. আবদুস সবুর চৌধুরী। তাঁরই তত্ত্বাবধানে কৃতিত্বের সাথে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে চট্টগ্রাম মেডিকেলের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী হিসেবে এমবিবিএস পাশ করেন। নিজেদের সন্তান এলাকার প্রথম ‘ডাক্তার’ হলো, পাশের খবর শুনে বৃদ্ধ পিতার দু’চোখে অশ্রু দেখে পাশে একজন মজা করে বলে উঠলো, ‘আজ থেকে তোমার নাম মুছে গেল।’ এখন থেকে এই বাড়ীকে কেউ আলী আকবর সওদাগরের বাড়ী বলবে না, বলবে ডাক্তার শামসুর বাড়ী।
কৃতি শিক্ষার্থী হিসেবে শামসুল আলম জাতীয় অধ্যাপক ডা: নুরুল ইসলামের পুত্র স্নেহ পেতেন। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের কেউ যদি ঢাকায় প্রফেসর নুরুল ইসলামের কাছে চিকিৎসার জন্য যেত, উনি বকা দিয়ে বলতেন, ‘এতদূর আসলে কেন? তোমাদের জন্য তো আমি চট্টগ্রামে শামসুকে দিয়ে এসেছি।’
মৃত্যুপথযাত্রী পিতার শেষ ইচ্ছানুযায়ী সরকারি চাকরি, নাগরিক জীবন সব ছেড়ে গ্রামের মানুষদের চিকিৎসা সেবা দিতে পটিয়ায় থেকে যান তিনি। এটা ছিল এলাকার মানুষদের কাছে বিস্ময়ভরা এক সিদ্ধান্ত। তখনকার সময়ে দুর্দান্ত ক্যারিয়ারের প্রলোভন ছেড়ে গ্রামে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল তাৎপর্যবহ।
ডাক এলো ‘মুক্তি’র : ১৯৭১ পুরো বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বাঁক বদলে যাওয়া এক সময়। যুদ্ধকালে শামসুল আলমের বয়স ৩০ বছর। পরবর্তী জীবনে আমাদের কাছে তিনি আন্দোলন-সংগ্রামমুখর একাত্তরের উত্তাল মার্চের দিনগুলোর কিছু কিছু গল্প শুনিয়েছেন। আমাদের ভাই বোনদের মুক্তিযুদ্ধ ভাবনার উৎস বাবার প্রত্যক্ষ ওই বয়ান।
এটা সকলেরই জানা স্বাধীনতাকামী জনগণের ওপর ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী যে সশস্ত্র অভিযান শুরু করে চট্টগ্রামও তা থেকে বাদ যায়নি। সশস্ত্র বাহিনীর সেই অভিযানের হাত থেকে রক্ষা পেতে তৎকালীন চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাজী মনির আহমদ পাঁচ ভাইবোন এবং সুবিশাল পরিবারের ২৫-৩০ জন নিয়ে শামসুল আলমের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। চিকিৎসক শামসুল আলম এরকম মানুষদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়েই নিজের কর্তব্য শেষ করেননি। সেই কাহিনীতেই এবার আমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছি।
মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো : মুক্তিযুদ্ধকালে দক্ষিণ চট্টগ্রামের এক বড় চরিত্র ‘ক্যাপ্টেন করিম।’ এটা আজকের দিনে খুব কমই আলোচনা হয়। রাউজানে জন্ম ক্যাপ্টেন করিমের। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রতিরোধপর্ব থেকে আনুগত্য পরিবর্তন করেন। কালুরঘাটে এক দফা প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারত চলে গিয়েছিলেন। তারপর দ্রুত ফিরে এসে আবার শামিল হন গেরিলাযুদ্ধে। দ্বিতীয় পর্বের এই ফিরে আসার পর্যায়ে বোয়ালখালীর ‘রাজাকার ক্যাম্প’ আক্রমণ করতে গিয়ে ক্যাপ্টেন করিম তাঁর কয়েকজন সহযোগীসহ গুলিতে আহত হয়েছিলেন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য আমাদের বাড়ীতে আনা হয়। এ বিষয়ে মনসা’র বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম বলেন, ‘আমি আহত ক্যাপ্টেন করিমকে নিয়ে ডা. শামসুল আলম সাহেবের বিনিনিহেরা বাড়ীতে যাই। সেখানে ডা. আলম ক্যাপ্টেন করিমের চিকিৎসা করেন। তার থাকার জন্য দোতলায় নিজের বেডরুম ছেড়ে দেন। সে রুমে আমি আর ক্যাপ্টেন করিম একসাথে থাকতাম।’ আহত ক্যাপ্টেন করিমকে ঐ চিকিৎসা দিতে গিয়েই তাঁর সঙ্গে বাবার ঘনিষ্টতা বাড়ে। এক পর্যায়ে তিনি ক্যাপ্টেন করিমের সাথে গেরিলাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। দক্ষিণ চট্টগ্রামের মুক্তিযুদ্ধের একটা বড় অধ্যায়ের সূচনা ছিল এই ‘জড়িয়ে পড়া’। যদিও অজ্ঞাত কারণে এই অধ্যায় খুব কম আলোচিত ও কম উল্লিখিত। বর্তমান লেখকের কাছে বিনিনিহেরার বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল আলম বলেন, ‘ডা: শামসুল আলম ক্যাপ্টেন করিমের নেতৃত্বে সরাসরি কালারপোল পুলিশ ফাঁড়ি আর্মি ওয়ারলেস স্টেশন ও খাসমহল আক্রমণ, ধলঘাট আক্রমণ প্রভৃতি অপারেশনে অংশ নেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজল আহমদ জানান, স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের দুইটি ট্রেনিং সেন্টার ছিল। একটা ছিল কাশিয়াইশ বর্ধনবাড়ি; আরেকটা বুধপরা হসপিটাল। হুলাইন আমিন শরীফ প্রাইমারী স্কুল সংলগ্ন পুকুরপাড়ে পরীক্ষামূলকভাবে মাইন বিস্ফোরণ করে দেখা হতো।’ কালারপোল অপারেশন সম্পর্কে গবেষক ডা. মাহফুজুর রহমান তাঁর গ্রন্থে (বাঙ্গালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম) বিবরণ দিয়েছেন এভাবে: অসহযোগ আন্দোলনের সময় কালারপোল পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা বাঙ্গালিদের আন্দোলনের পক্ষে ছিল। প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় এখানে যুবকদের অনেককেই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পাক বাহিনী পটিয়া দখল করার পর এ পুলিশ ফাঁড়িতে মুজাহিদ, রাজাকার ও নতুন কিছু পুলিশ অবস্থান নেয়।…ক্যাপ্টেন করিম, আহমদ শরীফ মনির, আজিজুল হক প্রমুখ বসেন ডা. শামসুর বাড়িতে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে। আলোচনা শেষে ফাঁড়ি আক্রমণের সিদ্ধান্ত হয়। একই দিন রাডার স্টেশন আক্রমণেরও সিদ্ধান্ত হয়। বেলা চারটার সময় একটি দল ডা. শামসুর বাড়ি হতে অপারেশনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এর একটি গ্রুপ ক্যাপ্টেন করিমের নেতৃত্বে কালারপোল ফাঁড়ির দিকে যায় এবং অপর গ্রুপটি আজিজুল হকের নেতৃত্বে লাহাড়া রাডার স্টেশনের দিকে যায়।
অনেক আগে লিখিত হলেও মুক্তিযুদ্ধে বাবার সম্পৃক্তির এরকম বিবরণ সম্প্রতি কেবল দেখলাম। এই লেখা উপলক্ষ্যে আমি যখন সরাসরি কথা বলেছি, তখন আরেকজন বীর মুক্তিযোদ্ধা জিরির কমান্ডার বদিউজ্জামান ঐ সময়ের বিবরণ দিতে যেয়ে ডা. শামসুল আলমের স্ত্রী নুরজাহান বেগমের কথাও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, ‘মুক্তিযোদ্ধারা প্রায়ই ডাক্তার সাহেবের বাড়ীতে যেত। যত রাতই হোক, ঐ মহিয়সী যেন অপেক্ষা করতেন। গরম খাবার ও পানির ব্যবস্থা করা হতো।’
দেমাগ্রীর পথে : এলাকায় মানুষদের আশ্রয় দেয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা দেয়ার পাশাপাশি নিজে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েই ডা. শামসুল আলমের যুদ্ধের কাহিনী শেষ হতে পারতো। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। হয়তো তাঁর শিক্ষা ও সচেতনতা বলছিলো এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে। সেপ্টেম্বরের দিকে তিনি নিজ গ্রামের ১১ জনসহ আশেপাশের আরো কয়েক গ্রামের প্রায় ৪০-৫০ জন তরুণকে নিয়ে উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত নিয়ন্ত্রিত মিজোরামের দেমাগ্রী যান। ক্যাপ্টেন করিম তাদের বোয়ালখালীর জ্যেষ্ঠপুরা, কেনপুরা পর্যন্ত এগিয়ে দেন। তিনিই ডা: শামসুল আলম এবং প্রশিক্ষণে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বিদায় জানান। ক্যাপ্টেন করিম যে এই পুরো প্রক্রিয়ার অন্যতম সংগঠক ছিলেন সেটা বোঝা যায়। এও বোঝা যাচ্ছে, এদের কাছে মুক্তিযুদ্ধ একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের বিষয় হয়ে উঠেছিল।
দেমাগ্রী থেকে আগরতলা : দেমাগ্রীর জীবনে ডা. শামসুল আলম সন্তুষ্ট ছিলেন না বলেই ইঙ্গিত মিলে। চিকিৎসক হিসেবে তিনি আরও বাড়তি দায়িত্ব-কর্তব্যের পরিসর খুঁজছিলেন। নভেম্বরের শেষ দিকে তিনি মুক্তিযুদ্ধের উর্ধ্বতন কমান্ড কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ করে রেডক্রস সোসাইটির মাধ্যমে দেমাগ্রী থেকে কলকাতা হয়ে আগরতলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পৌঁছান। দেমাগ্রীতে সহযোগীরা তাঁকে বিদায় জানায়।… তারপর অনেক যুদ্ধদিন পেরিয়ে একাত্তর শেষ হলো।
পলাতক জীবন, পুনর্গঠনের চ্যালেঞ্জ : মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন দেশে পা রাখার পর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম দেখলেন সবকিছু বদলে গেছে। অপ্রীতিকর অবস্থায়ও পড়লেন। ইতোমধ্যে স্থানীয় মুক্তিযুদ্ধের পরিসরে বহু কিছু ঘটে গেছে। বিশেষভাবে দেখলেন, নিজভূমে, নিজগ্রামে তিনি নিরাপদ নন। প্রাণভয়ে পালিয়ে থাকতে গিয়ে আশ্রয় নিতে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে স্বাধীন দেশে। প্রিয় সহযোগী, ঘনিষ্ঠ সহচর, বন্ধু ক্যাপ্টেন করিম ইতোমধ্যে নিহত। তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে রহস্যময়তা।
পটিয়ার মুক্তিযুদ্ধের এই নায়ককে হারানো বাবার জন্য এক বড় আঘাত ছিল। কারণ ক্যাপ্টেন করিমের সংস্পর্শেই বাবার মুক্তিযুদ্ধে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হওয়া। সময়ের এক অসাধারণ সাহসী সন্তান ছিলেন ক্যাপ্টেন করিম। অনেকগুলো সফল অপারেশনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। অত্যন্ত সুদর্শনও ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের কঠিন সময়ের মাঝেই ভালোবাসার সম্পর্ক এসেছিল ক্যাপ্টেন করিমের জীবনে। প্রেমকে স্থায়ীত্ব দিতেই ডাক্তার শামসুল আলমের ভাইয়ের মেয়েকে আংটি পরিয়ে রেখেছিলেন। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যাকে পরাজিত করতে পারেনি, সে সাহসী বীরযোদ্ধা পরাস্ত হয়েছিলেন নিজ দেশের মানুষদের হাতে। নভেম্বরে পাহাড়ের ঢালে ধূলি-ধুসরিত প্রান্তরে নিথর হয়ে পড়েছিল দেশের সে সূর্যসন্তানের মৃতদেহ। বাবা আমৃত্যু সে শোক বহন করেছেন। মেনে নিতে পারেননি তিনি এই মৃত্যুকে। হয়তো এসব কারণেও পরবর্তী জীবনে তিনি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সামাজিক পরিসরে আলাপে উৎসাহ দেখাতেন কম। চাইছিলেন একান্তই চিকিৎসা পেশায় থিতু হতে। কয়েকবার সহযোদ্ধারা এসেছিল সনদ নেয়ার প্রস্তাব করে। যাননি কখনো। জীবিত অবস্থায় তিনি এসবে আগ্রহী ছিলেন না। কেন আগ্রহী ছিলেন না- সেসব জানি না। হয়তো তাঁর ঘনিষ্ট সহযোগীরা বলতে পারবেন। যদি আদৌ তাঁরা বলতেন চান আর।
লেখক : বেসরকারি কলেজের শিক্ষক এবং ডা. শামসুল আলমের কন্যা