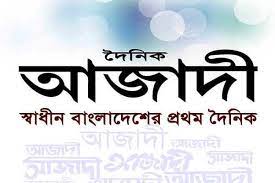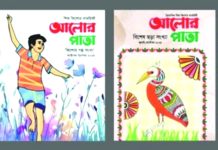কানাকড়ি ও ফটোপয়সা-২
পূর্ব প্রকাশিতের পর
আগে তো এখনকার মতো এতো সব মানিব্যাগ বা কয়েন ব্যাগ ছিল না। “আচ্ছা বাবা ওগুলো ও কি টাকা নাকি ?” সবকিছু চুপচাপ গভীরভাবে নিরীক্ষণে ব্যস্ত অভ্র ভাঙল তার মৌনতা এবার!
সেই প্রশ্নের সুত্র ধরে নজর গেল এবার, একই শোকেসের বা দিকটায় সাজিয়ে রাখা সেই সামুদ্রিক প্রাণীগুলোর খোলগুলোর দিকে, যার কয়েকটা ছিল আমারও ছোটবেলার খাজাঞ্চি খানার অমূল্য সম্পদ। সাথে এও মনে হল এটা যদি পুরাকীর্তির যাদুঘর না হয়ে, হতো ন্যাচারাল সাইন্স মিউজিয়ম তবে এগুলো নিশ্চয় পেত ফসিল অভিধা। আবার একই সাথে মনের ভেতর কেউ বলে উঠল “কড়ি দিয়ে কিনলাম” কথাটাও। হ্যাঁ বিমল মিত্রের বিখ্যাত এই উপন্যাস না পড়লেও, সেটিরই নাম কি না মনে পড়ল এই চায়নার মিউজিয়মে সাজিয়ে রাখা চার পাঁচ হাজার বছরের পুরানো এই কড়িগুলো দেখে, যেগুলো কি না আমাদের দেশের মতো এখানেও একসময় মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হতো?
হ্যাঁ বাবা, এগুলোও একসময় টাকা হিসাবেই লেনদেন করতো এখানকার মানুষেরা। শুধু এখানকার মানুষরা না, আমাদের দেশেও এই কড়িকে টাকা হিসাবেই ধরা হতো। যার কারণেই হয়তো আমাদের ভাষায় টাকাকড়ি কথাটার প্রচলন হয়েছিল। এটুকু বলেই কড়া ব্রেক ধরে ঠেকালাম নাবালক পুত্রদের কাছে নিজের জ্ঞানগম্যি ফলানোর বালখিল্য প্রচেষ্টাটি। আর সকল কিছুর মতোই, ভাষাজ্ঞান, শব্দজ্ঞান এসবের অবস্থা তো আমার ঠনঠনে। অকারণে কেন নিজে টিভি ঠকশোবিদদের মতো আবার ফাঁকা বকাবাদ্য করছি, ভেবে।
ভাল করে সেই কড়ি গুলো ফের দেখতে দেখতে সেই ফুটো পয়সাগুলোর মতো এই কড়ি গুলোর ও কয়েকটার মধ্যে ছিদ্র দেখতে পেয়ে ভাবলাম, যাক এক যাত্রায় ফুটোপয়সা ও কানাকড়ি দুটোরই দেখা মিলে গেল এখানে। ভাবতে ভাবতে দু পুত্রকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা তোমরা কি জানো পৃথিবীর কোন জাতি প্রথম টাকার প্রচলন শুরু করেছিল?
ভাব ধরে প্রশ্ন তো করলাম পুত্রদের, কিন্তু নিজেই তো নিশ্চিত জানি না সঠিক উত্তর এর। শুধু আবছা আবছা ভাবে যতোটুকু মনে পড়ছে তাতে মনে হচ্ছে চায়নাই প্রথম টাকা ধারনাটি সমাজে প্রচলন করে ধীর গতির পণ্য বিনিময়ের যে ব্যবসা ছিল, সেটির গতি বৃদ্ধি করেছিল। আবার একই সাথে মনে হচ্ছে একই ঘটনা তো মনে হয় গ্রীসেও হয়েছিল। তা হলে কে আগে গ্রীস নাকি চীন?
“চায়না নাকি বাবা?” প্রশ্নের ধরণ থেকে যেমন অনেক সময় উত্তর পেয়ে যায় অনেকেই আমারও প্রশ্নের ধরণ থেকে দীপ্রর এই উত্তর বের করা দেখে হাসতে হাসতে বললাম, যদিও এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না সঠিক যে কারা প্রথম টাকার প্রচলন করেছিল গ্রীস নাকি চীন? তবে কেন জানি মনে হচ্ছে চীনই হবে উত্তরটা। “ঠিক আছে রুমে গিয়ে গুগল করে দেখে নেব। ওহ এখানে তো গুগল আবার চলে না ঠিক মতো ।“ স্বাগত স্বরে বলল দীপ্র।
“বাবা আর দিজ প্রেসাস?” কড়িগুলো নিয়ে অভ্রর করা এই প্রশ্নে প্রমাদ গুনলাম। নিজেরই ছোটবেলার মনের ভেতরে থাকা এই প্রশ্নের উত্তর তো জানি না এখনও। কড়ি যে টাকা হিসাবে কেন ব্যবহার হতো একসময়, এ প্রশ্ন তো আমারও ছিল মনে। কাউকেই তো তা জিজ্ঞেস করিনি। যদিও মনে মনে ভাবতাম আচ্ছা কড়ি যে সময় টাকার মর্যাদা পেয়েছিল তখন নিশ্চয়ই সমুদ্রপাড়ের জেলেরাই সবচেয়ে ধনী মানুষ ছিল সমাজে। কিন্তু মানুষের গালগল্প আর ভাবসাব থেকে কিম্বা বইয়ের গল্প পড়ে যতোটুকু বুঝেছি তাতে তো মনে হয়েছে সাগরপাড়ের জেলেরা আজন্ম হাভাতেই ছিল।
সাথে সাথেই এও মনে হল, আচ্ছা আধুনিক টাকার ধারনার সাথে, মূল্যবান ধাতু সোনার যে একটা যোগসূত্র আছে তা কি অভ্র জানে না কি এখনি? আর না হয়, কড়ি বহুমূল্য কোন কিছু কি না, এই প্রশ্ন করলো কেন? নিজমনের ছোট বেলার প্রশ্নটা তো এতোটা উচ্চমানের ছিল না। ঐটা ছিল কড়ি কেন টাকা হবে, এরকম একটা সাধারণ প্রশ্নই শুধু। এখন বুঝে করুক আর না বুঝেই করুক, ছোটপুত্রের করা এই প্রশ্নের সাথে তো অর্থনীতির একটা জটিল ধারণার যোগসূত্র আছে!
এগুলো খুব দামি না হলেও খুব বেশি পাওয়া যায় না তো, তাই হয়তো এগুলোকে টাকা হিসাবে ব্যবহার করতো মানুষ, আদর করে অভ্রকে নিজের কাছে টেনে নিতে নিতে এই উত্তর দিয়েই আবারও হৃদয়ঙ্গম করলাম নিজজ্ঞানের দীনতা। কারণ কোন জিনিষ কতো কম বা বেশি পাওয়া যায়, কিম্বা কতো সহজে বা কষ্টে সংগ্রহ করতে হয়, তার উপরই তো মানব সমাজে সেটির মুল্যমান নির্ধারিত হয়। অতএব অভ্র যদি এক্ষুণি সেই ফাঁকটা ধরে আবার প্রশ্ন করে বসে, তবে তো ধরা খেয়ে যাবো!
কপাল ভাল পুত্র সেদিকে গেল না। তাতে মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বললাম, জানো বাবা আমার না ছোট বেলায় এরকম ছয়টা কড়ি ছিল । সে গুলো দিয়ে আমরা চার গুটি, ছয় গুটি নামের খেলা খেলতাম।
“আচ্ছা তোমরা এখানে কি করছ এতক্ষণ ধরে। এ ঘরের আর কিছু দেখবে না নাকি?” এদিকে এগিয়ে আসতে আসতে লাজুর করা এই প্রশ্নের উত্তরে -আরে তাইতো তাইতো, চলো বাবারা এই ঘরের বাকী জিনিষগুলোও দেখে নেই। বলেই পুত্রদের নিয়ে হাঁটা ধরলাম তাদের মাতাভিমুখে। “আচ্ছা এখান থেকে বেরিয়ে আমরা কোথায় যাবো? ওখানে কি খাওয়া দাওয়া করার রেস্টুরেন্ট আছে? ওদের তো দুপুরের খাবারের সময় হয়ে গেছে প্রায়”। পুত্রদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন মাতার এই প্রশ্নে পরিষ্কার হল ফের মাতা ও পিতার পার্থক্য। কারণ এ চিন্তা তো আমর মাথায় আসেনি। যদিও তার মানে অবশ্যই এই নয় যে, পিতারা তাদের সন্তানদের ক্ষুধা নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয়। বরং সমাজ সংস্কৃতিভেদে পিতাদেরই তো এ নিয়ে সর্বক্ষণ দৌড়ঝাঁপ করতে হয়। এই এখন ক’টা বাজে, তা দেখার জন্য পকেট থেকে ফোন বের পর্দায় চোখ ফেলতেই দেখি একটা বাজতে বাকী আছে মাত্র মিনিট চারেক।
অর্থাৎ এখনি না হলেও আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই খুঁজে পেতে হবে আশেপাশের কোন রেস্টুরেন্ট, যার হদিস ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে, তা নেই জানা। এ ব্যাপারে অবচেতনে এতক্ষণ তো ছিলাম আসলে লি খাঁর ভরসায়। আচ্ছা, তোমার ব্যাগে কি খাওয়া খাদ্যের কোন স্টক আছে কি? সামনে এগুতে এগুতে জিজ্ঞেস করলাম লাজুকে।
লেখক : প্রাবন্ধিক, সংগঠক