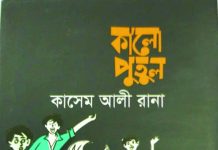কতো ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত সেই ভলগাা! যার তীরে এমন একটি শহর নভগরদ; যে শহর এখন বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে আলোকোজ্জ্বল একটি নক্ষত্রের আলোয় আলোকিত ভূমি। আলেক্সেই ম্যাক্সিমোভিচ পেশকভ (ম্যাক্সিম গোর্কী)। মানুষের যূথবদ্ধ জীবন ও সৌন্দর্য্যের সবচেয়ে মূল্যবান একটি সমন্বিত জীবনবোধ ও সমাজের প্রতিবিম্বিত প্রচ্ছদের শিরোনাম ম্যাক্সিম গোর্কী। সমগ্র বিশ্বের মানবিক অধ্যায়ের ইতিহাসে যাঁর সাহিত্যসনিষ্ঠ জীবন, অভূতপূর্ব নৈর্ব্যক্তিক বিরোধ ও সন্নিধি সর্বোপরি বহুমাত্রিক চিত্রমালায় গ্রথিত সুখ, দুঃখ ও বেদনার রক্ত, মাংস ও প্রাণের বিবরণ বিধৃত। ‘মা’ পাঠ অন্তে মনে হয় মানবিক বিচরণক্ষেত্রের সীমারেখাহীন জয়যাত্রার এক মহাকাব্যিক ছবি। এও মনে হয়েছে ম্যাক্সিম গোর্কীর সাহিত্যসত্তার অন্ত:স্থলে সতত অপেক্ষারত এক তীব্র ছোবলসম্পন্ন ভূজঙ্গ।
তাঁর জীবন পাঠ করলে দেখি অকস্মাৎ এক বিরাট হাতুড়ির আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ এক তাপমান জীবন। অপূর্ণ শৈশবে পিতার মৃত্যু; মাতুল গৃহে পরিপালন, প্রচন্ড কূট পরিবেশে মাতার প্রয়াণ এবং মাতুল গৃহ থেকে দাদু কর্ত্তৃক চরম প্রত্যাখ্যান, মাত্র এগার বছরে দোকানে কাজ, জাহাজের রান্নঘরে থালা বাসন ধোয়ার কাজ, পেন্টিং শপে কাজ করতে করতে বিদ্রোহী কবি নজরুলের মতোই এক জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে নাড়া বাঁধলেন। তিনি একদম ইউরোপীয় ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে শুরু করে বাইবেল পর্যন্ত পড়ালেন। এসব কিন্তু সবই চলছে কাজের অবসরে। অবশ্যই রাত জেগে।
এক সময় ম্যাক্সিম খুবই হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন কারণ তাঁর মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নের অদম্য ইচ্ছার যখন নির্মম সমাধি হয়ে গেল এবং মাসে মাত্র তিন রুবলের বিনিময়ে রুটি কারখানায় কাজ; একসময় তীব্র বিষাদাক্রান্ত! পূর্ণযুবক গোর্কী ভলগা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে নিজের বুকে চালালেন বুলেট। দারিদ্রের কষাঘাত, চতুর্দিকে নুয়ে পড়া জীবন, সমাজ এসব মিলিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করতে গিয়েও বেঁচে গেলেন কারণ বুলেট ফুসফুসে একটি ছোট ছিদ্রমাত্র করেছিল। তারপরেও গলায় অ্যাসিড ঢেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু হাসপাতালে একজন নার্স দেখে ফেলায় সে যাত্রায় বেঁচে যান।
পরবর্তীতে তাঁকে দেখছি তিনি জারবিরোধী গুপ্ত রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে ঘুরছেন। অনেকটা এই সময়ের অর্থাৎ ঊনিশ শতকের অন্ত্যপর্বে (১৮৯০-৯১?) তিফলিস শহরে ‘ককেশাস’ পত্রিকায় প্রকাশিত হলো তাঁর প্রথম লেখা ‘মাকার চুদ্রা’। ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর সর্বৈব পরিচিতি হলো ১৯৯৪ খৃস্টাব্দে ‘চেলকাশ’ গল্পটি প্রকাশের পরে। ১৯০১ খৃস্টাব্দে ‘ঝড়ো পাখির গান’, ‘তিনজনা’ নীচের মহল (১৯০২) এর পূর্বেই বেরিয়েছে। ‘শিকারী পাখির গান (১৮৯৫), ‘বুড়ি ইজেরসিল, ‘(১৮৯৪-৯৫)’ শরতের এক সন্ধ্যায় (১৮৯৪), ছাব্বিশজন ও একটি মেয়ে’। তাঁর লেখকজীবনের সূচনাংশের সঙ্গে সঙ্গে এইসব ছোটগল্পগুলো তাঁকে বেশ একটা পরিচিতির আসনে উপবিষ্ট করেছিল নতুবা জার সরকার কেন গোর্কীকে কারারুদ্ধের পরও আদেশ শিথিল করে। তাঁকে মুক্তিদানে বাধ্য হয়েছিলেন। কারাবাস হওয়ার আগেই কিন্তু তিনখন্ডে প্রকাশিত হয়েছে ‘রেখাচিত্র’ ও গল্প সংকলন, পাতিবুর্জোয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা।
১৯০৫ খৃস্টাব্দের দিকে ‘নবজীবন’ (Novaya-Zhizn) পত্রিকা অফিসে লেনিনের সঙ্গে ম্যাক্সিম গোর্কীর পরিচয় ঘটে। কিন্তু পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়া হয়। এবং এর কিছুকাল পরে ম্যাক্সিম গোর্কীকে গ্রেপ্তারের আদেশ জারী করা হয়। গোর্কী কৌশলে অনেকটা ছদ্মবেশেই ফিনল্যান্ড চলে যান। তারপর সুইজারল্যান্ড, বার্লিন, প্যারিস হয়ে চলে আসেন আমেরিকায়। এইসময়ে জীবনের এক কঠিন পর্ব তিনি অতিবাহিত করেন। রাজনীতি ও সাহিত্য সাধনা এবং শ্রম বিযুক্ত মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম, আন্দোলন এই বিষয়গুলো তাঁর জীবনের একটি আর একটির চমৎকার পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর সারাজীবনের যে বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা, মানুষের সমাজ ও সময়, সংকট, সংশয়ের সামনে চরিত্রহীন মানুষের শতরূপী মুখোশের সঙ্গে সাক্ষাৎ সবকিছুই এক অনবদ্য উপাদান বা রসদে পরিপূর্ণ হয়ে প্রকাশিত হলো সেই জগৎবিখ্যাত উপন্যাস ‘মাদার’ প্রথম খন্ড (১৯০৬)। এটি ইংরেজীতে অনুদিত হয়ে প্রথম আমেরিকায় প্রকাশিত হয়। ‘মাদার’র দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হয় ইটালী থেকে। এই উপন্যাসটি প্রকাশের আগেই অর্থাৎ ১৯০৫ খৃস্টাব্দে ম্যাক্সিম গোর্কী বলশেভিক দলের সদস্য হন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় অকটোবর বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে তিনি পুনরায় প্রকাশিত ‘নবজীবন’ পত্রিকায় লিখতে লাগলেন। কিন্তু ১৯১৮ খৃস্টাব্দে গোর্কীর কিছু নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশের ফলে বলশেভিক দলের পক্ষ থেকে অর্থাৎ সরকারের পক্ষ থেকে লেনিনের নির্দেশে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ‘নবজীবন’র ওপর নিষেধাজ্ঞা নেমে আসে।
সমাজতাত্ত্বিক আইন ও মত, পথ নিয়ে অনেক মতদ্বৈততা লেনিন ও গোর্কীর সঙ্গে ছিল। এই মতানৈক্য সাহিত্য বা রাজনীতির সমন্বয় বা রাজনৈতিক কিংবা মানবিক দর্শনের মাধ্যমেও সুরাহা হয়নি। এই দোটানার মধ্যেই গোর্কীর তিনখন্ডে বিখ্যাত রচনাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো। ‘আমার ছেলেবেলা’ (১৯১৩), ‘পৃথিবীর পথে’ (১৯১৮) ও ‘পৃথিবীর পাঠশালা’ (১৯২৩)। তাঁর এই যুগপৎ সাধনা যাকে বলে শোষক জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক সংগ্রামে ও সাহিত্যচর্চার ভেতর দিয়ে তাঁর বাণী ও স্বদেশপ্রেমের জাগরণের তথা সারা বিশ্বের শোষিত মানুষের উদ্দেশ্যে ঐক্য ও সংগ্রামের আহ্বান এক বিস্ময়কর ঔপন্যাসিকের অভিধায় ম্যাক্সিম গোর্কীকে সারা দুনিয়ার ও অবিভক্ত এই উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত করলো।
১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১৭ ফেব্রুয়ারি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সম্পাদিত ‘দি বেঙ্গলী’ পত্রিকায় প্রবন্ধ বেরিয়েছিল ‘ম্যাকসিম গোর্কী’-ঔপন্যাসিক, কবি এবং বিপ্লবের অগ্রদূত’ নামে। এমনও অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেল যে ক্রমাগত রুশ বিপ্লবের নানাবিধ সংবাদ এবং গোর্কীর কার্যক্রম পরস্পরের গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক ও সহায়ক শক্তি হিসেবেই একীভূত হয়ে গেল। সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং ম্যাক্সিম গোর্কী সমার্থক হয়ে গিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন সময়ে ‘ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন’ পত্রিকায় (জুলাই ১৯০৫ খৃঃ) লিখেছিলেন ‘গোর্কীর প্রধান লক্ষ্য হলো মানুষকে তার অধিকারের জন্য সংগ্রামে প্রস্তুত করা। জনগণের সেবায় তাঁকে কারাবরণও করতে হয়েছে। জেলকে তিনি খুব সম্মানজনক স্থান মনে করেন। শোনা যায় ইয়োরোপে গোর্কীর মতো আর কোন লেখক নেই যিনি জনগণের জন্য এভাবে সংগ্রাম করেছেন।’
তাঁর ‘One Autumn Night’, ‘Creatures’ that once were men,’ ‘Birth of a Man’, Twenty six Man and a girl.’ ‘The Lower Depths এইসব ছোট গল্পগুলিতে গোর্কীর সাম্যবাদী চেতনা, মানবজীবনায়নের নানাবিধ সংকট, সামাজিক বঞ্চনা ও প্রতিরোধের, সংগ্রামের সংকেতগুলিই মূর্ত হয়েছে। গোর্কীর কালজয়ী ‘মাদার’ উপন্যাসে শোষিত নির্যাতিত জীবনের অবসান ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হবার জন্য এই উপন্যাসের নায়ক থেকে অন্যান্য চরিত্রগুলো প্রত্যেকটি যেন জীবন্ত হাতিয়ার। তারা প্রত্যেকেই যেন প্রস্তুত, সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতা এবং অবরুদ্ধ জীবন পেরিয়ে যাবার ও মুক্ত হবার প্রেরনায় উদ্দীপিত এবং সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের কঠিন শপথে আমৃত্যু নিবেদিত।
‘মাদার’ উপন্যাসের বেশ কয়েকটি চরিত্র এমনকি ‘মাদার’ চরিত্রটিও একদম বাস্তব জীবন থেকে তুলে আনা বিষয়।
১৯০২ খৃষ্টাব্দের সরমভোতে শ্রমিক ধর্মঘটের নেতা দিয়োতর জালোমোভের সংগ্রামী জীবনের অবিকল প্রতিচ্ছবি ‘মাদার’ উপন্যাসের নায়ক প্যাভেল ভ্লাসভ। ‘মাদার’ উপন্যাসের মায়ের চরিত্রটিও হুবহু জালোমোভের মায়ের আলোছায়া।
গোর্কী ‘মাদার’ উপন্যাসে জারতন্ত্রের নির্যাতন, শোষণ, হত্যা, গুম এসবের বিরুদ্ধে গুপ্ত রাজনৈতিক সংগঠনের সমস্ত সদস্যদের কার্যক্রম এবং রুশিয়ার প্রায় পারিবারিক মাতৃকুলের আত্মনিবেদন, অনুপ্রেরণা এবং অসীম সাহসিনী একজন আদর্শ বিপ্লবী নারীর প্রতিবিম্ব হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। উপন্যাসের নায়ক ভ্লাসভের মতো অনেক যুবকই তখন জারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গুপ্তদলে ও রাজনৈতিক অধিকারের আদায়ের আন্দোলনে যোগ দিতে উন্মুখ ছিল। ‘মাদার’র জননী চরিত্রটি রাশিয়ার শোষিত সমাজের অনেক পরিবারের মায়েরই চিত্রকল্প।
এই কালোত্তীর্ণ ও বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে সুদূর প্রবাবপ্রসারী ‘মাদার’ উপন্যাসটি পড়তে গেলেই বা সম্পূর্ণ উপন্যাসের যে আবহ তাতে মনে হয় তরুণ কার্ল মার্কস’র ‘Economic and Philosophical Manuscripts 1944’ এ জীবনদর্শনের সেই রোমান্টিক মিশ্রণে একটি জীবন সম্পর্কিত রহস্যময় পুনর্গঠন কিন্তু against Hope’ র মতো জীবনের স্থায়িত্ব দীর্ঘজীবীতা এবং পুনর্বার জীবনের কাছেই সফলভাবে ফিরে আসার স্বপ্নকেই সেই হতাশাগ্রস্থ সময়ে; রুশিয়ার শোষিত, নির্যাতিত মানুষের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন।
‘মাদার’ উপন্যাসটি তাই সারাবিশ্বের মানুষের কাছে তার নিজের অস্তিত্বের দিকে, জীবনের কেন্দ্রের দিকে ফিরে আসবার একটি সুপ্রশস্ত পথের মতো, ডুবন্ত জাহাজের কোন এক যাত্রী লাইফবোটে ভাসতে ভাসতে অকস্মাৎ তীরের দেখা পাওয়ার মতো; ফিরে পাওয়া এক নূতন জীবনের সংবাদের মতো। যে জীবন শুধু নিজের জন্য নয়; সমাজ, মানুষ, সবার জন্য সমর্পিত একটি বোধিসম্পন্ন জীবন। ‘মাদার’ উপন্যাসের ভ্লাসভ, নিলোভনা ও অন্যান্য চরিত্রের ছায়া প্রচ্ছায়ায় তাই যেন জেগে আছে।
লেখক : কবি, প্রাবন্ধিক; প্রতিষ্ঠাতা- চট্টগ্রাম লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র