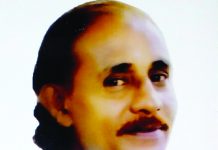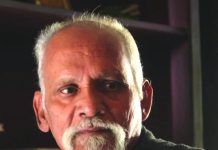নারীর নিরাপত্তা বিষয়টি ব্যাপক এবং আপেক্ষিক। ধর্মভিত্তিক ও পুরুষ শাসিত সমাজে বিষয়টি জটিলও বটে। অথচ এই নারী-সমাজ জনসমষ্টির মূল শক্তি। সন্তান প্রতিপালন, পরিবারের ব্যাবস্থাপনা, সেবামূলক কার্য ও মাতৃত্বের অপার মহিমায় মহিমান্বিত নারী চালিকা শক্তি হিসাবে নীরবে পুরুষ-সমাজকে এগিয়ে যেতে সহযোগিতা করে। ইদানীং বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ও নারী-শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যা নারীর সামাজিক নিরাপত্তাহীনতাকে প্রকট করে তুলেছে। নারীর আধিকার ও নিরাপত্তায় জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। ১৯৭৫ হতে ১৯৮৫ পর্যন্ত নারী উন্নয়ন দশক, ১৯৯৫ এর কায়রো সম্মেলন, ১৯৯৭ এর বেইজিং সম্মেলন এবং ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক “নারীর প্রতি বিরাজমান সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) সংক্ষেপে CEDAW নারী মুক্তির সনদ নামে পরিচিত। বাংলাদেশ সরকারও এই সকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে বিশ্বব্যাপী নারীর অধিকার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্যেগের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। আমাদের দেশের নারীর নিরাপত্তামূলক সামাজিক আইনগুলো কেন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার।
সামাজিক মর্যাদা, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, সম্পত্তিতে অধিকার, শিক্ষার সুযোগ ও সকল মৌলিক অধিকার দিয়ে সুস্থ জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা প্রদান করলে নারীর সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষা অনেকাংশে সহজতর হবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নারীর তুলনায় সামাজিকভাবে আমাদের দেশের নারীরা পিছিয়ে। এদেশে পুরুষদের শিক্ষার হার ২৯.৫% এবং মেয়েদের ১৩.৭%। ১৫ হতে ১৯ বছর বয়সী মেয়েদের ৭০ শতাংশই বিবাহিত। দেশের বিবাহিত নারীর ৮৭ শতাংশই স্বামীর দ্বারা শারীরিক, মানসিক, যৌন কিংবা অর্থনৈতিক নির্যাতনের শিকার বলে বিবিএস এর পরিসংখ্যান বলছে। গ্রামের দরিদ্র মহিলারা গার্মেন্টস শিল্পে, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও কুটির শিল্পে অধিক হারে অংশগ্রহণ করেছে, তথাপি তাদের নির্ভরশীলতার মাত্রা হ্রাস পায়নি। তারা মহিলা শ্রমিক বলে মজুরীও প্রান্তিক। গ্রামীণ এলাকায় নির্যাতনের হার অত্যধিক। কিছু অযৌক্তিক সামাজিক প্রথা চাপিয়ে দিয়ে নারীদের লাঞ্চনা করা হয়।
নারী যে শুধুই ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে তা নয়, যৌতুক প্রথা, লিঙ্গভিত্তিক শ্রম-বিভাজন, ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, স্বাভাবিক জীবন যাপনে ও মত প্রকাশে বাধা ইত্যাদি নানাবিধ শিকলে তারা বন্দী। ঘর থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত তাদের নিপীড়নের শিকার হতে হয়। পারিবারিক নির্যাতন আরও ভয়াবহ। পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়ে অনেক নারীর মৃত্যু ঘটে, আবার কেউ কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিচার এবং আইনী সহযোগিতা পাওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। নারী-পাচার, বাল্যবিবাহ, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করা, যৌতুক আদায়, উত্যক্তকরণ, কটূভাষা প্রয়োগ, জোরপূর্বক প্রেম করা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিয়ে দেয়া- এসব নারীর প্রতি বৈষম্য ও প্রচ্ছন্ন অনাচার। শিশু অবস্থায় মেয়েরা পিতার পরিবার থেকে জেনে আসে তারা এই পরিবারের স্থায়ী সদস্য নয়। এ সমাজে তারা অন্দরমহলের বাসিন্দা। তাদের একমাত্র পরিচয় গৃহিনী ও জননী। এভাবে কন্যা সন্তানরা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক বঞ্চনার শিকার। ঘরের বাইরে প্রথমে পা রাখতে হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। সেখানে সহপাঠী ও পুরুষ শিক্ষকের হাতে ধর্ষণের শিকার হতে হয়। এরপর কর্মস্থলে গিয়েও একই চিত্র। সহকর্মী থেকে শুরু করে উর্র্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা প্রতিদিনের পত্রিকা খুললে পাওয়া যায়। গণপরিবহনের অবস্থা আরও নাজুক, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নিরাপদ যানবাহনের কোনো ব্যবস্থা নারীদের জন্য আজও নেয়া হয়নি। ৪০ সিটের একটা বাসে ড্রাইভারের পাশে ১০ টির মতো সিট নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে, অন্য সিটে বসতে গেলেই নানা মন্তব্য ও কটূক্তি শুনতে হয়। গণপরিবহনে নারীর যৌন হয়রানি, ধর্ষণ এবং ধর্ষণের পর হত্যার মতো অমানবিক ঘটনাও ঘটেছে। তবে নারীর জন্য আলাদা বাস এর ব্যবস্থাই একমাত্র সমাধান নয়, মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে সর্বাগ্রে। সভ্যতার চরম উন্নতির সাথে সাথে আমরা ক্রমেই অন্ধকারে নিমর্জিত হচ্ছি। অথচ সংবিধানের ২৮ নং অনুচ্ছেদের ১ নং দফায় উল্লেখ আছে – ‘নারী-পুরুষভেদে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। ‘নারী সংগঠনগুলি ও রাষ্ট্রযন্ত্র নারীর নিরাপত্তামূলক সামাজিক আইনসমূহ প্রণয়নের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। নারীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে হবে। ১৯৯৫ সালে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ‘নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ১৯৯৫’ পাস হয়, যেখানে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। এই আইনের সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন থাকলে নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হতে পারতো। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০০৩) এর ১০ ধারায় যৌন নিপীড়নের শাস্তি সর্বোচ্চ ১০ বছর, নিচে ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান এবং অর্থদণ্ডও রাখা হয়েছে। এই আইন বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা হল নারীর গ্লানির ভয় ও লজ্জাবোধ। গবেষনা থেকে জানা যায়, নির্যাতনের শিকার হয়ে যেসব বিবাহিত নারী নারীকেন্দ্রগুলিতে যায় তাদের ৪৯.১৭% আইন সম্পর্কে অবহিত এবং ৫০.৮৩% অবহিত নয়। সুতরাং যে নারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে জানে না তার স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণ হবে কিভাবে? এছাড়া অর্থের অভাবে অনেকে আইনের আশ্রয় নিতে চায় না। অনেকক্ষেত্রে সাক্ষীর অভাবে এবং হুমকীর ভয়ে বাদী পালিয়ে বেড়ায়, ফলে অপরাধী খালাস পেয়ে যায়।
আমাদের দেশে নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা বিষয়টি অনেকটা শ্লোগান সর্বস্ব। নারীশিক্ষা প্রসার, গণসচেতনতা বৃদ্ধি, আইনের সফল বাস্তবায়ন ও পাঠ্যসূচিতে নারী-নিপীড়ন প্রতিরোধ বিষয়ক অধ্যায় সংযুক্ত করা জরুরি বলে আমি মনে করি।
তথ্যসূত্র : ১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা সংখ্যাঃ ৬৬ (নারীর নিরাপত্তায় বাংলাদেশে প্রচলিত সামাজিক আইন – মোঃ নুরুল ইসলাম ), ২. বাংলাদেশে নারী নির্যাতন, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র – বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ও জেরীনা রহমান খান
লেখক: সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালখালী হাজী মো. নুরুল হক ডিগ্রি কলেজ।