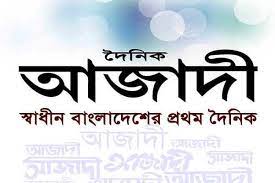দৃশ্যমান ও অদৃশ্য মহাপ্রাচীর
জন্মগতভাবে প্রায় সমুদ্রসমতলের মানুষ আমরা। আছি এখন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কতোটা উপরে সঠিক জানি না তা। তবে আন্দাজ করছি আছি হয়তো দুই আড়াই বা তিন হাজার ফুট উপরে মহাপ্রাচীরের এই মুতিয়ানু অংশে। এতোটা উচ্চতায় মহাপ্রাচীরের এই অংশের চড়াই উৎরাই ধীরেসুস্থে পেরুতেও যথেষ্ট শক্তিক্ষয় হওয়াটাই যখন আমাদের জন্য স্বাভাবিক, সেরকম অবস্থায় পুত্র আমার তার বালসুলভ চপলতার কারণে কিছুটা দৌড়ঝাঁপ করতে গিয়ে যে ভালই হাঁফিয়ে উঠেছে, দেখছি তার জোর ঘন ঘন শ্বাস টানা আর নিঃশ্বাস ফেলার সাথে তিনচার স্তর গরম কাপড়ের নীচে লুকিয়ে থাকা ছোট্ট বুকটির উঠানামা দেখে।
এমতাবস্থায় পানির বোতল হাতে পেলেই ঢক ঢক করে দ্রুত পানি খাওয়ার ইচ্ছে যে ওর হবেই সেটাও জানা কথা। অতএব বোতলের মুখ খুলে ওর হাতে তুলে দিতে দিতে সাবধান করার জন্য বললাম, বুঝতে পারছি বাবা, খুব টায়ার্ড হয়েছ। কিন্তু তা বলে তাড়াহুড়ো করে পানি খেতে যেও না এখনি। ধীরে ধীরে খাও। তাড়াতাড়ি পানি খেতে গিয়ে, পানি নাকে মুখে উঠে গেলে ঝামেলা কিন্তু বাড়বে। কষ্ট তো হবে তোমার। আর শোন, এখন আর দৌড়াদৌড়ি না। চল ঐ ঘরটাতে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তারপর ফিরে যাবো।
অল্প দূরে থাকা এই ঘুমটি ঘরটি থেকে ঐ ঘুমটি ঘরটি মানে যেখানে অপেক্ষা করছে পরিবারের বাকীরা, তার দূরত্ব কতোটা হবে? ধীরেসুস্থে ঘরটিতে ঢুকতে ঢুকতে কথাটা মনে হতেই ঘাড় ঘুরিয়ে চোখ আন্দাজে মনে হল, হবে হয়তো কিলোমিটার খানেক।
‘বাবা, বাবা ঐ যে দেখো, এখানেও দেখো কতো নাম লেখা! গ্রেটওয়ালের এ জায়গাগুলো মনে হয় নাম লেখার জন্যই রেখেছে’। ঘরটিতে ঢুকে বাঁ দিকের একটা জুতসই কার্নিশে বসেই উল্টো দিকের জানালার উপরের দিকে অংশটিতে পেছনে ফেলে আসা ঘরটিতে যেমন দেখা গিয়েছিল, তেমনি একটা আয়তাকার জায়গায়, নানান রঙ্গয়ের আঁচড়ে লেখা নানান ভাষার অক্ষর ও শব্দাবলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো দীপ্র।
বোঝা গেল, এরকম একটা ঐতিহাসিক স্থাপনায় নিজের নামটি লিখে রাখার প্রবল ইচ্ছাটি তার এখনো রয়েছে অটুট! ভাবলাম বলি, শোন বাবা এভাবে কোথাও এমন কি পাথর খুদেও নাম লিখে রেখেও কেউ তার নামকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। সময়, কাল তা মুছে দেয় তার নিজস্ব নিয়মে। নিজ নাম লিখে রাখতে হয় নিজের সুকর্মের মধ্য দিয়ে। তাতেই সে নাম হয়ে উঠে অব্যয় অক্ষয়। সাথে সাথেই মনে হল, আসলেই কি তাই? দুষ্কর্মের মধ্য দিয়েওতো কতজন তার নাম মানব ইতিহাসে অক্ষয় করে রেখেছে! এই যে কুবলাই, চেঙ্গিস, হালাকু খানেরা মঙ্গোলিয়ান সাম্রাজ্য বাড়াতে গিয়ে যা করেছিল, তাতে মানব ইতিহাসের ক’টা উপকার হয়েছে? সদ্য কৈশোরে উত্তীর্ণ হয়ে, যুক্তিতে বাবা মা’কে হারিয়ে দেবার জন্য মুখিয়ে থাকা পুত্রের কাছে আমার ঐ ‘সুকর্মযুক্তি’ মার খেয়ে ভূত হয়ে যেতে বাধ্য। থাক ঐ দিকে না গিয়ে, বরং চুপ করেই থাকি। ও তো নিশ্চয় ‘মৌনং সম্মতি লক্ষণং’ বলে যে প্রবচন আছে তা তো আর জানে না!
‘আচ্ছা বাবা, মঙ্গোলিয়ান আর চায়নিজ রা কি একই না?’ দেয়াল থেকে বেরিয়ে আসা একটা কার্নিশে বসে পা দোলাতে দোলাতে জানালার বাইরে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজে ঢাকা পাহাড় পর্বতগুলোর দিকে চোখ ফেলে করা পুত্রের এই প্রশ্নে থতমত খেলাম। কারণ এ জগতজীবনের বেশির ভাগ প্রশ্নের উত্তরই তো জানে না এ অধম। আর এ তো বড়ই জটিল প্রশ্ন। এর সঠিক উত্তর দিতে হলে তো থাকতে হবে নৃবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক সম্যক ধারনা, যার জানি আমি লবডঙ্কাটা!
তারপরও নিজের ইজ্জত রক্ষার্থে আমতা আমতা করে বললাম, হুম ওরা সবাই দেখতে একই রকম হলেও পুরোপুরি এক না। ওদের মধ্যে আবার অনেক ভিন্ন ভিন্ন জাত আছে। এই যেমন ধরো আমরা আর কলকাতার মানুষ দেখতে একই রকম হলেও আমরা তো এক না, তাই না?
‘কিন্তু বাবা, তা হলে কি দেশ ভাগ হয়ে গেলেই মানুষ ভিন্ন হয়ে যায় নাকি? একসময় তো বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান একসাথে ছিল। আমরা কি তখন তাহলে এক ছিলাম’?
আধাখেঁচড়া উত্তর দিতে গিয়ে, পড়েছি যে পুত্রের কাছে বিশাল বিপাকে বুঝলাম তা হাড়ে হাড়ে। কিন্তু এখন তো আর পিছু হটলে চলবে না! একটু ঢোক গিলে তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যা পাশ দেবার জন্য এ বিষয়ে যা পড়েছিলাম তা থেকে যতোটুকু মনে আছে তার শরণ নিয়ে বলতে শুরু করলাম–
শোন বিজ্ঞানীরা মানুষের মধ্যে মোটা চারটা রেইস আছে বলে মনে করেন, আর সেগুলো হল নিগ্রোয়েড, মঙ্গলোয়েড, ককেশয়েড, আর অস্ট্রালয়েড। সে হিসাবে এখন যাদের আমরা চায়নিজ বলি, কিম্বা যারা মংগোলিয়ান নামে পরিচিত, কিম্বা এমন কি আমাদের দেশে যাদের আমরা চাকমা বা গারো বলি, তারা সবাই এক রেইস মানে মঙ্গোলয়েড রেইসের। সে দিক থেকে চায়নিজরা আর মঙ্গোলিয়ানরা অবশ্যই এক।
‘তাহলে তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে এতো বড় একটা গ্রেট ওয়াল বানাল কেন’?
হায়! পড়লাম তো দেখি এবার এক্কেবারে যাকে বলে সখাত সলিলে! এরকম অতি সহজ প্রশ্নের কোনো ধরনের উত্তরই তা জানি না! বেশ একটা জোর দম নিয়ে তাই বললাম, শোন এই দেয়াল তো আমরা দেখতে পাচ্ছি বাবা, সেই জন্যই বলছো ওরা যদি একই হবে তবে এতো বড় দেয়াল কেন বানালো নিজেদের মধ্যে! কিন্তু মানুষ তো এর চেয়ে অনেক বেশি উঁচু আর শক্ত মহা মহাপ্রাচীর বানিয়েছে নিজেদের মধ্যে। সমস্যা হচ্ছে সেসব চোখে দেখা না গেলেও সেগুলোকেই বেশির ভাগ মানুষই চরম সত্য বলে মানে। তাও আবার যা তা মানা না, খুবই দৃঢ় ভাবে মানে তা। ফলে ঐসব অদৃশ্য মহাপ্রাচীর যতো বেশি রক্ত ঝরিয়েছে এ যাবতকালে মানুষের সমাজে এবং ঝরাচ্ছে এখনো, সে তুলনায় দৃশ্যমান এই মহাপ্রাচীর ঘিরে রক্তপাত অনেক অনেক কমই হয়েছে। এটুকু বলেই মনে হল আচ্ছা সদ্য কৈশোরে পা দেয়া পুত্রের জন্য আমার এই উত্তর কি খুব বেশ জটিল ভাবের হয়ে গেল না?
এ ভেবে উল্টো দিকের দেয়ালের কার্নিশে বসে পূর্ণ দৃষ্টিতে পুত্রের চোখে মুখের ভাষা পড়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম যে, ব্যাপারটি কি ও বুঝেছে? কিম্বা আদৌ কি ও কর্ণপাত করেছে সে, আমার মতো অদার্শনিক মুখনিঃসৃত এই দার্শনিক বাৎচিত? নাহ, কিছুই বুঝতে পারলাম না ওকে দেখে। তবে চোখের দৃষ্টি যেহেতু এই ঘরেই আবদ্ধ এখন, তাতে এ পরিষ্কার যে সামনের জানালা দিয়ে বাইরের হিম বাতাসে ওর মনে উড়ে চলে যায়নি দূরে কোথাও।
ও তাহলে ভাবছে না কি নিজ মনে একান্তে, যা বললাম তা? দাঁড় করাচ্ছে ব্যাখ্যা নিজের বুঝ মতো? আচ্ছা ওকে কি মানবসমাজের ঐসব অদৃশ্য মহাপ্রাচীর সমূহের দুয়েকটার জাজ্বল্যমান উদাহরণ দেব নাকি? কিন্তু তা দিলেই তো দেখা যাবে, তাতে ওর জন্য পিতা হয়ে আমি নিজেই বাড়াচ্ছি বিপদ। ও এখন যে বয়সে আছে, তাতে সম্ভবত ওর মনে এখনো এক্কেবারে সবজান্তা মানুষ না হলেও আশেপাশের অনেকের চেয় ঢের বেশি জানা মানুষ হল তার পিতাই। অতএব আমার কাছে শোনা ঐসব উদাহরণ যদি, দেশে গিয়ে বাইরের কারো সামনে ফস করে বলে দেয়, তবে তো হতে পারে ওর মহাবিপদ! ওইরকম কথা বলতে গিয়ে নিজেই তো পড়েছি এবং এখনো পড়ি অহরহ, সমাজের বাস্তব আর ভার্চুয়াল জগতে ঘুরে বেড়ানো মধ্যযুগীয় শ্বাপদদের হুমকির মুখে। আমাদের সমাজ শুধু যে কৌতূহলী মনের উপরই খড়গহস্ত তা তো নয়। ভিন্নমতাবলম্বীর ঘাড়ের উপর অষ্টপ্রহর কিরিচ তরবারি ছুরিকা ধরে রাখা শ্বাপদেরা গিজগিজ করছে চারিদিকে সারাক্ষণ। নাহ, কোনোই দরকার নেই আমার সোহরাবরুস্তম কাহিনির পুনরাবৃত্তি করার।
ওপাশে ঝিম মেরে বসে থাকা পুত্রের দিকে তাকিয়ে মনে মনে এতোসব কথা ভেবেও কি না অবশেষে অভ্যাসের দোষেই করেই বসলাম ভুলটা! জিজ্ঞেস করলাম, কী বুঝলে বাবা? তবে এখন যদি না বোঝ তাতেও চলবে। বড় হয়ে নিজে পড়ে, জেনে, বুঝে নিতে পারবে এ সব।
‘হুম বুঝতে পেরেছি। জানি! ইটস রিয়েলি ব্যাড’!
আমাদের সমাজে বাচ্চাদের, বিশেষত সদ্যকিশোরদের যে ধরনের আচরণকে জ্যাঠামি বলে তিরস্কৃত করা হয়, দীপ্রর কাছ থেকে আসা উত্তরটির চেয়ে, তার ভঙ্গিটাকে সে রকম মনে হতেই, ভাবলাম হায়রে! অবশেষে নিজেই কি না ঠেলে দিলাম পুত্রকে ঘোরতর বিপদে। এখন জানা দরকার মানব সমাজের ঠিক কোন জিনিশটাকে ও এজন্য দায়ী করে, ঐ রকম একটা রায় ঘোষণা করলো ও!
‘হাই গাইস’
এই চীনভ্রমণে আসার পর থেকে, প্রথমবারের মতো এ মুহূর্তে পশ্চিমা এক্সেন্টের এই ইংরেজি শব্দদ্বয় কানে যেতেই পিতাপুত্র একইসাথে ঘুমটি ঘরের উল্টা দিকের দরজার দিকে তাকিয়ে স্বয়ংক্রিয় ভাবে যুগলকণ্ঠে নিজেরাও বলে ফেলেছি ‘হাই’।
আমাদের উত্তরের সাথে পাল্লাহীন ঐ দরজার মুখে যে অদৃশ্য আলীবাবা পাল্লা ছিল তা বুঝি হাত করে খুলে গেল। ফলে দরজার মুখে এসে একটু থমকে দাঁড়ানো যুগল, সাথে সাথেই হাসিমুখে পা রাখলো এই ভেতর ঘরের। বোঝা যাচ্ছে বেশ ভারী ব্যাকপ্যাক পিঠে নিয়ে, মহাপ্রাচিরের ঐ অংশের কোনো এক জায়গা থেকে হেঁটে এসেছে দু’জনে। কোন দেশের যে তারা? তা তো জানি না সঠিক আবার জিজ্ঞেস করাটাও অনুচিত। তবে অপরিচিত লোকজনদের ‘হাই গাইস’ বলে তো যতোটা জানি আমেরিকানরাই সম্বোধন করে। সেক্ষেত্রে তরুণ তরুণীর আমেরিকান হবার সম্ভাবনাই প্রচুর।
‘ক্যান উই শেয়ার দিস প্লেস?’ হাসিমুখে প্রশ্নটি করলো এবার তরুণ।
অফ কোর্স। ইটস এ পাবলিক প্লেস। বলেই বুজতে পারলাম, আমাদের দুজনকে ঘুমটি ঘরটির দুই উল্টো দিকের কার্নিশ বসে থাকতে দেখায়, এরা হয়তো ভেবেছে গোটা ঘরটাতেই বুঝি নিজেদের দখলিসত্ব কায়েম করেছি। তরুণকে উত্তর দিয়ে দ্রুত নিজপুত্রের দিকে এগিয়ে যেতেই, সহাস্যে যুগল গলায় ধন্যবাদ দিতে দিতে ওরা দুজনেই ঐ পাশটায় গিয়ে নিজ নিজ পিঠের ভারী ব্যাকপ্যাক মেঝেতে নামাতেই, কেন জানি মনে হল, অনেক হয়েছে নিজেদের বিশ্রাম! এবার এদেরকে একটু প্রাইভেসি দেওয়া দরকার। এদের ব্যাকপ্যাকের সাইজ দেখে মনে হচ্ছে, এরা নির্ঘাত ব্যাকপ্যাকার টুরিস্ট, যাদের দর্শন হচ্ছে কম খরচায় যতো বেশি পারা যায়, এই দুনিয়ার নানান দিকে যতো বেশি পারা যায় ঘুরে বেড়ানো। আমাদের মতো আতিক্কা শখের ভ্রামণিক না এরা। এরাই হলো বরং জাত ভ্রামণিক। কোনদিক থেকে বা কতদূর থেকে হেঁটে যে এরা এসেছে এইমাত্র এখানে তা জানি না। তবে দেখে মনে হচ্ছে, এই জায়গায় তারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে চায়।
তাছাড়া আমাদেরও তো আছে ফেরার তাড়া। অতএব এক্ষুনি দিতে পারি ফিরতি হাঁটা। কিন্তু কথা হচ্ছে, এ ক’দিন নানান জায়গায় চায়নিজ টুরিস্টরা আমাদের উপস্থিতিকে যে ভাবে অবলীলায় উপেক্ষা করে নিজেদের কাজ চালিয়েছে যথেচ্ছারের মতো, এরা তো করেছে তার ঠিক উল্টো। যথেষ্ট বড় এই ঘরটাতে আমাদের দুজনের অকিঞ্চিৎকর উপস্থিতিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আমাদের কাছেই কি না পারমিশন চেয়েছেন! যার আদৌ দরকার ছিল না। এখন এই মুহূর্তেই যদি বেরিয়ে যাই, তবে ওরা ভাবতে পারে যে ওদের উপস্থিতিতে আমাদের প্রাইভেসি না হোক, কোন শলাপরামর্শের ব্যাঘাত ঘটেছে বুঝি। তাতে ওরা বিব্রত বোধ করলেও করতে পারে। দীপ্রর পাশে বসে ফিসফিসিয়ে তাই বললাম, বাবা ধরো আর মিনিট দুয়েক বসে থেকে, তারপর আমরা বেরিয়ে যাবো এখান থেকে, কেমন?
লেখক : প্রাবন্ধিক, ভ্রমণ সাহিত্যিক।