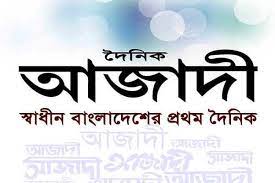বাবা– কতটা আপন ছিলে
বুঝিনি তার চিলে কণাও –২
বলছিলাম বাবার কথা। সে কথা কি লিখে শেষ করার মত? অনার্স শেষ করে মাস কয়েক অবসর। অপেক্ষা রেজাল্টের। এদিক–ওদিক ঘুরাঘুরি, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে সময় কাটে। একদিন মেজদা বললো, নূতন ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা বের হচ্ছে। তুই খোঁজ নিয়ে দেখতে পারিস। ঠিকানা জোগাড় করে গেলাম এক দুপুরে সদরঘাট এলাকায়, একেবারে নদীর ধারে। নিচে প্রেস, দোতলায় কমার্শিয়াল সেকশনে সুশ্রী এক চটপটে মহিলা। দেখে দৃষ্টি জুড়ায়, মনও। ভালো লাগলো প্রথম আলাপেই, বেশ বন্ধুসুলভ। নাম? মনে নেই। সে তো অনেক দিনের কথা। জীবনের এই চলার–পথে কত জনের সাথেই তো পরিচয় ঘটে। কারো স্মৃতি, কারো নাম মনে গেঁথে থাকে, অনেকের স্মৃতি, নাম কিছুদিন বাদে বিস্মৃতির আড়ালে চলে যায়। ঢাকা থেকে আসা ওই মহিলা বললেন, আগামীকাল একটা ‘সিভি’ নিয়ে আসুন। সেখানে নিউজ ডেস্কে দেখা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ডিপার্টমেন্টের হ্যাংলা–পাতলা গড়নের জিয়াউল হকের। তাকে চিনতাম, ইউনিভার্সিটিতে একই করিডোরে, একই বিভাগে দেখতাম। আমার বছর দুই সিনিয়র, যদিওবা আলাপ হয়নি কখনো। পরবর্তীতে তো বন্ধুই হয়ে গেল। সে অনেক স্মৃতি ডেইলী লাইফে, বছর চারেক সাংবাদিকতার সময়, ১৯৭৯ শেষ থেকে ১৯৮৪ সালের প্রথম দিক তক। তার সাথে টুকটাক আলাপ হলো। পরদিন গেলাম সিভি নিয়ে। যোগ দিলাম চট্টগ্রাম থেকে বের হওয়া প্রথম ইংরেজি দৈনিক, দি ডেইলী লাইফে। ঢাকা থেকে এলেন প্রথিতযশা সাংবাদিক, রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ওয়াহিদুল হক। চট্টগ্রাম থেকে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, লেখক আবুল মোমেন, এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, অধ্যাপক তপন জ্যোতি বড়ুয়া ও আরো জনা কয়েক। রমরমা দশা পত্রিকার। সে সময়কার লিডিং পত্রিকাগুলি থেকে একেবারে ভিন্ন। বাবার হোটেলে থাকি, খাই। অতএব, টাকা উপার্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। মাসিক দু–শ টাকা দিয়ে শুরু হলো সাব–এডিটর হিসাবে কাজ। আমাকে মাঝাঘষা করে ‘সাংবাদিকতার প্রথম পাঠ’ শেখানোর দায়িত্ব পড়লো বেটে–খাটো স্বল্পভাষী ফরিদা আকতারের উপর। পরে তিনি তো বিখ্যাত হয়ে গেলেন ঢাকায় নারী–বিষয়ক উন্নয়ন সংস্থা ‘উবিনীগের’ প্রধান কর্ণধার হয়ে। মাস কয়েক পর হলাম রিপোর্টার, বেতন বেড়ে হলো চারশ।
চাকরিতে যোগ দিয়েছে শুনে বাবা গেলেন ক্ষেপে। তার কথা, ‘লেখাপড়া গোল্লায় গেল। মাস্টার্স আর দেয়া হবেনা।’ তিনি খুব হতাশ। তাকে আশ্বস্ত করে বলি, কাজের পাশাপাশি এমএ পরীক্ষা দেব। এক সময় ক্লাস শুরু হলো। সকাল ৭–২০ মিনিটে চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়া শাটল–ট্রেনে ভার্সিটি যাওয়া–আসা শুরু হলো। শুরু যা হলো না, তা হলো লেখাপড়া। মন পড়ে থাকতো পত্রিকায়। ভার্সিটি থেকে দুপুর দুটো নাগাদ বাসায় ফিরে, মুখে খাবার গুঁজে দিয়ে, রেল স্টেশনের ওভারব্রিজ হেঁটে পার হয়ে সোজা সদরঘাট ডেইলী লাইফ অফিস। বাবার কথাই সত্যি হলো। সে বছর আর মাস্টার্স দেয়া হলো না। দেয়া হলো পরের বছর। তখন মেজদা সবে মাস্টার্স পাস করেছে। বাবা বলতেন, ‘তোরা যদি মাস্টার্স শেষ করতে না পারিস, তাহলে মরেও আমি শান্তি পাবো না।’ আমার জন্য তার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না। অন্যদের বলতে শুনতাম, ‘ওর মাথা ভালো, কিন্তু লেখাপড়ার ধারে–কাছে নেই।’ আমার ‘মাথা’ সম্পর্কে বাবার এমন উচ্চ–ধারণা কেন ছিল জানিনে। কেননা আমার সম্পর্কে আমার নিজের তেমন ধরনের কোন ধারণা ছিলনা। মনে আছে, মেট্রিক পরীক্ষার আগে ‘ব্রেন টনিকের’ বিজ্ঞাপন দেখলাম পত্রিকায়। ধারণা বদ্ধমূল হলো যে এটি খেলে বিজ্ঞাপনে যা যা উল্লেখ করেছে তাই হবে, অর্থাৎ ব্রেন উর্বর হবে, পরীক্ষায় আশ্চর্য সফলতা আসবে। আবদার ধরলাম, এটি কিনে দিতে হবে। কিন্তু আমার আবদার (এখন মনে হয় অন্যায় আবদার) বাবার কাছে খুব একটা গুরুত্ব পেলো না। উল্টো তিনি যা করলেন তা হলো মেট্রিক পরীক্ষার মাস খানিক আগে তার এক প্রিয়ভাজন, কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক বিমল কান্তি বড়ুয়াকে ডেকে বললেন, ‘বিকাশকে তোমার কাছে পাঠাবো। তাকে বাংলা–ইংরেজিটা একটু দেখিয়ে দিও’। বিমল স্যার ছিলেন স্কুলের কড়া শিক্ষকদের তালিকার প্রথম দিকে। বিকেলের দিকে তিনি প্রায়শ আমাদের বাসায় আসতেন। মা–বাবার সাথে গল্প করতেন। তাকে দেখলে আমি ধারে–কাছে ঘেঁষতাম না, ভয়ে। কিন্তু তার কাছেই যেতে হলো। আমার মনের দশা তখন ‘পড়বি তো পড় একেবারে মালির ঘাড়ের’ মত। তার বাসা আলকরণ। স্টেশন রোড থেকে হেঁটে তার বাসায় যেতাম। প্রথম দিন গিয়ে দেখি স্কুলে আমার সহপাঠী মৃদুল গুহ (পরবর্তীতে এডভোকেট ও প্রয়াত) সহ আরো বেশ কিছু ছাত্র লম্বা স্কুলের বেঞ্চে বসে ‘প্রাইভেট’ পড়ছে। মাস খানেক আমারও স্থান হলো ওদের দলে। এইখানে আসা ও বিমল স্যারের কাছে বিনে–পয়সায় প্রাইভেট পড়া, আমার জীবনের ‘টার্নিং পয়েন্ট‘ বললে এতটুকু বাড়িয়ে বলা হবে না। আমার বাংলা ও ইংরেজির যে ভিতটুকু আছে তার সম্পূর্ণ অবদান বিমল স্যারের। তিনি এমনভাবে পড়ালেন যে বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণ পুরোপুরি করায়ত্ত করেছিলাম অল্প সময়ে এবং ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েটে বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণে ফুল–মার্কস পেয়েছিলাম। স্কুল বয়সে যে বিমল স্যারকে দেখলে ভয়ে কাছে যেতাম না, সেই স্যারের সাথে পরবর্তীতে একটা পর্যায়ে বন্ধুর মত আলাপচারিতা হতো। তারও কিছু সময় পর তিনি তো আমার নিকট আত্মীয় হয়ে গেলেন। হল্যান্ড প্রবাসী তার সহোদরের একমাত্র কন্যার কারণে। এখন তার বয়স ৮৮ পেরিয়েছে। মনেপ্রাণে তার দীর্ঘায়ু কামনা করি।
বাবার ছবি তোলায় বেশ শখ ছিল। অফিসের ‘বিহারি‘ ক্যামেরাম্যানকে বাসায় ডেকে এনে নানা সময় আমাদের সবার ছবি তুলেছেন। তার কিছু কিছু এখনো আছে। স্কুল বয়সে বাবার সাথে বেশ ঘুরেছি। রেলওয়েতে তার চাকরির সুবাদে আমরা সবাই বিনে পয়সায় ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসে ভ্রমণ করার সুযোগ পেয়েছি। তিনি বছরে নির্দিষ্ট সংখ্যক ‘পাশ’ পেতেন। তার সাথে, মা সহ আমার প্রথম ঢাকা যাওয়া, সেখানে ঘোড়ার–গাড়ি চড়া। গুলিস্তানের কাছেই ছিল সে সময় ঢাকার একমাত্র রেল স্টেশন। ছিলাম আজকের পুরান ঢাকার এক হোটেলে। পাকিস্তান আমলে পুরান ঢাকাকে ঘিরেই ছিল ঢাকা। গ্রামের বাড়ি গেলে খুব মজা করে যেতাম। তখন চট্টগ্রাম–দোহাজারী রেল যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত চমৎকার। আমরা নেমে পড়তাম পটিয়া স্টেশনে। রেল স্টেশনগুলি ছিল পরিষ্কার। এখন জেনেছি বছর কয়েক ধরে গোটা চট্টগ্রাম–দোহাজারী রেল সংযোগই নেই। গোটা ট্রেনে সে সময় থাকতো দুটো কী তিনটে প্রথম শ্রেণির কামরা। নিজেকে একটা কিছু মনে হতো।
আগেই বলেছি বাবা ছিলেন অত্যন্ত সৎ এবং আজীবন সোজা পথে চলেছেন। তিনি ছিলেন রেলওয়ের হাউসিং এলোকেশন কমিটিতেও। জেনারেল ম্যানেজার অফিসে থাকার সুবাদে। নিয়ম মেনেই সুপারিশ করে বাবা পরিচিত কাউকে কাউকে ‘বাংলো’ পাইয়ে দিয়েছেন। এই ব্যাপারে একটি মজার ঘটনা ভাগাভাগি করি। তখন আমার স্কুল–বয়স। বাসায় অতিথি এলে আমরা (বোধকরি ভাইবোনদের মধ্যে আমিই একমাত্র) অপেক্ষা করতাম অতিথি কখন যাবে আর তাদের আনা–প্যাকেট কখন খুলতে পারবো। এক সন্ধ্যায় পড়ছি। এমন সময় এলেন এক দম্পতি। পারিবারিকভাবে আমাদের পরিচিত। আমার হাতে মিষ্টির প্যাকেট দিতেই সেটি নিয়ে দৌড়ে রান্নাঘরে মা–কে দিয়ে ফিরে আসলাম পড়ার টেবিলে। মনে মনে অপেক্ষায়, কখন বিদায় নেবে অতিথি। কিন্তু একি! হঠাৎ দেখি বাবা কিছুটা উত্তেজিত। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, আমাকে বললেন প্যাকেট ফিরিয়ে আনতে। ভদ্রলোক যতই বলেন, ‘না আমি অন্য কিছু ভেবে আনিনি, ভাইপো–ভাইঝির জন্যে এনেছি’, বাবা ততই উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন, ‘আপনি এক্ষুণি এই প্যাকেট নিয়ে বিদায় হন’। ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে নিয়ে, হাতে মিষ্টির প্যাকেট, বাসা থেকে বের হয়ে গেলেন। মনে মনে খুব রাগ হলো বাবার উপর। তাদেরকে এইভাবে বিদায় দেয়াটা যত না খারাপ লেগেছিল, তার চাইতে বেশি খারাপ লেগেছিল মিষ্টির প্যাকেটটা হাতছাড়া হয়ে গেল দেখে। পরে জেনেছি ওই ভদ্রলোক অন্যায়ভাবে বাসা এলোটমেন্ট চেয়েছিলেন। ছোট্ট ঘটনা, কিন্তু এতেই একজন ব্যক্তির সততার প্রমাণ মেলে। আমাদের ছিল বড় পরিবার। অনেক টানাটানি গেছে। কিন্তু বাবা তার নীতি থেকে সামান্যতম বিচ্যুত হননি, সুযোগ ছিল অনেক। আমাদের সব ভাই–বোনদের লেখাপড়ার জন্য আজীবন কষ্ট করে গেছেন। তিনি ছিলেন অত্যধিক চাপা। নিজের কষ্ট নিজের মাঝে লুকিয়ে রাখতেন। এমন কী শেষের দিকে তার যখন মারাত্মক শারীরিক দশা, তখনও তিনি আমাদের কাছ থেকে লুকিয়েছেন। নিজে নিজেই ডাক্তারের কাছে যেতেন। কেবল একবার আমাকে সাথে নিয়ে রিকশা চড়ে হাসপাতাল গিয়েছিলেন ডাক্তার দেখাতে। টানাটানির সংসার। কিন্তু কোনদিন, এমন কী আমরা যখন চাকরি করছি– তখনও বলেননি, তোরা কিছু আর্থিক–সাপোর্ট দে। এমনই ছিলেন বাবা। বোধকরি সব বাবাই এমন হয়। স্ত্রী, সন্তানদের সমস্ত কষ্ট, ঝঞ্ঝা থেকে বাইরে রেখে নিজের কাঁধে নিয়ে নেয় গোটা সংসারের ঝামেলা, সব দুঃখ, কষ্ট, সবকিছু, হাসিমুখে। বাবা মারা গেছেন ২৫ জুলাই ১৯৮২ সাল। তাকে কখনোই মুখ ফুটে বলা হয়নি, ‘বাবা ভালোবাসি তোমায়’। যেখানে আছ বাবা, ভালো থেকো।
লেখক : সাহিত্যিক, কলামিস্ট