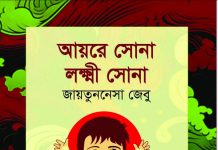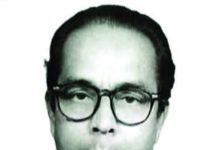কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঊনবিংশ শতকে জন্মগ্রহণ করে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত দেখে গিয়েছিলেন। মূলত ঊনবিংশ শতকের বাংলার সমাজজীবনের মধ্যে থেকেই তাঁর চেতনার উন্মেষ। তাঁর সমসাময়িক বঙ্গসমাজের চালচিত্রের আবহাওয়ার মধ্য দিয়েই তাঁর সাহিত্যের উদ্বোধন। বাংলার সমাজজীবনে পুরুষতান্ত্রিক এই মানবসভ্যতার ঘেরাটোপে নারীজীবনের অস্তিত্বের সংকট কবি খুব কাছ থেকেই দেখেছেন বলেই এই অব্যবস্থার রূপ দিয়ে গেছেন তাঁর সাহিত্য প্রতীতিতে। ‘রবীন্দ্র ছোটগল্প’ এর সুবিশাল ব্যাপ্তিতে নারীজীবনের অস্তিত্বের সংকট বারেবারেই ফিরে এসেছে। ‘স্ত্রীর পত্র’, ‘হৈমন্তী’, ‘অপরিচিতা’, ‘ঘরে-বাইরে ‘ প্রভৃতি ছোটগল্পের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে নারীজীবনের এই অস্তিত্বের সংকটের আবহমান বেদনার অনুভব। ‘হৈমন্তী’র হৈম, ‘অপরিচিতা’র কল্যাণী, কিংবা ‘ঘরে-বাইরে’ গল্পের বিমলা, এই চরিত্রগুলোতে সংস্কার আন্দোলনের ছায়া থাকলেও তারা কিন্তু কেউই এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ দেখাতে পারেনি, যেটা পেরেছে একমাত্র ‘স্ত্রীর পত্র’ ছোটগল্পের তুখোড় প্রতিবাদী চরিত্র ‘মৃণাল’।
মূলত তৎকালীন গোঁড়া সমাজব্যবস্থায় ‘মৃণাল’ চরিত্রটি উপস্থাপনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ নারীমুক্তি, নারীপ্রগতি বা নারীবাদ… যাই বলিনা কেন, মূলত শুভবুদ্ধিসম্পন্না, ব্যক্তিত্বময়ী এক নারীচরিত্রকে পাঠকসমাজে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন।
কাহিনীর বিচারে ” স্ত্রীর পত্র” ছোটগল্পটির কাহিনী সামান্যই।
গল্পের মুখ্য চরিত্র মৃণালের বড় জায়ের খুড়তুতো বোন বিন্দু অনাথ আর অসহায় বলে শত অনাদর, অবহেলা সয়েও বোনের শ্বশুরবাড়িতে পড়ে আছে। বোনের শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাদের ঘাড় থেকে এই বোঝা নামানোর জন্য এক উন্মাদ পাত্রের সাথে বিন্দুর বিয়ে দেয়। পরবর্তীতে উন্মাদ স্বামীর হাত থেকে প্রাণে বেঁচে ফিরে আবার দিদির শ্বশুরবাড়িতেই আশ্রয় নেয় অসহায় এই মেয়েটি। কিন্তু মৃণালের শ্বশুরবাড়ির লোকজন যখন সমাজের দোহাই দিয়ে আবারো সেই উন্মাদ স্বামীর সংসারেই তাকে ঠেলে পাঠিয়ে দেয়ার তোড়জোড় শুরু করে তখন বাড়ীর মেজবৌ মৃণাল প্রবলভাবে বাধা দেয়। কিন্তু সে অসফল হয়। আর কোনো উপায়ান্তর না দেখে একপর্যায়ে অসহায় বিন্দু গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা জুড়োয়। বিন্দুর দিদির মেজ জা, মানে এই বাড়ির মেজবৌ মৃণাল বিন্দুর প্রতি শ্বশুরবাড়ির এই নির্মম এবং অন্যায়কাজের প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও অসহায় এই মেয়েটির জীবন রক্ষা করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়, এটাই ‘স্ত্রীর পত্র’ ছোটগল্পটির মূল কাহিনী। সাধারণভাবে দেখতে গেলে এই কাহিনীটা যতই সাদামাটা ভাবের হোক না কেন গল্পের মূলবার্তা কিন্তু অত্যন্ত সুগভীর। তৎকালীন পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মৃণালের মত প্রাজ্ঞসর চেতনার অধিকারী এক নারীও কিভাবে পুরুষতন্ত্রের হাতে অবরুদ্ধ হয়ে ছিল, এবং শেষ পর্যন্ত সেই জাল কেটে বেরিয়ে এসে নিজসত্ত্বাকে কিভাবে আপন অস্তিত্বের মাঝে প্রত্যক্ষ করেছে। গল্পের মূল বার্তা সেখানেই!
গল্পের শুরুটা একটু ভিন্নধর্মী। সাধারণ একটা মেয়ে মৃণাল, যে কিনা নিষ্পেষিত নারীজাতির প্রতিনিধি হয়ে সমাজের সকল অন্যায়, সংসারের সকল অশোভন আচরণগুলোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে স্বামীর কাছে দেয়া এক চিঠির মোড়কে মূলত নিজের প্রতিবাদী এক জবানবন্দীই পেশ করে।
বিন্দুর প্রতি সমাজ-সংসারের এই সীমাহীন অন্যায়ের প্রতিবাদে গৃহত্যাগী মেজবৌ মৃণাল তার স্বামীকে লেখা পত্রের শুরুতেই ঘোষণা করেছে,‘আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি যে, আমার জগত এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানা লিখছি। এ তোমাদের মেজবৌয়ের চিঠি নয়।’ বাংলার সমাজজীবনে মেয়েদের এই যে একটা বড় পরিচয়, ‘বাড়ীর বৌ’ আর সেই সূত্রেই পরবর্তী জীবনে সন্তানের জননী, রবীন্দ্রনাথ যেন ‘মৃণাল’ চরিত্রটির মাধ্যমে মেয়েদের সেই নামসর্বস্ব পরিচিতিটাকেই চ্যালেঞ্জ জানালেন!
স্বামীকে পাঠানো এই চিঠিতে মৃণাল দ্ব্যর্থকন্ঠে আরো ঘোষণা করেছে যে, সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে মানে স্বামীগৃহে সে আর ফিরবে না। সে জানিয়েছে, ‘তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনে। আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ’- সে আরো জানিয়েছে যে, সে মরবে না, বাঁচার মত করেই বাঁচবে।
মৃণালের এই বাঁচার লড়াই কিন্তু একদিনে জন্মায়নি। মেয়ে হয়ে জন্মাবার পর থেকে প্রতিদিন যাপনের ভেতর দিয়ে নারীসত্তার অবমাননা তিলতিল করে কাঁটার মত তার মনটাকে বিঁধেছিল।শুধু স্বামীর ঘরের সকল অব্যবস্থা বিরূদ্ধে নয়, আমাদের মেরুদণ্ডহীন, দুর্বল মধ্যযুগীয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধেও ছিল তার বিদ্রোহ। গল্পের প্রতিটি অক্ষরে নারীর অবমূল্যায়নের ধারাপাত বর্ণিত হয়েছে।
মৃণালের বয়ানে আমরা জানতে পারি, ছোটবেলায় একসঙ্গে সান্নিপাতিক জ্বরে পড়ে সে আর তার ছোটভাইটি। ভাইটি মারা গেলেও মৃণাল বেঁচে ওঠে। এতে পাড়ার মেয়েরাই বলতে লাগলো, ‘মৃণাল মেয়ে কিনা তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেতো’! যারা এই মন্তব্য করেছিল, তারাও যে এই সমাজের হতভাগ্য মেয়ের দল যাদের মৃণাল খুব কাছ থেকেই দেখেছে। শ্বশুরবাড়ির সংসারের চৌহদ্দির ঘেরাটোপে এসেই মৃণাল বুঝতে পেরেছিল, সংসারে মেয়েমানুষের বুদ্ধি থাকলে পদেপদে বিপদ! স্বামীকে সে লেখে, ‘মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই! যাকে বাধা মেনে চলতে হবে সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোক্কর খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই!’ মৃণালের রূপকে পেরিয়ে যেদিন শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তার বুদ্ধির পরিচয় পেলো, সেদিনই সে ‘জ্যাঠা মেয়ে’ বলে তাদের কাছে আখ্যা পেয়ে গেল। শুধু শ্বশুরবাড়ির লোকজন নয়, এক্ষেত্রে মৃণালের মাও তাদেরই অনুগামী। মেয়েমানুষের বুদ্ধি যে সকল অনর্থের মূল সেই বিষয়ে ধারণা পেয়েই তিনি মেয়ের বুদ্ধির তারিফ না করে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে শিউরে উঠেছিলেন! ঘরকন্নার নিয়মের মাঝেও প্রতিটা পদেপদে যে অবিচার আর অনিয়ম, তা মৃণালের বুদ্ধিতে ধরা পড়ে গিয়েছিলো। তাই ব্যক্তিমানসের বিকাশে তার ব্যক্তিত্ব এক্ষেত্রেও জাগ্রত হয়ে উঠেছিলো। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ছোটগল্পের নারীচরিত্রগুলো আত্মকথনের ভেতর দিয়ে সে সময়কার সমাজ, সংসার, মানুষের ভূমিকা প্রভৃতিকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে সেখান থেকে বেরিয়ে এক নতুনবোধে উত্তরণ চেয়েছিলো বারেবারে। কিন্তু এই নারীচরিত্রগুলো ছিল বড়ই একা! সমাজ তাদের উপর অনেক অন্যায় নিয়মনীতি জোর করেই চাপিয়ে দিয়েছে। সেই চাপিয়ে দেওয়া সাংসারিক সম্পর্কগুলোর সকল অন্যায়- অবিচার তারা মনেমনে অনুভব করেছে, ক্ষেত্রবিশেষে বুদ্ধির বিকাশও ঘটিয়েছে, কিন্তু এই অবিচারের শেকল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে সমাজ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। কারণ, দিশাহীন পথে পা বাড়াতে অনেক ভয়! কিন্তু ‘স্ত্রীর পত্র’ ছোটগল্পটির সাহসী চরিত্র মৃণাল বিন্দুর আত্মহননের মধ্য দিয়ে সেই ভয়কে মাড়িয়ে সংসার থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল।
আসলে সেই সময়ে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, মানবচেতনার মুক্তি প্রভৃতি রবীন্দ্রমননে ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এক সুগভীর প্রভাব ফেলেছিল। কবি দেখেছেন, মেয়েরা নিপীড়িত হতে হতে হয় লুকিয়ে কাঁদে, নয়তো মরে!
সেই মরা থেকে তাদের বাঁচাতেই তিনি মৃণালের ওষ্ঠে দিলেন ভাষা।
এই ভাষার বলে বলীয়ান হয়ে তাই মৃণাল স্বামীকে জানালো যে, যে বাঁশির করুন সুর সে শুনেছিলো নিজের বিয়ের সময়, সেই সুর আবারও তার কানে ধ্বনিত হলো, যেদিন বিন্দু কাপড়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। কিন্তু এই বাঁশির সুরে আছে মুক্তির আনন্দ! সমাজে নিষ্পেষিত হওয়ার চেয়ে বিন্দুর আত্মহনন অনেক সম্মানের, মুক্তির আর মর্যাদার।
স্ত্রীদের পতিই সব, আর কপালের লিখন, সমাজে প্রচলিত এই দুটি মূল্যবোধের বিরূদ্ধে মৃণালের ছিল চরম প্রতিবাদ! বিন্দুর প্রতি সমাজ-সংসারের সীমাহীন নিগ্রহ দেখে এই দুটো মূল্যবোধ মৃণালের অস্তিত্বকেই নাড়িয়ে দিল! সংসারজীবনেও মেয়েদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধেরও যে একটা মূল্য আছে তা সে অনুভব করলো বিন্দুর আত্মহনননের ভেতর দিয়ে। তার মনে হলো, স্বামীগৃহের অত্যাচার, কপালের লিখন এসবের কাছে নিজেকে সঁপে না দিয়ে বিন্দু যে ইচ্ছামৃত্যুটাকে বেছে নিয়েছে তা তার নিজের কাছেই অনেক সম্মানের, অনেক মর্যাদার ছিলো।
মৃণালের ভাষায়, ‘তোমরাই যে আপন ইচ্ছামতো আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে, তোমাদের পা এতো লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে অনেক বড়ো।’ সংসারের এতকিছু সয়ে যাবার পরেও মৃণালের একটা নিভৃত জীবন ছিল, ছিল আপন সত্ত্বাবোধ, এক প্রতিভা, যার খোঁজ কেউ কোনদিন পায়নি। এমন কি তার স্বামীও না। পাওয়ার চেষ্টাও করেনি কেউ। মৃণাল ছিলো কবি।
এই পরিপ্রেক্ষিতে সে স্বামীকে লিখেছে, ‘আমার একটা জিনিস, যা ছিল তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে সেটা কেউ তোমরা জানোনি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সেইখানে আমার মুক্তি, সেইখানে আমার আমি। আমার মধ্যে যা কিছু তোমাদের মেজবৌকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা চিনতেও পারোনি! আমি যে কবি, সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি’। মৃণালের এই আলাদা সত্তাটাই তাকে সংসারের যাবতীয় ঝড়কে অনায়াসে উপেক্ষা করতে শিখিয়েছিল।
‘নারীকে আপনভাগ্য জয় করিবার, কেহ নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা?’ এই প্রশ্ন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই। তাই মৃণালের বক্তব্য তিনি তাঁর পুরুষসত্তায় বিশ্লেষণ না করে এক নারীচরিত্রের মাধ্যমেই তাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে সমাজের সামনে তুলে ধরলেন। দেখাতে চাইলেন, বিন্দুরা মরে কিন্তু মৃণালের মত মেয়েরা প্রতিবাদ করেই বাঁচে। ‘স্ত্রীর পত্র’ ছোটগল্পটাতে ‘মৃণাল’ চরিত্রটার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এটাই দেখালেন যে, একটা বীজকে খুব বেশিদিন মাটির তলায় লুকিয়ে রাখা যায় না। সময়ের সাথে, পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে সে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবেই! যদিও উপযুক্ত আলোবাতাসের অভাবে কিছু দুর্বল বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু কিছু আছে যেগুলো সকল রকম প্রতিকূল পরিবেশেও আপন অস্তিত্ব সগৌরবে জানান দেয়। পরিশেষে এটাই বলা যায়, পুরুষবান্ধব এই সমাজে অসহায় বিন্দুরা যেমন আছে, তেমন দুর্বার মৃণালেরাও কিন্তু কম নেই! তারা জানে, সমাজের সকল অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, সকল বিরুদ্ধশক্তিকে পায়ে মাড়িয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে।
লেখক : প্রাবন্ধিক, গল্পকার