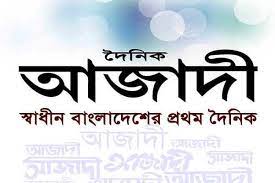বিশ্বে যখন কর্পোরেটদের ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য, তখন একটি নতুন আদল হাজির হয়েছে ‘স্টার্টআপ’ নামে। তরুণদের মধ্যে এ এক নতুন মুগ্ধতা উদ্ভাবন, স্বাধীনতা, নিজের বস হওয়া, ‘ডিজিটাল দেশ’ গড়ার হাতছানি। কিন্তু গভীরে গেলে প্রশ্ন ওঠে: এই স্টার্টআপ জগত কি আসলেই আমাদের মুক্তির দিক, নাকি আরেকটি নিয়ন্ত্রিত বিভ্রম?
একটা সময় ছিল যখন নতুন কোনো সফটওয়্যার, প্রযুক্তি বা আইডিয়া এলেই সেটা বড় কোম্পানির বিরুদ্ধে একধরনের বিপ্লব হিসেবে দেখা হতো। কিন্তু আজকের বাস্তবতায় তুমি যত বড় ইনোভেটরই হও না কেন, বড় কর্পোরেশনের ছায়া এড়িয়ে টিকে থাকা কঠিন। মাইক্রোসফট, শত কোটি ডলারের কোম্পানি কিভাবে ওয়ার্ডপারফেক্ট, নেটস্কেপ, কিংবা ইন্সটল-ভিত্তিক সফটওয়্যার গিলে খেয়েছে, তা একদিন ইতিহাস ছিল, আজ তা নিয়ম। স্টার্টআপের বাজার এখন মূলত সেই গিলার পন্থাকে আরও দৃষ্টিনন্দন ও ‘ইনোভেটিভ’ মোড়কে উপস্থাপন করে।
এঞ্জেল ইনভেস্টর, ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট, এক্সিলারেটর প্রোগ্রাম সবগুলোই তরুণ উদ্ভাবকদের শুরুতে কিছু পুঁজি দিয়ে, পরবর্তীতে তাদের নিয়ন্ত্রণ, মালিকানা ও ডেটার ওপর দখল প্রতিষ্ঠার পথ করে। অনেক স্টার্টআপই তিন বছরে মুনাফা না করেই অধিগ্রহণের (acquisition ) শিকার হয়। অর্থাৎ, যিনি আইডিয়া এনেছিলেন তিনি হয়ে যান কর্মচারী, আর কর্পোরেটটি পায় বাজার, প্রযুক্তি ও ব্র্যান্ড।
এই কাঠামো চাকরি বাজারেও ভয়ংকর প্রভাব ফেলে। আগে যেখানে একজন ব্যক্তি নির্দিষ্ট একটা প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ও নিয়মিত বেতনে কাজ করতো, এখন সেখানে তাকে ‘স্বাধীনতা’র নামে অনিশ্চিত আয় ও স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রাখা হচ্ছে। গিগ-ইকোনমি, কন্ট্রাক্ট বেইজড কাজ, স্টার্টআপ কালচারে ‘ফাউন্ডার’ নামের আড়ালে চলছে একপ্রকার আত্ম-শোষণ।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই স্টার্টআপ সংস্কৃতি মূলধারার অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে পরিপূর্ণভাবে যুক্ত। এটি পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে থেকেই নতুন দাস বাহিনী তৈরি করছে, যেখানে কর্পোরেশনগুলোর দায় নেই, অথচ লাভ আছে। অনেক সময়েই এই স্টার্টআপ ব্যবস্থাকে প্রমোট করা হয় দেশের উন্নয়ন নীতিতে, যেমন বিভিন্ন ডিজিটাল উদ্যোগ বা ইনোভেশন হাব, যেগুলোর মূল কন্ট্রোল আবার থেকে যায় আন্তর্জাতিক ফান্ড, নীতিনির্ধারক বা থিংক ট্যাঙ্কদের হাতে।
সিলিকন ভ্যালির বিফল স্টার্টআপ থেকে শেখার কথা: বিশ্বের সবচেয়ে উদ্ভাবনী স্টার্টআপ হাব হিসেবে পরিচিত সিলিকন ভ্যালিতেও বহু স্টার্টআপ বড় মাপে ব্যর্থ হয়েছে, বাধ্য হয়েছে মরে বা বিক্রি হতে। এই উদাহরণগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশেও উদ্যোক্তাদের বাস্তবসম্মত ও দূরদর্শী হওয়া প্রয়োজন। Theranos: রক্ত পরীক্ষা নিয়ে স্বপ্ন দেখানো এই স্টার্টআপটি জাল তথ্য ও ভুল ওভারপ্রমিসের জন্য বড় স্ক্যামে পড়েছিল, প্রতিষ্ঠাতা গ্রেফতার হয়েছেন। Jawbone: ওয়্যারেবল ডিভাইস বানানো প্রতিষ্ঠান, টেকনোলজি উন্নয়ন ও প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে গিয়ে প্রায় ৯০০ কোটি ডলারের ক্ষতি করে লিকুইডেশন করতে হয়েছিল। Quibi: মাত্র ৬ মাস পর ইউজার না পাওয়া ও বাজেট ফাঁকির জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ২০২০ সালে, ১৭০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ সত্ত্বেও। WeWork আসলে স্টার্টআপ না হলেও তার অপ্রস্তুত ওচঙ এবং উচ্চ মূলধনের অপব্যবহারে মূল্য হারিয়ে ব্যাপক সংকট পোহাতে হয়েছিল।
ছোট স্টার্টআপের প্রতি বড়দের আগ্রাসন: ‘সোওয়ালানো’ আর ‘মার্জার’ এর কাহিনি বিশ্বব্যাপী স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে বড় বড় কোম্পানি এবং বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ছোট স্টার্টআপকে ‘সোওয়ালানো’ বা ‘অধিগ্রহণ’ করে থাকে। এরা মূলত তাদের বাজার সম্প্রসারণ, প্রযুক্তি অর্জন, প্রতিযোগী নির্মূল, অথবা নতুন আইডিয়া ও ট্যালেন্ট হাতছানি দেয়ার জন্য এ কাজ করে।
কেন ছোট স্টার্টআপগুলো বড়দের কাছে বিক্রি বা মর্জ হয়? অর্থের প্রয়োজন: অনেক সময় বাজারে টিকে থাকতে পর্যাপ্ত তহবিল না পেয়ে ছোট স্টার্টআপ বিক্রি হওয়া ছাড়া বিকল্প থাকে না। বাজারে দ্রুত প্রসার: বড় কোম্পানির সাপোর্টে তাদের প্রযুক্তি বা সেবা দ্রুত বড় পরিসরে পৌঁছে দিতে পারে। প্রতিযোগিতা কমানো: বড় কোম্পানি প্রতিদ্বন্দ্বীকে কিনে তাদের দৌড় থেকে বের করে দেয়। তৈরি বা প্রণোদিত মডেল: বিনিয়োগকারী প্রাথমিক পর্যায়ে স্টার্টআপে টাকা দেন, পরে ব্যবসাটা বড় হওয়া বা সফলতা না পেলেই সেটিকে বিক্রি করে দেন বা মার্জ করে দেন।
বিশ্ব থেকে কিছু পরিচিত উদাহরণ: Facebook & Instagram: ইনস্টাগ্রাম তখনকার ছোট স্টার্টআপ, ফেসবুক তাদের কিনে নিয়েছিল বাজার দখলের জন্য। Google & YouTube ইউটিউব ছিল ছোট ভিডিও প্ল্যাটফর্ম, গুগল তাদের কিনে নিয়েছিল নিজের ভিডিও ব্যবসা শক্তিশালী করার জন্য। Amazon & Zappos: ছোট ই-কমার্সকে বড়রা ক্রয় করে থাকে দ্রুত বাজার দখলের জন্য।
টনবৎ বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাইড-শেয়ারিং কোম্পানি, যেটা প্রায় ১৪ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে লক্ষ কোটি ডলার লোকসান করছে। অনেকেই ভাবেন, এত লোকসান থাকলে কীভাবে তারা এখনও চালু আছে? আসলেই কি টনবৎ লাভ করছে? আর এই লোকসানের পিছনে যে অর্থ প্রবাহ, সেটা আসলেই কি অর্থনীতির জন্য ভালো?
টনবৎ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০৯ সালে, তার পর থেকে তারা প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবসা প্রসার, বাজার দখল এবং ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর অর্থ খরচ করেছে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ‘মার্কেট লিডার’ হওয়া, যেটা দীর্ঘমেয়াদি লাভের থেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। তারা চালক এবং গ্রাহক উভয়ের জন্য সাবসিডি (ছাড়) দিয়ে বাজার দখল করেছে। বিশ্বব্যাপী অনেক জায়গায় টনবৎ তার প্রবেশাধিকার অর্জনের জন্য স্থানীয় প্রতিযোগী ও নিয়ন্ত্রক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে বড় ব্যয় করেছে।
লোকসানের টাকা কোথা থেকে আসে? টনবৎ মূলত বড় বড় বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে পুঁজি সংগ্রহ করে চলেছে যেমন: ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্ম, প্রাইভেট ইকুইটি, পাবলিক মার্কেট (IPO ) বৃহৎ কর্পোরেট বিনিয়োগকারী
এই বিনিয়োগগুলো তাদের ধারাবাহিক লোকসান সামাল দিতে, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও বাজার প্রসার চালাতে সাহায্য করে। অর্থাৎ তারা প্রচুর ঋণ ও শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করছে। Uber -এর মত প্রতিষ্ঠানগুলো ‘অর্থনৈতিক বুদবুদের অংশ’ অর্থাৎ প্রচুর পুঁজির প্রবাহ হলেও সেগুলো দীর্ঘমেয়াদি লাভে রূপান্তরিত না হয়ে শুধুই বাজার মূল্য বাড়িয়ে তুলছে। এই ধরনের কোম্পানি তাদের আর্থিক প্রতিবেদনগুলোতে লোকসান দেখিয়ে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত করে, বাজারে ঋণের পরিমাণ বাড়ায়। এটি অর্থনীতিতে ঋণের ঘাটতি ও বুদবুদের সৃষ্টি করে, যেখানে বড় বড় বিনিয়োগকারী এবং বাজার মূল্য বেশিরভাগ সময় বাস্তবিক লাভের সাথে সামঞ্জস্য করে না। ফলে একটি বড় আর্থিক ‘বাবল’ তৈরি হয়, যা কোন এক সময় ফাটলে পুরো ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমে ঝড় তুলতে পারে যা যুদ্ধ বা প্রকৃত ধ্বংস ছাড়াই অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। টনবৎ এর মত সংস্থাগুলো অনেক কর্মীকে ফ্রিল্যান্সার বা কন্ট্রাক্টর হিসেবে নিয়োগ দিয়ে শ্রমিক অধিকারকে অবহেলা করে। তারা বাজার দখল করতে দীর্ঘমেয়াদী লোকসান স্বীকার করে, যা ছোট ও মাঝারি ব্যবসার জন্য অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে। অর্থনৈতিক বুদবুদ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি।
আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য মেসেজ: প্রযুক্তি ও নতুন ব্যবসার মডেল শেখা জরুরি, কিন্তু অতি আশাবাদী হয়ে বিনিয়োগে ঝাঁপিয়ে পড়া বিপজ্জনক। দীর্ঘমেয়াদি লাভ না হওয়া স্টার্টআপ ও কর্পোরেট দুনিয়ার বাস্তবতা বুঝে ব্যবসা বা বিনিয়োগ করতে হবে। অর্থনৈতিক বুদবুদ ও ঋণের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। টেকসই ও নৈতিক ব্যবসায় মনোযোগ দিতে হবে, যাতে অর্থনৈতিক সংকটের হাত থেকে বাঁচা যায়।
সতর্ক না থাকলে তরুণদের উদ্ভাবনী শক্তি আর স্বপ্নও পণ্য হয়ে উঠবে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির বদলে কর্পোরেট মুনাফার ইন্ধন। তাই দরকার এমন একটি বিকল্প স্টার্টআপ কাঠামো, যেখানে বিনিয়োগ মানে হবে পার্টনারশিপ, এবং ‘ফাউন্ডার’ মানে হবে কেবল শ্রমিক নয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মালিক। আমাদের শিক্ষা, নীতি ও প্রযুক্তি ভাবনায় এমন দৃষ্টিভঙ্গির বিপ্লব না আনলে, আমরা পরবর্তী প্রজন্মকে নতুন ধরনের কর্পোরেট দাসত্বে ঠেলে দিচ্ছি।
টনবৎ-এর ১৪ বছরের লোকসানেও টিকে থাকা কোনো সাধুতা নয়। এর পেছনে রয়েছে সিস্টেমিক ফাইনান্সিয়াল ডিজাইন যেখানে মানুষকে চাকরি না দিয়ে ‘উদ্যোক্তা হও’ বলো, আর তারা ব্যর্থ হলে আবার জনগণের টাকায় বেইলআউট করো। ঋণ-ভিত্তিক অর্থনীতি আজকের বিশ্বে যুদ্ধ ছাড়াই ধ্বংস আনে, এই স্টার্টআপ সংস্কৃতি অনেকভাবে debt-driven এর উপর দাঁড়িয়ে। নতুন দাসত্ব কিন্তু এবার চেইন নেই, আছে equity deals, term sheets, seed funding ।
ইতিহাসে যেভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য দিয়ে রাজনীতি আনে, আজ ঠিক একইভাবে ‘investment ’ দিয়ে ‘influence ’ কেনা হয়। তখন পাট, সোনা, খাদ্যশস্য নেওয়া হতো, আজ ডেটা, প্ল্যাটফর্ম, সিদ্ধান্তক্ষমতা নেওয়া হয়। বাংলাদেশের পরিণতি হবে Uber বা WeWork -এর মতো নয়, বরং তাদের fuel, testing ground, user data mine, cheap labor & logistic zone – এই ভূমিকায় নামিয়ে আনা হবে।
স্টার্টআপ, একটি অর্থনৈতিক ধারণা, বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার। লাভ নয়, ‘গ্রোথ’-এর নামে প্রাথমিকভাবে ক্ষতি করতে করতে বাজার দখল করার কৌশল। এটি একধরনের ‘ডিজিটাল ইম্পেরিয়ালিজম’ যেখানে সেবাটি দেশের ভিতরে, কিন্তু সিদ্ধান্ত ও মালিকানা দেশের বাইরে।
বাংলাদেশে ঝুঁকি কোথায়?
ছোট উদ্যোক্তা ‘inspiration ’ নিচ্ছেন, কিন্তু business crowd-out হচ্ছে চালু থাকা দোকান-ব্যবসা স্টার্টআপ ডিসকাউন্টে ধ্বংস হচ্ছে, স্টার্টআপ ব্যর্থ হলে, ফাউন্ডার শুধু চাকরি খুঁজবে, কিন্তু কর্মচারী, গ্রাহক, এবং বিনিয়োগকারী ধ্বংস হবে, বিদেশি স্টার্টআপকে বাজার দেওয়া হচ্ছে কিন্তু দেশীয় স্টার্টআপ regulatory বাধায় আটকে যায়, জনগণের করের টাকা যায় লোকসানে থাকা কোম্পানিকে বাঁচাতে এটি এক ধরনের নীরব অর্থনৈতিক ধ্বংস, যেখানে বন্দুক বা যুদ্ধ নয়, ‘ capital injection ’ দিয়ে ‘ economic manipulation ’ হয়।
১৭৫৭-পলাশী- ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি- অস্ত্র ও ষড়যন্ত্র- নবাবের পতন- খাজনা ও সম্পদ লুণ্ঠন। ২০২৫-নিউ-পলাশী- পশ্চিমা ভিসি ও স্টার্টআপ নিয়ন্ত্রক- ডলার ও কনসাল্টিং ফার্ম- রাষ্ট্রীয় নীতির বিকৃতি- তথ্য, পুঁজি ও বাজার নিয়ন্ত্রণ, এটা কি Neo-Plassey , নয় কি ?
লেখক: প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট।