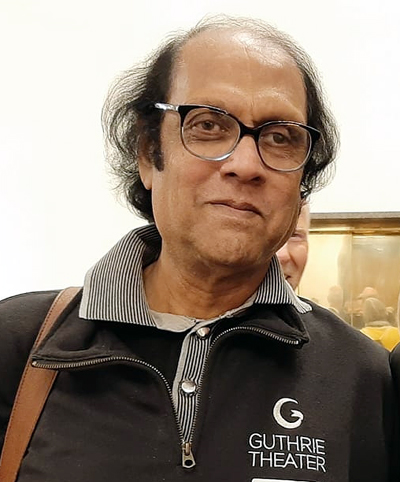“বঙ্গবন্ধু ছিলেন ‘রাজনীতির কবি’ আর তাঁর জীবনটাই একটি অমিমাংসিত কবিতা। এই জীবন্ত কবিতা বিশ্লেষণের ব্যস্ততা আজ বিশ্বময়। ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের বিবশষু ঘবংিবিবশ এ বলা হয়, “রাজনীতির প্রকৌশলী নন মুজিব. মুজিব হলেন রাজনীতির কবি, বাঙালির স্বাভাবিক প্রবণতা প্রায়োগিক নয়, শৈল্পিক। তাই মনে হয়, বাংলাদেশের সকল মানুষ, শ্রেণী ও মতাদর্শকে এক সূত্রে গাঁথা হয়তো মুজিবের মত রাজনৈতিক কবির পক্ষেই সম্ভব।”
সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়া সেই সময়ের বঙ্গবন্ধুর ইমেইজকে কেন্দ্র করে এমন উক্তি বেরিয়ে এসেছিল আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে। এর অনেক আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে হয়ে উঠেছিলেন বৈশ্বিক। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে অর্থনৈতিক মুক্তিকে যতটা তিনি বড় করে দেখেছেন, তেমনি পাশপাশি অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক চেতনার কথা একইভাবে উচ্চারণ করেছেন। ভাষা ও সংস্কৃতিকে তিনি কখনও রাজনীতি থেকে আলাদা করে ভাবেন নি। “আমার দল ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই সকল সরকারি অফিস আদালত ও জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা চালু করবে।”
এখানে বিষয়টির আরেকটু গভীরে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো সেই সময়ে বক্তৃতা কিংবা বিবৃতির পর, যাবতীয় তাঁর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক চিঠি সবকিছুই শেষ হত– ‘জয় বাংলা ’ শব্দটির মাধ্যমে ইতি টানার মধ্যে। এখানে তাঁর সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির আলাদা বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করি। রাজনীতির সাথে সংস্কৃতির যে একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, তাঁর উক্তির মাধ্যমে আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি– “রাজনৈতিক ক্ষমতা না পেলে সংস্কৃতিকে গড়ে তোলা যায় না। বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না বলেই বাংলা সংস্কৃতির বিকাশ হয় নি।”
তিনি বরাবরই রাজনীতিকে অধিকতর গণমানুষের সুপ্ত শক্তি হিসেবে ভেবেছেন যেখানে সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আশা–আকাঙ্ক্ষার অবলম্বন হিসেবে দেখেছেন। বঙ্গবন্ধুর যে সাংস্কৃতিক চিন্তা তা কোন পৃথক শ্রেণীর জন্য নয়, অনেকবেশি সাধারণ মানুষের জীবনধারা পরিবর্তনে সংস্কৃতির গুরুত্বকে তিনি তুলে এনেছিলেন। স্বাধীনতার পরেই তাঁর কণ্ঠে শুনতে পাই– “শিল্পী–সাহিত্যিকরা আর সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের জন্যে সংস্কৃতিচর্চা করবেন না। দেশের সাধারণ মানুষ, যারা আজও দুঃখী, যারা আজও নিরন্তর সংগ্রাম করে বেঁচে আছে, তাঁদের হাসি–কান্না, সুখ–দুঃখকে শিল্প–সংস্কৃতির উপজীব্য করার জন্য শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। ”
কোন সাহিত্য বা মহৎ শিল্পকর্ম জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সৃষ্টি হতে পারে না, এ বিশ্বাস থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর কোন বাঙালি তার রাজনৈতিক, সামাজিক দর্শন বঙ্গবন্ধু ছাড়া তাঁর মত কেউ আর ভাবতে পারেন নি। পাকিস্তান শাসন আমলে বাংলা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিশেষ করে আমাদের ভাষা– সংস্কৃতির বিকাশে নানা ধরণের অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল। এই অন্তরায় থেকে উত্তরণে প্রতিটি পর্যায়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন–
“ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন।” এই উক্তিটি কোন বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর জন্য নয়, তার এ উক্তি আজও সমসাময়িক পৃথিবী ব্যাপী সংগঠিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সংগ্রামের। মত প্রকাশের স্বাধীনতায় তাঁর এ উক্তি সম্পূরক। নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে এই চেতনা এখনও অনেকবেশি বিশ্বময় প্রতিফলিত হয়।
নিরন্তর সাংস্কৃতিক চর্চা মানুষ তৈরিতে ভূমিকা রাখে : বঙ্গবন্ধুর সাংস্কৃতিক ভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা। জাতীয় সংস্কৃতির গৌরবময় বিকাশকে অব্যাহত রাখতে ও আমাদের লোকজ সংস্কৃতির চর্চা, সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে বিশেষ আইন দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে একদিকে যেমন শিল্পীদের শিল্পচর্চা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে গ্রামের স্বজাত শিল্পীদের তাদের কথাগুলো বলার সুযোগ তৈরির পাশাপাশি শিল্প চর্চায় তাদের অধিগম্যতা তৈরি হয়েছে, শিল্প–সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করতে এরকম একটি ভিশনারি তৈরি করেন।
ভাষার আন্তর্জাতিকীকরণ : রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে নোবেল প্রাপ্তি বাংলা ভাষাকে এক অন্য মর্যাদায় অসীন করেছে। বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের ২৯ তম অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ প্রদান করেছেন, যা বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিকীকরণের ক্ষেত্রে এবং একটি রাষ্ট্রের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা দেয়। মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তাঁর এ প্রচেষ্টা তাঁর সাংস্কৃতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ। চীনে শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়েও তিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছেন। ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ স্মৃতিকথায় এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন–
“শান্তি সম্মেলন শুরু হলো। তিনশত আটাত্তর জন সদস্য সাঁইত্রিশটা দেশ থেকে যোগদান করেছে। সাঁইত্রিশটা দেশের পতাকা উড়ছে। শান্তির কপোত এঁকে সমস্ত হলটা সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। প্রত্যেক টেবিলে হেডফোন আছে। আমরা পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা একপাশে বসেছি। বিভিন্ন দেশের নেতারা বক্তৃতা করতে শুরু করলেন। প্রত্যেক দেশের একজন বা দুইজন প্রতিনিধিত্ব করতেন। বক্তৃতা চলছে। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে অনেকেই বক্তৃতা করতে শুরু করলেন । পূর্ব পাকিস্তান থেকে আতাউর রহমান খান ও আমি বক্তৃতা করলাম। আমি বাংলায় বক্তৃতা করলাম। আতাউর রহমান খান ইংরেজি করে দিলেন। ইংরেজি থেকে চীনা, রুশ ও স্পেনিশ ভাষায় প্রতিনিধিরা শুনবেন। কেন বাংলায় বক্তৃতা করবো না? ভারত থেকে মনোজ বসু বাংলায় বক্তৃতা করেছেন। পূর্ব বাংলার ছাত্ররা জীবন দিয়েছে মাতৃভাষার জন্য। বাংলা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু লোকের ভাষা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে না জানে এমন শিক্ষিত লোক চীন কেন দুনিয়ায় অন্য দেশেও আমি খুব কম দেখেছি। আমি ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে পারি। তবু আমার মাতৃভাষায় বলা কর্তব্য। আমার বক্তৃতার পরে মনোজ বসু ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে বললেন, “ভাই মুজিব, আজ আমরা দুই দেশের লোক, কিন্তু আমাদের ভাষাকে কেউ ভাগ করতে পারে নাই। আর পারবেও না। তোমরা বাংলা ভাষাকে জাতীয় মর্যাদা দিতে যে ত্যাগ স্বীকার করেছ আমরা বাংলা ভাষাভাষী ভারতবর্ষের লোকেরাও তার জন্য গর্ব অনুভব করি।”
এখানেই মাতৃভাষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ও বাঙালি স্বাজাত্যবোধ প্রকাশিত । এই স্বাজাত্যবোধ স্বাধীন বাংলাদেশ এর স্বপ্ন দেখতে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে।
বাংলা একাডেমি ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন: ১৯৭৪ সালে প্রথমবারের মত বাংলাভাষায় আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে এ কেবল দেশের শিল্পী– সংস্কৃতিপ্রেমীরা নয়, দেশ ও দেশের বাইরের অনেক শিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মীদের এক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল। এ থেকে বঙ্গবন্ধুর বৈশ্বিকতা ও মৈত্রীর দৃষ্টান্ত মেলে। আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে তিনি বিবৃতি দিয়েছিলেন– “যাঁরা সাহিত্য সাধনা করেছেন, শিল্পের চর্চা করেছেন, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সেবা করেছেন , তাঁদের দেশের জনগণের সঙ্গে গভীর যোগসূত্র রক্ষা করে অগ্রসর হতে হবে।”
জাতীয় কবির ধারণা প্রদান : নজরুলের গান ও কবিতায় অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়েছেন বঙ্গবন্ধু। নজরুলের অদম্য গতি বাঙালি জাতির মধ্যে সঞ্চারিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তিনি। নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবধর্মের জয়গান, শোষিত ও নিপীড়িতের শোষণমুক্তির সংগ্রামে প্রতিবাদ বঙ্গবন্ধুকে আলোড়িত করেছে। এই বিদ্রোহী তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বাঙালি জাতির দিশা হতে পারে একমাত্র মানবতার কবি, নজরুলের জীবনবোধ ও দর্শন । আর তাই স্বাধীনতার পরই কাজী নজরুলকে জাতীয় কবির সম্মানে অলঙ্কৃত করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করেন নি তিনি। তিনি কবি নজরুলকে পত্র লিখেছিলেন এভাবে-“মুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জনগণ ও আমার পক্ষে আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনার জন্মবার্ষিকীতে আপনার আদর্শে বাংলাদেশকে সিক্ত হতে দিন।”
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর বিশেষ উদ্যোগে কাজী নজরুলকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়, তাঁকে ভূষিত করা হয় জাতীয় কবির সম্মানে এবং কবির রচিত ‘চল্, চল্, চল্, উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল’ গানটিকে রণঙ্গীত এর মর্যাদা দান করা হয়।
শুধু শহরে নয়, গ্রামেও সংস্কৃতিচর্চার প্রসার : বঙ্গবন্ধু চেয়েছেন সংস্কৃতিকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে। আর সেক্ষেত্রে শুধু শহরেই নয়, গ্রামেও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের প্রসারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৭৪ সালে শম্ভুমিত্র তাঁর নাটকের দল ‘বহুরূপী নাট্য গোষ্ঠী’ নিয়ে ঢাকায় এলে বঙ্গবন্ধু তাঁদের গণভবনে আমন্ত্রণ জানান। শম্ভুমিত্র ও তাঁর নাটকের দলকে বঙ্গবন্ধু বলেন-“শুধু ঢাকা নয়, বাংলাদেশের অন্যান্য শহরেও বহুরূপীকে অভিনয় করতে হবে। আরো অনেকদিনের জন্য আসতে হবে। সরকার আমন্ত্রণ জানাবে।” ছড়িয়ে দেয়ার ভাবনা তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল।
এ বক্তব্য থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় কেবলমাত্র শহরকেন্দ্রিক সংস্কৃতি চর্চায় সীমাবদ্ধ না থেকে এটিকে গ্রামমুখী করার প্রয়োজনীয়তা
সাহিত্য–সংস্কৃতি বিকৃতির বিরুদ্ধে অবস্থান : অনুধাবন করেন, কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমাদের সংস্কৃতির শিকড় গ্রামকেন্দ্রিক এবং সংস্কৃতির বিকেন্দ্রীকরণে সাংস্কৃতিক চর্চাকে অনেকবেশি গ্রাম পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে।
এখানে বঙ্গবন্ধুর দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় ভাবনাও প্রতিফলিত হয়। আঞ্চলিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে সংস্কৃতিকে সর্বত্র পাকিস্তান আমলে ধর্ম ও জাতীয় সংহতির নামে বাংলা সংস্কৃতিকে ধ্বংসের চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে বর্জনের চক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন বঙ্গবন্ধু।
বাংলা সংস্কৃতি প্রসঙ্গে তাঁর এ ভাষণটি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূূর্ণ। এর মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য– সংস্কৃতি বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে।
ইতিহাস ও সংস্কৃতি : বাংলাদেশের রয়েছে শত শত বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। বাংলাদেশের সংস্কৃতি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে সমৃদ্ধ। ইতিহাসের সাথে সংস্কৃতির বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে। তাই ইতিহাস রচনায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু । আর ইতিহাসকে জনগণ বিশেষত তরুণদের কাছে পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। তাঁর ভাষায়– “ বাংলার মানুষ বিশেষ করে ছাত্র এবং তরুণ সম্প্রদায়কে আমাদের ইতিহাস এবং অতীত জানতে হবে। বাংলার যে ছেলে তার অতীত বংশধরদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারে না সে ছেলে সত্যিকার বাঙালি হতে পারে না।”
তবে সত্যিকার ইতিহাস রচনার অভাবও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, কেননা বাঙালির ইতিহাসকে বিকৃত করার ষড়যন্ত্র নানা সময়ে নানাভাবে হয়েছে। পরবর্তীতেও এ চক্রান্ত নতুনভাবে হতে পারে সে শঙ্কা তাঁর ছিল। তাই বাংলা ও বাঙালির প্রকৃত ইতিহাস রচনায় তিনি আহবান জানিয়েছেন– “আজও আমাদের গৌরবময় ইতিহাস রচিত হয় নি। নতুন করে বাঙালির ইতিহাস রচনা করার জন্য দেশের শিক্ষাবিদদের প্রতি আমি আহবান জানাচ্ছি।
জনগণের জন্যেই সাহিত্য : শিল্পের জন্য শিল্প নয়, সাহিত্যের জন্য সাহিত্য নয়, বঙ্গবন্ধু মনে করতেন জনগণই সাহিত্যের একমাত্র বিবেচ্য। ১৯৭১ সালে ১৫ ই ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমী আয়োজিত ভাষা আন্দোলন স্মরণ সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় তিনি বলেছেন–
“জনগণের জন্যেই সাহিত্য। এদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের লেখনীর মধ্যে নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন, দুঃখী মানুষের সাহিত্য সৃষ্টি করুণ। কেউ আপনাদের বাধা দিতে সাহস করবে না।”
বাঙালি জাতির শিকর হচ্ছে এর সংস্কৃতি। আর সংস্কৃতির বাহন হিসেবে ভাষা হচ্ছে জাতির সামগ্রিক ঐতিহ্যের ধারক। তাই বাংলাভাষাকে গণমুখী করার জন্য তিনি বুদ্ধিজীবীদের অনুরোধ করেছেন। তাঁর এ বিবৃতির মাধ্যমে একদিকে সাহিত্যের স্বরূপ কি হওয়া উচিত তা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে লেখক ও সাহিত্যিকদের এ বিবৃতি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বময়, ঘুমন্ত বাঙালি নজরুলের বিদ্রোহী চেতনায় জাগ্রত হয়েছিল। আর বঙ্গবন্ধু সারাজীবন সংগ্রাম করে নেতৃত্ব দিয়ে বাঙালি জাতিকে উপহার দিয়েছেন স্বাধীন– সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই তিন কিংবদন্তীর জীবন দর্শনকে পর্যালোচনা করলে আদর্শগত এক ঐক্যের খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলা ভাষা, বাঙালির ইতিহাস ও সংস্কৃতির অস্তিত্বে এই তিন ব্যক্তিত্বকে আলাদা করার কোনো সুযোগ নেই।
লেখক : কবি, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব