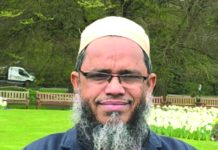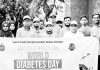বাংলাদেশ, বাঙালি, বাংলাভাষা আর মহান স্বাধীনতার সাথে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অবিচ্ছেদ্য নাম। স্বাধীন বাংলার এই রূপকারককে আমরা নানাভাবে চিনি ও জানি। যিনি নিজেই একটি চলমান ইতিহাস। পৃথিবীর অনেক দেশের নেতাই লিখেছেন অনেক লেখা। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অগুনিত গুণকে ছাড়িয়ে লেখকসত্তায় এক অনন্যরূপ ধারণ করেছেন। তিনি তাঁর জীবনের অনেক মূল্যবান সময় প্রায় ১৪ বছর জেলে কাটিয়েছেন। যেই সময়গুলি ছিল দুঃসহ আর নিঃসঙ্গ। বঙ্গবন্ধু রাজবন্দী হিসেবে কারাগারে থাকাকালীন তাঁর অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর হিসেবে বাংলা ভাষায় তিনটি বই লিখেছেন।
১. অসমাপ্ত আত্মজীবনী (২০১২), ২. কারাগারের রোজনামচা (২০১৭) এবং ৩. আমার দেখা নয়াচীন।
কেউ কেউ তাঁর বইয়ের সংখ্যা মনে করেন চারটি। ‘আমাদের বাঁচার দাবী ৬–দফা কর্মসূচী’ (১৯৬৬) লেখক শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। আমরা প্রথম এটির সন্ধান পাই তাঁর কারাগারের রোজনামচা (২০১৭) গ্রন্থে। গ্রন্থের ৩০৮ পৃষ্ঠা থেকে ৩২০ পৃষ্ঠায় এটি মুদ্রিত। প্রায় সোয়া চার হাজার শব্দের বইটিকে পুস্তিকা বলা যেতে পারে। শেখ মুজিব নিজেও একে ‘পুস্তিকা’ বলেছেন (কারাগারের রোজনামচা, পৃ. ৩১০।)
জাতির পিতার লেখা অমূল্য তিনটি গ্রন্থই তিনি অত্যন্ত সহজ, সরল ও সাধারণভাবে বর্ণনা করেছেন।
‘আসমাপ্ত আত্মজীবনী’ বঙ্গবন্ধুর লেখা প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এটি তাঁর স্মৃতিচারণমূলক আত্মজীবনী। কিন্তু ডায়েরি নয়। ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে যখন তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন তখন তিনি এই গ্রন্থটি লিখেন। গ্রন্থটি শেষ হয়েছে ১৯৫৫ সালের ঘটনাবলীর মধ্যদিয়ে। কিন্ত হঠাৎ গ্রন্থের সমাপ্তি এবং আর লেখার সুযোগও হয়নি বলে এটির নাম ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’। এই গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে আমরা পাই লেখক বঙ্গবন্ধুকে। এই গ্রন্থটিতে তাঁর লেখক সত্তার পূর্ণরূপ প্রকাশ পায়। একজন দক্ষ কথাসাহিত্যিকের কলমের ছোঁয়ায় উঠে এসেছে জীবনের নানান দিক। তাঁর শৈশব –কৈশোর, শিক্ষা জীবন, নিজ গ্রাম, স্বদেশ প্রেম আর পিতৃপুরুষের কথা। তাঁর কলমের কালিতে তিনি এঁকেছেন এক এক করে দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশ ভাগ, পূর্ব বাংলার রাজনীতি, ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন ও পাকিস্তানের রাজনীতি। এক শিল্পীর তুলিতে আঁকা বাঙালির ইতিহাসের বাস্তব ছবি। এই গ্রন্থটি তিনি অতি সহজ সরল ভাষায় রচনা করলে ও বাংলা ভাষার লেখনীর দক্ষতা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।
একজন দক্ষ রাষ্ট্রনায়কের হাতে এক অসাধারণ জীবন সাহিত্যমূর্ত রূপ ধারণ করেছে। যেখানে কোনো ভূমিকা বা লুকোচুরি নেই, নেই সাহিত্যের কোনো কঠিন পরিভাষা। রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুণে আর তাঁর সত্য নিষ্ঠার গুণে এই গ্রন্থটি সাবলিল ভাষায় বাংলাদেশ ও বাঙালি জনগণের প্রতি ভালোবাসা ও বাঙালি জাতির ইতিহাসের আকর গ্রন্থও হয়ে উঠেছে।
তাঁর লেখক সত্তায় বাংলার চিরাচরিত লোকসাহিত্যের প্রতি জানা যায় আগ্রহের কথা, ‘নদীতে বসে আব্বাস উদ্দিন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটি দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতেছিলেন তখন মনে হচ্ছিল নদীর ঢেউ গুলি যেন তাঁর গান শুনছে।’ (অসমাপ্ত আত্মজীবনী পৃষ্ঠা, ১১১)। আবার প্রকৃতি প্রেমী বঙ্গবন্ধুর লেখায় ভাষার উপমার সৌন্দর্য্য এভাবে চিত্রিত হয়। পাঠক নিজেই যেন না দেখা তাজমহলের সৌন্দর্যকে দর্শন করতে পারে। যেন বর্ণনাটা শেষ হয়েও অতৃপ্তি থেকে যায়। গ্রন্থটিতে তিনি ভাষার ব্যবহারের যে দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন তা অকল্পনীয়। অতি সাধারণ করে বলতে গেলে বলতে হয় তাঁর সক্রিয় শৈলী সমৃদ্ধ ভাষা বৈশিষ্ট্য এই আত্মজীবনীকে বহুমাত্রিক রূপ দিয়েছে। ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ গ্রন্থে কোথাও নেই আত্মপ্রচারণা, বর্ণনায় ভাষার জটিলতা। কিন্তু আছে সহজ– সরল ও অকপট স্বীকারোক্তি। সত্যের নিঃসংকোচন প্রকাশ আর তাঁর সাহসী ভাষাই ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’র শ্রেষ্ঠত্ব মানতে হয়।
বঙ্গবন্ধুর লেখা দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘কারাগারের রোজনামচা’। এটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯১৭ সালে। এই গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য লেখক সত্তার উন্মেষ ঘটেছে। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু জেলে বন্দি থাকেন। সেই সময় কারাগারে প্রতিদিনের ডাইরি লেখা শুরু করেন। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত লেখাগুলি এই বইয়ের প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রন্থটি রচনার। ধীমান প্রাবন্ধিক গবেষক শামসুজ্জামান খান তাঁর ‘লেখক বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় গ্রন্থ কারাগারে রোজনামচার মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন– “তিনি তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘কারাগারের রোজনামচা’য় জেলের নানা পরিভাষা, রীতি–কেতা নিয়মকানুন যে অভিনিবেশ, অনুপুঙ্খতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন আর কোনো কারা সাহিত্যেই তার বিবরণী মেলা ভার। (লেখক বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য, পৃৃৃৃষ্ঠা, ২০–২১)
এই গ্রন্থটিতে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এক লেখককে আমরা খুঁজে পাই। এখানে তিনি জেলখানার সুনিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রন্থটির শুরুতে দুইটি শ্লোগানের মত ছোট ছোট বাক্য পাওয়া যায়–প্রথমটি ‘জেলের ভিতর অনেক ছোট ছোট জেল আছে’ আর দ্বিতীয়টি হলো ‘থালা বাটি কম্বল জেলখানার সম্বল।’
অতি সহজ সরল অথচ সাবলীল ভাষায় আকর্ষণীয়ভাবে জেল জীবনের বর্ণনা লিখেছেন। ‘আমার ঘরের দরজার কাছে একটা কামিনী ও একটা শেফালী গাছ। কামিনী যখন ফুল দেয় আমার ঘরটা ফুলের গন্ধে ভরে থাকে। একটু দূরেই দুইটা আম আর একটা লেবু গাছ। বৃষ্টি পেয়ে গাছের সবুজ পাতাগুলি যেন আরও সবুজ আরও সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বড় ভাল লাগল দেখতে।’ ( কারাগারের রোজনামচা পৃষ্ঠা, ১১৯)।
‘কারাগারের রোজনামচা‘’ তে তিনি লোকভাষার প্রয়োগ অতি দক্ষতার সাথে করেছেন। সেখানে রয়েছে উপমা আর চিত্রকল্পের এক অপূর্ব সমন্বয়।
এই গ্রন্থটির বিশেষ দিক হচ্ছে –তিনি শুধু কারাগারের বর্ণনাই চিত্রিত করেননি। সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও পাকিস্তান স্বৈরাচারী শাসকের অত্যাচার নিপীড়নের এক বাস্তব চিত্র এঁকেছেন। তাঁর বর্ণনায় পাঠক দার্শনিক বঙ্গবন্ধুকে খুঁজে পায়। তিনি লিখেন– ‘বাজে গাছগুলি আমি নিজেই তুলে ফেলি। আগাছাগুলিকে আমার বড় ভয়, এগুলি না তুললে আসল গাছগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন আমাদের দেশের পরগাছা রাজনীতিবিদ– যারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক তাদের ধ্বংস করে, এবং করতে চেষ্টা করে। তাই পরগাছাকে আমার বড় ভয়। আমি লেগেই থাকি। কুলাতে না পারলে আরো কয়েকজনকে ডেকে আনি। আজ বিকেলে অনেকগুলি তুললাম।’ ( করাাগারের রোজনামচা,পৃষ্ঠা ১১৭)।
বইটি পড়ার সময় পাঠক মার্জিত রসবোধের সাথে ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক ভাষা বোধের পরিচয় পায়। ৫ ই জুন ১৯৬৬ রবিবার তিনি লিখেন– ‘একবার জেলে এলে খুব কম লোকই ভাল হয়েছে। দুই একজন ভাল হলেও তাদের ছাড়তে এত দেরি করে ফেলে যে– আবারও পাগল হয়ে যায়।’ এই জায়গায় আমরা একজন মনোবিজ্ঞানীকে খুঁজে পাই।
বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর ভালোবাসার বর্ণনা যেকোনো বড় লেখকের অংশে কম নন। তিনি লিখেন-‘পাঁচ মাসের মধ্যে বাংলায় কথা বলতে পারি নাই। কারণ কেহই বাংলা জানে না।’
(কারাগারের রোজনামমচা, পৃষ্ঠা ,২৬৭)
‘কারাগারের রোজনামচা’ বাঙালি গণ জাগরণের এক ঐতিহাসিক দলিল। আমার দেখা নয়াচীন ( ২০২০) গ্রন্থটি রচনার দিক থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম লেখা গ্রন্থ। কিন্তু প্রকাশের দিক থেকে এটি তৃতীয় গ্রন্থ। ১৯৫২ সালের চীন সফরের স্মৃতি নির্ভর ভ্রমণ কাহিনি তিনি ১৯৫৪ সালে রচনা করেছেন। এটিও কারাগারে রাজবন্দি থাকাকালীন রচিত।
মাতৃভাষায় রচিত এই গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধুর ভাষাশৈলীর সৌন্দর্যবোধ বাংলা ভাষাভাষীর মানুষকে বিমুগ্ধ করে। এই গ্রন্থটি রচনায় তিনি এমনই এক লেখক সত্তার পরিচয় দিয়েছেন যাতে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শ এক দেশ প্রেমিক আর প্রকৃতির প্রতি সৌন্দর্যপ্রিয় এক তরুণ লেখককে খুঁজে পায়। ২৫ দিনের স্মৃতি কথা তিনি দক্ষতা আর শিল্প নিপুনতার সাথে লিখেন। পাঠক বিমুগ্ধ হয়ে যান কিন্তু বিনয়ের অবতার মুজিব লেখেন–
‘হংকং এর কাছে যখন গেলাম তখন মনে হতে লাগলো দূর থেকে দেখতে কি সুন্দর দেশ! পাহাড়ের উপর থেকে আস্তে আস্তে একটা দেশ নিচের সমুদ্র পর্যন্ত নেমে আসছে, মধ্যে মধ্যে নদী। একটা বাড়ি অনেক উপরে, একটা বাড়ি অনেক নিচে। সমুদ্রের পাড়ে জাহাজ ভিড়ে আছে, কোনো কোনো জাহাজ আবার ছেড়ে যাচ্ছে। আবার ছোট ছোট লঞ্চগুলি এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। আমি লেখক নই, আমার ভাষা নাই, তাই সৌন্দর্যটা অনুভব করতে পারছি, কিন্তু গোছাইয়া লেখতে পারি না। পাঠকবৃন্দ আমায় ক্ষমা করবেন।’ (আমার দেখা নয়াচীনপৃষ্ঠা ২৪,, ২৫)
তাঁর লেখার ভাষা চিত্রময় হয়ে উঠেছে। দেশটির চলমান চিত্র যা পাঠক না দেখেও দেশটি দেখে ফেলে। এটাই লেখকের সার্থকতা। এই গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু গণচীন ও তৎকালীন পূর্ব বাংলা এবং সমাজের চালচিত্র সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। যাতে সুস্পষ্ট রাষ্ট্র নির্মাণের পরিকল্পনা প্রকাশ পেয়েছে। চীনের শান্তি সম্মেলনে প্রায় সবাই ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করেছেন কিন্তু তিনি মাতৃভাষায় বক্তৃতা করেছেন। তিনি বলেন– ‘বাংলা আমার মাতৃভাষা মাতৃভাষায় বক্তৃতা করা উচিত। কারণ পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের কথা দুনিয়ার সকল দেশের লোকই কিছু কিছু জানে। মানিক ভাই, আতাউর রহমান খান ও ইলিয়াস বক্তৃতাটা ঠিক করে দিয়েছিল। দুনিয়ার সকল দেশের লোকই যার যার মাতৃভাষায় বক্তৃতা করে। শুধু আমরাই ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করে নিজেদের গর্বিত মনে করি।’( আমার দেখা নয়াচীন, পৃষ্ঠা, ৪৩)
প্রকৃতিপ্রেমী বঙ্গবন্ধুর শৈশব কৈশোর বেড়ে উঠেছে প্রকৃতির কোলে, তাইতো তাঁর লেখক সত্তার বড় দিক প্রকৃতির বর্ণনা। লেখক বঙ্গবন্ধু নয়া চীনের বর্ণনায় আত্মতৃপ্তি লক্ষ্য করা যায়। তিনি তার ক্ষুরধার লেখনীতে সে দেশের উন্নতির সাথে নিজ দেশের ও রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখেন তিনি লিখেন, ‘নয়াচীনের উন্নতি দেখে সত্যিই আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। যদি দশ বৎসর তারা দেশকে শান্তিপূর্ণভাবে গড়তে পারে তবে দেশের জনসাধারণের কোনো দুঃখ– দুর্দশা থাকবে না, অশিক্ষা কুসংস্কার মুছে যাবে।’( আমার দেখা নয়াচীন, পৃষ্ঠা, ১১৮)
‘আমার দেখা নয়াচীন‘’ গ্রন্থটিতে নানান জায়গায় লেখার বিষয় প্রসঙ্গ ও রসবোধ দৃশ্যপটের মতো পরিবর্তন করে তিনি পাঠককে পাঠে আকৃষ্ট করে রেখেছেন। বিদেশী ভাষা ব্যবহার ও শিক্ষার ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে ক্যান্টনের হোটেলে পৌঁছেই দোভাষীর কাছ থেকে শান্তি সম্মেলনের স্লোগান গুলি চীনা ভাষায় শিখে নেন। পাঠককে আনন্দ দিতে লিখেন-‘এই কথা কয়টাই আমার চীনা ভাষার পাণ্ডিত্য।’ (আমার দেখা নয়াচীন, পৃষ্ঠা, ৩৩)
তিনি সাধু ভাষা রীতিতে ছয় দফা প্রচার করেন। তথাপি রাজনৈতিক জটিল বিষয়গুলিকে তিনি সহজ সরলভাবে প্রকাশ করেছেন এবং ভাষার দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চে ভাষণে সংখ্যা বাচক শব্দ দিয়ে স্তবক শুরু করেননি। এই ভাষণে বাংলা ভাষার ব্যবহারে দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়। ৭ই মার্চের ভাষণ আসলে দীর্ঘ একটি কবিতা।
রাশেদ রউফ যথার্থই বলেছেন – ‘মূলত ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু লেখক সত্তা বাঙালির সামনে প্রস্ফুটিত হয়।’ বিশ্বের নানা জনের ভাষণের সাহিত্যমূল্য নিয়ে যদি আলোচনা হয়, তাহলে তাঁর ৭ ই মার্চের ভাষণটা নিঃসন্দেহে থাকবে শীর্ষে। সাহিত্যমূল্য ও প্রাকৃত ছন্দের কারণে সেই ভাষণ কে বলা হয়ে থাকে দীর্ঘ কবিতা।’( দশদিগন্তে বঙ্গবন্ধু, পৃষ্ঠা ৭৯)।
শামসুজ্জামান খান বলেছেন– ‘বঙ্গবন্ধু ছিলেন রাজনীতির মহানায়ক, কিন্তু তিনি যদি শুধু সাহিত্য চর্চা করতেন তাহলেও হতেন এক খ্যাতকীর্তি লেখক। (লেখক বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩০)।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লিখিত গ্রন্থগুলির ভাষা দক্ষতা দেখে বলা যায় তিনি শুধুমাত্র একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন না। তিনি একজন কথা সাহিত্যিকও ছিলেন। তাঁর লেখক সত্তায় ফুটে উঠেছে এই দেশ ও জনগণের কথা, সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করার কথা। এক স্বপ্নদ্রষ্টা মহান পুরুষ লিখে গেছেন স্বদেশ প্রেম আর স্বাধীনতার কথা।
লেখক : প্রাবন্ধিক; বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, নিজামপুর সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম