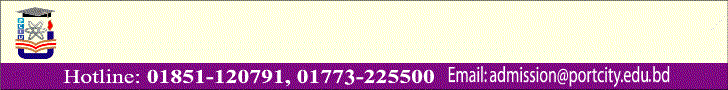‘সাম্পান, হুনি, দরগা– এ নিয়ে চাটগাঁ’—এমন একটি প্রবাদ প্রাচীনকাল থেকে চট্টগ্রামে প্রচলিত আছে। ‘সাম্পান’ নামের জল–জোছনার গাড়িটি তখন থেকেই চট্টগ্রামের নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। এই জল–জোছনার গাড়িটি ‘কেঁ..কুরুত…’ করতে করতে চট্টগ্রামের খাল–বিল–নদী–নালার বুক চিড়ে ছুটে চলেছে শতাধিক বছর ধরে। এ ইতিহাসেরও আগের ইতিহাস আছে। সে–ই ইতিহাসই একদিন খুঁজে নেয়, জল–জোছনার গাড়ি সাম্পানকে।
চট্টগ্রাম আরাকান রাজাদের অধীনে আসার পর নৌ–চলাচল শুরু হয়। তখন নৌকা ব্যবহার হতো যুদ্ধবাহন হিসেবে। আরাকান রাজাদের মতো শক্তিশালী নৌ–বল ভারতবর্ষে অন্যকারো ছিল না। পর্তুগীজ জলদস্যুরা বাংলায় ডাকাতির প্রয়োজনে নৌকার ব্যবহার করত। বাংলার জলপথ রক্ষার জন্য যুদ্ধ নৌকা রাখারও নিয়ম ছিল।
নৌকার আদি নাম ছিল ‘নওয়ারা’। চট্টগ্রামের মানুষ নৌকাকে সাম্পান এবং সাম্পানকে নৌকা বলে।
নদীবেষ্টিত এ–জনপদের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রথম নৌকা তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন সপ্তদশ শতকের শেষভাগে নবাব সায়েস্তা খাঁ। তিনি প্রথমবার ৩০০ নৌকা তৈরি করিয়েছিলেন। তখনও সাম্পানের ধারণা এ–জনপদের মানুষের মধ্যে আসেনি। সাম্পান তৈরির চিন্তা চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের মধ্যে আসে আরও পরে। অনেক ব্যবসায়ীর চাঁদ সওদাগরের মতো বাণিজ্যে যাত্রা করার জন্য নিজস্ব জাহাজ ছিল। চট্টগ্রামে সে–সব জাহাজ তৈরি হতো। গোসালডেঙ্গা, হালিশহরের হিন্দু–বালামী ও বাহারূয়াগণ এসব জাহাজ তৈরির প্রধান কারিগর ছিলেন। তাঁরা রেঙ্গুন গিয়ে প্রথম সাম্পান দেখতে পান। পাল তোলা সাম্পান জাহাজের মতো দ্রুত গতিতে চলত। চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীরা এ–কারণে আকৃষ্ট হন। এছাড়া পাল তোলা সাম্পান দৃষ্টি নন্দন ছিল। এর একটা কারণ ছিল। তারা জাহাজের বিকল্প হিসেবে সাম্পান চট্টগ্রামে নিয়ে আসেন। বাস্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর চট্টগ্রামের জাহাজের কদর ধীরে ধীরে কমতে থাকে। চৌধূরী শ্রী পূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা তত্ত্বনিধি লিখেছেন, ‘…মুসলমান কারিগরগণ সাম্পান প্রস্তুত করে।
পুরাকালে এদেশে সাম্পানের ব্যবহার ছিল না; প্রথমতঃ রেঙ্গুন হইতেই ইহার আমদানী হয়। এখন ইহা এদেশে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। এবং প্রতি বৎসর ছোট বড় শত শত সাম্পান প্রস্তুত হয়। এ দেশীয় সাম্পানওয়ালারা ঐ সকল সাম্পানে করিয়া আকিয়াব, রেঙ্গুন, সুন্দীপ প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন করে। পাল–সহযোগে ই্হা স্টিমারের ন্যায় খুব বেগে চলে। পাল তুলিয়া পবন ভরে সাম্পান বহর যখন কর্ণফুলী নদী বাহিয়া সারি সারি চলিতে থাকে তখন দূর হইতে ইহার দৃশ্য বড় নয়ন মনমুগ্ধকর। বর্তমানে এত বড় বড় সাম্পানও তৈয়ার হয় যে তাহার এক একটীতে ২০০০ আড়ি ও ততোধিক ধানের বোঝাই করিতে পারা যায়।’
সাম্পান চালানোর সময় যে ‘কেঁ..কুরুত…’ শব্দ শুনি, এটি হালিশ চালানোর সময় কঁপিয়ে উঠার শব্দ। সাম্পানের পেছনের দিকে দুই পাশে দুটি খুঁটি থাকে। সে–ই খুঁটি দুটির সঙ্গে বেতের আঁংটা দিয়ে হালিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। মাঝি দাঁড়িয়ে একটু সামনে ঝুঁকে দুই হাতে হালিশে চাপ দিলে বেত আর কাঠের সংঘর্ষে এমন শব্দের সৃষ্টি হয়। শব্দটি সাম্পানের প্রধান বৈশিষ্ট্যও। ছোট–বড় সব সাম্পানে মাস্তুল থাকে। মাস্তুলে নানান রঙের পাল খাটানো হয়। কখনো আরও একটা ছোট তিনকোণা পাল খাটানো হয়। পালে হাওয়া লাগলে সাম্পান দ্রুত ছুটে। লম্বা দাঁড়কে হালিস বলে। দাঁড়ের হাতলকে বলে পইর। মাঝির দু’পায়ের ফাঁকে হাঁটু বরাবর আবদ্ধ থাকে হাইল। হাইলকে কক্সবাজারে বলা হয় সুপন। সাম্পানের দিক ঘোরানোর জন্য মাঝি সেটি পা দিয়েই ঘোরায়। সাম্পানে সর লাগানো হলে জোরে চলে।
সাম্পান শব্দটা এসেছে চীনা শব্দ ‘সাং পাং’ থেকে। চীনা ভাষায় ‘সাং পাং’ শব্দ দুটোর অর্থ হচ্ছে তিন মাথা। সাধারণত নৌকা বা অন্যান্য নৌ–যানের দুটো মাথা বা গলুই থাকে। সাম্পানে গলুই থাকে তিনটি। সামনে একটা, পেছনে দুটো। পেছনের গলুই দুটো মোষের শিংয়ের মতো দু’ভাগে বিভক্ত। এ কারণেই এর নামকরণ করেছে সাম্পান। আরাকানি ভাষায় সাম্পানকে বলে ‘থাম্মান’। জাপানিরা বলে ‘জুমপেন’। মালয়ী ভাষায় বলে ‘সামপেন’। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় ‘সাম্মান’। কারো মতে, সাম্পান একটি ক্যান্টনিজ শব্দ। এ ভাষায় সাম অর্থ তিন এবং পান অর্থ কাঠের টুকরো। এ থেকে সাম্পান নামের উদ্ভব। এর আভিধানিক অর্থ ‘তিন টুকরো কাঠ’। একটি সম্পূর্ণ কাঠের টুকরো দিয়ে চ্যাপ্টা তল, তার দু’পাশে আস্ত আরো দু’খানা টুকরো জোড়া দিয়ে চায়না সাম্পানের কাঠামো তৈরি হয়। চট্টগ্রামের সাম্পান আস্ত কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরি হয় না। তাতে ব্যবহৃত হয় কাঠের সরু ফালি। চট্টগ্রামের সাম্পানের কিছু উপাদানের নকশা চায়না সাম্পানের মতো।
সাম্পানের গঠন ও নির্মাণ শৈলী অন্য নৌকার চাইতে ভিন্ন। সাম্পানের সামনের দিকটা বাঁকানো চাঁদের মতো, যাতে সমুদ্রের ঢেউ কেটে সামনের দিকে যেতে পারে। পেছনের দিকটা একরকম সোজা বলা যায়। দেখতে অনেকটা হাঁসের মতো। বাংলাদেশে দুই ধরনের সাম্পান আছে। সমুদ্র উপকূলের আশপাশে চলার জন্য ছোট সাম্পান আর সমুদ্রে চলাচলের জন্য বড় সাম্পান। এসব সাম্পান দৈর্ঘ্যে ৬ থেকে ১৫ মিটার পর্যন্ত হয়। মাছ ধরার সাম্পানের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭ ফুট, প্রস্থ ৯ ফুট। দীনেশচন্দ্র সেন ‘বৃহৎবঙ্গ’ বইতে লিখেছেন, ‘দেখতে এটি হাঁসের মতো। এটি তৈরি হয়েছে চীন দেশের নৌকার আদলে।’
বইলাম, চাপালিশ, গামারি, গর্জন ইত্যাদি কাঠ দিয়ে সাম্পান তৈরি হয়। মিয়ানমার ও টেকনাফের বেশিরভাগ সাম্পান ছিল সেগুন কাঠের তৈরি। এসব সাম্পানে চট্টগ্রামের ব্যবসায়িরা শুধু বাণিজ্যেই যেতেন না, একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করতেন। নদীতে, গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণেও যেতেন।
রফিক আজাদের ‘সুন্দর সাম্পানে চড়ে মাধবী এসেই বলে–‘যাই’’ কবিতার মতো অসংখ্য কবিতা–গল্প–উপন্যাসে সাম্পানের উল্লেখ রয়েছে। সাম্পান ও সাম্পানমাঝির জীবনকথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলার শিল্প–সাহিত্য–সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। সাম্পান কিংবা সাম্পানওয়ালার জীবনভিত্তিক আঞ্চলিক সঙ্গীতগুলো লোকসংস্কৃতির অমূল্যসম্পদ। এ–সব লোকগানের সঙ্গে চট্টগ্রামের যেসব শিল্পী–গীতিকারের নাম জড়িয়ে আছে, তাঁরা হলেন– রমেশ শীল, মলয় ঘোষ দস্তিদার, আবদুল গফুর আলী, বুলবুল আকতার, সৈয়দ মহিউদ্দিন, ইয়াকুব আলী, মোহাম্মদ নাসির, সঞ্জীত আচার্য্য, এম.এন.আখতার, মোহনলাল দাশ, শেফালী ঘোষ, কান্তা নন্দী, আসকর আলী পণ্ডিত, সেকান্দর পণ্ডিত, অচিন্ত্য কুমার চক্রবর্তী, লক্ষীপদ আচার্য, আহমদ কবির আজাদ, দীপক আচার্য, নুরুল আলম, শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব, কল্যাণী ঘোষ, ইকবাল হায়দার, সিরাজুল ইসলাম আজাদ, খোরশেদুল আনোয়ার, গীতা আচার্য, এম.এ. রশিদ কাওয়াল, রবি চৌধুরী প্রমুখ। আশুতোষ চৌধুরীর সংগৃহীত প্রায় তিনশত বছরের পুরাতন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (চতুর্থ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা) ‘নসর মালুম’–এ সাম্পান মাঝির কথা আছে।
১৯৩২ সালে কলকাতার হিজ মাস্টার্স ভয়েস (এইচএমভি) থেকে জগন্ময় মিত্রের তত্ত্বাবধানে শিল্পী মোহাম্মদ নাসিরের কণ্ঠে প্রথম চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের যে গ্রামোফোন রেকর্ড বের হয়েছিল, সেই রেকর্ডের এই গানটি– ‘দেবাইল্যা বানাইলরে মোরে/সাম্পানর মাঝি।’ ১৯৪১ সালের দিকে মলয় ঘোষ দস্তিদারের কণ্ঠে, কথা ও সুরে গ্রামোফোন রেকর্ডে বের হয়, ‘চোড চোড ঢেউ তুলি…’ গানটি। ১৯৬৮ সালে আঞ্চলিক গানের রাণী শেফালী ঘোষের কণ্ঠে ‘ওরে সাম্পানওয়ালা’ গানটি গ্রামোফোন রেকর্ডে বের হয়। সত্তরের দশকে গানটি খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।
সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে সঞ্জীব আচার্য্য’র লেখা ‘সাম্পানওয়ালা’ নামের আঞ্চলিক নাটকটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। নাটকের শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করে পংকজ বৈদ্য–অঞ্জু ঘোষ। পরে এটি ১৯৮২ সালে (মতান্তরে ১৯৭৮ সালে) চলচ্চিত্র হয়। ২০০৬ সালে ছবিটি রি–মেক হয় ‘ওরে সাম্পানওয়ালা’ নামে। আব্দুল গফুর হালীর ‘কুশল্যা পাহাড়’, ‘গুলবাহার’সহ অনেক নাটকেও সাম্পান আর সাম্পানওয়ালার কথা আছে।
বাংলা একাডেমি প্রকাশিত শিল্পী কল্যাণী ঘোষ ‘চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান’ গ্রন্থে লিখেছেন,‘চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের সাথে ‘সাম্পান’ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। উল্লেখ্য, চীন সাগরের উপকূল থেকে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের এই বিশেষ ধরনের নৌকার বড় বৈশিষ্ট্য হলো ঝড়–ঝঞ্ঝার মধ্যেও ডোবে না। সাম্পানের এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে সাম্পানের ওপর ভিত্তি করে চট্টগ্রামের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামও তৈরি হয়েছে।’ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ধূসর রঙের লোগোটি শিল্পী কামরুল হাসান অঙ্কন করেছেন সাম্পানের আদলে। এটি সাম্পানের সামনের দিকটার অনুকরণে করা হয়েছে। ধূসর রঙেও সাম্পানের রঙের প্রভাব কাজ করেছে। এরমাধ্যমে সাম্পান আন্তর্জানিক মর্যাদা লাভ করে।
সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। সাম্পান ও সাম্পানমাঝির গৌরবোজ্জ্বল সে–দিনগুলো আর নেই। নদী–নালা–খাল–বিলগুলো যন্ত্রচালিত নৌকার অত্যাচারে বিধ্বস্ত। চাটগাঁর কোলাগাঁয়ে, হালিশহরে, বরকলে, সন্দ্বীপ, মহেশখালী, কক্সবাজারের কুতুবদিয়া, মাতারবাড়ি ও চৌফলদণ্ডি, ভারুয়াখালি, রামু, গুমাতলী, বালুখালি, গুনধুম, হ্নীলা, টেকনাফ, চিরিঙ্গা, চানখালি–শঙ্খ–হালদা নদীর উজানে এবং আরও অনেকস্থানে সাম্পানের একসময় বড়–বড় কারখানা আর আড্ডা ছিল– এসব এখন অতীত ইতিহাস। বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের কারণে একদিন চট্টগ্রামের নৌপথে জাহাজের আধিপত্যকে হটিয়ে পাল তোলা জল–জোছনার গাড়ি সাম্পান যে–স্থান দখল করেছিল, ইঞ্জিনচালিত নৌকা এসে তা আবার দখলে নিয়েছে। সৈয়দ মহিউদ্দিনের একটি গানে আছে– ‘সাম্পান মাঝি সাম্পান বায়/আগের মতো পেসিঞ্জার ন পায়।/ নৌকার মাথিত ইঞ্জিল দেখি/ মানুষ গেইয়ে হেইখ্যা ঝুখি/সরে সরে আইবু যাইবু/দেরি গইত্যু কনে চায়।।’ ফলে, ভালো নেই আজ আমার জল–জোছনার গাড়ি সাম্পান আর সাম্পানমাঝিরা। ভালো নেই কর্ণফুলী আর তার চারপাশ।
লেখক : প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার