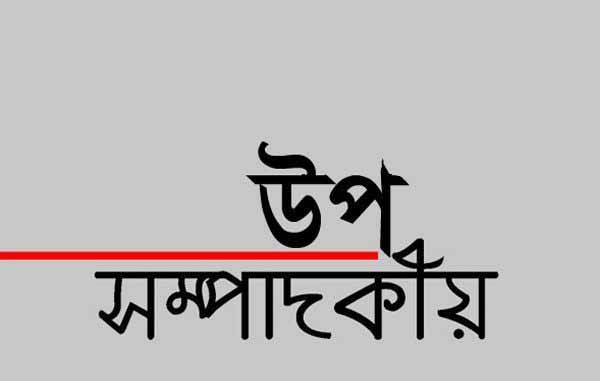সপ্তাহ কয়েক ধরে হল্যান্ডে বেশ ঠান্ডা পড়ছে। আবহাওয়াবিদরা পূর্বাভাসে জানিয়েছেন গত বছরের তুলনায় এই বছর অনেক বেশি ঠান্ডা পড়বে, তুষারপাতও হবে বেশি। শীত যে বাড়বে তা এখন থেকেই টের পাওয়া যাচ্ছে। তবে ঘরে–বাইরে যত ঠান্ডাই পড়ুক না কেন, আগামী ২৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য ডাচ পার্লামেন্ট নির্বাচনকে ঘিরে হল্যান্ডের ‘রাজনীতির–মাঠ‘ ইতিমধ্যে বেশ গরম হয়ে উঠেছে। কথাটা বোধকরি ঠিক বলা হলোনা। এদেশে ‘রাজনীতির–মাঠ‘ শব্দটি একেবারে অচেনা। কেননা এদেশের রাজনীতি আমাদের দেশের মত মাঠে গিয়ে গড়ায় না। রাজনীতিকে ঘিরে তাবৎ আলোচনা, তর্ক–বিতর্ক সব চার দেয়ালের মধ্যেই সীমিত। আর সীমিত থাকে টিভি টক–শোতে, কোন হলঘরে, কিংবা কলেজ বা কোন প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক নেতাদের ‘ভিজিটের‘ মধ্যেই। ঘরের বাইরে রাজনৈতিক কোন স্লোগান নেই। দেয়ালে কোন চিকা, পোস্টার কিংবা দলীয় শীর্ষ নেতা থেকে শুরু করে পাতি নেতা, সিকি নেতার ছবি নেই। কেবল দেশের বিভিন্ন শহরে হাতে গোনা নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানের দেয়ালে বিভিন্ন দলের পোস্টার সাঁটানো চোখে পড়ে। মজার ব্যাপার হলো, প্রধান কয়েকটি দলের দলীয়–প্রধানের ছবিও নেই ওই সমস্ত পোষ্টারে। তাদের মতে ব্যক্তি নয়, দল আগে। আমাদের ঠিক উল্টো। ব্যস, ঐখানেই শেষ রাজনৈতিক প্রচারণা। মাঝে মধ্যে অবশ্য দেখা যায় রাজনৈতিক নেতাদের কর্মী–সমর্থক নিয়ে খোলা বাজার বা শপিং সেন্টারে পথচারীদের মাঝে দলীয় লিফলেট বিতরণ করতে। অতি আগ্রহী কেউ কেউ এই সুযোগে নেতাদের নিয়ে সেলফি তোলেন। নেতারাও মুখে হাসি মেখে তাদের সাথে ছবি তোলেন। ভোট চাইতো! কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, বৃহদাংশ ডাচ জনগণ রাজনীতিতে খুব একটা আগ্রহী নন। রাজনীতিতে তাদের বিশ্বাস একেবারে তলানিতে। সমপ্রতি পরিচালিত এক সমীক্ষায় জানা যায়, রাজনীতিবিদের প্রতি ডাচ জনগণের বিশ্বাস খুব কম। তরুণদের মাঝে তা আরো কম। তাদের মতে, রাজনীতিবিদরা কেবল কথাই বলেন, কাজের কাজ কিছু করেন না। তারপরও তাদের অনেকে ভোটকেন্দ্রে যান। ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। যারা কেন্দ্রে যেতে পারেননা, তারা নিজের ভোট পরিচিত কাউকে বা পরিবারের কোন সদস্যকে ‘অথরাইজড‘ করে দেন। ভোট দেবার একটি কার্ড ডাকযোগে আপনার বাসায় পৌঁছে যাবে নির্বাচনের সপ্তাহ তিনেক আগে। ওই কার্ড এবং পাসপোর্ট কিংবা আইডি কিংবা ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখিয়ে আপনি আপনার ভোট দিতে পারবেন। মোট ১৫০টি সংসদীয় আসনের জন্যে ছোটবড় মিলিয়ে এবার লড়ছে মোট ২৬টি রাজনৈতিক দল। এক কোটি চুরাশি লক্ষ জনসংখ্যার ওলন্দাজদের এই দেশে ভোটার সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষ। আমি ভোট দিচ্ছি গত ৩৪ বছর ধরে। এক দলকেই বারবার ভোট দিয়েছি তা ভাবার কোন কারণ নেই। এখানে প্রায় সবাই তাই করে। দলীয় অন্ধ ভক্তের সংখ্যা হাতে গোনা। দলের নীতিমালা ও তাদের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো যাচাই করে ভোটার সিদ্ধান্ত নেন আগামীবার কাকে কিংবা কোন দলকে ভোট দেবেন। অবশ্য কিছু কিছু ভোটার আছেন যারা কোন কোন দলের অন্ধ সমর্থক। পছন্দের প্রার্থী যতদূর সম্ভব নির্ভুল নিশ্চিত করার জন্যে ডাচরা রাজনৈতিক টেলিভিশন টক–শোগুলো নিয়মিত দেখেন, পত্র–পত্রিকা পড়েন। আজ প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় ১৭% ভোটার এখনো জানেন না তারা কাকে ভোট দেবেন। প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভোটার কোন দলের প্রতি তাদের অগ্রাধিকার জানালেও এখনো দোটানায় রয়েছেন।
চলিত সপ্তাহে দেশ থেকে বেড়াতে এসেছেন মাঝারি গোছের ব্যবসায়ী মোজাম্মেল হোসেন। দেশে তার গার্মেন্টস ব্যবসা। যখন শুনলেন এক সপ্তাহ পর এদেশে জাতীয় নির্বাচন, অবাক হয়ে বলেন, ‘কী বলেন, একটা পোস্টারও তো চোখে পড়লো না এই কদিনে। কোন মিছিল, কোন স্লোগান কিছুই তো দেখিনা।‘ উত্তরে বলি, ‘আজ বলে নয়, ভোটের দিনও টের পাবেন না এই দেশে জাতীয় নির্বাচন হচ্ছে।‘ পোলিং স্টেশন খোলা থাকবে ভোর সাড়ে ছটা থেকে রাত নটা। রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ভোর সাড়ে ছটায় পোলিং সেন্টার খোলা হয়, যাতে অফিস–গামী যাত্রীরা অফিস যাবার পথে সহজে ভোট দিতে পারেন। রেল স্টেশন ছাড়াও শপিং সেন্টার, স্কুল–কলেজ ইত্যাদি জায়গায় ভোট কেন্দ্র খোলা হয়ে থাকে। সেন্টারের সামনেও কোন দলীয় কোন নেতা–কর্মী নেই। কোন পোস্টার নেই। আপনার যখন সময় হবে তখন ভোট দিয়ে আসবেন। ভোট দিয়ে যে যার কাজে চলে যায়, কেউ নিজ অফিসে, কেউ তার ব্যবসা বা অন্য কাজে। সবকিছু অতি স্বাভাবিকভাবে চলে। ভোট গ্রহণ শেষ হবার ঘন্টা খানেকের মধ্যে, ছোট ছোট শহরে তারও আগ থেকে ফলাফল ঘোষণা শুরু হয়। সবার দৃষ্টি টেলিভিশনের পর্দায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মী জড়ো হন কোন এক শহরের কোন এক হলে। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির নেতারা যারা জয়ী হবেন বলে আশা করেন বিজয়ী–ভাষণের জন্যে প্রস্তুত থাকেন। নির্বাচনে হেরে গেলে বিজিত দল এবং নেতাকে শুভেচ্ছা জানান সাথে সাথে। কারচুপির কোন অভিযোগ বিগত ৩৪ বছর শুনিনি। হেরে–যাওয়া কোন দল কখনো কারচুপি হয়েছে এমন অভিযোগ তোলেনি। যদিওবা এই ধারা বাংলাদেশ তো বটেই, গণতন্ত্রের ধারক–বাহক দাবিদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিত্য ব্যাপার।
২. এই সময়ে এই নির্বাচন হবার কথা ছিল না। চরম ডান ও ইসলাম–বিরোধী নেতা খিয়ের্ট বিল্ডার্স বিগত কোয়ালিশন সরকার থেকে ১১ মাসের মাথায় তার দল, ফ্রিডম পার্টিকে সরিয়ে নিলে সরকার পতন আবশ্যক হয়ে পড়ে। ইমিগ্রেশন (অভিবাসন) এবং এসাইলাম পলিসিকে নিয়ে কোয়ালিশন সরকারে থাকা অন্য ৩টি দলের নীতির সাথে তার মতবিরোধ হলে বিল্ডার্স এই সিদ্ধান্ত নেন। দেখা দেয় রাজনৈতিক শূন্যতা। তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী ডিক স্কোফ যিনি বিল্ডার্স কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন, বিল্ডার্সের এই সিদ্ধান্তকে ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন ও অপ্রয়োজনীয়‘ বলে মন্তব্য করেছিলেন। খিয়ের্ট বিল্ডার্স বলেন, আসন্ন নির্বাচনে তার দল ফ্রিডম পার্টি আরো শক্তিশালী রূপে আত্মপ্রকাশ করবে, তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং সে লক্ষ্যে কাজ করে যাবেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, বিগত নির্বাচনে বিল্ডার্সের ফ্রিডম পার্টি যা ডাচ ভাষায় ‘পারটাই ফান ফ্রাইহাইদ বা পেই ফেই ফেই সর্ব বৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসাবে জয়ী হয়। আসন্ন নির্বাচনেও তার দল সব চাইতে বড় দল হিসাবে নির্বাচিত হবে বলে অনেকটা নিশ্চিত। দেশের নানা জরীপে তার দল অন্যান্য দলগুলিকে পেছনে রেখে এগিয়ে আছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প নীতির ‘আমেরিকা ফার্স্ট‘ নীতির মত খিয়ের্ট বিল্ডার্সও এই বলে ডাচ জনগণকে তার দিকে ভিড়িয়েছে যে ‘হল্যান্ড ইজ ফুল‘, অর্থাৎ হল্যান্ডে এখন অন্য দেশ থেকে লোক নেবার মত অবস্থা নেই। তিনিও ট্রাম্পের মত ‘হল্যান্ড ফার্স্ট‘ এবং মুসলিম দেশগুলি থেকে মাইগ্রেন্টস আসার সকল পথ বন্ধ করে দেবার দাবি করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে। আজ প্রকাশিত এক জরিপের ফলাফলে জানা যায়, খিয়ের্ট বিল্ডার্সের দল ৩০ থেকে ৩৩টি আসন জয়ী হয়ে শীর্ষে স্থান অধিকার করবে। দ্বিতীয় স্থানে যৌথভাবে থাকবে লেবার পার্টি (পারটাই ফান আরবাইডস বা পেই ফেই ডেই আ) এবং গ্রিন পার্টি পার্টি মিলে তৈরী মোর্চা। তবে একই অবস্থানে রয়েছে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি (সিডিএ)। উভয় দল ২২ থেকে ২৬টি আসন লাভ করবে বলে ওই জরিপে প্রকাশ। মোট ২৬টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে আরো যে দুটি দল ‘লাইমলাইটে‘ রয়েছে তা হলো ৪৮–বছরের তুর্কি–কুর্দি বংশদ্ভুত ‘স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্যে পিপলস পার্টি‘ (ফেই ফেই দে) নেত্রী, দিলেন ইসিলগজ এবং ৩৮ বছরের রব ইয়েতেনের নেতৃত্বে ‘ডেমোক্রেসি ৬৬‘ (দেই –৬৬)। তবে এই সমস্ত জরিপের ফলাফল যে সব সময় সঠিক হয় তা ভাবার কোন কারণ নেই। গেল নির্বাচনেও ফ্রিডম পার্টি শীর্ষে ছিল। কিন্তু মোট যে আসন পেয়েছিল তা এককভাবে সরকার গঠনে যথেষ্ট ছিলনা। ফলে দলটিকে আরো ৩টি দলের সাথে সমঝোতা করে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হয়েছিল। স্বাভাবিক নিয়মে বিল্ডার্সের প্রধান মন্ত্রী হবার কথা। কিন্তু তা হয়নি। কেননা বিল্ডার্সের নেতৃত্বে কোন রাজনৈতিক দল কোয়ালিশন সরকারে যেতে আগ্রহী নয়। ফলে বিল্ডার্সকে ‘বিটার পিল‘ বা তিতা টেবলেট গিলতে হয়। তিনি প্রধান মন্ত্রীর আশা ত্যাগ করে তার পছন্দের এক অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে (বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালী সরকারের প্রধান মন্ত্রী ডিক স্কোফ) প্রধান মন্ত্রী হিসাবে মনোনীত করেন। সরকারে না থাকলেও তিনি দলীয় প্রধান হিসাবে মূল চাবিকাঠি নাড়তে থাকেন এবং তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ অভিবাসন ইস্যু নিয়ে সরকারে অন্য দলগুলির সাথে বনিবনা না হলে, তিনি সরকার থেকে তার দলের সমর্থন উঠিয়ে নেন। ফলে অসময়ে পতন ঘটে সরকারের।
৩) এবারের নির্বাচনে অনেক ইস্যু থাকলে যে দুটি বিষয় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু তা হলো: অভিবাসন ও আবাসন। ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত হল্যান্ডেরও বৃহৎ জনগোষ্ঠী বন্যার স্রোতের মত ধেয়ে আসা শরণার্থী বন্ধ করার জন্যে দাবি জানিয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। তাদের ধারণা ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে এরা এদেশে এসে নানা ধরনের সামাজিক ও নিরাপত্তা বিষয়ক সমস্যা সৃষ্টি করে। এই সমস্ত কারণে ‘সহনশীল‘ দেশ হিসাবে পরিচিত হল্যান্ড এবং এ দেশের জনগণ দিনদিন বিদেশিদের প্রতি বিষিয়ে উঠছে। আর এই একটি ইস্যুকে সামনে নিয়ে চরম ডানপন্থী নেতা বিল্ডার্স জনগণকে তার দিয়ে টেনে আনছেন। ফলে যে সমস্ত বাম ও সোসালিস্ট দল এই ইস্যুতে আগে কিছুটা নমনীয় ছিল এখন তারাও তাদের সুর পরিবর্তন করে ‘বিদেশী অনুপ্রবেশ‘ বা শরণার্থী বন্ধে নির্বাচিত হলে পদক্ষেপ নেবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। ‘আবাসন‘ হলো দ্বিতীয় বড় ইস্যু। বর্তমানে গোটা দেশে প্রায় চার লক্ষ আবাসন সংকট রয়েছে, যার ফলে বাড়ীর মূল্য অস্বাভাবিক আকাশচুম্বী। ভাড়াটে বাড়ির যেমন সমস্যা ঠিক তেমনি সমস্যা কেনা বাড়ির। চাহিদার তুলনায় বাড়ি অনেক কম। যা আছে তার মূল্য আকাশচুম্বী। ফলে অনেকেই বছরের পর বছর বাড়ি ভাড়া না পেয়ে বা কিনতে না পেরে সীমাহীন সমস্যায় রয়েছেন। ”নির্বাচন এক ধরনের ‘গ্যাম্বলিং‘। কে হারে কে জেতে আগ–বাড়িয়ে বলা মুশকিল,” মন্তব্য এক রাজনৈতিক ভাষ্যকারের। দেখা যাক, ক‘দিন বাদে (২৯ অক্টোবর) অনুষ্ঠিতব্য হল্যান্ডের সংসদীয় নির্বাচনের ফলাফল কী দাঁড়ায়। সেদিনের প্রতীক্ষায়। (২৩–১০–২০২৫)