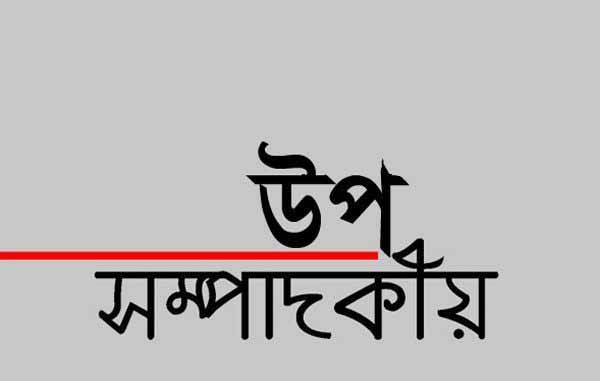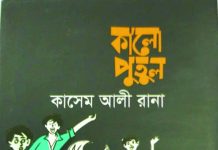বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের সংবিধানের মূলনীতি থেকে সমাজতন্ত্রকে বাদ দেওয়ার জন্য বিকল্প খুঁজে বেড়াচ্ছে। আসলে, স্বাধীনতার কয়েক মাস পর থেকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ক্ষমতাসীন সরকারের উদ্দিষ্ট ছিল না। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে যে বাকশাল কর্মসূচি ঘোষিত হয়েছিল তাতে বেশ কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি প্রচলনের উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ওগুলো বাস্তবায়নের আগেই বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রক্তাক্ত রাজনৈতিক পট–পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎখাত হয়ে যাওয়ায় ওগুলোর পক্ষে–বিপক্ষে মতামত প্রদানের সুযোগ নেই। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ব্যানারে যে ছাত্র–ছাত্রীরা ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্ট অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে তাদের মাধ্যমে গঠিত সরকার সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্রকে ছুড়ে ফেলতে চাইছে, ব্যাপারটা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। সমাজতন্ত্র ব্যতিরেকে বৈষম্য–নিরসন খুবই দুরূহ ব্যাপার। সোভিয়েত স্টাইলের সমাজতন্ত্র বিংশ শতাব্দীর আশি ও নব্বই দশকে পরিত্যক্ত হয়ে গেলেও ‘একুশ শতকের সমাজতন্ত্রের’ নানা পরিবর্তিত মডেল বিশ্বের নানা দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করায় সফলভাবে অনুসৃত হয়ে চলেছে। ২০২৫ সালে সমাজতন্ত্রের যে পরিবর্তিত মডেলগুলো বিশ্বের কয়েকটি দেশে চালু রয়েছে সেগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি সমাজতন্ত্রের পুরানো মডেলগুলোর সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটিগুলো থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিয়েছে। এগুলোর মধ্য থেকে দুটো মডেল নিয়ে আজ আলোচনা করতে চাই: ভিয়েতনাম ও কেরালার মডেল। এই দুটো মডেল থেকে বাংলাদেশের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে মনে করি।
১৯৫৪ সালে ভিয়েতনামের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে ফ্রান্সকে, কিন্তু ১৯৫৫ সালে আবার মার্কিন পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দক্ষিণ ভিয়েতনামে জেঁকে বসেছে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে, কুড়ি বছর ধরে ভিয়েতনামে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম উত্তর ভিয়েতনামের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মহারক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। প্রায় কুড়ি লাখ ভিয়েতনামীর মৃত্যুর বিনিময়ে ঐ যুদ্ধে বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছিল ভিয়েতনাম, লজ্জাজনক পরাজয় মেনে নিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে ১৯৭৫ সালে পালাতে হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। আশির দশকে পোলান্ডে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন সফল হওয়ায় পূর্ব ইউরোপের সকল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের সংগ্রামের মাধ্যমে ডমিনো স্টাইলে ভেঙে পড়ে সমাজতন্ত্র। সবশেষে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলোপ ঘোষণা করে রাশিয়া। আশির দশক ও নব্বই দশকের এই ঐতিহাসিক প্রতিবিপ্লবের ধারার কারণে মনে করা হয়েছিল, সমাজতন্ত্র ক্রমশ বিশ্ব থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোতে সমাজতান্ত্রিক মডেলগুলোর পতনের পর্বেই ভিয়েতনাম ১৯৮৬ সালে তাদের সমাজতান্ত্রিক মডেলে যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধন করে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত ও টেকসই করায় চমকপ্রদ সফলতা অর্জন করতে সমর্থ হয় ।
ভিয়েতনাম প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতা–যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছে ১৯৭৫ সালে। তিন দশকের চরম–বিধ্বংসী স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে ঐ সময় ভিয়েতনাম বাংলাদেশের মত বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র দেশ হিসেবে বিবেচিত হত। বিশ্বের জনগণের কাছে ভিয়েতনাম হলো সবচেয়ে বেশি রক্ত–ঝরানো স্বাধীনতা–যুদ্ধে বিজয়ী দেশ। সমাজতন্ত্রী ভিয়েতনাম বিশ্বের একমাত্র দেশ যে দেশটি বিশ্বের দু’দুটো সুপার–পাওয়ার ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পরাজিত করে নিজেদের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছে, ফ্রান্স পরাজয় বরণ করেছে ১৯৫৪ সালে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭৫ সালে। ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বরে সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনাম যখন স্বাধীন দেশ হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল তখন ‘জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার তবু মাথা নোয়াবার নয়’– সুকান্তের এই অবিস্মরণীয় কবিতার লাইনটি আক্ষরিকভাবে প্রযোজ্য ভিয়েতনামের বীর জনগণের ক্ষেত্রে। যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে স্বাধীন ভিয়েতনামকে মার্কিনীরা অর্থনৈতিক অবরোধ দিয়ে পঙ্গু রাখারও ব্যবস্থা করেছে দুই দশক। এতদ্সত্ত্বেও ভিয়েতনাম কখনোই কোন দেশের কাছে মাথা নত করেনি, ভিক্ষার জন্যে হাত পাতেনি। এমনকি, অনুদান ও ‘সফট লোনের’ আশায় জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটেগরিতে অন্তর্ভুক্ত হতেও আবেদন করেনি। অথচ, কী দারুণ কষ্টকর ছিল ১৯৭৫–পরবর্তী বছরগুলোতে ভিয়েতনামের জনগণের জীবন! ভিয়েতনামের জনগণের মাথাপিছু জিডিপি ১৯৭৪ সালে ছিল মাত্র ৬৫ ডলার (যা বাংলাদেশের চাইতেও কম), ১৯৮৫ সালে ছিল ২৮৫ ডলার। ২০২৫ সালে আইএমএফ এর প্রাক্কলন মোতাবেক ভিয়েতনামের মোট জিডিপি ৪৯০ বিলিয়ন ডলার। ২০২৫ সালে ভিয়েতনামের মাথাপিছু নমিনাল জিডিপি ৪৮০৬ ডলারে পৌঁছে গেছে, যেটাকে ‘মিরাকল’ বলা হচ্ছে। ক্রয়ক্ষমতার সমতার ভিত্তিতে ভিয়েতনামের মাথাপিছু জিডিপি ২০২৪ সালে পৌঁছে গেছে ১৭,৪৮৪ পিপিপি ডলারে। ভিয়েতনামের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ২০০৫ সালে সর্বোচ্চ ৮.৫ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছিল। সর্বশেষ ২০২৪ সালে ভিয়েতনামের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৫ শতাংশ। ২০২৪ সালে ভিয়েতনামের মাত্র ২ শতাংশ জনগণ দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করছে। ১৯৮৬ সালে ভিয়েতনাম ‘দোই মোই’ বা রিনোভেশন নাম দিয়ে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করে। ১৯৮৬ সালে ‘দোই মোই’ সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার ৩৯ বছর পর এখন পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন–চিন্তকরা ভিয়েতনামের অর্থনীতিকে ‘সোশালিস্ট–ওরিয়েন্টেড মার্কেট ইকনমি’ হিসেবে বর্ণনা করছেন। ‘দোই মোই’ কর্মসূচিতে ‘কালেকটিভ ফার্মিং’ নিষিদ্ধ হয়েছে, জমির ওপর জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ উভয়কে উৎসাহিত করা হয়েছে। ‘দোই মোই’ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের প্রধান তিনটি ডাইমেনশান হলো: ১) অত্যন্ত শক্তহাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উদারীকরণ, ২) অত্যন্ত দ্রুত অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির বি–নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারী হস্তক্ষেপ হ্রাসের মাধ্যমে ব্যবসা করার খরচ ও বাধাবিঘ্ন কমিয়ে ফেলা এবং ৩) রাষ্ট্রীয় খাতের বিনিয়োগ প্রবলভাবে জোরদার করার মাধ্যমে মানব উন্নয়ন (শিক্ষা) ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নকে প্রথম অগ্রাধিকারে পরিণত করা। বিশেষত, প্রাইমারী শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক (ভোকেশনাল) শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিয়ে ভিয়েতনাম ২০০০ সালের মধ্যেই তার পুরো জনসংখ্যাকে শতভাগ শিক্ষিত করে তুলেছে এবং জনগণের বিশাল একটি অংশকে প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনে সফল করে তুলেছে। একইভাবে উল্লেখযোগ্য যে ভিয়েতনাম তার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বৈষম্য তেমন একটা বাড়তে দেয়নি। ভিয়েতনামের জনগণের শতভাগ ২০২৫ সালে স্বাস্থ্য বীমার আওতায় সেবা পেয়ে চলেছে। জনসংখ্যা নীতির ব্যাপারে ভিয়েতনাম কঠোরভাবে ‘দুই সন্তান নীতি’ অনুসরণ করে চলেছে। আয় ও সম্পদ বৈষম্যের ক্ষেত্রেও ভিয়েতনাম অত্যন্ত সযতনে বৈষম্যবৃদ্ধির প্রবণতাকে প্রতিরোধ করে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফলকে কয়েকটি নগরে কেন্দ্রিভূত না করে ভিয়েতনাম গ্রামীণ জনগণের মাঝে উন্নয়নের সকল ডাইমেনশানকে পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। বৈদেশিক বিনিয়োগকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করে চলেছে ভিয়েতনাম। স্যামসাং, এল জি, অলিম্পাস, পাইওনিয়ার– এসব কোম্পানির দক্ষিণ–পূর্ব এশীয় হাব এখন ভিয়েতনামে। এখন ভিয়েতনামে প্রতি বছর বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ দাঁড়াচ্ছে ২০–২৫ বিলিয়ন ডলার। ভিয়েতনামের ব্যাংকিং ব্যবস্থা এখনো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রয়ে গেছে, কিন্তু ব্যাংকঋণে উদ্যোক্তাদের অভিগম্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে সহজ ও বহুলবিস্তৃত করা হয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক গতিশীলতার পেছনের চাবিকাঠি হলো ভিয়েতনামে দুর্নীতির প্রকোপ অনেক কম, ভিয়েতনামের শ্রমশক্তি ও মানবপুঁজি বাংলাদেশের চাইতে অনেক শিক্ষিত, দক্ষ এবং পরিশ্রমী। ভিয়েতনামের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন চমকপ্রদ। বন্দর, মহাসড়ক ও সুলভ গণপরিবহনের ক্ষেত্রে ভিয়েতনাম দ্রুত আধুনিকায়নে সফল একটি দেশ। তৈরী পোশাক রপ্তানিতে ভিয়েতনাম এখন বাংলাদেশকে হটিয়ে মাঝে মাঝে গণচীনের পর বিশ্বের দ্বিতীয় অবস্থানটি দখল করে নিচ্ছে। ইলেকট্রনিকস পণ্য রপ্তানিতে এখন সিঙ্গাপুরের পর ভিয়েতনাম দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ায় দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে। চাল রপ্তানিতে থাইল্যান্ডকে হটিয়ে ভিয়েতনাম ভারতের পর বিশ্বের দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে। ব্রাজিলের পর কফি রপ্তানিতে ভিয়েতনাম বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। সাড়ে নয় কোটি জনসংখ্যার দেশ ভিয়েতনামের মোট রপ্তানি আয় বাংলাদেশের চাইতে কয়েকগুণ বেশি। ২০২৪ সালে ভিয়েতনামের রপ্তানি আয় ছিল ৪০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে গণচীনের চলমান বাণিজ্য যুদ্ধের কারণে গণচীনে উৎপাদনরত অনেক শিল্পকারখানা এখন ভিয়েতনামে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। ভিয়েতনাম থেকে রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শিক্ষা নিতে পারে প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয়টিতে। উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমজীবী জনগণের ক্ষমতায়ন এবং গ্রাম–সমবায়ের ক্ষেত্রেও ভিয়েতনাম বাংলাদেশকে পথ দেখাতে পারে। সোভিয়েত স্টাইলের সমাজতন্ত্রকে যে যুগোপযোগী সংস্কার করতেই হবে, এটা বুঝে নিয়েই ভিয়েতনাম ‘দোই মোই’ সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। ‘মুক্ত বাজার অর্থনীতির’ অহিফেনের মৌতাতে বুঁদ না হয়েও যে ‘একুশ শতকের সমাজতন্ত্রের’ মাধ্যমে অর্থনৈতিক ‘মিরাকল’ ঘটানো সম্ভব, সেটারই অকাট্য প্রমাণ ভিয়েতনাম। ভিয়েতনামের একদলীয় শাসন আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই সমাজতান্ত্রিক মডেল থেকে বাংলাদেশের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। বিশেষত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, আয়বৈষম্য নিরসন ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে কীভাবে ভিয়েতনাম অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে তা গভীরভাবে বিবেচনা করা সমীচীন মনে করি।
দক্ষিণ ভারতের ছোট্ট রাজ্য কেরালা। মাথাপিছু জিডিপি বেশি না হলেও যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতের মত একটি নিম্নআয়ের দেশেও ঈর্ষণীয় জীবনযাপন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়্ত কেরালার জনগণ তৃতীয় বিশ্বে তার সফলতম নজির সৃষ্টি করেছেন। ন্যায়বিচার সমুন্নতকারী প্রবৃদ্ধি (equitable growth) মডেলের এক অনন্য নজির কেরালা। আয় ও সম্পদবৈষম্যকে নিয়ন্ত্রণে রেখে জনগণের মাথাপিছু জিডিপি’র প্রবৃদ্ধিকে দ্রুত বাড়িয়ে চলেছে রাজ্যটি। ১৯৬৯ সালে কেরালার কম্যুনিস্ট–নেতৃত্বাধীন সরকার ‘লাঙল যার জমি তার’ নীতির ভিত্তিতে ভূমি মালিকানার ব্যাপক পুনর্বন্টনের লক্ষ্যাভিমুখী কৃষি সংস্কার আইন পাশ করে, যার প্রধান পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ছিল: ১) কোন পরিবারকে আট হেক্টরের বেশি জমির মালিকানা রাখতে না দেওয়া, ২) ভাগচাষি (tenant farmer) ও বর্গাদার কৃষকদেরকে তাদের চাষকৃত জমির কার্যকর মালিকে (virtual owners) পরিণত করা, ৩) মধ্যস্বত্বভোগীদেরকে উৎখাত, ৪) কৃষিজোতের একত্রিকরণ, এবং ৫) তৃণমূল জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারের কৃষি সংস্কারের কর্মসূচিতে সম্পৃক্তকরণের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ (mass mobilization)। কেরালার কৃষি সংস্কারমালা খেতমজুরদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নে এবং গ্রামীণ শ্রমজীবী জনগণের সংগঠন জোরদারকরণে অনেক বেশি শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পেরেছে, যার ফলে তৃণমূল গণতন্ত্র ও ‘কল্যাণ অর্থনীতি’ প্রতিষ্ঠায় কেরালা মডেল অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১০ সালে লন্ডনের খ্যাতিমান প্রকাশনা সংস্থা পিয়ারসন থেকে প্রকাশিত আমার ও নিতাই নাগের রচিত গবেষণা–গ্রন্থ ইকনমিক ইন্টিগ্রেশন ইন সাউথ এশিয়া: ইস্যুজ এন্ড পাথওয়েজে আমি নিচের পরিবর্তনগুলোকে কেরালা মডেলের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হিসেবে প্রশংসা করেছি: ১) কার্যকর ও কম দুর্নীতিপূর্ণ রেশন ব্যবস্থা ও ফিডিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে ভর্তুকি–দামে নিম্ন–আয়ের পরিবারগুলোর মধ্যে চাল–বিতরণ. ২) খেতমজুরদের কর্মসংস্থানের নিরাপত্তাবিধান এবং নিম্নতম মজুরি আইন বাস্তবায়ন, ৩) অবসরপ্রাপ্ত ও বর্ষীয়ান কৃষিশ্রমিকদের জন্যে পেনশন চালু, ৪) দলিতশ্রেণীর জনগোষ্ঠীসমূহের জন্যে বর্ধিত সরকারী চাকুরি, ৫) বর্গাদারদের ভূমিস্বত্বের নিরাপত্তা (security of tenure) জোরদারকরণ এবং জবরদস্তিমূলক উচ্ছেদের আশংকা নিরসন, ৬) গ্রামীণ ভিটেমাটিতে বসবাসরতদেরকে দখলিস্বত্ব প্রদান, ৭) ভূমিহীন পরিবারগুলোকে বসতবাটি নির্মাণের জন্যে প্লট প্রদান, ৮) কৃষিশ্রমিকদের দৈনিক সর্বোচ্চ কর্মঘন্টা নির্ধারণ এবং তাদের জন্যে সামাজিক নিরাপত্তা স্কিম চালু, ৯) গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্যসুবিধা বৃদ্ধির জন্যে সরকারী ক্লিনিক ও হাসপাতাল নেটওয়ার্কের ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং ১০) অনুপস্থিত ভূমি মালিকানা উৎসাদন। কেরালার কৃষি সংস্কার, শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা, তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের অংশগ্রহণমূলক সংগঠন ও রাজনৈতিক সচেতনতা, বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং প্রগতিশীল ও পরমতসহিষ্ণু রাজনৈতিক সংস্কৃতি অমর্ত্য সেনের বিচারে উন্নয়নের সবচেয়ে অনুকরণীয় মডেল উপহার দিয়েছে বিশ্ববাসীকে। এই স্বীকৃতিকে কি মর্যাদা দেবে না বাংলাদেশের নীতি–প্রণেতারা?
লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ ও অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়