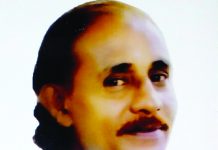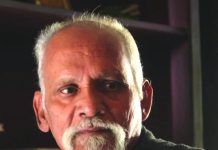দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রশাসিত বলয়ে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ছিল কালবৈশাখী ঝড়ের মতো। হাতে ছিল বিদ্রোহের নিশান, কণ্ঠে ছিল তারুণ্যের গান। এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে তাঁর পদার্পণ, যখন পুরো বিশ্বজুড়ে অবলুণ্ঠিত হচ্ছে সমস্ত মানবিক মূল্যবোধ। সর্বনাশা এক মহাযুদ্ধের কারণে দিকে দিকে কোটি কোটি লাশের কফিন। ভার্সাই সন্ধির ছুরিকাঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছিল তুরস্ক ও জার্মানির ভৌগোলিক সীমারেখা। আগ্রাসী মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি আর দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের চিৎকারে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল পুরো পৃথিবীর আকাশ–বাতাস। আর অধিকার বঞ্চিত মানুষের অধিকারের দাবি নিয়ে নজরুল লিখলেন বিদ্রোহী কবিতা। ‘আমি এলাম, দেখলাম এবং জয় করলাম’ জুলিয়াস সিজার কথিত এ প্রবাদ বাক্যটির সাথে তুলনা চলে বাংলা সাহিত্যে নজরুলের উপস্থিতিকে।
বাংলা সাহিত্যে মানবজাতির শক্তি, গতি ও জয়াশা প্রথম উচ্চকিত হয়েছে তাঁর কবিতায় ও গদ্যে এবং প্রবন্ধে। তাঁর মানুষ বড় ও মহীয়ান। সকল জাতের, সকল ধর্মের, সকল বর্ণের মানুষ – যেখানে কোনো বিশেষ ধর্ম বা জাত বা সামপ্রদায়িক সংকীর্ণতা দিয়ে মনুষ্যত্বকে আড়ষ্ট করা যায় না। তাঁর দৃষ্টিতে দেশ শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয় বরং দেশের মানুষের সুখ, দুঃখ এবং সমস্ত অত্যাচার, নিপীড়ন, ধর্মান্ধতা, সংকীর্ণতা তথা সব মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রাম – যা তিনি লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।
নজরুলের নতুন বিদ্রোহ চেতনায় এসেছে নারী এক অনন্য সাধারণ ভূমিকায়। যেখানে নারী সত্তার স্বীকৃতির চারিত্র্য আলাদা। সমঅধিকার ভিত্তিক নারী একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে–সেটি ছিল তাঁর দাবি। তাঁর বিখ্যাত বিদ্রোহী কবিতায় বিদ্রোহের বাণীর সাথে সাথে নারীর সৌন্দর্য – মহিমা সৃষ্টি করেছেন। একই সাথে নারী অতি মানবীয় সত্তায় আবৃত নয়, বরং সমঅধিকারের আসনে আসীন। স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কারের যক্ষপূরীর বন্দিনী নারীকে দাসত্বের সকল চিহ্ন ফেলে মুক্তির মন্ত্রে ডাক দিয়েছেন।
নারী কবিতায় নজরুল লিখেছেন -‘সাম্যের গান গাই/ আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।’ রুশ বিপ্লবের আগল–ভাঙা ঢেউয়ের কথা তিনি জেনেছিলেন যেখানে শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্বে নারী মুক্তি সম্ভব হয়েছে। সমাজতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে নারীর সমানাধিকার– এটি যাতে আনুষ্ঠানিক না হয়ে বাস্তবে প্রতিফলিত হয়, তার জন্য সেরূপ আইন – কানুন তৈরি হয়েছিল। নারী শুধু দেশের কাজে যুক্ত হবে না – কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল যাতে গৃহস্থালি কাজে নারীর শ্রম লাঘব করা সম্ভব হয়। স্তালিন বলেছিলেন – ‘নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া মানবজাতির ইতিহাসে কোনরকম আন্দোলন সফল হয়নি’। এই কথারই প্রতিধ্বনি নজরুলের কবিতায়– ‘কোনকালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারি / প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়ী লক্ষী নারী’।
নজরুল কাব্যে কঠোর কোমলের যে বৈপরীত্য – সে বৈপরীত্যে তার সৃষ্ট নারী অনন্য। কোথাও সে মনো– রাজ্যের একক রানি, কোথাও বিরহ– বিধুরা– প্রিয়া, কোথাও সমাজ বধূ, কোথাও কুমারী, কোথাও মমতাময়ী মা। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নারী চরিত্র–চিত্রণে দার্শনিক তত্ত্বের ভারে বা স্তরের বাহুল্যে নারীর প্রকৃত স্বরূপ চাপা পড়েনি। তাতে যে চিত্রকল্প এবং দার্শনিক মতবাদ এসেছে, তা নারীর সৌন্দর্য, ত্যাগ ও প্রেমকে মহিমাই দান করেছে।
লেখক : প্রাবন্ধিক; সাবেক অধ্যক্ষ, আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ।