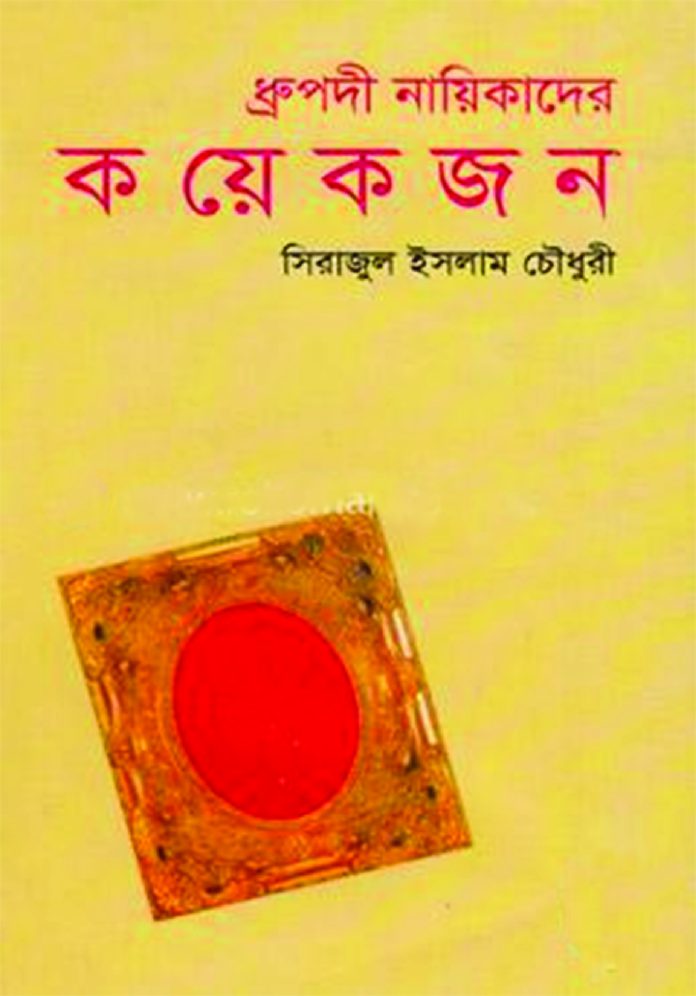সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (জন্ম: ২৩ জুন, ১৯৩৬)বাংলাদেশের প্রখ্যাত লেখক, প্রাবন্ধিক এবং শিক্ষক। তাঁর অনন্যসাধারণ বই “ধ্রুপদী নায়িকাদের কয়েকজন “( প্রথম প্রকাশ ২০০২ সালে, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা)
বিশ্বসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কিছু নারী চরিত্রকে ঘিরে এক গভীর আলোচনা তুলে ধরেছে। এই নায়িকারা তাঁদের সময়ের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তবে তাঁদের সৃষ্টি করেছেন পুরুষ লেখকেরাই। লেখকের মতে, পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের কারণে নারীরা নিজের গল্প বলার সুযোগ পাননি।
বইটি হোমারের হেলেন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নায়িকাদের আলোচনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। হেস্টার প্রিন, এমা বোভারি, আনা কারেনিনা এবং নোরা–এই চারজন ঊনিশ শতকের নায়িকা, যাঁরা প্রত্যক্ষ বা নীরবভাবে পিতৃতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন।
হেলেন ও পেনেলোপের গল্প
হোমারের ইলিয়াড মহাকাব্যে হেলেনকে ধ্বংসের কারণ হিসেবে দেখা হলেও, যুদ্ধের মূল দায় আসলে প্যারিস ও দেব–দেবীদের উপর। হেলেন কেবল একটি অজুহাত ও শিকার। অডিসিতে তাঁর মাতৃত্বের দিকটি কিছুটা দেখানো হলেও মূল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি নন। ইউরিপিদিসের নাটক হেলেন–এ তিনি একজন গৃহহীন নারী, যিনি তাঁর স্বামী ও কন্যাকে ফিরে পেতে আকুল। এই নাটকে তিনি জয়ী হলেও, মেনেলাউস হেলেনের বুদ্ধিমত্তার সমান নয়। হেলেন ছিলেন জিউসের কন্যা, তবে জিউস কখনও তার দায় স্বীকার করেননি–কারণ হেলেন ছিল কেবল তার কামনার ফল।
অন্যদিকে, অডিসিতে পেনেলোপ তার সতীত্ব বজায় রেখে রাজ্য পরিচালনা করেছেন বিশ বছর, কিন্তু তবুও তিনি কেবল একজন ‘অপেক্ষারত নারী’ হিসেবেই রয়ে যান। হোমার নারীর চেয়ে পুরুষের বীরত্বকেই গুরুত্ব দেন।
সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও দ্রৌপদীর অপমান
বাল্মীকির রামায়ণ–এ রাম রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সীতাকে উদ্ধার করেন, কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর সতীত্ব নিয়ে সন্দেহ করেন এবং অগ্নিপরীক্ষা দিতে বাধ্য করেন। এমনকি অগ্নিপরীক্ষার পরেও সীতাকে গ্রহণ করেন না রাম। মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ঘটে তাঁর স্বামী যুধিষ্ঠিরের ভুলে। দ্রৌপদীকে সম্পত্তির মত ব্যবহার করা হয়, তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। নারীকে মাতৃত্বের যন্ত্র হিসেবে দেখা হয়, কিন্তু পুরুষদের কেউ বিচার করে না।
দিদো ও শকুন্তলার বঞ্চনা
ভার্জিলের এনিড–এ দিদো নারী হওয়ায় কখনোই নায়িকা হয়ে উঠতে পারেন না। স্বামী হারিয়ে তিনি একাকী, শোকস্তব্ধ। মহাভারতে শকুন্তলা তাঁর স্বামী দুষ্যন্তের কাছে সন্তানসহ অধিকার দাবি করতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। একটি স্বর্গীয় বার্তা না এলে তাঁর পরিচয় কী হতো?
ইভ ও নারীর স্বাধীনতা
ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, ইভকে মানবজাতির প্রথম পাপের জন্য দায়ী করা হয়। কিন্তু ঈশ্বর তো সর্বজ্ঞ তিনি ইভকে ক্ষমা করতে পারতেন না? প্যারাডাইস লস্ট–এ মিলটনের দৃষ্টিভঙ্গি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিচ্ছবি–এখানে আদমও ভুল করেন, কিন্তু দোষ পড়েছে ইভের কাঁধে।
ঊনিশ শতকের নায়িকারা: নীরব বিদ্রোহ
দ্য স্কারলেট লেটার–এর হেস্টার প্রিন, ব্যভিচারের অভিযোগে সমাজচ্যুত হলেও তাঁর সন্তানের পিতার পরিচয় প্রকাশ করেন না। তিনি নিঃশব্দে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেন, সমাজের বঞ্চিতদের সেবা করে।
এমা বোভারি স্বাধীনতা খোঁজেন, কিন্তু পুরুষরা তাঁকে শুধু ব্যবহার করে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে এমন নারীরা সমাজে টিকে থাকতে পারেন না।
আনা কারেনিনা ভালোবাসার জন্য স্বামীকে ত্যাগ করেন, কিন্তু প্রেমিক ভ্রনস্কিও তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতা করে। সমাজ তাঁকে মা, স্ত্রী ও প্রেমিকার আলাদা আলাদা রূপে ভাগ করে ফেলে। তাঁর মৃত্যু নিঃসন্দেহে তৎকালীন জারতান্ত্রিক সমাজের এক ব্যর্থতার প্রতীক।
আ ডল’স হাউজ–এর নোরা এক রাতে নিজের স্বামীকে ছেড়ে চলে যায়, কারণ স্বামী তাঁকে মানুষ হিসেবে সম্মান করেন না। তাঁর এই বিদ্রোহ পুরো পুঁজিবাদী সমাজের বিরুদ্ধে।
রবীন্দ্রনাথের নারীরা
রবীন্দ্রনাথের লেখায় পুরুষের আধিপত্য স্পষ্ট। পুরুষরাও আসলে স্বাধীন ছিলেন না, কারণ তাঁরা ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন। তারা নিজেদের দুঃখ ঢেকে নারীদের দমন করত।
নষ্টনীড়–এ চরুলতার কোনো লেখা ছাপা হয় না, কেবল পুরুষদের লেখা প্রশংসিত হয়। স্ত্রীর পত্র–এ মৃণাল তাঁর স্বামীকে চিঠি লিখে সংসার ছাড়েন। কিন্তু প্রশ্ন থাকে–যদি তাঁর সন্তান থাকত, তবে কি তিনি যেতে পারতেন?
চতুরঙ্গ–এর নানিবালা স্বামীকে ছেড়ে আত্মহত্যা করেন–এ যেন এক চূড়ান্ত প্রতিবাদ। শেষের কবিতা–এ অমিত মনে করেন তিনিই জিতেছেন, কিন্তু আসলে পরাজিত তিনিই। যোগাযোগ–এ কুমুকে বন্দি করে রাখে তাঁর স্বামী, কিন্তু কুমুর নীরবতা এক প্রতীকী প্রতিবাদ। দ্বিপত্রিকায় স্বামী–স্ত্রী দুজনেই লেখেন, কিন্তু শুধু স্ত্রীর গল্প প্রকাশিত হয়।
উপসংহারে এটা বলা যায় যে, এক হাজার বছর আগে কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে সম্পত্তি ও বিয়ের ধারণা তৈরি হয় এর আগে নারীরা কারোর অধীনে ছিল না। গ্রিক পুরাণে নারীদের যৌনদাসী হিসেবে দেখা হয়েছে। সমাজ নারীকে ‘পবিত্র’ ও ‘অপবিত্র’–এই দ্বৈত মানদণ্ডে পরিমাপ করেছে। এইভাবেই পুঁজিবাদ পিতৃতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করেছে। আজও নারীরা শ্রেণিকক্ষে বা কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা ও বৈষম্যের শিকার হন। নারীদের ওপর আরোপিত ‘পবিত্রতা’র ধারণা তাদের মনস্তত্ত্বে গভীর প্রভাব ফেলে। ফলত, সমাজের অগ্রগতিও বাধাগ্রস্ত হয়।
পিতৃতন্ত্র এক ধরনের ‘সহানুভূতি’র মাধ্যমে নারীদের শাসন করে। ফলে নারীরাও নারীদের শোষণ করে। সভ্যতার শুরু থেকেই দ্বন্দ্ব আছে এবং থাকবে। সমতা নয়, বরং ন্যায়ভিত্তিক সম্পর্ক তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।