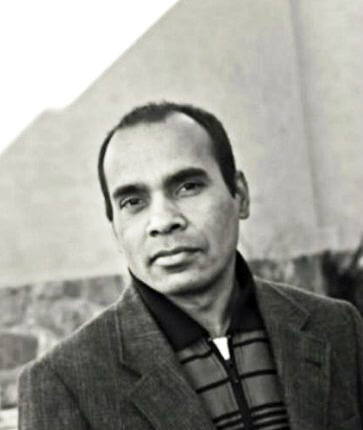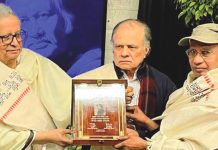দেশে দেশে প্রান্ত থেকে উঠে এসে অনেকে লেখালেখিতে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছেন। এরকম অনেক নজির রয়েছে আমাদের দেশেও। একইভাবে অনেক প্রান্তিক জনপদও বই এবং বইয়ের পেছনের মানুষদের ধারণ করে সাহিত্যের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করেছে। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় জগতের নানা প্রান্তে। এই প্রসঙ্গগুলো নিয়ে আমি কিছু কথা বলতে চাই।
নরওয়ের ধ্রুপদী লেখক নুট হামসুন ছিলেন আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক প্রজন্মের একজন তুমুল জনপ্রিয় এবং লেখালেখির আন্তর্জাতিক জগতে বহুল পরিচিত। হামসুনের জন্ম ১৮৫৯ সালে আর রবীন্দ্রনাথের ১৮৬১ সালে। হামসুন ১৯২০ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।
কেমন ছিল হামসুনের জন্ম ও বেড়ে উঠার কাল, শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্য? হামসুনের জন্ম চরমতম দরিদ্র পরিবারে নরওয়ের রাজধানী অসলো থেকে প্রায় দুইশ মাইল দূরবর্তী জনপদ লোমে। হামসুনের তিন বছর বয়সে দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিমজ্জিত তাদের পরিবার অসলো থেকে প্রায় সহস্র মাইল উত্তরের জনপদ হমস্ট্রয়ে তার এক চাচার জমিনের মজুর হিসেবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশে পাড়ি জমান।
নয় বছর বয়সে হামসুনকে তার নিজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরেক চাচার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় তার চাচা পরিচালিত ডাকঘরের কাজে সাহায্য করার জন্যে। এখানে তিনি চাচার হাতে নির্যাতন এবং নিগ্রহের শিকার হন। তাকে অনাহারেও কাটাতে হয়। তার চাচার নির্যাতনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় এক পর্যায়ে আতঙ্কতাড়িত নাজুক আচরণের প্রকাশ ঘটে তার মাঝে। এই অবস্থায় পনের বছর বয়সে তার চাচার আশ্রয় থেকে হামসুন পালিয়ে বাঁচেন।
এর পরের পাঁচ বছর হামসুন নির্ধারিত কোনো কাজে যোগ না দিয়ে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে টাকার বিনিময়ে যখন যে কাজ পেয়েছেন তাই করেছেন। কখনো দোকানের গোমস্তা বা কেরানি, কখনো শিক্ষানবিশ মুচি, কখনো কুলি, কখনো রান্নার সহযোগী কখনো বা প্রাকপাঠশালার শিক্ষক।
সতেরো বছর বয়সে দড়িশিল্পীর কাছে শিক্ষানবিশি হিসেবে কাজ শুরু করেন। এই সময়েই তিনি লেখালেখিও শুরু করেন। একই সময়ে তিনি নরওয়ের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ইরেসমাস জালের সঙ্গে পরিচয় হয়। হাঁসুন ইরেসমাসকে লেখালেখি চালিয়ে যাবার প্রয়োজনে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দেবার অনুরোধ করেন। ইরেসমোস এই অনুরোধে সাড়া দেন। লেখালেখিতে সফল হতে থাকেন হামসুন। তিনি আন্তর্জাতিক সাহিত্য পরিমণ্ডলে এক কিংবদন্তি হিসেবে জায়গা করে নেন। তার একাধিক উপন্যাসে ইরেসমাসের আদলে মূল চরিত্র নির্মাণ করেছেন হামসুন। এই হামসুন একসময় দেশটির রাজধানী অসলোতে রাত যাপন করেছেন পথে প্রান্তরে যাত্রী ছাউনিতে অনাহারে এমন ঘটনাও ঘটেছে প্রথম জীবনে। টিকে গেছেন অদম্য স্পৃহা আর প্রত্যয়ের জোরে।
হামসুনের গল্পই লেখালেখি জগতের প্রান্ত থেকে ওঠে আসা কেন্দ্রের শীর্ষ কোনো প্রতিভার প্রথম ও শেষ গল্প নয়। এরকম গল্প পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও আছে। আমরা লালন ফকির, কাজী নজরুল ইসলাম বা সুবোধ ঘোষের নাম উল্লেখ করতে পারি। লালন এবং নজরুলের প্রান্তরের জীবন ও জীবিকা ঘিরে গল্পগুলো আমাদের অজানা নয়।
হামসুনের গল্পই লেখালেখির দুনিয়ায় জমিন থেকে উঠে আসা লেখকজীবনের প্রথম ও শেষ গল্প নয়। এরকম গল্প পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও আছে। এমনকি আমাদের ভূমিতেও আছে। আমরা লালন ফকির, কাজী নজরুল ইসলাম বা সুবোধ ঘোষের নাম উল্লেখ করতে পারি। লালন এবং নজরুলের প্রান্তরের জীবন ও জীবিকা ঘিরে গল্পগুলো আমাদের অজানা নয়। সুবোধ ঘোষের লেখক হয়ে উঠার গল্পটা বলে নিতে চাই। সুবোধ ঘোষের জন্ম ঢাকার বিক্রমপুরের বহর গ্রামে ১৯০৯ সালে। তিনি পরলোকগমন করেন কলকাতায় ১৯৮০ সালে।
মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে হাজারিবাগ সেন্ট কলম্বাস কলেজে ভর্তি হয়েও অভাব অনটনের জন্য পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। জীবিকার তাগিদে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় তাকে। সংসারের ঘানি টানার প্রয়োজনে হেন কোনো কাজ নেই যা তিনি করেননি। পড়াশোনা ছেড়ে কলেরা মহামারী আকার নিলে বস্তিতে টিকা দেবার কাজ নেন। কর্মজীবন শুরু করেন বিহারের আদিবাসী অঞ্চলে বাসের কন্ডাক্টর হিসেবে। এরপর সার্কাসের ক্লাউন, বোম্বাই পৌরসভার চতুর্থ শ্রেণীর কাজ, চায়ের ব্যবসা, বেকারির ব্যবসা, মালগুদামের স্টোর কিপার ইত্যাদি কাজে তিনি তার প্রথম জীবনের অনেকটা অংশ ব্যয় করেন। বহু পথ ঘুরে ত্রিশ দশকের শেষে আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে সহকারী হিসেবে স্থিত হন। ১৯৪৬ সালে আগস্ট উত্তর দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালী থেকে তিনি গান্ধীজির সহচর থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন।
সুবোধ ঘোষের লেখালেখির শুরুটা কেমন ছিল? পেশায় বাসকন্ডাক্টর সুবোধ থাকেন কলকাতার বস্তিতে। রোববারের বিকেলের দিকে অনামিসঙ্গের নিয়মিত সাহিত্যে চক্রে যান। অন্য সকলে আলোচনা করে, নিজ নিজ লেখাজোকা পড়ে। সুবোধ চুপচাপ, কোনো কথা বলে না, কোনো লেখা পড়ে না। আদতে তিনি লেখেনও না। একবার সাহিত্যচক্রের বন্ধুরা শর্ত জুড়ে দিলেন এরপরের রোববারে এখানে আসলে তোমাকে অবশ্যই কোনো লেখা নিয়ে আসতে হবে। তা না হলে তুমি এখানে আসতে পারবে না। কী আর করার। পরের রোববারের সকালে ছুটির দিনে বস্তির ঘরের মেঝেতে বসে লিখে ফেললেন দুটি গল্প অযান্ত্রিক আর ফসিল। গল্প দুটো সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন সাহিত্যচক্রের আড্ডায়। বন্ধুরা ধরে বসলো, সুবোধ তুমি আবারো কেন এলে? তোমাকে তো বলেছি কোনো লেখা না নিয়ে এলে তুমি এখানে আসতে পারবে না। সবার ধারণা ছিল বাসকন্ডাক্টর সুবোধ কি আর লিখতে পারবে? কিন্তু সত্য ছিল ভিন্ন। সুবোধ গল্প দুটো পড়লেন। এরপর হলো ইতিহাস। এই গল্প থেকে নির্মিত হয়েছে বিখ্যাত ছায়াছবি। তার লেখাজোকা অনূদিত হয়েছে ভারতবষের্র বিবিধ ভাষায়, নির্মিত হয়েছে ছবি বহুভাষায়। তিনি লিখেছেন গোটা তিরিশেক উপন্যাস, প্রায় আড়াইশর মতো ছোটগল্প, লিখেছেন প্রবন্ধ এবং কবিতা।
সোনার চামচ মুখে দিয়ে আর যাই হোক বহুস্তর জীবনের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ আর হয়ে ওঠে না। আবার পণ্ডিতবুজুর্গ হয়েও লেখাজোকায় খুব যে একটা তল খুঁজে পাওয়া যায় না সেরকম উদাহরণও অঢেল।
এবার আয়ারল্যান্ডের এক লেখকের গল্প বলি। লেখকের নাম ডারমোট বোলজের। ডারমোটের জন্ম ডাবলিন শহরের বাইরে ফিনগ্লাস নামক একটি পশ্চাদপদ প্রায় বস্তি এলাকায় ১৯৫৯ সালে। ফিনগ্লাস এলাকাটি এতটাই ও পিছিয়ে পড়া এবং নিগৃহীত ওখান থেকে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাবার কথা কল্পনাও করতে পারতো না। ডারমোট স্কুলে পড়ার সময় কবিতা লেখা শুরু করেন। সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় তার এক সহপাঠী তার খাতায় কবিতা দেখে তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলো এই বলে, ‘ডারমোট, তুমি কবিতা লেখো কেন? ফিনগ্লাস থেকে কেউ কবি হতে পারবে না। কেননা কবি হতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে। ফিনগ্লাস থেকে কেউ তো আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারবে না। আর কবি হতে হলে তো বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে। ফিনগ্লাস থেকে সর্বোচ্চ একজন সৈনিক হবার কথা ভাবতে পারো।’
এই কথা শুনে ডারমোটের মন খারাপ। ভাবতেছে সৈনিক হয়ে তাঁকেও শিখতে হবে কিভাবে মানুষ মারতে হয়। তিনি কবিতা লেখা ছেড়ে দেননি। ভেবেছেন কবি হতে পারবে না তাতে কি, কবিতা তিনি লিখেই যাবেন। একদিন তার ইংরেজি শিক্ষক কবিতা দেখে বলছেন, ‘ডারমোট, তুমি তো কবি।’
ডারমোটের উত্তর, ‘স্যার, আমি কবি না, কবি হতেও পারবো না। কারণ কবি হতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয়। ফিনগ্লাস থেকে তো কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারবে না। আমিও পারবো না। তাই আমিও কবি হতে পারবো না। শিক্ষক বললেন, ‘শুনো, কবি হবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে না। কবি হবার জন্যে দরকার তিনটি জিনিস: কাগজ, কলম আর কল্পনার স্বাধীনতা।’ সেই ডারমোটের গল্প উপন্যাস নাটক কবিতা অনূদিত হয়েছে পৃথিবীর বহু ভাষায়। তার নাটক প্রযোজিত হয়েছে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে।
লেখক হবার জন্যে যেকোনো অভিজ্ঞতাই একটা সুযোগ। এমন কি জেলখানাও লেখকের জন্যে একটা সৌভাগ্য। প্রান্তিক জনপদ বা ছোট শহর একজন জাত এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ লেখকের জন্যে একটা সুযোগ বটে। আর ওই জনপদের জন্যে লেখক আখরে এক ভূমিদূত। তার নিজ জনপদ তাঁকে চিরন্তন আগলে রাখবে আপনার করে। তাই বলে বড় শহরের অভিজ্ঞতাকে বাতিল করে দিচ্ছি না। আদতে লেখক নিবেন জীবনের অভিজ্ঞতা শহর ছোট হোক আর বড় হোক। বড় শহরে বুদ্ধিবৃত্তিক অভিজ্ঞতা বা চর্চা অনেক ক্ষেত্রে কৃত্রিম ঝাড়িঝুড়ি আর প্রহসনে ঘেরা। গণমাধ্যম আর প্রতিষ্ঠানের স্বার্থসিন্ডিকেটের কাছে একজন জাতলেখক অনেকক্ষত্রে নিগ্রহের শিকার হন অথবা উপেক্ষিত হয়ে থাকেন। এরকম উদাহরণ আমাদের ঢাকা শহরে যেমন আছে, তেমন পৃথিবীর তাবৎ বড় শহরে।
এই পর্যায়ে একটা ঘটনা বলি।
একবার গণমানুষের লেখক আর অভিজাত সাহিত্য নিয়ে ইউরোপের একটি কাগজে সমপ্রতি আমি একটি বিতর্কমূলক প্রবন্ধ ছাপিয়েছিলাম। ওই প্রবন্ধ পড়ে আমার বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করে সুইডিশ কবি ক্রিস্টার গুস্তাবসন আমাকে একটি মেইল করেছিলেন। মেইলটির একজায়গায় প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, একবার ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় একটি কাগজের সাহিত্য সম্পাদক একদা তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, ‘তারা একজন অপরিচিত লেখকের ভালো বইয়ের আলোচনা নাও ছাপতে পারেন। কিন্তু একজন প্রতিষ্ঠিত লেখকের খারাপ বইয়ের আলোচনা ছাপাবেন ঠিক ঠিক। ‘ এই কটূসত্যটা প্রায় বড় শহরের সাহিত্যের মোড়লিপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমাদের ঢাকা শহরের সাহিত্যপাতার সম্পাদকদের কয়জন এই দুষ্ট দোষ থেকে মুক্ত?
গূঢ় সত্য হল লেখালেখির আদিকাল থেকেই অন্যবিধ পেশার মানুষের মতোই লেখকরা খ্যাতি ও যশের মোহে প্রান্ত গ্রাম থেকে শহরে ছোটেন। কেউ কেউ আবার প্রান্তিক জনপদে স্থিত হবার প্রত্যয় গ্রহণ করেন। এরকম উদাহরণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ভুরি ভুরি থাকলেও আমাদের দেশে কম। এখানে সদ্য বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক হোসেন উদ্দিন হোসেনের কথা বলা যায়। তিনি নিজ গ্রামে স্থিত হয়ে লেখালেখি চালিয়ে গেলেন। এরকম উদাহরণ আরো বেশি থাকলে আমাদের দেশে লেখালেখি জগতের কেন্দ্র ও প্রান্তের একটা দৃষ্টিনন্দন ভারসাম্য খেয়াল করা যেত।
এখানে ভিন্ন কয়েকটি উদাহরণ দিতে চাই। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে ওয়েলসের জাতীয় কবি ইফোর এপ গ্লিন এর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়েছিল আমার। ইফোর জাতে ওয়েলশ হলেও বাবার কর্মূসূত্রে তাদের পরিবার বিলেতে স্থিত এবং ইফোরের জন্ম বিলেতে। ইফোর নিজ ভাষায় লেখালেখি করবেন বলে ফিরে গিয়েছেন মাটিঘেঁষা মূলে প্রান্তিক জনপদে। তিনি সরকারি ভাতা লাভকারী জাতীয় কবি হয়েও থাকেন রাজধানী কার্ডিফ থেকে প্রায় দুইশ মাইল উত্তরের এক গ্রামীণ জনপদে।
নোবেল পুরস্কার জয়ী সুইডিশ কবি টমাস ট্রান্সট্রয়মার প্রায় চার দশক থেকেছেন স্টকহোম থেকে প্রায় দুইশ কিলোমিটার পশ্চিমের এক প্রান্তিক শহর ভেস্তেরসে। এরকম হাজারো দৃষ্টান্ত দেশে দেশে।
এবার দেশের রাজধানী বা কবিতা বা সাহিত্যের রাজধানী বিষয়ে কথা বলতে চাই। দেশের রাজধানীই যে কবিতারও রাজধানী হবে,সেরকম নিশ্চয়তা নাই। ভারতের উদাহরণ দিয়েই শুরু করতে চাই। ভারতের সাহিত্যের রাজধানী বলতে কলকাতাকেই ধরে নিতে হবে। কলকাতা দেশটির ইউনেস্কো সাহিত্যনগরীও। কলকাতার শত শত বছরের লেখালেখির ঐতিহ্য সম্পর্কে আমরা কম বেশি প্রায় সকলেই জানি।
অসলো নরওয়ের রাজধানী হলেও, সাহিত্যের রাজধানী নিশ্চিত না। সাহিত্যের দৃষ্টকোণ থেকে দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বার্গেন তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে নিতান্তই ছোট এক জনপদ লিলেহামার দেশটির ইউনেস্কো সাহিত্যনগরী।
অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে নরউইচ এবং এডিনবার্গ ইউনেস্কো সাহিত্যনগরী, বিলেত নয়। এখানে আরো একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই। ওয়েলসের একটি ছোট জনপদ, নাম তার হে। যে গ্রামটির নামে ‘হে উৎসব’ আয়োজন করা হয় অন্যদেশেও। এই জনপদে লোকসংখ্যা দুইহাজার। এখানে বইয়ের দোকানের সংখ্যা কুড়ি। এই তথ্য থেকে আমরা লেখক পাঠকের ঘনত্ব সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে পারি।
আইসল্যান্ডের উদাহরণ দিতে চাই। দেশটি উত্তরমেরুতে অবস্থিত। তিন লক্ষ আঠাশ হাজার লোকসংখ্যার দেশটিতে প্রায় সবাই লেখক, সবাই পাঠক। দেশটির রাজধানী রেইকিভিক ইউনেস্কো সাহিত্যনগরীর মর্যাদায় অভিষিক্ত। অন্যদিকে মার্কিনমুল্লুকের আইওয়াকে মনে করা হয় সারা দুনিয়ার লেখকদের রাজধানী। আইওয়া বিশ্বের প্রথম ইউনেস্কো সাহিত্যনগরী। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ‘ছবির দেশে, কবিতার দেশে’ বইটিতে লেখকদের শহর আইওয়া সম্পর্কে বিশদ লিখেছেন। শুনে অনেকে অবাক হতে পারেন ২০১৫ সালে যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাগদাদ ইউনেস্কো সাহিত্যনগরীর মর্যাদায় উন্নীত হয়। এখানে বাগদাদের একটা অনন্য ঐতিহ্যের কথা বলতে চাই। এখানে ‘বই বাজার’ নামে একটা লেখকমেলা বা নিয়মিত হাট প্রচলিত রয়েছে। এই মেলায় দেশের লেখকরা নিজ নিজ বই নিয়ে হাজির হন এবং বিক্রি বা প্রদর্শন করেন।
সাহিত্যের রাজধানী বা গুরুত্বপূর্ণ নগর মানে যে জনপদে লেখক ও লেখালেখির প্রাণবন্ত কর্মযজ্ঞ, উপলক্ষ ও পার্বণ থাকবে অহরহ । এর জন্যে সেই জনপদকে অনেক বড় শহর হতে হবে বা রাজধানী হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাদকতা নাই। তবে এর নাটাইটা থাকতে হবে লেখকের হাতেই। পৃথিবীর কোনো দেশেই আমাদের দেশের মতো দৃষ্টিকটুরকম মন্ত্রী আর আমলাতোষণ সাহিত্যপরিমণ্ডল নাই।
বেশি কথা না বলি। অনেক সময় দেখা যায়, ঢাকা শহরে বই প্রকাশনা অনুষ্ঠানে একজন মন্ত্রী বা একজন জ্যেষ্ঠসচিবের নাম আমন্ত্রণপত্রে না থাকলে যেন ওই লেখক গুরুত্বের প্রত্যাশিত পর্যায়ে উঠতে পারেন না। প্রথম কথা হলো পৃথিবীর খুব কম ধ্রুপদী লেখকই তাদের বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠান করেন। আর করলেও নিতান্তই নিজের বন্ধু আর আত্মীয় পরিমণ্ডলের লোকজনদের দাওয়াত করেন একধরনের আড্ডা আয়োজনের মতো করে। সুন্দর দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেও ছিল। শামসুর রাহমানসহ আমাদের অনেক ধ্রুপদী কবি গোটাজীবনে তাদের নিজের বইয়ের কোনো প্রকাশনা অনুষ্ঠান করেননি।
আমাদের দেশের মতো কোনো দেশের মন্ত্রী আর আমলারা তাদের কর্মকালীন মেয়াদে নির্ধারিত প্রাসঙ্গিক কাজের বাইরের কোনো অনুষ্ঠানাদিতে অযাচিত সময় ব্যয় করেন আমার জানা নাই। একটি বইয়ের আলোচনায় একজন মন্ত্রী আর আমলাকে জড়াতে হবে কেন? আর একজন মন্ত্রী বা আমলার কাজের কি খুব অভাব? তাদের হাতে কি এতই সময়? পৃথিবীর আর কোনো দেশে আমাদের দেশের মন্ত্রী আমলার মতো নিজ কাজ বা দফতরের সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন?
নতুন আরেক উপদ্রব পড়ুক আর না পড়ুক এখন সবাই লেখক। যে কারণে এখন প্রকৃত একজন লেখককে তুলে আনার তেমন সুযোগ অবশিষ্ট নাই। যে কারণে পদধারী মানুষদের পদের ভারে আর চাপে রাষ্ট্রাচার ঢুকে গেছে কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত। কেন্দ্রে যেমন মন্ত্রীর পরে সচিব, প্রান্তে তেমন ডিসির পরে এডিসি, এডিসির পরে ইউএনও। একই রাষ্ট্রাচার ঢুকে গেছে সাহিত্যের আয়োজনগুলোতেও। এই প্রবণতায় আমরা লেখালেখির তাৎপর্য খুইয়ে বসেছি প্রায়। কেন্দ্র হারিয়েছে কেন্দ্রের কাছে, কেন্দ্রও আর লেখালেখি জগতের কেন্দ্রে নাই। কেন্দ্র থেকে প্রান্ত সব এখন আমলাতন্ত্রের দুয়ারে দুয়ারে। এর থেকে উত্তরণের পথ প্রান্ত থেকেই আসতে পারে। প্রান্তের লেখকদের দেমাক আর রেখে দাঁড়ানো প্রত্যয় থেকে। যে প্রত্যয়ে থাকবে লেখালেখির প্রতি জীবনপণ দায়বদ্ধতা। এই প্রত্যয়ে সূর্য সেন আর প্রীতিলতার চট্টলা হতে পারে লেখালেখির রাজধানী বা ইউনেস্কো সাহিত্যনগরী। মনোযোগটা চাই লেখালেখি ঘিরে দৃশ্যমান পরিকাঠামো যেমন পত্রপত্রিকা, গ্রন্থাগার, প্রকাশনা, উৎসব, সভা সেমিনার, পাঠচক্রসহ বহুবৈচিত্র্যময় লাগসই উদ্যোগ যেখানে সকল বয়সের, সকল দল পথ ও মতের মানুষের বহমাত্রিক বহুবৈচিত্র্যের প্রতি।
ক্ষমতার করিডোর বা আমলাতন্ত্র নিয়ে কথা আর না বলি। এই পর্যায়ে অন্য একটি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে চাই। একটি জায়গায় লেখালেখি ও রাজনীতির চমৎকার মিল। লেখালেখির মতন রাজনীতিতে গণমানুষের নেতা উঠে আসেন প্রান্ত থেকেই। তার উদাহরণ আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরো অনেকে, দেশে এবং বিদেশে।
চট্টগ্রাম আলোকসঞ্চারী হবে কেবল বন্দরনগরী বা বাণিজ্যের রাজধানী হিসেবে নয়, সাহিত্যনগরী হিসেবেও। চট্টলা নিয়ে আমার ভাবনা এমনই। বিপ্লবটা করতে হবে লেখকদেরই সূর্যসেন, প্রীতিলতা আর বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে !
লেখক : বাঙালি-সুইডিশ কবি এবং সুইডিশ রাইটার্স উনিয়নের পরিচালনা পরিষদের সদস্য