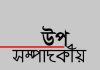নির্বাসনে অসম্বদ্ধ সংলাপ এবং যাযাবর
হপ্তাখানেক ধরে আমার অস্থায়ী ঠিকানা হয়েছে ঘরের ভেতর তেতলার একটি কামরায়। সেখানে এখন দিনের অনেকটা সময় কাটে। কখনো বিছানায় আঁধশোয়া অবস্থায় কাঁধ থেকে মাথার অংশটা দেয়ালে হেলান দিয়ে বই পড়া। ঘন্টার পর ঘন্টা। কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়লে পাশের কামরায় চেয়ার টেনে বসা। পাশের এই ছোট্ট কামরাটি আমার লেখালেখি আর পড়াশুনার। সেখানে আছে একটি টেবিল। তাতে দুটো ল্যাপটপ- একটি পুরানো, আর একটি সদ্য কেনা। পেছনে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে দুটো বুক-শেলফ। তাতে কিছু বই, ফাইল, সিডি, ছবির এলবাম, পুরানো ম্যাগাজিন ইত্যাদি। হাতের ডাইনে একটি সাইড বুক-সেলফ দেয়ালের সাথে সাঁটা। তাতে কয়েকটি ছবি ফটো-স্ট্যান্ডে। আর আছে এখন-ওখান থেকে পাওয়া প্রশংসাবাণী সম্বলিত কয়েকটি ক্রেস্ট। আছে পদ্মাসনে গৌতম বুদ্ধের একটি ছোট্ট পিতলের মূর্তি। পাশে একটি ফটো-ফ্রেম। তাতে বাঁধানো বাবার ১৭ বছর বয়সের একটি ছবি, সাথে তার বন্ধু, গোপাল কৃষ্ণ গোস্বামী, ১৯৩১ সালে তোলা, সবকিছু ছবির নিচে বাবার হাতে লেখা। বাবার বাংলা ইংরেজি হাতের লেখা ছিল দেখার মত, ঠিক আমার উল্টো। দুজনের পরনে ধূতি, শার্টের সাথে কোট, পায়ে সেন্ডেল, পোশাকের সাথে কেমন যেন একটু বেমানান। কিন্তু অতি সুন্দর ও আমার কাছে অতি মূল্যবান এই ছবি। পুলকিত, রোমাঞ্চিত হই ১৭ বছর বয়সে বাবা কেমন ছিলেন তা দেখতে। সুন্দর মুখশ্রী, মাথাভর্তি চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। পেছনে ঝুলানো পর্দা দেখে টের পেতে অসুবিধা হয়না যে ষ্টুডিওতে তোলা। বাঁয়ে হাতের বা-দিকে নিচ থেকে এঁকেবেঁকে উঠে আসা সিঁড়ি যেখানে এসে শেষ হয়েছে তার পাশে একটি স্টিলের আলমিরা। তাতে বেশ কিছু নতুন, এখনও প্যাকেট খোলা হয়নি শার্ট, পাঞ্জাবি-পায়জামা, আফটার শেভ ইত্যাদি উপহার সামগ্রী। এসব বছরের নানা উপলক্ষে নিকটজন, দূরের-জনদের কাছ থেকে পাওয়া। প্রাপ্তি যখন প্রয়োজনের চাইতে অতি মাত্রায় বেশি হয় তখন প্রাপ্ত-উপহার সামগ্রির এমন অবহেলায় পড়ে থাকবে সেটাই তো স্বাভাবিক। অথচ একটা সময় গেছে, যখন ইউনিভার্সিটি পড়তাম, মেজদার ইস্ত্রি করে রাখা শার্ট ‘চুরি করে’ গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে যেতাম। সে টের পেতনা। এই কর্মটি দুপুর বেলায় ঘটতো বেশী। কারণ তখন সে ইউনিভার্সিটি থেকে এসে দুপুরের বিশ্রাম নিতো। রাতে বাসায় যখন ফিরতাম তখন চতুষ্পায়া প্রাণীর সমগোত্রীয় বানিয়ে আমার উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি বাণী ছুঁড়ে দিতো। অপরাধী যখন তার কৃত-অপরাধ সম্পর্কে জ্ঞাত তখন নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ ভেবে কিছু না বলে অন্য কামরায় বা রান্না ঘরের দিকে চলে যেতাম। শার্ট সে সময় ছিল বড় জোর দু কী তিন খানা। এর বেশি নয়। অথচ বাবুগিরি করা চাই। এখন তো আলমারি পুরো নিজ দখলে। তাতে ঝুলে থাকা শার্ট, স্যুট, টাই প্যান্ট গুনতে সময় লেগে যাবে অনেক। সব যে নিজের কেনা তা নয়। ইউরোপে ‘ডে’ অর্থাৎ ‘দিবসের’ তো শেষ নেই। বার মাসে তের পাবনের মতো। বার্থ ডে, ম্যারেজ ডে, ফাদার্স ডে, ভ্যালেন্টাইন্স ডে, নিউ ইয়ার্স ডে, ফ্রেন্ডশীপ ডে। এর বাইরে আছে নিজ ধর্মীয় বিশ্বাসের না হলেও সেন্ট নিকোলাস ডে, ক্রিস্টমাস ডে। আছে বিয়ের এক-দুই-তিন দশক-পূর্তি উৎসব। আছে মাঝে মধ্যে ‘বেহুদা’ পার্টি, অর্থাৎ কোন ‘অকেশন’ ছাড়া ডাকা পার্টি, কিছু বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণ করা, খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন, আর আড্ডা দেয়া। বাঙালির আড্ডা মানে তো একে-ওকে নিয়ে আলোচনা, কিংবা বলা যেতে পারে সমালোচনা। তখনও প্রাপ্তিযোগ হয় উপহার সামগ্রির। উপহার আসে স্ত্রীর কাছ থেকে, শাশুড়ি থেকে, শ্যালিকার কাছ থেকে, এমন কী ছেলে-মেয়ের কাছ থেকেও। সবার আলাদা আলাদা দেয়া চাই। ফলে প্রাপ্তির-হার এতো বেশি যে তাতে প্রাপ্য-বস্তুর প্রতি সঠিক বিচার করা হয়না। অনেক সময় তা বছরের পর বছর পড়ে থাকে আলমারিতে, অনাদৃত হয়ে। যে স্টিল আলমিরার কথা বলছিলাম, তাতে আছে একটি বিশেষ প্যাকেট। মায়ের ব্যবহৃত একটি সাদা শাড়ি। মা যখন ২০১০ সালে চলে গেলেন, চিরদিনের তরে, তখন দেশ থেকে সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম মায়ের এই স্মৃতিটুকু। মা নেই। মাঝে-মধ্যে স্টিলের আলমিরাটি খুললে চোখে পড়ে। এখনও এই বয়সে কোন কষ্ট হলে, ব্যথা পেলে কোথায়ও- শরীরে কিংবা মনে- ‘মাগো’ বলে উঠি আপনাতে। বোধকরি আমরা সবাই।
ফিরে আসি আমার নির্বাসনে- শখের বশে এই নির্বাসন নয়। প্রায় বছর আড়াই তাকে ঘরের বাইরে ঠেঁকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু পারলাম না। শেষ রক্ষা হলোনা। আমাকেও পরম আদরে ধরলো ‘করোনা’। খুব কম পরিবার আছে যেখানে ‘করোনা’ হানা দেয়নি। কেড়ে নেয়নি কাছের জনকে। দেরিতে আসায় এবং ভ্যাকসিন, বুস্টারের কারণে আমার ক্ষেত্রে বোধকরি খুব একটা সুবিধে করে উঠতে পারেনি। এখন অনেকটা ভালোর দিকে। তবে দিন নেই রাত নেই- ঘরের দুটি কামরায় এক প্রকার বন্দী। সময় যেন যেতে চায়না। ভাগ্যিস হাতের কাছে বিনয় মুখোপাধ্যায় ছিলেন। তার সাথে, অর্থাৎ তার লেখার সাথে প্রথম পরিচয় যখন ঘটে তখন তার লেখার সবটুকু বুঝে উঠার মত বিদ্যে হয়নি। বাংলা চর্চা যাদের আছে বোধকরি তাদের সবাই না হলেও অনেকেই তার লেখা অন্ততঃ একটি বই পড়েছেন, নিদেনপক্ষে নাম শুনে থাকবেন, ‘দৃষ্টিপাত’। বিনয় মুখোপাধ্যায়ের নাম পরিচিত না হলেও ‘যাযাবর’ নামটি শোনেননি তেমন বাঙালি খুব একটা পাওয়া যাবেনা। ‘যাযাবর’ নামের আড়ালে বিনয় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন তার অপূর্ব লেখাগুলি।
১৯৫০ সালে ‘দৃষ্টিপাত’ সমকালীন বাংলা সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে এবং লেখক বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা নরসিংহ দাস পুরস্কার লাভ করেন। ‘দৃষ্টিপাত’ বিগত শতকের চল্লিশ দশকের দিল্লীর পটভূমিকায় লেখা। প্রকাশকাল ১৯৪৭।
এই কদিনে যাযাবরের লেখা যে চারটি বই পড়া হলো তা হলো: ‘দৃষ্টিপাত’, ‘জনান্তিক’, ‘ঝিলম নদীর তীর’ ও ‘লঘুকরণ’। এই কটি এবং ‘হ্রর্ষ ও দীর্ঘ’ ও ‘বৃষ্টি যখন নামল’ সব একসাথে যোগ করে বের হয়েছিল ‘যাযাবর অমনিবাস।’ ইংরেজি ‘অমনিবাস’ শব্দের বাংলা অর্থ ‘পূর্বে প্রকাশিত বইগুলির একত্রে প্রকাশিত গ্রন্থ’। তবে সাধারণ পাঠকের কাছে তিনি সবিশেষ পরিচিত ‘দৃষ্টিপাতের’ জন্যে। বেঁচেছিলেন মাত্র ৩৮ বছর। লিখেছেন ৬টি বই। তার লেখার এমন জাদু যে সেই ১৯৪৭ সালে লেখা বই, ‘দৃষ্টিপাত’ আজও প্রায় ৭৩ বছর পরও নেশা ধরায়। একবার শুরু করলে শেষ না করা পর্যন্ত যেন নিস্তার নেই। সাহিত্যিক অরুনকুমার মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন- ‘তাঁকে আমি কখনও দেখিনি, কিন্তু তার বই পড়েছি গত পঞ্চাশ বছর ধরে। যখনই হাতের কাছে পেয়েছি, পড়েছি। এর প্রধান কারণ সুখপাঠ্যতা, শেষ কারণ সুখপাঠ্যতা।’ যাযাবর স্বনামেও দুটি বই লেখেন। তা হলো, ‘খেলার রাজা ক্রিকেট’ ও ‘মজার খেলা ক্রিকেট’।
শুরুতে জন্মদিনে উপহারের কথার উল্লেখ করেছিলাম। জন্মদিন উপলক্ষেও যাযাবরের খুব মজার কথা আছে। ‘লঘুকরন’ নিবন্ধে জন্মদিন প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, “জগতে সমস্ত কিশোর-কিশোরীরই অন্তরের কামনা, জন্মদিনটা আরও ঘন ঘন আসুক। হায়, তারা তো কল্পনাও করতে পারেনা যে তাদের জীবনেই এমন এক সময় আসবে যখন প্রতিটি জন্মদিনের মধ্যেই থাকবে আসন্ন বার্ধক্যের ক্রমিক পদক্ষেপ। সেটা তখন যৌবনের ফেয়ারওয়েল পার্টি; জোড়ার ট্রাফিক সিগন্যাল। বয়স বাড়ছে এ অনুভূতি জীবনের পূর্বাহ্নে যেমনই আনন্দদায়ক, অপরাহ্নে তেমনি অপ্রীতিকর। দাদার চেয়ে অনেক বড় হওয়ার সাধ, বড় হয়ে বাবার মতো হলে- আপনিই উবে যায়।” তার লেখা পড়তে গিয়ে কোন কোন জায়গায় আপনাতে হেসেছি। ‘স্ত্রীষু’ নিবন্ধে তিনি লেখেন, “পত্নিমাত্রেরই ধমনীতে বয় একনায়কত্বের রক্ত। স্ত্রী হচ্ছেন সেই বস্তু যার অভাবে সংসার চলে না এবং উপস্থিতিতে সংসার অভাবে অচল হয়। যাকে পাওয়ার পূর্বে পুরুষেরা কবিতা পড়ে এবং পাওয়ার পর পড়ে গীতা। যাকে না পেয়ে খোঁজে পটাশিয়াম, সায়ানাইড বা লেক এবং পেয়ে সন্ধান করে গেরুয়া বা রুদ্রাক্ষ। বোধহয় তার সম্পর্কেই লেখা হয়েছে- যাহা চাই, তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।” আজকের দিনে আধুনিকারা যাযাবরকে পেলে যে একহাত দেখে নিতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এমন কী হয়তো তাকে অবাঞ্চিত ঘোষণা করে তার পুশকুত্তলিকা দাহ করতেন। নারী সম্পর্কে আর এক স্থানে তিনি লেখেন, ‘গণিতশাস্ত্রে শূন্যের নিজের কোন সত্তা নেই। তার মূল্য নির্ধারিত হয় পার্শ্বস্ত সংখ্যাটির গুরুত্বে। দশের চাইতে কুড়ির কদর বেশি। ষাটের চাইতে আশির ওজন অধিক। সমাজে নারীর মর্যাদা নিরূপিত হয় পিতা অথবা পতির গৌরবে। কবিরা যে নারীকে আকাশের চন্দ্রমার সঙ্গে তুলনা করেন সেটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কে না জানে যে, চাঁদের আলো তার নিজের নয়- সমস্তটাই পরস্ব।’ যাযাবর বেঁচে থাকলে হয়তো আজকের দিনে এই উপলদ্ধি থেকে সরে দাঁড়াতেন। হয়তো তুলনাটা ভিন্নভাবে সাজাতেন। দিন বদলেছে, বদলেছে নারী। তারা এখন আর ৭০ বছর আগের অবলা নেই। নারী এখন অনেক সবল। নারীরা এখন নিজ আলোয় আলোকিত হচ্ছেন, চাঁদের আলোর আর প্রয়োজন পড়ে না। ঘরে বাইরে সর্বত্র। বোধকরি এই সত্যটি উপলদ্ধি করেছেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি বলেছেন, ‘নারীকে দুর্বল শ্রেণি বলা মানহানিকর; এটি নারীর প্রতি পুরুষের অবিচার। শক্তি বলতে যদি নৈতিক-শক্তি বোঝানো হয়, তাহলে নারী পুরুষের চেয়ে অপরিমেয় শ্রেষ্ঠ।’
লেখক : সাহিত্যিক, কলামিস্ট