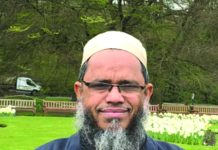গতরাত থেকে ভাবছিলাম এবারের কলামে কী নিয়ে লিখবো। আমার প্রতিদিনকার অনিয়মের নিয়ম হচ্ছে দেরিতে ‘ব্রেকফাস্ট‘ সারা। ব্রেকফাস্ট সারতে সারতে ডিনার টেবিলের উপর থাকা ল্যাপটপ খুলে দিনের কয়েকটা পত্রিকা পড়া। দেরিতে ব্রেকফাস্ট এই কারণে আমার প্রতিদিনের ‘ব্রেকস্লিপ‘ হয় অনেকটা দেরিতে। ‘ব্রেকস্লিপ‘ শব্দটি এর আগে আর কোথাও ব্যবহার হয়েছে কিনা জানা নেই। সে কারণে একটু ব্যাখ্যা দেয়া অসংগত হবেনা। সকালে ঘুম থেকে উঠে ‘উপোস–ভাঙা‘ যদি ‘‘ব্রেকফাস্ট‘ হতে পারে, তাহলে ‘ঘুম–ভাঙা‘ কেন ‘ব্রেকস্লিপ‘ হতে পারবেনা– এই যুক্তিতে এই শব্দের অবতারণা। যাই হোক, দৈনিক আজাদী খুলতেই প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি সহ একটি সংবাদ চোখে পড়লো। আগ্রহভরে পড়লাম। সংবাদের শিরোনাম ‘ঐতিহ্যের সিআরবি ভবন সংস্কারের উদ্যোগ‘। মনে মনে বলে উঠি, ‘ইউরেকা‘। অর্থাৎ পেয়েছি। সিআরবি নিয়েই লেখা যায়। কেননা সিআরবি–র সাথে অনেকের মত আমার, আমাদের গোটা পরিবারের সম্পর্ক। আমার বেড়ে–ওঠা এই সিআরবিকে ঘিরে বললে এতটুকু বাড়িয়ে বলা হবেনা। কত স্মৃতি বিজড়িত এই এলাকাটি, দৃষ্টিনন্দন সিআরবি ভবনটি। আজ যে স্থানটি শিরীষতলা নামে পরিচিতি, খ্যাতি লাভ করেছে আমাদের স্কুল–কলেজ বয়সে ওই নামে ডাকা হতোনা। শিরীষতলার ঠিক উল্টোদিকে যে খোলা মাঠ তাতে আমরা বিকেলে ফুটবল খেলতাম। আরো বড় হয়ে যখন কলেজে পড়ছি, তখন সিআরবি রোড ধরে কয়েক বন্ধু মিলে হেঁটে যেতাম গল্প করতে করতে। এমন কী বৃষ্টির দিনেও ছাতা মাথায় হাঁটতাম, লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন। এ ছিল কতিপয় তরুণের এক ধরনের পাগলামি বা খামখেয়ালি, যাতে ছিল এক অজানা অনাবিল আনন্দ আর ভালোলাগা। মাথার উপরে সারিবদ্ধ গাছের ছায়া, কোলাহল নেই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এলাকা। তখন এখানে আজকের মত এতো লোকের, যানবাহনের ভিড় ছিল না। চট্টগ্রামের ফুসফুস হিসাবে পরিচিত এই এলাকায় ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে শতবর্ষী গাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে সেই কবে থেকে। এই রাস্তা ধরে সার্কিট হাউসের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল রানী এলিজাবেথের গাড়িবহর। বাবার কাঁধে বসে সে দৃশ্য দেখার কথা এখনো মনে আছে। এখন এই শিরীষতলায় ফি–বছর বৈশাখী মেলা বসে, একুশে ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে অনুষ্ঠান হয়। গোটা এলাকা উৎসবে পরিণত হয়।
২. লেখাকে এগিয়ে নেবার আগে ফিরে যাই ‘ইউরেকা’ শব্দের পেছনের কাহিনীতে। হয়তো অনেকের জানা। তারপরও সবার জানা নেই ধরে নিয়ে বলছি সে মজার কাহিনী। ‘ইউরেকা‘ একটি শব্দ যা দিয়ে মনের ভাব, আনন্দ প্রকাশ করা যায়। এর অর্থ হচ্ছে ‘আমি পেয়েছি‘। এটি প্রাচীন গ্রিক গণিতবিদ ও আবিষ্কারক আর্কিমিডিসের ব্যবহৃত একটি বিস্ময় ও আবেগসূচক শব্দ। শ্রুতি আছে, একবার স্নান করতে গিয়ে তিনি দেখলেন, বাথটাবে পা রাখার পর পানির স্তর উপরের দিকে উঠে আসছে। তিনি বুঝতে পারলেন যে, স্থানচ্যুত পানির পরিমান তার শরীরের যে–অংশে ডুবে ছিল তার আয়তনের সমান। তিনি বুঝতে পারলেন অনিমিয়ত বস্তুর আয়তন নির্ভুলের সাথে পরিমাপ করা সম্ভব যা ইতিপূর্বে এক জটিল সমস্যা বলে বিবেচিত হতো। নিজের এই আবিষ্কারে এতটাই উচ্ছসিত হয়েছিলেন যে কথিত আছে তিনি বাথটাব থেকে লাফিয়ে উঠে ন্যাংটা অবস্থায় সিরাকুসের (ঝুৎধপঁংব) রাস্তায় বেরিয়ে এসে বলতে থাকেন ‘ইউরেকা, ইউরেকা‘ অর্থাৎ ‘আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি‘। উল্লেখ্য, সিরাকুস ইতালির দ্বীপ সিসিলির একটি ঐতিহাসিক শহর এবং আর্কিমিডিসের জন্মস্থান। ফিরে আসি সিআরবিতে– চট্টগ্রামে যে কটি দৃষ্টিনন্দন ভবন বন্দর নগরীর শ্রী বৃদ্ধি করে চলেছে তার মধ্যে লাল ইমারতের ‘সেন্ট্রাল রেলওয়ে বিল্ডিং‘ যা সংক্ষেপে সিআরবি হিসাবে পরিচিত কেবল অন্যতম নয়, সেরা। ব্রিটিশরা আমাদের দেশ শোষণ ও শাসন করেছে দুশো বছরেরও বেশি সময় ধরে। তবে তারা রেখে গেছে কিছু অপূর্ব স্থাপত্য। তার মধ্যে ১৮৯৭ সালে নির্মিত এই ভবন অন্যতম। বিশাল এই ভবনের দুই প্রবেশ মুখে দুটি লোহার গেইট। ভবনের ঠিক মাঝখানে বড় গাড়ি–বারান্দা। দুই গেইট দিয়েই গাড়ি প্রবেশ করতে পারে। গাড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়ালে চোখে পরে একটি সিঁড়ি উপরের দিকে উঠে গেছে। দোতলায় উঠেই রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের (জিএম) বড়সড় কামরা। সেখানে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলে যা চোখে ধরা পড়ে তা চোখ–মন দুটোই কাড়ে। সামনে বাগান। তাতে নানা বর্ণের, নানা জাতের ফুল, গাছ–গাছালিও। যখনকার কথা বলছি তখন বাগানের খুব যত্ন নেয়া হতো। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই নিচ তলায় রেলওয়ের জনসংযোগ বিভাগ কর্মকর্তার অফিস। বিভাগের প্রধান (পাবলিক রিলেশন্স অফিসার) ছিলেন মোস্তফা ই জামিল। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বদলি হলে বন্ধু শফিকুল আলম খান হন তার স্থলাভিষিক্ত। তারও আগে একজন ছিলেন, যিনি আমার বাবার সমসাময়িক, নাম কে এল রহমান। আশির দশকের শুরুতে যখন সাংবাদিকতায় যোগ দেই তখন দেখেছি চট্টগ্রামের এমন কোন সাংবাদিক ছিলেন না, সিনিয়র থেকে জুনিয়র, যিনি মোস্তফা জামিল কিংবা শফিকুল আলম খানের অফিসে যাননি এবং গিয়ে তার অফিস–টেলিফোন ব্যবহার করেননি। এদের কেউ যেত সংবাদ সংগ্রহের লক্ষ্যে, কারো টার্গেট নানা জায়গায় ফোন করা, কেউবা পত্রিকা কিংবা ম্যাগাজিনের জন্যে বিজ্ঞাপনের ধান্ধায়। তখন মোবাইল ফোনের আগমন ঘটেনি। কয়েক বন্ধু সাংবাদিককে তো দেখতাম তার কামরায় ঢুকেই প্রথমে টেবিলের উপর রাখা দুটো ল্যান্ড ফোনের একটি কাছে টেনে নিয়ে একটার পর একটা ফোন করতে। ওনারা সৌজন্যের খাতিরেও অনুমতি নেবার প্রয়োজন মনে করতেন না। যেন নিজের অফিস। শফিকুল আলম খানকেও কখনো দেখিনি সামান্যতম বিরক্তি প্রকাশ করতে।
শিরিষ তলার একেবারে কাছেই পাহাড়ের উপর রেলওয়ে ক্লাব এবং তারও উপরে চমৎকার রেলওয়ে রেস্ট হাউস। চমৎকার এই ক্লাবে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম আমাদের পাড়ার ক্লাব, মুক্তধারা থেকে। প্রধান অতিথি ছিলেন সাহিত্যিক আবুল ফজল। বছর বার/তের আগে ‘রেমিটেন্স‘ শীর্ষক এক প্রকল্পের কাজে দেশে গেলে দিন কয়েক ছিলাম এই রেস্ট হাউসে। আমার সাথে হল্যান্ড থেকে গিয়েছিলেন আমস্টারডাম ইউনিভার্সিটির এক সিনিয়র অধ্যাপক এবং এক ডাচ তরুণী গবেষক। চট্টগ্রাম শহরের বুকে এমন একটি চমৎকার স্থান আছে তা দেখে এবং সেখানে দিন কয়েক অবস্থান করে তারা মুগ্ধ হয়েছিলেন। রেলওয়ের রেস্ট হাউসটির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন আমার বড় ভাই, সমরেশ চৌধুরী। তখন তিনি রেলওয়েতে চাকরি করতেন, জিএম অফিসে। বাবা চাকরি করতেন রেলওয়েতে, জি এম অফিসে। বসতেন দোতলায়, জি এমের চেম্বারের কাছাকাছি বড় এক কামরায়, আরো অনেকের সাথে। একনিষ্ঠ ও সততার কারণে বাবা ছিলেন জেনারেল ম্যানেজের পছন্দ ও কাছের মানুষ। ফলে অফিসে তার প্রভাবও ছিল বেশ। মাঝেমধ্যে ঝকঝকে গাড়ি এসে হাজির হতো আমাদের বাসার সামনে। বিশেষ করে অফিস ছুটির দিনে। রেলওয়েতে নানা কাজে বিদেশী ডেলিগেট এলে তাদের গাইড হিসাবে ওই গাড়িতে তিনি সঙ্গী হতেন কাপ্তাই, রাঙামাটির উদ্দেশে। নানা কারণে সিআরবি যেতে হয়েছে স্কুল বয়সে। শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে দু একদিনের জন্যে অফিস না গেলে বাবা তার হাতে–লেখা ইংরেজি দরখাস্ত আমাকে তার অফিসে দিয়ে আসতে বলতেন। হেঁটে যেতাম। রেলওয়েতে বাবা অনেক আত্মীয়–স্বজন, পরিচিতজনকে চাকরি দিয়েছেন। এখন মনে হয় সে–সময় চাকরি পাইয়ে দেয়া অনেক সহজ ছিল। মেজমামা গ্রাম থেকে শহরে এলেন। বাবা তাকে অফিসে চাকরি পাইয়ে দিলেন। আমার দুই চাচাতো ভাই ছাড়াও, দুই পিসতুতো ভাই, দিদির দেবর, গ্রামের কয়েক দূর আত্মীয়, এমন কী মামার গ্রামের কয়েক দূর আত্মীয়কেও রেলওয়েতে চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন। আমাদের ছয় ভাইদের মধ্যে সবার যিনি বড় সমরেশ, যাকে সবাই সমর নামে চিনতো তাকেও।
আগেই উল্লেখ করেছি জিএম অফিসে চাকরি করার সুবাদে বাবার বাড়তি সমাদর ছিল নানা জনের কাছে। পাকিস্তান আমলে ও পরবর্তীতে দেশ স্বাধীন হবার বেশ কিছুকাল পরও রেলওয়ে হাসপাতাল চিকিৎসা ও পরিবেশের দিক থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের চাইতে অনেক উন্নতমানের ছিল। ইনডোর হাসপাতাল ছিল একেবারে ঝকঝকে, পরিষ্কার। জন্ডিস হয়ে একবার আমাকে দিন দশেক রেলওয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। যে সেবা পেয়েছি ডাক্তার আর নার্সদের কাছ থেকে তা এখন দেশে তথাকথিত ফাইভ ষ্টার হাসপাতালেও বোধকরি পাওয়া যাবেনা। সিআরবি ভবনের পাশে যে রাস্তাটি সার্কিট হাউসের দিকে চলে গেছে তা পার হলেই রেলওয়ে হাসপাতাল। অসুখ বিসুখ হলে অফিস যাবার আগে বাবা বলতেন দশটার দিকে হাসপাতালে গিয়ে অপেক্ষা করবি, আমি আসবো। হাসপাতালে বেশ কয়েকজন ডাক্তার নিজ নিজ চেম্বারের বসতেন। সবার পক্ষে সিএমও (চিফ মেডিকেল অফিসার) বা ডিএমও (ডেপুটি মেডিকেল অফিসার)-র কাছে পৌঁছানো সম্ভব হতোনা। বাবার কথা অনুয়ারি সিএমও অথবা ডিএমও–র চেম্বারের সামনে বারান্দায় রেলিংয়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতাম। দরোজার সামনে দর্শনার্থী/রোগীর লাইন। দেখা গেলো বাবা এলেন, লাইনে না দাঁড়িয়ে সোজা ভেতরে গিয়ে চেয়ারে বসতেন। রেলওয়ের কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই। কত যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছি। বিনা পয়সায় পাঠ্য বই বাঁধাই থেকে শুরু করে, অফিসের ক্যামেরাম্যানকে বাসায় ডেকে এনে আমাদের সবার ছবি তোলা, ফ্রি রেল ভ্রমণ, হাসপাতালে বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা এমনি আরো কত কি। তখন রেল–যোগাযোগ ছিল উন্নত। চট্টগ্রাম থেকে দোহাজারী গামী রেলগাড়িতে প্রথম শ্রেণীতে একটি কী দুটি বগি থাকতো। কোন উপলক্ষে গ্রামে যেতে হলে বাবার সুবাদে প্রথম শ্রেণীর কামরায় ট্রেন ভ্রমণ করার সুযোগ হতো। ঢাকা ভ্রমণেও একই সুবিধা ভোগ করেছি। বাবা যখন অবসরে গেলেন তখন সমরদা বাবার বাসাটা তার নামে বরাদ্দ করার জন্যে আবেদন করলেন। তখন আসজাদ আলী সাহেব ছিলেন রেলওয়ের জিএম। তার ছেলে মঈনুদ্দিন আসজাদ ছিল আমার সহোদর সঞ্জয়ের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে সূত্রেও কিছুটা যোগাযোগ ছিল। এক পর্যায়ে আমার কয়েক ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক বন্ধু সহ তদবির করার জন্যে শরণাপন্ন হলাম জি এম আসজাদ আলী সাহেবের। তাদের মধ্যে যদ্দুর মনে পড়ে ছিলেন এম নাসিরুল হক, জাহিদুল করিম কচি ও ওসমান গনি মনসুর। বড় আকারের বাসাটা দাদার নামে বরাদ্দ হলো। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমরা সব ভাই–বোন তখন কেউ স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি। বাবা অবসরে। এমন অবস্থায় ওই বাসা দাদার নামে বরাদ্দ না হলে আমাদের যে কী হতো সে একমাত্র উপরওয়ালাই জানে। তাই বলি রেলওয়ের কাছে আমাদের আজীবনের ঋণ।
লেখক : সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কলামিস্ট।