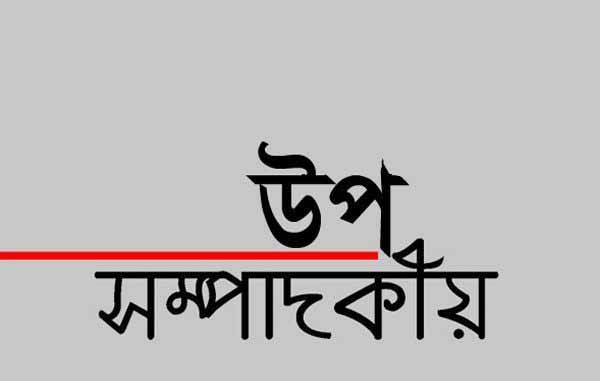শুরু হলো নতুন জীবন। নতুন চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে অনুপ্রেরণামূলক গ্রন্থের লেখক, রয় টি বেনেটের একটি কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, ‘আজকের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি চ্যালেঞ্জ আগামীকাল তোমাকে আরো শক্তিশালী করে তুলবে। জীবনের প্রতিটি চ্যালেঞ্জ তোমার আগামী–দিনকে আরো সুন্দর করে তোলার জন্যে, তিক্ত করে তুলতে নয়।’ তার আরও একটি অনুকরণীয় ও অনুপ্রেরণামূলক উক্তি রয়েছে। তিনি বলেছিলেন, ‘নিজের উপর বিশ্বাস রাখো। একটি কথা মনে রেখো, তুমি নিজেকে যতটা ভাবো তার চাইতেও বেশি সাহসী তুমি, নিজেকে যতটা জান তার চাইতেও বেশি প্রতিভাবান তুমি এবং যতটা কল্পনা করো তার চেয়ে বেশি কিছু করতে সক্ষম তুমি।’ বোধকরি নিজের অজান্তে এই বিশ্বাসগুলি আমার মধ্যে কাজ করেছিল। এই কারণে হল্যান্ডে ‘ডে–ওয়ান’ থেকে ভয়, সংশয়, শংকা মনের ভেতর জাগেনি। যখনি যার মুখোমুখি হয়েছি, আলাপ করেছি, সে ইউরোপীয় রাজনৈতিক নেতা হোক, কিংবা সংস্থার কোনো কেউকাটা হোক কোন জড়তা, ভয় ছাড়া কথা বলেছি। এই সাহস যে দেশে সাংবাদিকতা পেশার কারণে জন্মেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। রিপোর্টার হিসাবে কাজ করতে গিয়ে এই সাহসটুকু জন্মেছিল আপনাতেই। রিপোর্টিংয়ের এটি হচ্ছে বড় প্রাপ্তি। চ্যালেঞ্জ ছাড়া জীবন একঘেঁয়ে। সেই কারণে বছর তিনেক সকাল সাড়ে সাতটা থেকে দুপুরের আড়াইটার আরামের সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত চাকরি ছেড়ে আবার ফিরে গিয়েছিলাম রিপোর্টিংয়ে, বাংলাদেশ টাইমসসে। দুবাই থেকে আমার ছোটবেলার এক অর্থবান (পড়াশুনা খুব একটা করেনি) বন্ধু ঢাকায় টাইমস অফিসের জীর্ণ–শীর্ণ একটি লম্বাটে কামরায় সারিবদ্ধ বসে থাকা এগার রিপোর্টারদের মাঝে আমাকে দেখতে পেয়ে খুব হতাশ। দেশে বেড়াতে এসে এক সন্ধ্যায় সে এসেছিল আমার অফিসে। সবার সামনে কিছুটা উচ্চঃস্বরে বলে, ‘এ কোথায় এসেছিস?’ ওকে ইশারায় চুপ করতে বলি। বিদেশ যাবার আগে সে আমাকে বাংলাদেশের প্রেস ইন্সটিটিউটে (পিআইবি) দেখেছিল। সেখানে নিজস্ব কামরা, পিয়ন ছিল। সে অফিস ছিল অনেক পরিপাটি। অফিস–বাসা করার জন্যে ছিল গাড়ি। সেই চাকরি ছেড়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর মত চাকরি, রিপোর্টিং। সরকারি চাকরিতে আরাম ছিল বটে, তবে ছিলনা চ্যালেঞ্জ। চাটগাঁ ছেড়ে ঢাকা আসাটাও কিছুটা চ্যালেঞ্জ ছিল। জন্ম ও বেড়ে উঠা চাটগাঁ শহর ছেড়ে ঢাকা এলাম দ্বিগুণ বেতনের চাকরি নিয়ে। অচেনা শহরে সাংবাদিকতা। আবার নতুন করে সংবাদের সোর্স বের করা, এর ওর সাথে যোগাযোগ তৈরি করা। চ্যালেঞ্জ বৈকি। হল্যান্ড আসার আগে ঢাকায় যে তিনটি বছর কাটিয়েছি একই কর্মক্ষেত্রে থিতু হয়ে বসে থাকিনি। চাকরি পরিবর্তন করেছি, পত্রিকা পরিবর্তন করেছি, পত্রিকা থেকে সরকারি/আধা–সরকারি প্রতিষ্ঠানে, তারপর আবারো ফিরে গেছি সক্রিয় সাংবাদিকতায় এবং তা চালিয়ে গেছি দেশ ছাড়ার দিন পর্যন্ত। মূল কথা হচ্ছে, জীবনটা একটা চ্যালেঞ্জ এবং এই চ্যালেঞ্জ যারা মোকাবেলা করতে পারে, নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে তাহলে এ–কথা নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি– সামনের দিন সুদিন।
যাই হোক–এলাম নতুন দেশে। নতুন ভাষা। তবে সুবিধে এই ওলন্দাজদের এই দেশে ডাচ ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি সর্বত্র চালু। ট্রাম, বাস, ট্রেন থেকে শুরু করে রাস্তা পরিষ্কার করে যে সুইপার সেও ইংরেজি বলতে পারে। লক্ষ্য করি ডাচরা বিদেশিদের সাথে ইংরেজি বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তবে ভিন্ন চিত্র দেখবেন পার্শ্ববর্তী দেশ বেলজিয়াম, ফ্রান্স কিংবা ইতালিতে। দেখবেন স্পেন সহ পূর্ব ইউরোপের প্রায় সব দেশে। এই ব্যাপারে ফরাসীরা বেশ রক্ষণশীল। দোকানে, স্টেশনের টিকেট কাউন্টার কিংবা পথ চলতে গিয়ে অপিরিচিত কাউকে যদি কোন কারণে কিছু ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করেন, প্রতিপক্ষ উত্তর দেবে ফরাসি ভাষায়, সে আপনি বুঝুন আর নাই বুঝুন। মজার ব্যাপার হলো ওরা ইংরেজিতেই বলবে, ‘নো অংলে‘, অর্থাৎ ইংরেজি না। অথচ সে ঠিকই বুঝতে পেরেছে এবং কিছু ইংরেজি বিদ্যা পেটে আছে। তা না হলে সে উত্তর দিলো কী করে। অবশ্য সময়ের সাথে সাথে এখন এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে অনেক। এখন প্যারিসেরও শপিং মলে ইংরেজিতে কথাবার্তা হয়। এই ভাষা না জানার কারণে লক্ষ্য করি ফ্রান্স, ইতালি, গ্রিস, কিংবা স্পেন অর্থাৎ যে সমস্ত দেশে ইংরেজির চল খুব কম বা নেই, সেখানে দেশ থেকে আসা বাংলাদেশি তরুণদের প্রায় ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে ‘অড জব’ করতে হয়। আইফেল টাওয়ার কিংবা সী–বীচে, বীচের ধারের রেস্তোরাঁয় এদের অনেককে ফুল কিংবা গিফট আইটেম ফেরি করতে দেখা যায়। তবে ইউরোপে কোন কাজকেই খাঁটো করে দেখা হয় না। শ্রমের মর্যদার প্রকৃত প্রয়োগ এখানে রয়েছে। আমাদের দেশে সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েদের সুপার মার্কেট, রেস্তোরাঁ কিংবা জুতার দোকানে কাজ করার কথা ভাবা যায়না। যদিওবা ইদানিং কিছু পরিবর্তন আসছে। কিন্তু ইউরোপে কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীরা তো বটেই এমন কী স্কুলগামী ছেলে–মেয়েদেরও এই ধরনের কাজ করতে দেখা যায় অহরহ। এমন না যে তাদের সবার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। ওরা নিজেদের স্বাবলম্বী ভাবতে, দেখতে পছন্দ করে, মা–বাবার ওপর নির্ভর না করে। এমন কী প্রায় ক্ষেত্রে তারা তাদের কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ের টুইশন–ফিও পার্ট–টাইম চাকরি করে ম্যানেজ করে।
ফিরে আসি নিজের কথায়। দেশে টাইপ মেশিনে রিপোর্ট করতাম। কম্পিউটারে কখনো কাজ করিনি। তখনও আমাদের দেশে পত্র–পত্রিকায় কম্পিউটার চালু হয়নি। চালু হবার একটা প্রক্রিয়া চলছে। পিআইবি–র কাছাকাছি একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছিলাম। কয়েক সপ্তাহ সেখানে গিয়েছিলাম। যে তরুণ মাস্টারনি কম্পিউটারে কিভাবে কাজ করতে হয় আমাদের শেখাচ্ছিল। সাংবাদিক জেনে আমার সাথে ছাত্র–সুলভ আচরণ না করে ভিআইপি ট্রিটমেন্ট দিতে শুরু করলো। অন্য শিক্ষার্থীরা তা থেকে বঞ্চিত ছিল। হাতে গোনা কয়েকটি ক্লাসে যে বিদ্যা অর্জন করেছিলাম এবং যে কম্পিউটার–বিদ্যা নিয়ে হল্যান্ড গিয়েছিলাম, তাতে আর যাই করা যাক না কেন, কাজ করার মত অভিজ্ঞতা যে হয়নি সে খুব জানা ছিল। হল্যান্ড আসার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সুমনা একটি সেকেন্ড–হ্যান্ড ল্যাপটপ উপহার দিলো। সেটি নিয়ে বার দুয়েক তার বড় ভাই, তখন তিনি ফিলিপ্সসে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করছিলেন, তার কাছ থেকে কিছু তালিম নেই। অফিস গিয়ে বাসায় টাইপ করা নিউজ যখন কম্পিউটারে টাইপ করতে যাই তখন মাঝেমধ্যে সমস্যা দেখা দিতো। আটকে যেতাম। সম্পাদক কিংবা অন্য কোন এক সহকর্মী এসে দেখিয়ে দিতো। তখনও আমার কোন ডাচ ভাষাজ্ঞান ছিলো না। মনে পড়ে প্রথম রিপোর্টটি করি বিশ্বব্যাপি গ্লোবাল ওয়ার্মিং–এর ওপর। সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম ইন্দোনেশীয়–ডাচ এক বিশেষজ্ঞের। নাম প্রফেসর নিমপুনো। সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম ডাচ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভবনে। সেখানে ওই আমার প্রথম যাওয়া। হেগ শহরের সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশন–লাগোয়া বিশাল ও দৃষ্টিনন্দন এই ভবন। পরে অনেকবার যাওয়া হয়েছে, সাংবাদিকতা বিষয়ক কাজ ছাড়াও নানা মিটিংয়ে অংশ নিতে, কখনোবা বক্তা হিসাবে। সেটি ছিল আমার প্রথম রিপোর্ট। সাবমিট করলাম। কিছু কাটছাঁট করে সংবাদটি চলে গেলো। পত্রিকা হলে ছাপার অক্ষরে দেখতে পেতাম সংবাদটি। কিন্তু কাজ করি নিউজ এজেন্সিতে (আই পি এস– ইন্টার প্রেস সার্ভিস)। এজেন্সি নিউজ ট্রান্সমিট করেই খালাস। আমার করা সেই সংবাদ যে ঢাকার পত্রিকায়ও ছাপা হয়েছে তা জানলাম টাইমসসে সহকর্মী সৈকত রুশদীর (বর্তমানে কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছে) কাছ থেকে। সেটি বাই–লাইনে গিয়েছিল, সেই কারণে সৈকত টের পেল সুদূর হল্যান্ড থেকে করা তার প্রাক্তন সহকর্মীর করা সংবাদ। এক ধরনের ভালোলাগা অনুভূতি। এরপর বাই–লাইনে আরো কয়েকটি বিশেষ প্রতিবেদন তৈরি করলাম, সম্পাদকের পরামর্শে। তার মধ্যে একটি ছিল বেশ মজার। বিষয় – হল্যান্ডে বসবাসরত বিদেশি, তথাকথিত কন্ট্রাক্ট–ম্যারেজের মাধ্যমে এদেশে থাকার অনুমতি এবং তাদের দ্বারা সৃষ্ট নানা অপরাধ। বিভিন্ন জনের সাথে আলাপ করলাম, নিজে বিদেশি বিধায় ভেতরের অনেক কিছুই জানা ছিল। টের পাই বিদেশি বিধায় কাজটি আমাকে দেয়া হয়েছে। এক পর্যায়ে যেতে হলো ডাচ ইমিগ্রেশন পুলিশ বিভাগে। দায়িত্বে ছিলেন এক ডাচ তরুণী পুলিশ অফিসার। আগেই পরিচয় দিয়ে সময় নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলাম। হাসিমুখে বসতে বলে আলাপচারিতা শুরু হলো। হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপের এক পর্যায়ে তার কাছে জানতে চাইলাম, এই যে অনেক বিদেশি এদেশে স্থায়ীভাবে থাকার জন্যে অর্থের বিনিময়ে ডাচ নাগরিকদের সাথে তথাকথিত ‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ করছে, এই ব্যাপারে আপনাদের কী বলার আছে। উত্তরে মহিলা বললেন, বিষয়টি আমাদের জানা। কিন্তু চ্যালেঞ্জ করা খুব কঠিন। যেমন গোপন তথ্যের ওপর ভিত্তি করে হয়তো আমরা তদন্ত করতে গেলাম। যাকে নিয়ে সন্দেহ তিনি ওই মুহূর্তে বাসায় নেই (যদিওবা আমরা জানি যে তিনি সেখানে থাকেন না)। আমাদের বলা হলো, তিনি বেড়াতে গেছেন বা কাজে গেছেন। বাসায় তার কিছু কাপড়–চোপড়, জুতা দেখানো হলো। কিংবা বলা হলো, মনমালিন্য চলছে, তাই সে কিছুদিন ধরে বাসায় থাকছে না। এখন আপনিই বলুন আপনি কীভাবে প্রমাণ করবেন যে এটি চুক্তিভিত্তিক বিয়ে বা কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ। তারপর হেসে বললেন, ‘তোমার কি প্রয়োজন? আমি কিন্তু ব্যাচেলর।’ উত্তরে হেসে বলি, ‘টু লেট, আমি বিবাহিত, স্ত্রী বাংলাদেশি ডাচ।’ তখন হল্যান্ডে আমার অবস্থান মাত্র মাস কয়েক। চলবে
লেখক : সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কলামিস্ট