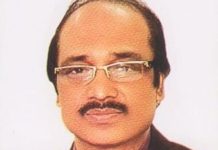বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ ১০ অক্টোবর ১৮৬১ খিষ্টাব্দে পটিয়ার ঐতিহ্যবাহী গ্রাম সূচক্রদণ্ডীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী নুরুদ্দিন এবং মাতার নাম মিশ্রীজান। পারিবারিক পরিমণ্ডলেই আব্দুল করিমের প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি। এরপর তিনি ভর্তি হন সূচক্রদণ্ডী মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে। আব্দুল করিম পটিয়া স্কুল হতে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এট্রান্স পাস করেন। কিন্তু আজহার উদ্দিন খাঁনের মতে, আব্দুল করিম কুড়ি বছর বয়সে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাস করেন। তবে ড. আহমদ শরীফের মতে, ১৮৯৩ সালেই তিনি এন্ট্রান্স পাস করেন এবং ১৮৯৩ সালের জুলাই মাসে তিনি চট্টগ্রাম কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র ছিলেন। যতদূর জানা যায়, দক্ষিণ চট্টগ্রামের মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম এন্ট্রান্স পাস করা ব্যক্তি ছিলেন। এন্ট্রান্স পাস করে তিনি চট্টগ্রাম কলেজে এফ. এ. ক্লাসে পড়াশুনা শুরু করেন কিন্তু টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তাঁর চূড়ান্ত পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হয়নি। ফলে এখানেই তাঁর প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতি ঘটে। আধুনিক, আমৃত্যু উদার ও মানবিক বোধের প্রেরণায় তিনি ছিলেন মানবতাবাদী মানুষ। অসামপ্রদায়িক মনের ও মননের অধিকারী এ মহান সাধক জীবন জীবিকার প্রয়োজনে কর্ম জীবনে প্রবেশ করেন। তাঁর প্রথম কর্মস্থল চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুল। তিনি মাত্র কয়েকমাস এখানে শিক্ষকতা করেন। এরপর তিনি সীতাকুন্ড মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে এক বছরের জন্য (১৮৯৫–৯৬) অস্থায়ী প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন। ১৮৯৬–৯৭ সালে প্রথমে তিনি চট্টগ্রাম সাব জজ আদালতে, পরে পটিয়া মুন্সেফ আদালতে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করেন। কবি নবীন চন্দ্র সেনের (১৮৪৭–১৯০৯) আগ্রহে ও আনুকূল্যে ১৮৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে চট্টগ্রাম কমিশনার অফিসের কেরানি পদে তিনি নিয়োগ পান। কিন্তু পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পুঁথি সংগ্রহের এক প্রয়াসে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আব্দুল করিম চাকরিচ্যুত হন। বেশ কিছুকাল কর্মহীন থাকার পর তিনি আনোয়ারা মধ্য–ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন। সেখানে তিনি ১৮৯৯ সাল হতে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।
১৯০৬ সালে আব্দুল করিম শিক্ষকতার পেশা ত্যাগ করে চট্টগ্রাম বিভাগের ইন্সপেক্টর অব স্কুল এর অফিসে দ্বিতীয় কেরানির পদে চাকরিতে যোগ দেন। দীর্ঘ ২৮ বছর চাকরির পর ১৯৩৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে আব্দুল করিমকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব দেয়া হলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি। সক্রিয় কর্মজীবন হতে অবসর নিয়ে তিনি সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ডেও অংশ নেন। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ও বেঞ্চের প্রেসিডেন্ট, পটিয়া ঋণ সালিশি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘকাল পটিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ছিলেন তিনি। বিপদে, সম্পদে, শোকে–আনন্দে, সুখে–দুঃখে তিনি ছিলেন এলাকাবাসীর মমত্বশীল অভিভাবক, উপদেশক ও সহায়ক।
জীবিত অবস্থায় এই মহান সাধক তাঁর কর্মের স্বীকৃৃতি, সম্মান ও সমাদর পেয়ে গেছেন।
ক) ১৩১০ বঙ্গাব্দে বঙ্গিয় সাহিত্য পরিষদ। তাঁকে পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য বা ফেলো নির্বাচিত করেন। পরে ১৩১৯ বঙ্গাব্দে তাকে আজীবন সহায়ক সদস্য করে নেয়া হয়। খ) ১৩২৪ বঙ্গাব্দে তিনি সাহিত্য পরিষদ এর কার্যনির্বাহী কমিটিতে শাখা পরিষদ হতে সদস্য মনোনীত হন। গ) ১৩৩২ বঙ্গাব্দে তিনি সাহিত্য পরিষদ এর চট্টগ্রাম শাখার সহ সভাপতি নির্বাচিত হন। এ সহ–সভাপতি পদও তাঁর জন্য বিরল সম্মান বয়ে আনে। ঘ) ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টল ধর্মমণ্ডলী তাঁকে ‘সাহিত্য বিশারদ’ উপাধিতে ভূষিত করেন। ঙ) ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া সাহিত্য সভায় তাঁকে সাহিত্য সাগর উপাধিতে ভূষিত করেন। চ) স্যার আশুতোষ মুখপাধ্যায় এন্ট্রান্স পাস কেরানি আব্দুল করিমকে প্রথমে প্রবেশিকা পরীক্ষার উপরে বি.এ পরীক্ষায় বাংলা পরীক্ষক নিযুক্ত করেন এবং ১৯৪৭ সাল অবধি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ছিলেন। ছ) ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বাংলা অনার্স পরীক্ষায় একটি পত্রের পরীক্ষক নিযুক্ত করেন।
উপর্যুক্ত সম্মান ও পদক ছাড়াও তাঁর সময়কালের তিনিই ছিলেন একমাত্র মুসলিম সাহিত্যিক, যার প্রবন্ধ কলিকাতার প্রথম শ্রেণির পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হত। ঊনিশ শতকের শেষ দশক থেকে তিনি পুঁথি সংগ্রহে মনোযোগী হন। এই কাজে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রাসাদ শাস্ত্রী, দীনেশ চন্দ্র সেন, নগেন্দ্র নাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহান্ব তাঁর পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। আদি পর্বের পুঁথি সংগ্রহ প্রয়াসে এদের পাশাপাশি আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের নাম ও উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ, সম্পাদনা, বিবরণ, লিপিবদ্ধ আলোচনা সাহিত্য বিশারদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের সম্পাদিত এবং রচিত বই–এর সংখ্যা ১৫, তাঁর সম্পাদিত প্রকাশিত বইগুলি নিম্নরূপ, ১। নরোত্তম ঠাকুর রচিত, ‘রাধিকার মান ভঙ্গ’, ১৩০৮ বাংলা, ১৯০১ সাল। ২। ‘বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ’ ১ম, খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৩২০ বাংলা, ১৯১৩ সাল। ৩। ‘বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ’ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ১৩২১ বাংলা ১৯১৪ সাল।
৪। কবি বল্লভ রচিত, ‘সত্য নারায়ণের পুঁথি’, ১৩২২ বাংলা, ১৯১৫ সাল। ৫। দ্বিজ রতিদেব রচিত, ‘মৃগলুব্ধ’, ১৩২২ বাংলা, ১৯১৫ সাল। ৬। রামরাজা রচিত, ‘মৃগলুব্ধ সংবাদ’, ১৩২২ বাংলা, ১৯১৫ সাল। ৭। দ্বিজ মাধব রচিত, ‘গঙ্গামঙ্গল’, ১৩২৩ বাংলা, ১৯১৬ সাল। ৮। আলী রাজা রচিত, ‘জ্ঞান–সাগর’, ১৩২৪ বাংলা ১৯১৭ সাল। ৯। বাসুদেব ঘোষ রচিত, ‘শ্রী গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস’, ১৩২৪, বাংলা ১৯১৭ সাল। ১০। মুক্তারাম সেন রচিত, ‘সারদা–মঙ্গল’, ১৩২৪ বাংলা ১৯১৭ সাল”। ১১। শেখ ফয়জুল্লাহ রচিত, ‘গোরক্ষ বিজয়’, ১৩২৪ বাংলা ১৯১৭ সাল।
বর্ণিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণসহ সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত ১১টি বই ১৯০১–১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ড. এনামুল হকের সঙ্গে যুগ্মভাবে ‘আরাকান রাজ সভায় বাঙ্গালা সাহিত্য লিখে প্রকাশ করেন। যা ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর লিখিত ‘ইসলামাবাদ’ বইটি তাঁর জীবদ্দশায় বই আকারে প্রকাশিত হয় নি। সভাপতির অভিভাষণ হিসেবে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে ‘ইসলামাবাদ’ নামের প্রবন্ধগুলি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু শেষ হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ এর অক্টোবর মাসে ‘ইসলামাবাদ’ বইটি প্রকাশিত হয়।
পুঁথি সংগ্রহ সংরক্ষণ চর্চার প্রেরণা তিনি পারিবারিক সূত্রেই পেয়েছিলেন। তাঁদের পরিবারে কিছু প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ ছিল। তাঁর পূর্বপুরুষ কাদির রাজা ১৭৭০ সাল নাগাদ দৌলত কাজীর ‘সতী ময়না থোর চন্দ্রানী’ কাব্যটি পুত্রের শিক্ষার প্রয়োজনে স্বহস্তে নকল করেছিলেন। সে সূত্র ধরেই তাঁর পুথি সংগহের প্রেরণা। তিনি প্রায় ২০০০ পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। যা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম রত্ন হিসেবে বিবেচিত।
সাহিত্য জগতে আব্দুল করিমের খ্যাতি ছিল অপরিসীম। তিনিই একমাত্র লেখক যাঁর একাধিক প্রবন্ধ একই সময়ে বিভিন্ন উচ্চ মানের সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হত। তিনি নিজে কোন পত্রিকা প্রকাশ করেননি। কিন্তু তাঁর খ্যাতির কারণে সাময়িক পত্রিকার মান ও গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য একাধিক সাময়িক সাহিত্য পত্রিকা আত্ম প্রকাশ করলে তাকে অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত করা হতো।
১৯১৮ সালে তিনি প্রচণ্ড আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছিলেন, ‘বাংলার মুসলমানদের পৈতৃক জন্মভূমি যেখানেই হোক না কেন, বাঙলায় পদার্পণ করিয়া অবধি তাঁহারা খাঁটি বাঙালিই হইয়া গিয়োছেন। একথা বোধ হয় কোন শত্রুও অস্বীকার করিতে পারে না। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মে বটে, বাংলাদেশের প্রচলিত বাঙালা ভাষা ও তাহাদের মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষার স্থানাধিকার মরিয়া এত যুগযুগান্তর পর্যন্ত নির্বিবাদে চলিয়া আসিতেছে। …আব্দুল করিম কিশোর বয়সে যাকে বালিকা বধু হিসেবে নিজ জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করেছিলেন এবং যার সঙ্গে দীর্ঘ ৭১ বছর ঘর সংসার করেছিলেন সেই প্রিয়তমা জীবন সঙ্গিনী ১৯৫৩ সালের ২৫ মার্চ ইন্তেকাল করেন। প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুতে আব্দুল করিম অনেকটা অসহায় ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। নিঃসঙ্গ সাহিত্য বিশারদ ১৯৫৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সকালে গ্রামের নিজ বাড়িতে ৯২ বছর বয়সে লেখনীরত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে এক স্বনামধন্য লেখক উল্লেখ করেছেন, “ লিখতে বসে তাঁর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। মহান সাধকের এই ধরনের মরণই কাম্য। তিনি ‘চট্টগ্রামের অলিখিত কাহিনী’ লিখতে ছিলেন তখন তাঁর এই অলিখিত কাহিনী অলিখিত রয়ে গেল”।
চিত্ত, বিত্ত, জীবন এবং যৌবন এসমস্তই চঞ্চল। কিন্তু কীর্তিমান ব্যক্তি চিরজীবী। কীর্তিমান সাহিত্যবিশারদ ও তাঁর কর্মকাণ্ডের কারণে আজও জীবিত।
লেখক: প্রাবন্ধিক, সম্পাদক–শিল্পশৈলী