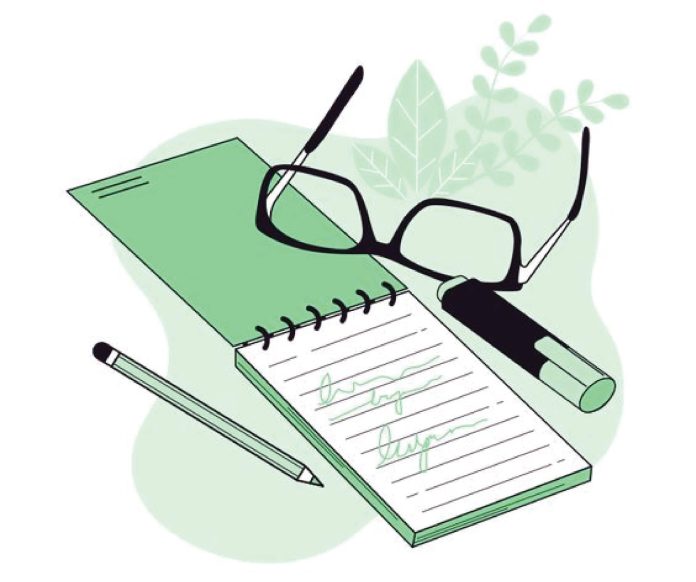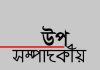বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত অর্থবছরের শেষ তিন মাসে (এপ্রিল–জুন) ভোক্তাঋণ প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা বেড়েছে, যা আগের প্রান্তিকের তুলনায় প্রায় ১৭ শতাংশ বেশি। অথচ এই ঋণের সুদের হার ক্ষেত্রবিশেষে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত। এত উচ্চসুদেও সাধারণ মানুষের ঋণ নেওয়ার এই প্রবণতা ইঙ্গিত দেয়, দেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি বর্তমানে গভীর আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।
অর্থনীতিবিদদের মতে, এই সংকটের প্রধান কারণ হলো উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং আয়বৈষম্য। যখন গড় মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের কাছাকাছি থাকে, তখন মানুষের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়ার ফলে সাধারণ আয়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। এতে পরিবারগুলো দৈনন্দিন খরচ মেটাতে ঋণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পত্রিকান্তরে বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগের কথা প্রকাশিত হয়েছে। বলা হয়েছে,
এত ঋণ মানুষ নিচ্ছে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত উচ্চসুদে। অর্থাৎ পরিবারের দৈনন্দিন জীবন টিকিয়ে রাখতে গিয়ে ভবিষ্যতের আয়কে বন্ধক রাখতে হচ্ছে। অন্যদিকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্মীরা একই সুবিধা পান প্রায় বিনা সুদে। এই বৈষম্য শুধু অর্থনৈতিক অসমতা নয়, সামাজিক অসন্তোষকেও উসকে দিতে পারে। তাঁরা বলেন, ভোক্তাঋণের এই বৃদ্ধি সমাজের আর্থিক চাপ ও দুর্বলতার প্রতিচ্ছবি। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সরকারকে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আরো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। একই সঙ্গে মানুষের আয় বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করা এবং সাধারণ মানুষের জন্য ঋণ সুবিধা আরো সহজলভ্য করার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। শুধু ব্যাংকের কর্মীদের জন্য নয়, সবার জন্য সাশ্রয়ী ঋণের ব্যবস্থা করা জরুরি।
বিশেষজ্ঞরা বলেন, বাংলাদেশের নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি এক অদৃশ্য অথচ প্রবল সঙ্কটে রয়েছে–তা কেবল কর্মসংস্থানের নয়, বরং আত্মপরিচয়ের। তারা সমাজে একধরনের প্রতিশ্রুতিশীল শ্রেণি হিসেবে বিবেচিত হলেও বাস্তবে তারা নিজেরাই জানে না, তারা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। তাদের শিক্ষা আছে, কিন্তু কাজ নেই; স্বপ্ন আছে, কিন্তু পথ নেই; সম্মান চায়, কিন্তু বাস্তবতা বারবার অপমান করে। এই শ্রেণির ভেতরকার অস্থিরতা এখন নিছক ব্যক্তিগত বেদনা নয়, তা হয়ে উঠছে সামষ্টিক উদ্বেগ। যেখানে একটি সমাজের সবচেয়ে সচেতন, সম্ভাবনাময় শ্রেণি–যুব মধ্যবিত্ত–নিজেকে মূল্যহীন, অসফল বা নিরর্থক ভাবতে শুরু করে, সেখানে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎও ধীরে ধীরে ঘোলাটে হয়ে পড়ে। হতাশ, বিভ্রান্ত ও আত্মপ্রতারণায় নিমজ্জিত এই শ্রেণির মানুষরা হয়তো আজ ক্ষোভ পোষণ করছে চুপচাপ, কিন্তু আগামীকাল সেই ক্ষোভ রূপ নিতে পারে সামাজিক অস্থিরতা, আত্মঘাতী নিস্তেজতা কিংবা সহিংস প্রতিবাদে। এজন্য দরকার একটি সহানুভূতিশীল রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি, দরকার পরিবার–সমাজ–শিক্ষা–নীতিনির্ধারকদের সম্মিলিত বোঝাপড়া–যেখানে একজন মানুষ শুধু আয়ক্ষমতা দিয়েই মূল্যায়িত হবে না, বরং তার আত্মপরিচয়, মানসিক ভারসাম্য এবং ধৈর্যকে মর্যাদা দেওয়া হবে।
বিশ্লেষকরা বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উচ্চমূল্যের কারণেও দেশের মধ্যবিত্তের দিশেহারা অবস্থা। মধ্যবিত্ত তাদের সঞ্চয় থেকে যে মুনাফা পায়, দেশের মূল্যস্ফীতি তার চেয়ে বেশি। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। মধ্যবিত্তের সঞ্চয়ের একটা বড় অংশ চিকিৎসা খাতে চলে যায়। চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে গিয়ে অনেক পরিবারই পথে বসেছে। নিত্যপণ্যের বাজারে চাল–আটা, মাছ–মাংস, শাকসবজি সবকিছুর দামই এখন ঊর্ধ্বমুখী। বাজারে নাজিরশাইল, মিনিকেট, মোটা চাল সব ধরনের চালের দাম এখনো অনেক। অতীব গুরুত্বপূর্ণ নিত্যপণ্য উচ্চমূল্য ধারণ করেছে। ফলে মধ্যবিত্ত ধীরে ধীরে ক্রয়ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। বলা যায়, এ দেশের একশ্রেণির অসৎ ও অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা তাদের ইচ্ছামতো পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়ার কারণেই এই বিপন্ন অবস্থা। জনগণকে বারবার দুর্ভোগ ও অসহায়ত্বে ফেলে দেয়া ন্যায়সঙ্গত কাজ নয়। বাজারে পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও নানা অজুহাতে দাম বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে প্রায় সব পণ্যের। খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। গ্রাম ও শহর সর্বত্রই মূল্যস্ফীতির এই পাগলা ঘোড়া ধাবমান। মূল্যস্ফীতির প্রথম প্রভাবই হলো মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়া। যে কারণে মূল্যস্ফীতি বাড়লে দরিদ্র মানুষ সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়ে। বিপাকে পড়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণিও। নিত্যদিনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে মধ্যবিত্ত দরিদ্র হয়ে পড়েছে। তাই সাধারণ মানুষের ওপর থেকে অর্থনৈতিক চাপ কমানোর জন্য সুদূরপ্রসারী নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।