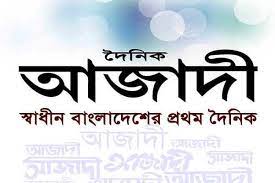মানুষের ইতিহাস মূলত সংগ্রামের ইতিহাস। এই সংগ্রাম কখনো ছিল জীবিকার, কখনো অধিকারের, কখনোবা সম্মিলিত অস্তিত্বের। আধুনিক উন্নয়ন ধারণা যত এগিয়েছে, একটি বিষয় ক্রমেই স্পষ্ট হয়েছে–উন্নয়ন যদি জনমানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া হয়, তবে তা হয় কাচের ভবন, যার শোভা আছে, স্থায়িত্ব নেই। আর এই অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন এমন একটি অর্থনৈতিক কাঠামো, যেখানে মানুষ কেবল ভোক্তা নয়, অংশীদার–নির্দেশকও বটে। এটাই ‘জনঅংশগ্রহণমূলক অর্থনীতির‘ মূল দর্শন। অর্থনীতির প্রান্তিকের কেন্দ্রীকরণ বর্তমানে বিদ্যমান প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনেকাংশেই অর্থনৈতিক সম্পদ, মূলধন, শিল্প বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র বা সীমিত গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত, ফলে শহর বা রাজধানী অঞ্চলে শিল্প–কারখানা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি থাকে, আর প্রান্তিক অঞ্চলগুলো (গ্রাম, প্রত্যন্ত এলাকা) বঞ্চিত হয়। এর ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পায় । প্রচলিত পুঁজিবাদ বা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী প্রায়শই উন্নয়নের দর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। তারা উন্নয়ন দেখে, কিন্তু স্পর্শ করতে পারে না । এই প্রেক্ষাপটে সমবায়ের মতো জনভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো আমাদের সামনে বিকল্প হিসেবে উঠে আসে। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় সমবেতভাবে, মুনাফা বণ্টিত হয় ন্যায্যভাবে এবং মূল লক্ষ্য থাকে সদস্যদের জীবনের মানোন্নয়ন। বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় ‘জনঅংশগ্রহণ‘ বা participatory economics একটি সময়োপযোগী ধারণা হয়ে উঠেছে। এই ধারণার মূল কথা হলো– সাধারণ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থনীতিকে চালনা করা, যেখানে মুনাফা নয়, বরং মানুষের কল্যাণই প্রধান লক্ষ্য। এই প্রেক্ষাপটে সমবায় ব্যবস্থা জনঅংশগ্রহণমূলক অর্থনীতির একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।
সমবায় : জনঅংশগ্রহণের বাস্তব রূপ
সমবায় হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে সদস্যদের আর্থ–সামাজিক উন্নয়নের জন্য সমবেতভাবে কাজ করা হয়। এক কথায়, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের অর্থনীতি হলো সমবায়ের মূল চেতনা। সমবায় ব্যবস্থায় জনঅংশগ্রহণের দিকগুলো : সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতন্ত্র : প্রতিটি সদস্যের সমান ভোটাধিকার ও মত প্রকাশের সুযোগ। অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা : লাভ– ক্ষতির দায়ভাগ সকল সদস্যের। স্থানীয় সম্পদে নিয়ন্ত্রণ : সদস্যরা নিজেরাই পুঁজি, শ্রম ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করেন।
স্বনির্ভরতা ও স্বশাসন : সরকারি অনুগ্রহ নয়, বরং নিজস্ব উদ্যোগে বিকাশ । কেন প্রয়োজন এমন অর্থনীতি? ধনী–গরিবের ব্যবধান হ্রাসে সহায়ক, দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে সহায়ক, স্থানীয় সম্পদের স্থানীয় ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয়, বাজারের একচেটিয়াতা ভাঙার সক্ষমতা তৈরি হয়।
বিশ্বব্যাপী যখন সামাজিক ব্যবসা, ইনক্লুসিভ গ্রোথ এবং কোমিউনিটি বেসড ডেভেলপমেন্ট‘ আলোচনায় আসছে, তখন বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অংশগ্রহণমূলক অর্থনীতিতে সমবায় হয়ে উঠতে পারে পরিবর্তনের হাতিয়ার।
মানুষ একা জন্ম নেয়, কিন্তু একা বাঁচে না এই চিরসত্য কথাটির সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপই হলো ‘সমবায়‘। আমাদের দেশে সমবায় শুধু একটি সংগঠন নয়, বরং এটি একটি আন্দোলন, একটি দর্শন, একটি জনভিত্তিক উন্নয়ন চিন্তা। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে, সমবায় হয়ে উঠতে পারে এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ১৮৪৪ খ্রি. ইংল্যান্ডের রচডেল (Rochdale) অঞ্চলের ২৮ জন বস্ত্রশ্রমিক মিলে আধুনিক সমবায় আন্দোলনের সূচনা করেন। তারা “Rochdale Equitable Pioneers Societ” প্রতিষ্ঠা করেন এরপর ইউরোপসহ পৃথিবী দেশে দেশে সমবায় আন্দোলন অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে জনঅংশ্রহণের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে পৃথিবী উন্নত সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার ক্ষেত্র হিসেবে উঠে এসেছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে সমবায়ের যাত্রা প্রায় শতবর্ষ পেরিয়ে এসেছে। ব্রিটিশ শাসনামলে কৃষকদের ঋণ সমস্যা মোকাবেলায় এটি শুরু হলেও স্বাধীনতা– পরবর্তী সময়ে সমবায়কে গণমুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি সদস্যসহ ১,৯০,০০০–এর বেশি সমবায় সংগঠন রয়েছে। কৃষি, মৎস্য, ক্ষুদ্রঋণ, দুগ্ধ উৎপাদন, কুটির শিল্প এমনকি নারীর ক্ষমতায়নেও সমবায়ের সরব উপস্থিতি রয়েছে। সমবায়ের মূল শক্তি এর সমান অংশীদারিত্ব এবং লাভের ন্যায্য বন্টন। এখানে ধনী–গরিব, নারী–পুরুষ কিংবা শিক্ষিত–অশিক্ষিত সবাই সমান ভোটাধিকার পায়। সমবায় একটি ন্যায়সঙ্গত উন্নয়ন মডেল, যেখানে মুনাফা নয়, বরং জনগণের ক্ষমতায়নই মুখ্য। বর্তমান বিশ্বে যখন সামাজিক ব্যবসা, ইনক্লুসিভ ফিন্যান্সিং এবং টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা আলোচিত, তখন সমবায় তার নিজস্ব গৌরব নিয়ে উঠে আসছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এই মডেল হতে পারে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের কার্যকর মাধ্যম। সমবায়ের সম্ভাবনার বিপরীতে রয়েছে কিছু দীর্ঘস্থায়ী ও কাঠামোগত সমস্যা : অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও স্বচ্ছতার অভাব, রাজনৈতিক প্রভাব এবং গ্রুপিং সরকারি তদারকির দুর্বলতা, প্রকৃত সদস্যদের অংশগ্রহণহীনতা, ঋণ খেলাপি ও দুর্নীতি। এসব সমস্যা সমাধান না হলে সমবায় কাঠামো শুধু কাগজে–কলমেই সীমাবদ্ধ থাকবে ।