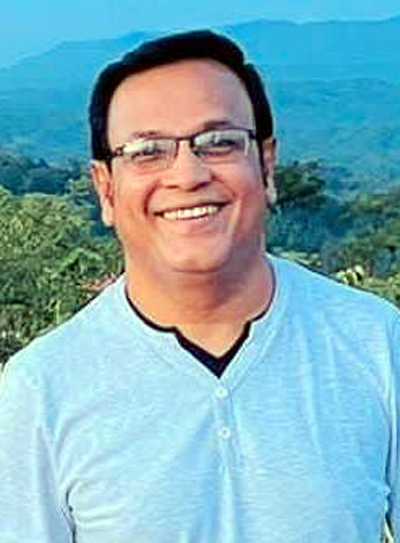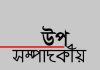কথায় আছে, শিশুর প্রথম পাঠশালা তার পরিবার। শিশুর প্রতিটি হাঁসি তার বিকাশের একটি ধাপ। শিশুর বেড়ে ওঠা শুধু শারীরিক নয়, তার মন–মানসিকতার যত্নও সমান জরুরি। কবি সুকান্তের একটি লাইন মনে পড়ে গেলো, ‘আমি সেই দিনের কথা ভাবি, যেদিন শিশু কণ্ঠে গান গাইবে ভালোবাসার, শান্তির’। আবার কবি জসীম উদ্দীনের কথা বলা যায়, ‘শিশুরা মাটির খেলায় মেতে উঠে ভবিষ্যতের স্বপ্ন গড়ে’। সামাজিক অবক্ষয়ের ছবি আমাদের চার পাশে এখন এতই স্পষ্ট যে, তার শিকড়ে পৌঁছানোর চেষ্টা না করলে নয়। সেই অবক্ষয়ের সূচনা হয় কেন, কখন, কীভাবে? শিক্ষাদীক্ষাহীন, দুর্বিনীত শিশুই কি ধর্ষকে পরিণত হয়? তা হলে সন্তানের লালন করব কীভাবে? শিশু–মনোবিদরা বলেছেন, সন্তান প্রতিপালনের কোনও বাঁধাধরা নৃতাত্ত্বিক ছক নেই। নৃতত্ত্বের অধ্যাপক মেরিডিথ স্মলের মতে, শিশুরা বাবা–মা, পাড়া–প্রতিবেশীদের যৌথ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নিয়ে বড়ো হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই পণ্ডিতরা বোঝার চেষ্টা করেছিলেন যে, হিটলার, ফ্র্যাঙ্কো, মুসোলিনির মতো যুদ্ধ–উম্মাদ স্বৈরাচারীদের নির্মাণের শুরু কি শৈশবে? ফ্যাসিস্টদের ব্যক্তি–বৈশিষ্ট্যের শিকড় খুঁজতে গিয়ে পৃথিবী বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী থিয়োডর অ্যার্ডানো আর হ্যানা আরেন্ট লক্ষ করেছিলেন, কর্তৃত্বের কাছে নিরঙ্কুশ আনুগত্য, নির্বিরোধ বশ্যতা, আগ্রাসন এবং যুক্তিবাদ ও বৌদ্ধিক বিচারের বিরোধিতা–ফ্যাসিবাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলির গোড়া পত্তন শৈশবেই।
এদের গবেষণার সূত্র ধরে বিশিষ্ট মনোবিদ ও ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বিশেষজ্ঞ ডায়ানা ব্লুমবার্গ বমরিন্ড ১৯৬০–৭০’এর দশকে তিন ধরনের সন্তানপালন পদ্ধতির কথা বললেন। প্রথম পদ্ধতিটি হলো অথরিটেরিয়ান বা স্বৈরাচারী সন্তান প্রতিপালন, যেখানে বিধিনিষেধের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। শিশুর থেকে প্রত্যাশাও আকাশছোঁয়া, নির্বিচার, কঠোর। বেয়ারা আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় শাস্তির মাধ্যমে। শিশুর আবেগের মূল্যই থাকে না। ক্ষমাহীন, নিষ্করুণ পৃথিবীর জন্য শিশুকে প্রস্তত করা হয়। বমরিন্ডের মতে, স্বৈরাচারী শাসনে প্রতিপালিত শিশু জীবনে সাফল্য পায় মাঝারি রকমের– বাধ্য, অনুগত, প্রথানুবর্তী পুরুষ হিসেবে পরিচিত হয়। কিন্তু মনে পুষে রাখে অবরুদ্ধ ক্রোধ, নালিশ–অল্প প্ররোচনাতেই যার বিস্ফোরণ ঘটে। এদের সামাজিক দক্ষতা কম হয়। কারণ অভিজ্ঞতা দিয়ে কিছুই শেখে না, বড় হয় অপরের আজ্ঞাবহ হয়ে। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো আথোরিটেটিভ বা কর্তৃত্বময় সন্তানপালন, যেখানে সন্তানপালনে আরোপিত বিধিনিষেধ, প্রত্যাশাগুলি স্পষ্ট, সামঞ্জস্যপূর্ণ; কিন্তু অন্য দিকে আছে নমনীয়তা, প্রশংসা, শাস্তির বদলে ক্ষমার জায়গা, শিশুদের সম্ভাবনা ও ব্যক্তি–স্বাধীনতা বিকাশের সুযোগ। এই ধরনের লালনের ফল শুভ হয়। সুখী, সংবেদনশীল, সামাজিক ভাবে পরিপক্ব, পরিপূর্ণ, স্বাধীন, স্বাবলম্বী শিশুর গড়ে ওঠার সুযোগ ঘটে।
মোনোবিদ বমরিন্ড বর্ণিত তৃতীয় পদ্ধতিটি পারমিসিভ বা সম্মতিমূলক সন্তানপালন। শিশুর কাছে প্রতাশা নামমাত্র, দাবিও নেই, নেই বিধিনিষেধের অর্গল।
এমন প্রতিপালনের ফলে শিশু বড় হয় অসংযত, ভোগপরায়ন, অসহিষ্ণু, হতাশাগ্রস্ত যুবক হিসেবে।
বমরিন্ডের এই ত্রিবিধ শিশু–প্রতিপালনের ধারণার সঙ্গে ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত গবেষণা পত্রে মনোবিদ জি এলেনর ম্যাকবিলএবং জন মার্টিন যোগ করেছেন উদাসীন শিশু প্রতিপালনের ধারণা যেখানে শিশুর কাছে অভিভাবকের কোনও দাবি দাওয়া নেই, তার প্রতি মনোযোগও নেই।
মনোবিদরা মানছেন, সন্তান যেভাবেই মানুষ করুন, বৃহত্তর সমাজের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধই শেষ কথা বলে। বিখ্যাত মনোবিদ জুডিথ হ্যারিস–এর মত, পিতা–মাতা নয়, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ শিশুরা শেখে সমবয়সীদের থেকে। শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে পিতা–মাতার ভূমিকা নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি করা হয়। একটা বয়সের পর শিশুর জীবন গঠনে বাবা–মা নয়, সমবয়সীরাই নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়। বাবা–মা’র রুচি এবং নির্দেশ তারা শেষ পর্যন্ত সমবয়সীদের পরামর্শেই গ্রহণ বা বর্জন করে। দেখা গিয়েছে, বিবাহবিচ্ছিন্না মা যেখানে একাই সন্তান পালন করেন, সেখানে সন্তানের অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের ঝুঁকি অনেক বেশি। সন্তান প্রতিপালনের গলদের জন্য নয় একার রোজগারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মা সাধারণত যেখানে বসবাসে বাধ্য হন, সেখানে স্বল্প–আয় পরিবারের শিষ্টাচারহীন বাচ্চা বেশি । তাদের অপভাষা রপ্ত করে শিশু বড় হয়। এই বক্তব্য মনোবিদ মহলে একই সঙ্গে নিন্দা এবং প্রশংসার ঝড় তুলেছিল। বলা হয়েছিল, জুডিথ বাবা–মায়ের ভূমিকা লঘু করছেন। তবে এখন শিশু–মনোবিদরা মানেন, জীবনগঠনে সমবয়সী বন্ধুদের প্রভাবও কম নয়।
বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা, খেলাধুলা সামাজিক যোগ্যতা বৃদ্ধি করে। এর মধ্যে রয়েছে সামাজিক, মানসিক, জ্ঞানীয় এবং আচরণগত দক্ষতা, যা সামাজিক অভিজোযনে প্রয়োজনীয়। পৃথিবী বিখ্যাত ইতিহাসবিদ জোহান হুইজিঙ্গা মানুষকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন, ‘হোমো লুডেন্স’ (খেলার মানুষ) বলে। মানুষ খেলার মাধ্যমে বিশ্বকে বুঝতে চায়। তার সাংস্কৃতিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটে প্রধানত খেলার মাধ্যমে। আমাদের যাবতীয় ‘সোশাল ন্যারেটিভ’ সংগঠনমূলক কাজ, প্রকৃতপক্ষে ‘খেলারই অংশ, যা মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে নতুন অর্থ দেয়। তাই খেলাধুলাটা জরুরি। এতে ক্যালরি ব্যয় হয়, খেলাধুলার সূত্রেই পাড়া–প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয়। ফলে শিশুর সাংস্কৃতিক বোধও প্রসারিত হয়। গলির চার পাশে কি নোংরা আবর্জনা ছড়িয়ে; আশপাশে কোনও বাড়ি কি জরাজীর্ণ; পার্কগুলো কি নিরাপদ; পাড়ায় ধর্মসভায় কথা হচ্ছে বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা হচ্ছে, না কি শহীদ দিবস স্মরণের বা রবীন্দ্র–নজরুল জয়ন্তী নিয়ে সভা হচ্ছে, অভিবাদনের জন্য খাদ্য–বস্ত্র বিতরণের আয়োজন হচ্ছে এ সব কিছুই তাকে তার পারপাশ্বিক সমাজ–বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করে। সে সমাজমনস্ক হয়ে ওঠে। সংবেদনশীল সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মনন গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে।
মোবাইল, ট্যাব ধরিয়ে চার দেওয়ালে আটকে রাখা নয়, বাবা–মা যদি এই ধরণের যৌথ, সমষ্টিগত সামাজিক আখ্যানের সঙ্গে শিশুকে সংযুক্ত করেন, তা হলে সে দায়িত্বশীল সুস্থ নাগরিক হিসেবে বড় হয়ে উঠতে পারে, আমাদেরও ‘সামাজিক অবক্ষয় ‘ নিয়ে হা–হুতাশ করতে হয় না। শিশুরা যখন সমবয়সীদের সঙ্গে সময় কাটায়, তখন তারা ভাগাভাগি করা, সহযোগিতা, নেতৃত্ব, প্রতিযোগিতা এবং সমস্যার সমাধান করতে শেখে। এই প্রক্রিয়ায় তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। একটি শিশু যদি পড়াশোনায় মনোযোগী বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটায়, তবে সে নিজেও অনুপ্রাণিত হয়। যেমন রুবেল যদি নিয়মিত পড়াশোনা করে, তবে তার বন্ধু শাওনও তাকে দেখে পড়ায় মনোযোগী হতে পারে।
নৈতিক চরিত্র গঠন: সমবয়সী সঙ্গীরা যদি ভদ্র আচরণ করে, যেমন শিক্ষকের প্রতি সম্মান দেখানো বা বড়দের সাহায্য করা, তবে সেটি অন্য শিশুদেরও একই আচরণে উদ্বুদ্ধ করে। আবার, নেতিবাচক দিকও থাকতে পারে। যেমন বন্ধুদের মধ্যে কেউ যদি অসৎ আচরণ বা মিথ্যা বলাকে স্বাভাবিক মনে করে, তবে অন্য শিশুরাও তাতে প্রভাবিত হতে পারে। খেলতে গিয়ে বাচ্চারা যখন খেলনা ভাগ করে নেয়, তখন তারা সহযোগিতা ও ত্যাগের গুণ অর্জন করে।
পড়াশোনায় অনুপ্রেরণা: একজন মেধাবী ও মনোযোগী শিক্ষার্থীর সঙ্গে সময় কাটালে অন্যরাও পড়াশোনায় আগ্রহী হয়। নৈতিক গুণাবলি অর্জন– ভদ্রতা, সত্যবাদিতা, বড়দের সম্মান করা এসব গুণ সমবয়সী বন্ধুদের মাধ্যমে শিশুরা দ্রুত শিখতে পারে। সব সময় প্রভাব যে ভালো হবে তা নয়। ভুল সঙ্গও শিশুর চরিত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। অসদাচরণ শেখা– বন্ধুরা যদি মিথ্যা বলা, অসততা বা অবাধ্য আচরণকে স্বাভাবিক মনে করে, তবে শিশুর মধ্যেও এসব অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে। শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ—কিছু শিশু যদি পড়াশোনায় উদাসীন হয় এবং শুধু খেলাধুলা বা মোবাইলে সময় নষ্ট করে, তবে অন্যরাও তার প্রভাবে পড়াশোনা থেকে সরে যেতে পারে।
অভিভাবকের করণীয়: অভিভাবকদের উচিত সন্তানের সমবয়সী বন্ধুদের সম্পর্কে সচেতন থাকা। তাদের বন্ধুদের স্বভাব ও কার্যকলাপ বোঝার চেষ্টা করা জরুরি। একই সঙ্গে সন্তানকে সঠিকভাবে বোঝানো দরকার যে ভালো বন্ধু কেমন এবং খারাপ বন্ধুত্ব এড়ানো কেন প্রয়োজন।
অতএব, সন্তানের বেড়ে ওঠায় সমবয়সীদের প্রভাব অপরিসীম। তাই অভিভাবকদের উচিত সন্তানের বন্ধু নির্বাচন, তাদের কার্যকলাপ এবং পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রাখা। সঠিক সমবয়সী সঙ্গ শিশুকে ভালো মানুষ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।
লেখক: প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট।