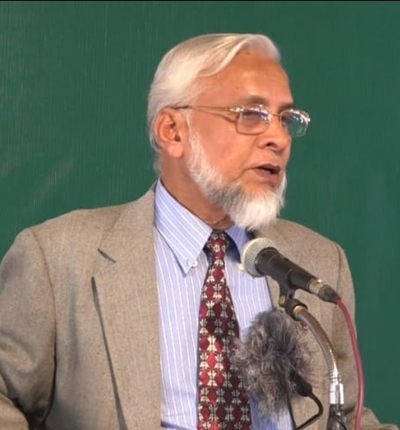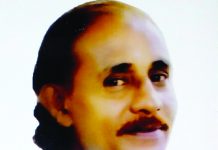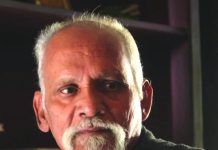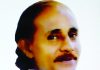আদিম মানব যুগের প্রাথমিক আচার–আচরণ থেকে আজকের কথিত সভ্য যুগীয় মানবাচরণে উত্তরণের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ, বিস্তৃত ও ঘটনাবহুল। ধর্ম বিশ্বাসীদের মতে সমাজ ও সময়ের প্রয়োজনানুসারে স্রষ্টা যুগে যুগে নবী রাসুল বা বার্তা বাহক বা মহামানব পাঠিয়ে মানবকুলে শুদ্ধতার অগ্রগতি চলমান রেখেছেন। আপাত সিদ্ধান্তে তার ধারাবাহিকতা ও পরিক্রমার ফলেই আজকের এই সমাজ নির্মিত হয়েছে। তেমনি, এক্ষেত্রে বিনির্মিত আধুনিক সভ্যতায় গ্রীক দার্শনিক মহামতি সক্রেটিসের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনার দাবি রাখে।
জ্ঞাতা মহল অদ্যাবধি এমনো একটি প্রশ্ন বা কৌতূহল পোষণ করে আসছে যে, বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস–জীবনের কর্ম, কথামালা বা তত্ত্বের বেশিরভাগই এখনো অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। এটা ঠিক যে তিনি কিছু লিখে যাননি অথবা লিখলেও তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। জেনোফেনের রচনা, প্লেটোর ডায়ালগগুচ্ছে তাদের নিজস্ব তত্ত্ব বা তথ্য লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সক্রেটিসকে যতটুকু উদ্ধৃত করা হয়েছে তা থেকেই আজ অবধি সক্রেটিসের পরিচয় এবং তত্ত্বখ্যাতি। এও অনুমান আছে যে এ্যাথেন্সে তাকে যেমন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তাঁকে নিয়ে সব কর্মকাণ্ড বা উদাহরণ প্রয়োগও দীর্ঘ সময়কাল ধরে বাহ্যত নিষিদ্ধ ছিল।
সক্রেটিসের জন্ম এথেন্সে ৪৬৯ বা ৪৭০ খ্রীষ্টপূর্ব সালে। এথেন্সের সম্ভ্রান্ত ১০টি প্রধান গোষ্ঠীর অন্যতম এ্যালোপেকি গোষ্ঠীর এক সঙ্গীন পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা সপ্রেনিস্কস্ একজন ভাস্কর ছিলেন। সক্রেটিসও প্রথম জীবনে ভাস্কর্যকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেন। অন্যদিকে সক্রেটিস ভারী অস্ত্রে সজ্জিত পদাতিক বাহিনীতেও কাজ করেছিলেন।
সক্রেটিসের মা ফেনারিটি একজন প্রশিক্ষিত ধাত্রী ছিলেন। পরবর্তীতে সক্রেটিস নিজেকে সত্য, ন্যায় ও বিবেকের ধাত্রীরূপে বর্ণনা করতে চাইতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল জানথিপি – যিনি ইতিহাসে বদমেজাজী ও ঝগড়াটে মহিলা বলে চাউর আছে। যদিও প্লেটোর রচনায় এর কোন সমর্থন মেলে না। সত্তর বছর বয়সে সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় তাঁর তিন সন্তান ল্যাক্সোক্লিস, সফ্রেনিস্কস্ ও মিনিক্সিনস্ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলো। ধনৈশ্বর্যের সাধ না থাকায় সারাজীবন তাঁকে সচ্ছলতা ও দারিদ্রের মাঝামাঝি অর্থনীতির কঠিন রেখায় থেকে জীবন যাপন করতে হয়েছে।
অতি সংক্ষেপে তাঁর জীবন ও চিন্তা–তত্ত্ব:
সক্রেটিস জিতেন্দ্রীয় পুরুষ ছিলেন। তিনি বুদ্ধি ছাড়া কোন বৃত্তির বশ্যতা স্বীকার করেন নি কখনো। তাঁকে পুরুদস্তুর স্বশিক্ষিত দার্শনিক বলা যায়।
এথেন্সের বাজারের মধ্য দিয়ে হাঁটার সময় দু’পাশের ভোগ্যপণ্য দ্রব্যের দিকে নির্দেশ করে বলতেন, “এসবের কোন কিছু আমার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই।”
সক্রেটিস চাইতেন যোগ্যলোক যোগ্যস্থানে থাকুক। তাই তাঁর স্পষ্ট যুক্তি “জুতাজোড়া মেরামত করতে চাইলে চর্মকারের কাছে যেতে হবে। তেমনি রাষ্ট্র নামক জাহাজটি বিগড়োলে কাকে দিয়ে কাজ করাবো”? এখানে তিনি যোগ্য, দক্ষ, জ্ঞানী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।
নিজে যা সত্য বলে জেনেছেন, তা পৃথিবীর কেউ স্বীকার না করলেও তিনি অনড় থেকেছেন। পৃথিবীর নির্ভীকতম যোদ্ধাও এই নিরীহ শত্রুহীন বৃদ্ধ সত্রেটিসের চেয়ে নির্ভীকতর নয়।
বেঁটে মোটা গড়নহীন থ্যাবড়া নাক উঁচু কপালে, ডেবডেবে চোখওয়ালা একজন মানুষ ছিলেন সক্রেটিস।
একটি বিশেষ বিষয় – বাল্যকাল থেকেই তিনি নাকি একটি নৈর্ব্যক্তিক কন্ঠস্বর বা শব্দ শুনতে পেতেন। সেই সংকেত নির্দেশমূলক নয়, নিষেধসূচক। মাঝে মাঝে তাঁর বাহ্যজ্ঞান শুন্য হয়ে পুলক–মূর্চ্ছা বা ভাবালেশ দেখা দিতো। সেই সময় তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা, এমনকি কোন একটি সময়ে প্রায় বিশ ঘন্টা ঠাই দাঁড়িয়ে থাকতেন। শত ডাকাডাকিতেও সাড়া পাওয়া যেতো না। এ ছাড়াও বিশেষ পদ্ধতির আচরণ ও ডায়োলেকটিক পদ্ধতির কথোপকথনের জন্য পঁচিশ বছর বয়সেই সক্রেটিস তাঁর কালের সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
সক্রেটিস তাঁর দর্শনের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন প্রকৃতি নয় –মানুষ। ধর্ম, নৈতিকতা, জ্ঞানই হলো তাঁর প্রধান আলোচনা ও অনুসন্ধানের বিষয়। তাঁর মতে ন্যায় বিচার, কর্তব্য–অকর্তব্য ভালোমন্দ ইত্যাদি প্রশ্নে মনস্থির করতে না পারলে সুশৃঙ্খলভাবে সমাজে বসবাস করা অসম্ভব। এখানেই তাঁর প্রচলিত প্রবাদ ‘নিজেকে জানো’ কথাটার মূল নিহিত।
সক্রেটিসের মতে – অপরীক্ষিত জীবন, যাপন করারই যোগ্য নয়। কর্তব্য–অকর্তব্য, উত্তম–অনুত্তম এর আদর্শ খুঁজলোনা যে মানুষ, ন্যায়–অন্যায়; ভালোমন্দ; সুন্দর–কুৎসিত; শ্রেয়–পরিত্যাজ্য স্থির করতে পারলো না যে, তার বেঁচে থাকাতো উদ্ভিদ বা কীট পতঙ্গের বেঁচে থাকারই সামিল।
অন্যদের উন্নত করার এবং চুম্বকের মতো আকর্ষণ শক্তি ছিল সক্রেটিসের। তাঁর সান্নিধ্যে এলে মোহগ্রস্ত, অভিভূত এবং পরাস্ত না হয়ে উপায় থাকতো না কারো। তাঁর সঙ্গে আলাপের পর জ্ঞান গর্বিত ব্যক্তিটির মনেও দেখা দিতো এক প্রচণ্ড লজ্জাবোধ এবং তা ছিল নিজের অজ্ঞানতার মধ্যে ডুবে থাকার লজ্জাবোধ, দেখা দিতো এক ধরনের হীনতার লজ্জাবোধ।
‘ধারণা’ অবিনশ্বর। যেমন, বিশ্বের যাবতীয় সুন্দর বস্তু ধ্বংস হয়ে গেলেও সুন্দরের যে ‘ধারণা’ তা বিনাশ হবে না। সুতরাং কোন চিন্তা বা গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য হওয়া উচিত ‘ধারণা’ অর্জন।
তাঁর মতে প্রকৃত দুর্ভাগ্য -‘একটি মন্দ কাজ করা’। অন্যদিকে প্রকৃত সুখও -‘একটি ভালো কাজ করা’। যে মানুষ ভালো কি মন্দ তা বাস্তব অর্থে জেনে থাকে, সে ইচ্ছে করে মন্দকে পছন্দ করতে পারে না।
ভালো মানুষ মন্দ মানুষের চেয়ে প্রবল, এবং মন্দ মানুষ কখনোই কোন(ভালো) মানুষের ‘প্রকৃত ক্ষতি’ করতে পারে না। কারণ প্রকৃত ক্ষতি হচ্ছে আত্মিক ক্ষতি। সে রকম ক্ষতি অন্যের দ্বারা নয়, একমাত্র নিজের মন্দ কাজের ফলেই ঘটতে পারে।
সক্রেটিসের মতে ভালোত্ব – ‘আত্মার স্বভাবের অঙ্গীভূত এবং এই কারণে ভালো মানুষের পক্ষে মন্দ করা বা অন্যের ক্ষতি করা সম্ভব নয়। ভালোত্বকে তিনি দু’ভাগে ভাগ করেছেন। এক – ‘লৌকিক ভালোত্ব’, দুই – ‘দার্শনিক ভালোত্ব’। লোকিক ভালোত্ব হচ্ছে দৈনন্দিন আচরণে ভালোত্ব, অভ্যাস যার ভিত্তি। যা ইন্দ্রিয়–প্রত্যক্ষের মতোই অস্থির ও পরিবর্তনশীল। আর দার্শনিক ভালোত্ব হচ্ছে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা স্থির ও অপরিবর্তনশীল।
এথেন্সের দৈনন্দিন আচরণীয় ধর্মের সঙ্গে সক্রেটিসের সস্বন্ধ থাকা আদৌ সম্ভব ছিল না। তাই তাঁর বিরুদ্ধে অধার্মিকতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। অথচ তাঁর একটা নিজস্ব ধর্মমত ছিলো। অন্যদিকে উল্লেখযোগ্য যে, (প্রায় সমসাময়ীককালে) ভারতবর্ষের বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে এর আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।
তাঁর মতে প্রকৃত জ্ঞান পেতে হলে দেহের ফাঁদ থেকে রেহাই পাওয়া প্রয়োজন। দেহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ বিশুদ্ধজ্ঞান লাভের কোন আশা নাই সত্য, তবে এই মর্তের জীবনেও দৈনন্দিন মৃত্যুর একটি অভ্যাস করা যায়। এই রক্তমজ্জার দেহকে অতিক্রম করে অল্প সময়ের জন্য হলেও চিরন্তণ সত্তার জগতকে তার স্বরূপে অবলোকন করা যায়। এইভাবে দেহমুক্ত অবস্থায় (মেডিটেশনের মাধ্যমে) আত্মিক অমরত্বের পুর্বস্বাদও পাওয়া যেতে পারে।
সক্রেটিসের কাছে জ্ঞান ও ভালোত্ব অভিন্ন ছিলো। ভালোত্বের জ্ঞান ছাড়া ভালোত্ব অর্জন করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জ্ঞান ছাড়া সঠিক পথে রাষ্ট্র কোন মতেই পরিচালিত হতে পারে না।
একভাবে, সক্রেটিস মানুষকে দুইভাগে ভাগ করেছেন – বোকা ও বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমানরা সত্য ও অসত্য, ন্যায় ও অন্যায়ের পরিণাম সম্পর্কে ধারণা করতে পারে। অন্যদিকে বোকারা তা পারে না বলেই যাবতীয় অন্যায় অনাচার অপরাধ সংঘটনে বাধ মানে না।
মজার ব্যাপার এই যে, সক্রেটিস জন্মেছিলেন এথেন্সের গণতন্ত্রের যৌবন বা গৌরবকালে। অথচ সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে তিনি কোনভাবেই মেনে নিতে পারেন নি। পরবর্তীতে চলমান গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে সর্বশুদ্ধ এই মানুষটিকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়।
এথেনীয় আইনে নির্দেশ ছিল যে, অভিযুক্ত ব্যাক্তির পক্ষে পাল্টা বা বিকল্প শাস্তির প্রার্থনা করা যেতো। সক্রেটিস এই সুযোগটি গ্রহণ করে মৃত্যুদণ্ডের বদলে কাছাকাছি কোন একটা শাস্তি কারাদণ্ড বা নির্বাসন চাইতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, তেমন কিছু করলে প্রকারান্তরে মিথ্যা অভিযোগকেই স্বীকার করা হয়।
সক্রেটিসের কথা – “মৃত্যুকে আমি এক তিলও পরোয়া করি না, কিন্তু অন্যায়কে পুরোপুরিই করি। তাই ভাবলাম, কারাদণ্ড ও মৃত্যুর ভিতর দিয়ে হলেও আইন ও ন্যায় বিচারের পক্ষে থাকবো।”
সক্রেটিসের মৃত্যু হয়েছে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। এতটুকু অতিশয়োক্তি করে বলা যায় যে, পশ্চিমী সভ্যতার আজ যা কিছু শ্রদ্ধেয়, বুদ্ধির মুক্তি, সত্যের প্রতি অবিচল, নিষ্ঠা, গভীর স্বদেশ প্রেম, মানব কল্যাণের আদর্শ, সুতীক্ষ্ণ নির্মম নির্মোহ আত্মবিশ্লেষণ, প্রবল জীবন তৃষ্ণা – এসবের একটা প্রধান উৎস হচ্ছে সক্রেটিসের দর্শন এবং সন্দেহ নাই সক্রেটিস নামক মানুষটি।
সক্রেটিস নিজের অর্জিত বা আচরিক বৈশিষ্ট প্রতিষ্ঠায় প্রথাগতভাবে কোন শ্রেণি বা গোষ্ঠী সৃষ্টির চেষ্টা বা চিন্তা মাত্র করেন নি। সে জন্যই হয়তোবা মানব গোষ্ঠীর জন্য কল্যাণকর তাঁর আবিষ্কৃত দর্শন বা তত্ত্ব সমূহ ধর্ম, গোষ্ঠী ও স্থান নির্বিশেষে সর্বকালীন সর্বজনীন ভাবেই গ্রহণযোগ্য পথনির্দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সর্বক্ষেত্রে তাঁর অনুসৃত নীতিমালা সমাদৃত হচ্ছে ‘সুশিক্ষার মৌলিক আকর’ স্বরূপ। সুতরাং কালের পর কাল উত্তরোত্তর মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে সক্রেটিসের প্রাসঙ্গিকতা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বৃদ্ধিই পেয়ে চলেছে।
তথ্যপঞ্জি: সক্রেটিস : হাসান আজিজুল হক; History of Western Philosophy – B Russell; A Critical History of Greek Philosophy – W.T Stace ; The Greek Thinkers- Jhon Burnet ; Outlines of History of Greek Philosophy – Edward Zeller , The Greek Wey of Western Civilization – Edith Hamilton ; The Greek Philosophy -W.K.C Guthrie A history of Political Theory – George H. Sabina Westen Political thought – john Bowte Dialogues of Plato
লেখক : শিক্ষা–সংগঠক; প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট