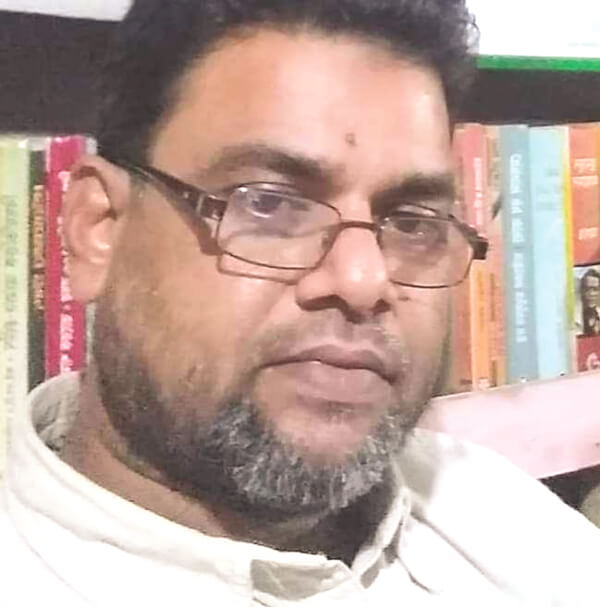আধুনিক দুনিয়ায় সংবাদমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত হলেও এর সংশ্লিষ্ট কর্মীরা বরাবরই ঝুঁকিতে অবস্থান করেন। বাংলাদেশের সামপ্রতিক সরকারি বেসরকারি ভূমিকা এই ঝুঁকিকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে। বলা চলে – সমকালীন বাংলাদেশে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পেশার নাম সাংবাদিকতা।
সংবাদকর্মীদের উপর নানামুখী নিপীড়ন সব আমলেই চলেছে। অপমান অপদস্থ তো হয়েছেন –ই, অপমৃত্যুর স্বীকারও খুব কম হননি। কোনও সংবাদ কিংবা সংবাদ বিশ্লেষণ যখনই যাদের বিপক্ষে গেছে, তারাই হিংস্র পশুর মতো হামলে পড়েছে সংবাদকর্মীদের উপর। স্বাধীনতার পর থেকেই সংবাদমাধ্যম শাসকদের চোখ রাঙানি সয়ে চলছে। মাত্রাটা কখনও বেড়েছে কখনও কিছুটা শ্লথ হয়েছে, কিন্তু নিপীড়ন বহালই থেকেছে।
সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা বিষয়টা আমাদের মহান সংবিধানে স্বীকৃত আছে। তারপরও সংবাদমাধ্যম সেই স্বাধীনতা নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোগ করতে পারেনি, পারে না। এর জন্য সরকার যতোটা দায়ী, ঠিক ততোটা দায় সরকারের বিরোধী পক্ষেরও। প্রত্যেকেই স্ব স্ব সুবিধা ও দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে সংবাদমাধ্যমের উপর চড়াও হয়।
আমাদের দেশে মিডিয়া বয়কটের একটা মেনিয়া চালু হয়েছে। বিচ্ছিন্ন মন্তব্যের জের ধরে মিডিয়ার বয়কটের ডাক দেয় একটি মহল। আবার একটি সংবাদ বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক পত্রিকা বয়কটের ডাকও দেয়। সংবাদ বিশ্লেষকেরা পর্যন্ত হামলার শিকার হন মাঝেমাঝে। বয়কট ও হামলার ঘটনাকে কি একই সূত্রে বিশ্লেষণ করা যায় না? যায়, কিন্তু সেটিকে আমলে নেওয়া হবে না রাজনৈতিক মতপার্থক্যের অজুহাত দেখিয়ে।
বয়কট যেমন সমাধান নয়, তেমনি এটা ভদ্রোচিতও নয়। বয়কটের ডাক দেয়াটাও নাগরিক অধিকার হয়তো, কিন্তু বাকস্বাধীনতা তথা মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে আমলে নিলে এটিকে পলিটিক্যাল মেনিয়াই বলা চলে। এই পলিটিক্যাল মেনিয়া থেকেই জন্ম নিচ্ছে সংবাদমাধ্যমের প্রতি নাগরিক অসহিষ্ণুতা। এই অসহিষ্ণুতা উস্কে দিচ্ছে সহিংসতাকে। সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ছে গোটা জনপদে। ঝুঁকি বাড়ছে সংবাদকর্মে। সংবাদকর্মকে ঝুঁকিমুক্ত করার কর্মসূচী প্রণয়নটা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংবাদমাধ্যমের কর্তাব্যক্তিরা যতো দ্রুত এটা করতে যাবেন, ততোই মঙ্গল হবে মিডিয়ার।