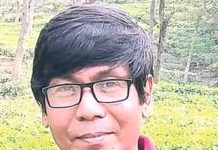সারা বিশ্বে ২৭.৬ কোটির বেশি মানুষ বাংলা ভাষা ব্যবহার করে তাই বাংলা বিশ্বে ষষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন হচ্ছে চর্যাপদ। প্রাচীন বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলির সন্ধানে চর্যাপদ নিয়ে ১৯২৬ সালে ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রথম বিজ্ঞানসম্মত আলোচণা করেন তাঁর The orgin and development of the Bengali language গ্রন্থে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বলেছেন বাংলা ভাষার যে সমস্ত বাগভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গি তার নিজের বিশেষত্ব তা
চর্যাপদেও উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে মিশনারীদের দ্বারা বাংলা গদ্যের শুরু হয়। কাজী মোতাহার হোসেন চৌধুরী বাংলা গদ্য সৃষ্টির পেছনে শ্রীরামপুর মিশন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতি মিশনারীদের অবদান উল্লেখ করেন। তাছাড়া রামবসু, রাজা
রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মীর মোশারফ হোসেন প্রমুখের ধারাবাহিক সাধনায় বাংলা ভাষা নতুন রুপ পরিগ্রহ করে। বিশ শতকে এসে বাংলা ভাষার গতি সঞ্চারিত হয় প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী
নজরুল ইসলাম এবং অন্যান্যদের প্রচেষ্টায়। খৃষ্টান মিশনারীগণ ধর্ম প্রচারের জন্য বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন করেন এতে কোনও সন্দেহ নেই। ১৭৭২ সালে হেলহেড সিভিলিয়ান হয়ে বাংলাদেশে আসেন এবং ১৭৭৮ সালে ইংরেজিতে Grammar of Bengali language রচনা করেন। চার্লস উইলকিনসের
অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বাংলা হরফযুক্ত মুদ্রণযন্ত্র সৃষ্টির মাধ্যমে এই বইয়ের বাংলা মুদ্রণ সম্ভব করেন। উইলকিনস বাঙালি কর্মকার পঞ্চাননকে বাংলা হরফ নির্মাণ বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন। ইংরেজ আমলে যতি, ছেদ চিহ্নের ব্যবহার এবং ছন্দের সাথে পদ্য রচনার প্রচলন বাংলা ভাষাকে কয়েক ধাপ এগিয়ে
নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল প্রাপ্তিতে বাংলা ভাষা বিশ্ব দরবারে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারি ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।
অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ১৯৬৫ সালে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে বাংলা টাইপরাইটারের জন্য উন্নতমানের কি–বোর্ড উদ্ভাবন করেন যার নাম ‘মুনীর অপটিমা’।
প্রাচীনকাল থেকে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে সাহিত্য চর্চার একমাত্র মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। এজন্য প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ উপস্থিত। মুসলিম শাসনের শুরুতে বাংলা ভাষায় আরবি, ফারসি ও তুর্কি ভাষার প্রভাব দেখা যায়। ১৪৮৭ সালে ভাস্কো–ডা–গামার ভারতে আগমনের পর থেকে
পর্তুগিজ শব্দ বাংলা ভাষায় যুক্ত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমনের ফলে এবং ইংরেজদের ২০০ বছরের শাসনামলে অনেক ইংরেজি শব্দ বাংলায় প্রবেশ করে।
ভারতবর্ষে উর্দুর জন্ম মুঘল শাসনামলে। মূলতঃ সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাধারণ ভাষা হিসেবে হিন্দি, ফারসি ও আরবি ভাষার সংমিশ্রণে উর্দুর আবির্ভাব হয়। উর্দু লিখা হতো ফারসি বর্ণমালায়। যেহেতু মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর উদ্যাগে উর্দুর জন্ম তাই কালক্রমে উর্দু শাসকশ্রেণির এবং মুসলমান অভিজাত শ্রেণির
ভাষায় পরিনত হয়। বৃটিশ আমলে সরকারি ভাষা হিসেবে ফারসি পরিত্যক্ত হলে উর্দুর প্রচলন বেড়ে যায়। আর বনেদী মুসলমানগন উর্দুকে সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। ভারতে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা হিন্দিকে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তুতি নিলে মুসলীমলীগের নেতৃবৃন্দ উর্দুকে
রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় আলোচনার অবতারণা করেন। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৪.৬০% মানুষের ভাষা বাংলা আর ৭.২% এর ভাষা উর্দু হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বলেন ‘উর্দু’ একমাত্র
উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। জিন্নাহর মুখের উপর বঙ্গবন্ধু এবং টাঙ্গাইলের শামসুল হক সর্বপ্রথম প্রতিবাদ করে বলেছিলেন ‘না’ উর্দু নয় বাংলাই হবে রাষ্ট্রভাষা। যেজন্য বঙ্গবন্ধুকে কারাবরণ করতে হয় এবং ঢাকা বিশ্ব্বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতিসত্ত্বাকে ধ্বংস করার জন্য ও
শিক্ষাদীক্ষায় বাঙালিদের পশ্চাতে ফেলার জন্য ও বাঙালি সংষ্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য জোরপূর্বক বাংলা ভাষার উপর আঘাত হানে। ফলশ্রুতিতে বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রসমাজ তমুদ্দিন মজলিস ও সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার জন্য আন্দোলনে ঝাপিয়ে
পড়ে। যার ফলে ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবীতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউরসহ অনেকেই শহীদ হন এবং তাদের প্রাণের বিনিময়ে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়। পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলনের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বাঙালি দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন
করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ১৯৭০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমির একুশের অনুষ্ঠানমালা উদ্বোধনকালে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে সেদিন থেকেই সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হবে। তাতে যদি ভুলও হয় তবে পরে তা সংশোধন করা হবে’। আদালতের রায় বাংলায় লিখার
নির্দেশ দেন বঙ্গবন্ধু। আমার দেখা নয়াচীন গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু বলেন, চীনের বিশ্ববিদ্যালয় গিয়ে আমাদের দলনেতা পীরসাহেব উর্দুতে বক্তৃতা করলেন এবং ফজলুল হক সায়েদা তা ইংরেজি করে দিলেন। আর চীনের বিশ্ব্বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর চীনা ভাষায় বক্তৃতা করলেন, দোভাষী তা ইংরেজি করে দিলেন, আমি
দেখলাম দুয়েক জায়গায় দোভাষী ভালো ইংরেজি করতে পারছে না, সেখানে ভিসি নিজেই ওকে ইংরেজি করে দিচ্ছে। ভদ্রলোক ভালো ইংরেজি জেনেও জাতীয় ভাষায় কথা বলেন। আমরা বাঙালিরা ভালো বলতে না পারলেও ইংরেজি আর উর্দু বলার জন্য পাগল হয়ে যাই।
বঙ্গবন্ধু একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক ছিলেন। ইংরেজি জানা সত্ত্বেও ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু বাংলায় বক্তৃতা করেন। ১৯৭৫ সালর ১২ মার্চ সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে জারীকৃত একপত্রে বঙ্গবন্ধু লিখেছিলেন, ‘মাতৃভাষার প্রতি যার ভালোবাসা নেই, দেশের প্রতি যে তার ভালোবাসা আছে
একথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়’। ১৯৮৭ সালে ‘বাংলা ভাষা’ প্রচলন আইন বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্রীয় কাজে বাংলার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তথাপি দুঃখজনক হলেও সত্য এর প্রয়োগ নেই। সর্বত্র ইংরেজি ও ভুল বানানের ছড়াছড়ি। ফেব্রুয়ারি মাস এলেই বাঙালিদের বোধোদয় হয়, ইংরেজি সাইনবোর্ডের
উপর বাংলা ব্যানার ঝুলিয়ে দেয়, আবার মাস শেষে খুলে নেয়। হরহামেশাই নজরে আসে যানবাহন, সাইনবোর্ড, দেয়াল লিখন, অফিস, বইপুস্তক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সর্বত্রই ভুল বানানের ছড়াছড়ি। এমনকি নীতিবাক্যও ভুল বানানে লিখে প্রচার করা হয় যা দণ্ডনীয় অপরাধ। শুধু ফেব্রুয়ারি নয় সবসময় বাংলার
ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারিভাবে নজরদারীর জন্য মনিটরিং সেল করা উচিত। প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের নাম সাইনবোর্ডে বাংলার নিচে ইংরেজি থাকতে পারে। তবে ভুল বানান এবং শুধুমাত্র ইংরেজি সাইনবোর্ড রাখার ক্ষেত্রে জরিমানার ব্যবস্থা করলে মানুষ সতর্ক হবে এবং বাংলা ভাষার স্বকীয়তা রক্ষা পাবে।
উল্লেখ্য আলবার্ট আইনস্টাইন নিজ দেশ জার্মানির নাগরিকত্ব ত্যাগ করে সুইজারল্যান্ড ও আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর সময় বিড়বিড় করে জন্মভূমির জার্মান ভাষায় শেষ কথা বলে গেছেন যা পাশে থাকা কেউই বুঝতে পারেনি। নিজ ভাষার প্রতি তাঁর যে টান তিনি মৃত্যুর সময় প্রমাণ করে গেছেন। দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। আর দেশপ্রেমের পূর্বশর্ত হচ্ছে ভাষাপ্রেম। তাই বলি—
শুদ্ধ বাংলা চর্চা করি, দেশপ্রেমে জীবন গড়ি’।
লেখক: উপাধ্যক্ষ, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, চট্টগ্রাম।