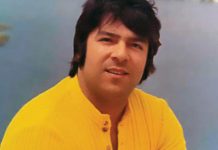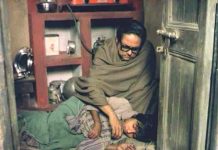বাংলাদেশের সমকালীন চিত্রকলার প্রেক্ষাপটে বিমূর্ত শিল্প একটি স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে বহু দশক ধরে শিল্পীদের আত্মপ্রকাশ ও চিন্তার মুক্তভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামপ্রতি ধানমন্ডিস্থ সফিউদ্দিন শিল্পালয়ে প্রদর্শিত শিল্পী মুহাম্মদ মনসুর কাজীর তৃতীয় একক চিত্রপ্রদর্শনী ‘বিমূর্তের সহাবস্থান’ এই ধারার একটি সতেজ ও আত্মবিশ্লেষণমূলক সংযোজন বলা চলে। এই শিল্পীর শিল্পভাষায় বিমূর্ততা নিছক আকার, রং বা গঠনের খেলা নয়, বরং অনুভূতির, স্মৃতির এবং দর্শনীয় এক জার্নাল।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা ইন্সটিটিউটে এম ফিল অধ্যায়নরত শিল্পী মনসুর কাজীর চিত্রে আমরা দেখি পরিপক্ব বিমূর্ত ভাষা, যেখানে আকার, বর্ণ এবং টেক্সচারের সংমিশ্রণে গড়ে উঠে এক অন্তর্মুখী অভিজ্ঞতা। বিশেষত প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া তার “Emotion Series” এবং “Face Series” চিত্রকর্মে বিমূর্ততার মধ্যেও অনুভবযোগ্য কাঠামো লক্ষণীয়–যা জ্যামিতিক রূপরেখা, ধূসরতা ও একধরনের মেটালিক অনুভবের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মানসিক সংঘাত ও আত্ম–অনুসন্ধানের প্রতীক হয়ে ওঠে।
তার কাজে রয়েছে দেশের খ্যাতিমান শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়ার সুশৃঙ্খল বিমূর্ততার প্রভাব, আবার শিল্পী শফিকুল ইসলামের মতো পৃষ্ঠতলের সংগঠনে রয়েছে কোলাজধর্মী গভীরতা। কোথাও কোথাও শিল্পী মোহাম্মদ ইউনুসের গড়নের শক্তিমত্তা এবং রঙের রুক্ষতা প্রতিধ্বনিত হয়। তবে মনসুর কাজী এসব প্রভাব ছাপিয়ে নিজের একটি স্বর গড়ে তুলেছেন, যেখানে রয়েছে নগর বাস্তবতা, স্মৃতির অবয়ব, এবং ব্যক্তিগত নৈঃশব্দ্য।
বিশ্ব চিত্রকলার ক্ষেত্রে মার্ক রথকো, পল ক্লে কিংবা ভাসিলি কান্দিনস্কির মত শিল্পীদের বিমূর্ততায় যেমন এক আধ্যাত্মিক স্তর কাজ করেছে, মনসুর কাজীর কাজে তেমন কোনো প্রত্যক্ষ ধর্মীয় অনুষঙ্গ না থাকলেও এক প্রকার ধ্যানমগ্নতা, নিস্তব্ধতা ও আত্মসংলাপ পরিলক্ষিত হয়। এটি তার কাজকে শুধু ফর্মাল বিমূর্ততা থেকে আলাদা করে তোলে না, বরং ব্যক্তিক অস্তিত্বচর্চার দলিল হিসেবেও দাঁড় করায়।

উদাহরণস্বরূপ, তাঁর একটি চিত্রে টেক্সচারের ব্যবহারে গঠিত ধূসর অবয়ব যেন এক প্রাচীন দেয়ালের প্রতিচ্ছবি–যেখানে সময়ের ক্ষয়িষ্ণুতা ও জ্যামিতিক বিভাজনে ফুটে ওঠে এক পরিপাটি বিশৃঙ্খলা। অন্য একটি ছবিতে দেখা যায় মুখাবয়বের বিমূর্তকরণ, যা চেনা থেকে অচেনায় রূপান্তরিত হয়ে আমাদের আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন তোলে। এই কাজগুলো যেন শিল্পীর একটি অন্তর্দৃষ্টি–নিবদ্ধ আত্মজিজ্ঞাসার ফলাফল।
চট্টগ্রামে বেড়ে উঠা মনসুর কাজীর চিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁর রঙের ব্যবহার: মাটির রঙ, ধাতব ছায়া, কালো–ধূসর প্যালেট–সবকিছু মিলে এক নিরব অথচ তীব্র ভাষ্য নির্মাণ করে। বিশেষত লাল রেখার সন্নিবেশ যেন একটি অন্তর্গত স্পন্দনের প্রতিধ্বনি, যা দর্শকের সঙ্গে সংলাপে আবদ্ধ হয়।
তবে কিছু কাজ অতিরিক্ত বিমূর্ততার দিকে ঝুঁকে গিয়ে দর্শকের সাথে সংযোগে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে । কখনো টেক্সচারের স্তর এত বেশি হয়ে যায় যে মূল রূপ বা রঙের আবেদন ম্লান হয়ে যায়। হয়তো এখানেই শিল্পীর আগামী কাজগুলোতে আরও পরিশীলন ও ভারসাম্যের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। কিছু চিত্রে অতিরিক্ত কাঠামোগত ভার এবং ঘনত্ব পাঠকের বোধে অনুপ্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে । বিশেষত যেখানে রঙ ও রূপরেখার ভারসাম্য কিছুটা পরিমিতির বাইরে চলে গেছে ।
শিল্পীর নিজের ভাষ্যমতে “একজন শিল্পী হওয়া মানে হলো সবকিছু… মাধ্যম, সময় বা বয়স–কিছুই গুরুত্বপূর্ণ না। প্রতিদিন কাজ করে যেতে হয়।”এই বক্তব্যই তার দৃঢ় সংকল্প ও ধারাবাহিক সৃষ্টিশীলতার সাক্ষ্য বহন করে।
পরিশেষে, মুহাম্মদ মনসুর কাজীর বিমূর্ত চিত্রভাষা বাংলাদেশের বিমূর্ত শিল্পের ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে তাতে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করছে। তার কাজ কেবল রঙের খেলায় সীমাবদ্ধ নয়–এগুলো সময়, স্মৃতি ও আত্মচেতনার এক অন্তর্মুখী ভাষ্য। এই ধারাবাহিকতা রক্ষায় শিল্পীর সৃজন আরও পরিণত ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে–এই প্রত্যাশাই রইল।
ইমেইল : ziatg@yahoo.com