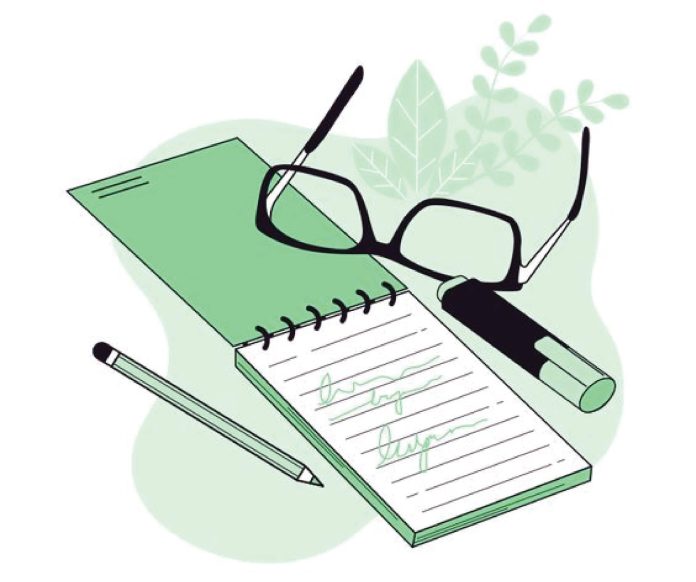দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আবারও ৩০ বিলিয়ন ডলারের ঘরে ফিরেছে বলে পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা গেছে। খবরে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, ১৬ জুলাই পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ২ কোটি ৬৬ লাখ ২০ হাজার ডলার বা ৩০ দশমিক ০২ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান জানান, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ব্যালান্স অব পেমেন্ট অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন ম্যানুয়াল (বিপিএম–৬) অনুযায়ী রিজার্ভের পরিমাণ ২ হাজার ৪৯৯ কোটি ৫৪ লাখ ৫০ হাজার ডলার, অর্থাৎ প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলার। আর বাংলাদেশ ব্যাংকে নিজস্ব হিসাব অনুযায়ী দেশের রিজার্ভের পরিমাণ এখন আবারও ৩০ বিলিয়ন (৩০.০২ বিলিয়ন) ডলার ছাড়িয়েছে। এর আগে গত ৩ জুলাই পর্যন্ত দেশে মোট রিজার্ভ ছিল ৩১ দশমিক ৫৭ বিলিয়ন ডলার এবং বিপিএম–৬ অনুযায়ী তা ছিল ২৬ দশমিক ৫১ বিলিয়ন ডলার। ওই সময় ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ ছিল ২০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। এদিকে জুলাই মাসের শুরুতে বাংলাদেশ ব্যাংক এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) সদস্যদের কাছে ২ দশমিক ০২ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করেছে। এত বড় অঙ্কের পরিশোধের পরও রিজার্ভে বড় ধাক্কা লাগেনি। বরং রিজার্ভ স্থিতিশীল রয়েছে এবং ১৬ জুলাই শেষে তা দাঁড়ায় ২৯ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন ডলারে। বিপিএম–৬ অনুযায়ী হিসাব করলে সেই সময় রিজার্ভ ছিল ২৪ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন ডলার। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করছে, রপ্তানি আয় এবং রেমিট্যান্সপ্রবাহ ইতিবাচক থাকায় রিজার্ভে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে।
বিশেষজ্ঞরা বলেন, নানা সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে দেশের অর্থনীতি। কয়েক বছর ধরেই স্মরণকালের উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা, ডলার সংকট, রিজার্ভের ক্ষয়, বিনিয়োগ খরা, রাজস্ব ঘাটতি, ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি, ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি ও অনিয়ম–দুর্নীতি, বিদ্যুৎ–জ্বালানি খাতের লুটপাট, অব্যবস্থাপনাসহ অর্থনীতি বিভিন্ন সংকটে নিমজ্জমান। গত বছরের আগস্টের ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থানে সরকার পরিবর্তনের পর বিভিন্ন খাতে অস্থিরতা বাড়তে থাকে। তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন খাতের বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হতে থাকে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এত দিন পর্যন্ত বেশকিছু বাণিজ্যসহ বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধা পেয়েছে। বাণিজ্য ও অনুদানের ক্ষেত্রে সুবিধা পেয়েছে। উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পর যেমন চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে তেমনি সুযোগও তৈরি হবে। তখন আগের পাওয়া সুবিধাগুলো পাওয়া যাবে না এবং আরো শক্তিশালী দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা করতে হবে। শুধু পোশাক শিল্পের ওপর নিভর্র না করে বাংলাদেশের রফতানি পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ ও রফতানি পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ অর্থনীতিকে আরো চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে।
তাঁরা বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে হলে রেমিট্যান্স ও রপ্তানি বৃদ্ধির বিকল্প নেই। রেমিট্যান্স বৃদ্ধি করতে হলে বিদেশে বেশি বেশি লোক পাঠাতে হবে। আর রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশকে উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে হলে বেশি করে শিল্পায়ন করতে হবে। ব্যাপক শিল্পায়নই কেবল একটি দেশকে অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে পারে। শিল্প উদ্যোক্তারা নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপনের মাধ্যমে লোকজনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, নতুন পণ্য উৎপাদন করে দেশের চাহিদা মিটায়, আবার সেই পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। ফলে তারা একদিকে আমদানি কমিয়ে পরনির্ভরতা কমায়, অপরদিকে পণ্য রপ্তানি করে দেশকে এগিয়ে নেয়। সুতরাং উদ্যোক্তাদের সার্বিক সহযোগিতা দিতে হবে। শিল্পকারখানায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের যোগান দিতে হবে। ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা করতে হবে।
অর্থনীতিবিদরা এটাও বলছেন, কেবল রেমিট্যান্স ও রফতানি আয়ের প্রবৃদ্ধি দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধির ধারায় এগিয়ে নেওয়া যাবে না। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হলে অবশ্যই বিদেশী বিনিয়োগ নিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগও বাড়াতে হবে। যেকোনো দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রধান শর্ত আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। কিন্তু এ দুটি উপাদানই এ মুহূর্তে বাংলাদেশে অনুপস্থিত। এজন্য সুস্থির পরিবেশ জরুরি।