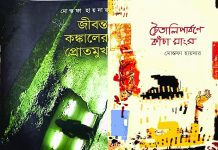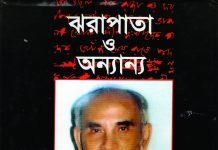মুক্তিযুদ্ধের সময় ইয়াসমিনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্পে। নয় মাস পর সে যখন ফিরে এল, স্বাধীন দেশের অনেক কিছুই তখন বদলে গেছে। কোথাও আশ্রয় মেলেনি তাঁর। না পরিবার, না প্রেমিক, না সমাজ কেউই গ্রহণ করল না তাকে। একা বেঁচে থাকার সংগ্রামেও পরাস্ত হতে হলো। বিয়ে করলেও সে বিয়ে টিকল না। একপর্যায়ে লেখাপড়া জানা ইয়াসমিনের আশ্রয় মেলে পতিতাপল্লিতে। সেখানেই এক নিষ্করুণ পৃথিবীর ছবি আবিষ্কার করে সে। যে ছবি কেবল তারই দেখা। বিশদে বললে নারীর চোখে দেখা।
রিজিয়া রহমানের রক্তের অক্ষর–এর ইয়াসমিন সভ্য সুশীল পৃথিবীকে যেন আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। যে পৃথিবীর ছবি কেবল ইয়াসমিনের মতো নারীরাই দেখেছে।
১৯৩৯ সালে ভারতের কলকাতায় জন্ম নেওয়া রিজিয়া রহমানকে দেশভাগের পর জন্মভিটা ছেড়ে চলে আসতে হয় পূর্ববঙ্গে। তবে তার আগেই বাবার চাকরির সূত্রে ফরিদপুরে থাকছিলেন তিনি। দাঙ্গার রক্তাক্ত দৃশ্য তাই প্রত্যক্ষ করেননি সরাসরি। রিজিয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘আত্মীয়–স্বজন যারা প্রাণ বাঁচাতে ফরিদপুরে আমাদের বাড়িতে চলে এসেছিলেন তাদের মুখে সেই ভয়ংকর খুনোখুনির গল্প শুনেছি। দেশভাগের পরে বাবা সরকারি কর্মচারী হিসেবে ‘অপশনে’ পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) নাগরিকত্ব নিয়েছিলেন। তখনো আমার দাদার দেশটি আমার দেশই ছিল। দেশের বাড়িটি অক্ষুণ্নই ছিল। স্কুলের প্রতি গ্রীষ্মের ছুটিতে আমের দিনে কলকাতায় এবং বাবার জন্মস্থানের গ্রামে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ হয়নি বেশ অনেক দিন পর্যন্ত। তারপরই এল বাধা–বিদেশি নাগরিকের জন্য ভিসা–পাসপোর্ট ইত্যাদির প্রতিবন্ধকতা। তথাপি অনুভব করতে শুরু করলাম–পৈতৃক সূত্রে পাওয়া আমার স্থায়ী ঠিকানাটি হয়ে গেছে বিদেশ।’
ভিটেমাটি হারা রিজিয়া রহমান ১৯৪৭ সালের দেশভাগ, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছুঁয়ে পরিণত হয়েছিলেন। তার দশকের অনেক কথাসাহিত্যিকের এমন অভিজ্ঞতা আছে। তবে রিজিয়া নারী হিসেবে একধাপ এগিয়ে দেখেছেন তার পরিপার্শ্বকে।
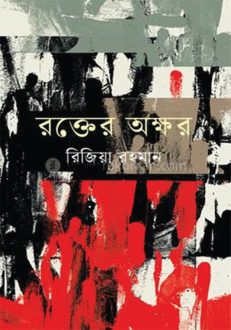
রবীন্দ্রনাথকে হৃদয়ে স্থান দিলেও রিজিয়ার নারী চরিত্র ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসের কুমুদিনী, ‘ ‘শেষের কবিতার’ লাবণ্য, ‘নষ্টনীড়ের’ চারুলতা কিংবা ‘ঘরে–বাইরের’ বিমলার চেয়ে অনেক আলাদা আর নিজের মাটির ওপরে দাঁড়ানো।
তবে রিজিয়া নিজেই এক লেখায় বলেছেন, তিনি প্রথাগত নারীবাদী নন। প্রত্যেককে মানুষ হিসেবেই দেখেন। নারীর সংগ্রামকেও সামগ্রিকভাবে মানুষের সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন না। এ যেন ভার্জিনিয়া উলফের কথারই প্রতিধ্বনি।
১৯৭৭ সালে বিচিত্রায় প্রকাশিত ‘রক্তের অক্ষর’ উপন্যাস রিজিয়া রহমানকে দেশে বিদেশে বিপুল খ্যাতি এনে দিল। কিন্তু এই উপন্যাসের ইয়াসমিনকে কোনো যৌনপল্লির অন্ধ গলিতে খুঁজে পাননি তিনি। সে জগৎও চাক্ষুষ করেননি রিজিয়া।
সেটা তাঁর নিজের বয়ানে শোনা যাক। রিজিয়া লেখেন, সে সময়ে ‘ঢাকার পতিতালয়’ শিরোনামে ‘সাপ্তাহিক বিচিত্রায়’ একটি প্রচ্ছদ কাহিনি করেছিল। পতিতাদের নিয়ে বিস্তৃত চিত্র প্রতিবেদন ছিল সেই সংখ্যায়। পতিতাদের একদিকের খবর জানা ছিল, অপর দিকটি কখনো জানা হয়নি। সে–ই প্রথম জানলাম। মনে আছে, পরে ‘বিচিত্রা’ পড়ে স্তম্ভিত হয়েছিলাম, ঘুমোতে পারিনি সে রাতে। সেই আঘাতের বেদনাই আমাকে ‘রক্তের অক্ষর’ লিখতে বাধ্য করেছিল। সমাজে উপেক্ষিত, ঘৃণিত এইসব নারীদের জীবনের কথা আমার মতো আমার পাঠকদেরও স্তম্ভিত করেছিল হয়তো। সেই প্রথম সচেতন মানুষেরা ভাবতে পেরেছিল, নিষিদ্ধ জগতের দেহব্যবসায় নির্বাসিত পতিতারাও মানুষ। মানবাধিকারের এমন নির্লজ্জ উদগ্র লঙ্ঘন বিবেকসম্পন্ন মানুষকে বিচলিত করেছিল বলেই হয়তো ‘রক্তের অক্ষর’ পাঠক সমাজে গুরুত্ব অর্জন করতে পেরেছে।’
অর্থাৎ ইয়াসমিন আসলে তার চারপাশের নারীদের কোলাজ বললে ভুল হবে না। এই লড়াই খানিকটা রিজিয়ার নিজেকেও করতে হয়েছে সমাজ, রাষ্ট্রের নানা স্তরে স্তরে। তাই আমরা এক প্রতিরোধেরই বয়ান যেন পাই। খানিকটা কি আত্মপরিচয়েরও সন্ধান আছে এতে। আর আছে নারীকে অপর করে তোলে যে পৃথিবী তারও উন্মোচন।
রিজিয়া রহমানের প্রথম দিককার উপন্যাস ‘উত্তরপুরুষ’ চট্টগ্রামের পটভূমিতে লেখা। চার শ বছরের পুরোনো শহরের ফিরিঙ্গি বাজার, পাথরঘাটায় এর কাহিনি ডালপালা ছড়ায়। পর্তুগিজদের উত্তরপুরুষ ফিরিঙ্গি বাজারের আধুনিক ফিরিঙ্গিদের জীবনযাপন নানা স্রোত ধারায় বয়ে চলে এই উপন্যাসে। সেখানেও আমরা দেখতে পাব নিপীড়িতদের মধ্যে নারীরাই সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত। নারীদের উপর, কুমারী মায়ের উপরে নেমে আসা নিপীড়নের কথাও আমরা পাব সেখানে। অর্থাৎ সমাজ, সভ্যতা পাল্টে গেলেও নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞতার পরিবর্তন হয় না। লড়ে যাওয়াই তার নিয়তি।
শিক্ষিত লেখাপড়া জানা মেয়ে ইয়াসমিন তাই ইতিহাস পার হয়ে যেন বর্তমানে এসে হাজির হয়। আমরা হয়তো দেখতে পাব ভবিষ্যতের দিকেও এই নিয়তি নিয়েই যাত্রা করেছে সে। দস্তয়েভস্কির ‘দা হাউজ অব দা ডেড’ উপন্যাসের আলেকজান্ডার পেত্রোভিচের মতোই এক দুর্দশাগ্রস্ত পৃথিবীকে দেখে ইয়াসমিন। যেখানে মনুষ্যত্বের অবনমনই মুখ্যত শেষ কথা। ইয়াসমিন পেত্রোভিচের মতোই অনুভব করে ‘পৃথিবীতে কেউ কারও নয়’। যৌন পল্লিতে পুরুষদের ধর্ষণের শিকার এক মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে ছুরিতে প্রাণ যায় তাঁর। এই মৃত্যু যেন তার প্রতিবাদ। আবার একই সঙ্গে মুক্তিও। মৃত ইয়াসমিন আমাদের আঙুল তুলে বলে, এটাই তোমরা। এটাই তোমাদের পৃথিবী।