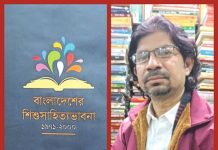‘তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদঘাটন / সূর্যের মতন’। রবির কিরণের মতো ছড়িয়ে পড়া আলোক রেখাকে ধারণ করে যিনি জগৎব্যাপী তাঁর মহিমা ছড়িয়েছেন, দেশ–কাল–সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে যিনি এখনো সমান প্রাসঙ্গিক, এখনো প্রতিটি বাঙালি তাদের প্রতিটি আবেগ–অনুভূতির ধারক বাহকের অন্যতম মাধ্যম করে রেখেছেন বাঙালির একমাত্র ভরসার রবিকে—-সেই রবিই বাঙালি তথা বিশ্বের একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি বিশ্বজনীন নিঃসন্দেহে।
তাঁর বিশ্বজনীন সত্তার প্রকাশ ঘটেছে বিশ্বময়। শুধু মহাকাব্য ছাড়া সাহিত্যের সব শাখায় তাঁর সুদৃঢ় পদচারণা তাঁকে মহীরুহে পরিণত করেছে সেই কবেই।
দীর্ঘ জীবন লাভের দৌলতেই হোক, অথবা অনুভবের গভীরতায় অনুভূতিকে ছুঁতে পেরেছেন বলেই হোক। মানবমনের বৈচিত্র্যময় অনুভূতিকে তিনি যেভাবে নান্দনিকভাবে সাহিত্যে উপস্থাপন করেছেন, আজও তা অতুলনীয়! আজও বাঙালির একমাত্র সুখকর অনুভূতির নাম রবীন্দ্রনাথ। দুঃখের অনুভূতি ব্যখ্যা করতেও রবীন্দ্রনাথ। শোকে ,তাপে, আনন্দে, বেদনায় সবেতেই একমাত্র রবীন্দ্রনাথ।
এত বিচিত্রতা, একই অঙ্গে! স্বয়ং দেবতা যেনো তাঁর হাতে অপার ঐশ্বর্য, আনন্দ বেদনার সংমিশ্রণ নিয়ে দণ্ডায়মান। আমরা তাঁকে খুঁজি নিত্যদিনের নিত্য সমাচারে। তাঁর প্রতিটি সাহিত্যের প্রতিটি লাইন যেনো আমাদের ভাবাতে বাধ্য করে। আমরা ডুবে যাই ভাবনার অতলে। তাঁকে নিয়ে ভাবা কঠিন, কিন্তু ভীষণ প্রশান্তির। সেই প্রশান্তির রেশ নিয়েই আমরা দিন কাটাই। তাঁর শব্দচয়নে এত গভীরতা, অনুভূতি, ভালোবাসা, প্রশান্তি, চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, নিমেষেই হারিয়ে যাওয়া, সর্বোপরি প্রেম—-সে সবকে একসুতোয় গেঁথে তিনি মালা করেছেন।
আর সেই মালা গলায় ধারণ করে জীবনপথের প্রতিটি দিন আলোকিত করার প্রত্যাশায় থাকে প্রত্যেক রবীন্দ্র ভাবাবেগপূর্ণ মানুষ।
পূজা, স্বদেশ, প্রকৃতি, প্রেম, বিচিত্র প্রভৃতি আলাদা আলাদা পর্যায়ে তিনি তাঁর গান, কবিতাগুলোকে বিন্যস্ত করেছেন, কিন্তু কোথায় গিয়ে যেনো মনে হয় একের ভেতরে সমস্ত অনুভূতি তিনি মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিলেন। তাঁর সামগ্রিক সাহিত্য একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান। তাঁকে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তাঁর একটি ‘তুমি’ তে তিনি অনায়াসে প্রিয়তমা, দেশ, মা, মাটিকে মিশিয়ে দিতে পারেন।
সেই ক্ষমতাবলে তিনি ভুবনজয়ী হলেন। তাঁর সৃষ্টির প্রতি পরতে পরতে রূপক শব্দের ব্যবহার, তাঁর সৃষ্টিকে করে তুলেছেন অনন্য সাধারণ। তিনি একই শব্দের মাধ্যমে বহু বহু অর্থকে বোঝাতে সক্ষম, একথা সর্বজন বিদিত। যার কারণে সময়ের বিবর্তনে তাঁর সৃষ্টির মাহাত্ম্য পাল্টে যায়। তাঁর সৃষ্টি হয়ে ওঠে সবসময়ের জন্য প্রাসঙ্গিক।
কোথাও তিনি লিখলেন হয়তোবা, ‘এসো এসো আমার ঘরে এসো—শেষের দিকে বলেন, ‘ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের পরে,এসো আমার ঘরে’। বিখ্যাত কন্ঠশিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য এক গানের অনুষ্ঠানে এই গানটি নিয়ে তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। তিনি বিশ্লেষণের ভঙ্গিতেই বলে গেলেন, ‘এই কথাটা খেয়াল করো, অর্থাৎ একটা খুব পার্টিকুলার কোনো মুহূর্ত, সেটা হয়তো পার্সোনাল হতে পারে, কিন্তু দেখো এমনভাবে কথাটা সাজানো, একটা খুব পার্সোনাল মুহূর্ত কিন্তু ইউনিভার্সাল।’
আমি ‘তোমাকে’ ক্ষণকালের জন্য চাই না, আমি ‘তোমায়’ চিরকালের মতো আমার মধ্যে ধারণ করে রাখতে চাই। সেই ‘তোমাকে’ বলতে প্রিয়ও বোঝানো হয়, যাকে প্রাণের পরে ধরে রাখতে চাই। আবার অন্যভাবে বলতে গেলে সে তুমি পরম প্রেমময় গ্রষ্টাও হতে পারে। যাকে আমি আমার করে লাভ করতে চাই। এমনি আরেকটি গান, ‘যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে, জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে’।
এখানেই সাদামাটা একটি প্রেমের আবহ ছড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই কি মনে হয় না, এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অন্য কিছু বুঝায়?
‘ঘর’ শব্দটিকে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এখানে ঘর, মন, পৃথিবী একাকার হয়ে মিশে যায়। তেমনি ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!’-এই গানটি স্বদেশ পযায়ের্র অন্তর্ভুক্ত। যেখানে দেশকে মা ভাবা হয়েছে, আবার কোথাও গিয়ে মনে হলো আমার সাদামাটা মাকে তুলে ধরেছেন তিনি। আবার কোথাও গিয়ে মনে হলো দেবী দুর্গার প্রশস্তি বন্দনা।
কী অদ্ভুত কলমের শক্তি রবীন্দ্রনাথের।
তিনি গ্রষ্টা, সৃষ্টি করেছেন অগুনতি, আমরা মুগ্ধ হয়েছি। আমরা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছি, আমরা বিস্মিত, আমরা আপ্লুত! এখানেই রবীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ গান, কবিতা তাঁর পূজা, প্রকৃতি, প্রেম, স্বদেশ প্রভৃতির বিভাজন থেকে সরে এসে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে বলে মনে হয়। এখানেই তাঁর চরম সার্থকতা। রবীন্দ্র উপন্যাস এক কথায় গভীর মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারার প্রতিফলন। তাঁর প্রতিটি উপন্যাস তাঁর তীক্ষ্ণ, ক্ষুরধার মানসিকতার প্রতিচ্ছবি।
নৌকাডুবিতে হেমনলিনীর মুখ দিয়েই তিনি উচ্চারণ করলেন প্রথমবারের মতো,‘আঘাত আর ক্ষতর মধ্যে বোধহয় একটা তফাৎ আছে!’
বাংলা সাহিত্যের এই বিশাল যজ্ঞে একথা আর কেউ উচ্চারণ করতে পেরেছিলো? কী সূক্ষ্ম অথচ কী গভীরতায় মোড়ানো তাঁর প্রতিটি লাইন! প্রতিটি ভাবধারা! ‘হৈমন্তী’ গল্পে বলেছিলেন নিদারুণ সত্যি এক কথা! ‘যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম। এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দুঃখ পাইতে হইবে। অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার রাখিতে যাইবার মতো এমন বিড়ম্বনা আর নাই।’ রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য ‘চিত্রাঙ্গদা’! সেই কতকাল আগে রচিত এক নৃত্যনাট্য, আজ এত বছর পরেও সমান প্রাসঙ্গিক। নারী স্বাধীনতার এই কঠিন সত্যিটুকু সেই সময়ের নিদারুণ সমাজবাস্তবতায় দাঁড়িয়ে তিনিই উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করে গেলেন। আর তারই ধারাবাহিকতায় আজ নারীদের বিদ্যাশিক্ষার একটি বৃহৎ ক্ষেত্র উন্মোচিত হলো হয়তো। তিনিই নারীকণ্ঠে প্রথম উচ্চারণ করে গেলেন নারীর আত্মপরিচয়!
‘আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী। /নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী। / পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি নহি,/ হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।/ যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সংকটে সম্পদে,/ সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে / পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।/ আজ শুধু করি নিবেদন -/আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী।’
কালিদাসের মেঘদূত পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে বর্ষাকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেলেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ। সেখানে বর্ষা শ্যামল মনোহর হয়ে উঠলো আপন শক্তিতে। বর্ষাকে তাঁর মতো করে বাংলা সাহিত্যে আর কেউ উদযাপন করতে পারেন নি। আর তাই, বাংলার বর্ষা মানেই রবীন্দ্রনাথ! বর্ষাকেই নয় শুধু, বাংলা ষড়ঋতুর প্রতি পর্বে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাই একান্তভাবে, নিবিড়ভাবে। আজও তাঁর ‘এসো হে বৈশাখ’ ছাড়া বর্ষবরণের কথা আমরা ভাবতেই পারি না। তাঁর কোনো বিকল্প এখনো তৈরী হলো না সমগ্র বাংলা সাহিত্যে।
রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো মানবমনের মনস্তাত্ত্বিক দিক নিয়ে সাহিত্য রচনা। তিনি শুধু বাঙালি মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারা নিয়েই ভাবেন নি। তিনি মানবমনের মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারা নিয়ে খেলেছেন। যেখানে শুধু বাঙালিই নয়, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ তাঁর মনস্তাত্ত্বিক দর্শনের সাফল্যে অভিভূত না হয়ে পারেনি। তাঁর এই চিন্তা ভাবনা পশ্চিমাদেরও আকৃষ্ট করেছিলো সঙ্গত কারণেই।
বহু ভাববাদী মানুষের সাথে তাঁর একাত্ম হওয়া তাঁকে জীবনের বৈচিত্র্যময়তা অনুধাবন করতে সাহায্য করেছিলো হয়তো! দুঃখের দহনতাপও কী করে সাহিত্যের উপজীব্য হয়, তিনি তা দেখিয়েছেন। দুঃখকে নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করেছেন তাঁর সাহিত্যে। জীবনের বাঁকে বাঁকে যেসব অনাকাঙ্ক্ষিত অনুভূতি, সে সবকেও তিনি দু‘হাতে বরণ করেছিলেন। তুলে নিয়ে বসিয়েছেন সাহিত্যের আসরে। আর তাতেই তাঁর সাহিত্যজীবনে বাড়তি মাত্রা যুক্ত হলো। অতি বড় আনন্দ, অতি বড় দুঃখ, অতি সূক্ষ্ম ব্যথা– কোনোটাই তাঁকে সাহিত্যরচনা থেকে বিরত রাখতে পারেন নি।
প্রতি পলে পলে তাঁর কলমকে তিনি সচল রেখেছিলেন, জীবনকে সাহিত্যের একমাত্র অনুষঙ্গ করে তোলার জন্য। তিনি তা পেরেছিলেন। তাতে তিনি সামগ্রিকভাবে সফল। সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্য একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান। তাঁকে পাঠ করাও তেমন সহজসাধ্য নয়, অনুধাবন করাও বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর। তাঁকে অনুভব করতে হয় নীরবে, নিবিড়ভাবে।
ধারণ করতে হয় মননে, হৃদয়ের গহীনতম প্রকোষ্ঠে।
লেখক: প্রাবন্ধিক।