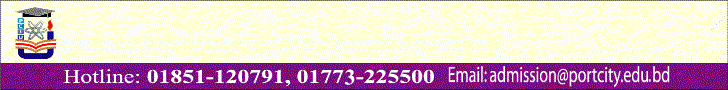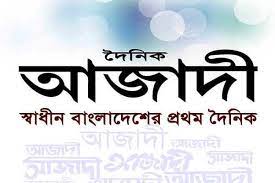১৯০৩ সাল। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী জর্জ জিমেল ভাবছেন শিল্পায়ন এবং নগরায়ন ব্যক্তি মনে কী প্রভাব ফেলবে। বাকিটা ইতিহাস। তিনি রচনা করলেন ‘মেট্রোপলিস অ্যান্ড মেন্টাল লাইফ’ নামে এক কালোত্তীর্ণ প্রবন্ধ, যা সমাজবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব থেকে শুরু করে নগর পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষানবীশ ও বিশারদদের আজও ভাবায়। জিমেলের মূলকথা ছিল, নগর জীবনে থাকে অসংখ্য উদ্দীপনা, নানাবিধ কার্যকলাপ ও অশেষ সম্পর্ক তৈরির সম্ভাবনা। কিন্তু, এই ‘অশেষ উদ্দীপনা’ মানুষকে পাগল করে দিতে পারে। তাতে ফল হয় উল্টো, অশেষের মাঝে নিজের মানসিক শান্তি না হারানোর অভিপ্রায়ে নাগরিক মানুষ নিজের মধ্যে এক ভোতা অনুভূতি সৃষ্টি করেন। তিনি চারপাশ দেখেও দেখেন না, শুনেও শুনেন না। তথ্য অনেকটা এই তত্ত্ব মানে, বটে। শহুরে জীবনে আমরা অনেকে জানি না পাশের বাসার হাসি-কান্নার উৎস কী! বড় দালানের পাশে বড় ডাস্টবিনে সর্বহারা শিশুরা, কুকুরেরা ঘাঁটে উচ্ছিষ্ট খাবার, শোঁ করে পাশ দিয়ে চলে যায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি। কে কাকে দেখে?
তবে আজকালকার ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, টিকটকের যুগে জিমেলের ‘অশেষ উদ্দীপনা’ শুধু নগরের রাস্তায় নেই। হাজারো উদ্দীপনা, সম্পর্কের হাতছানি, নিরবচ্ছিন্ন কোলাহল আমাদের মুঠোর মধ্যে, কানের গোড়ায়, ল্যাপটপে, মুঠোফোনে এবং ট্যাবে। জিমেলের তত্ত্ব ঠিক থাকলে দুটো কথা বলা যায়। প্রথমত, এই নিরবচ্ছিন্ন-প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক মাধ্যমে আমাদের অনুভূতি আরো ভোতা থেকে ভোতা হয়ে যাওয়ার কথা। দ্বিতীয়ত, আমরা কে কী বলল অর্থাৎ কী ফিডবেক বা প্রতিক্রিয়া দিল তাতে ‘থোড়াই যায় আসে’ ভাব নিয়ে থাকার কথা। দুটো আংশিক সত্য। কিন্তু, জিমেল ভাবেননি আরেক কথা। সেটা হল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে অন্যদের প্রতিক্রিয়া পায় অনেকটা নিরবচ্ছিন্নভাবে। যেমন, ফেসবুকের ফলোয়ার, ফ্রেন্ডস, লাইক, লাভ, কেয়ার রিয়েকশন। এই প্রতিক্রিয়া পেতে পেতে, না পেলে আর ভালো লাগে না, ব্যক্তি হয়ে উঠে প্রতিক্রিয়া-লোভী। এইতো ইনস্টাগ্রামে, ফেসবুকে ফলোয়ার, লাইক ইত্যাদি পাবার আশায় মানুষ কতনা কিছু করছে। এমন কি অনেকে দুর্ঘটনার কবলেও পড়েছে।
এই যে নিরবচ্ছিন্ন-প্রতিক্রিয়ার যুগে বড় হচ্ছে ছেলে-মেয়েরা, তারা বেশি বেশি ফিডব্যাক সংস্কৃতিতে আসক্ত হয়ে উঠছে। ফ্রাঙ্কলিন কোভির পরামর্শক হেইডেন শ বলেমি এই যুগের কর্মীরা দিনে একবারের বেশি তাদের কাজের উপর ফিডব্যাক চান। তারা মনে করেন কর্মক্ষেত্রে দেয়া ফিডব্যাক একেবারেই অপর্যাপ্ত। তবে, টুইলোর কার্যনির্বাহী জেক লসন নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে বলেন, মিলেনিয়ালরা (যাদের জন্ম ১৯৮০ থেকে ২০১০ এর মধ্যে) যে সারাক্ষণ নিজেদের প্রশংসা চাচ্ছে তা নয়। বরং তারা প্রতিনিয়ত শিখতে চায়, নিজেদের জ্ঞান গরিমাকে দ্রুত বিকশিত করতে চায়। তারা তাঁদের অগ্রগতিকে নিয়মিত পরিমাপও করতে চায়। তারা কেমন করছে না করছে এটার সুস্পষ্ট একটা ধারণা তাদেরকে দিতে হবে। এক্ষেত্রে পেশাজীবনে মনস্তত্ত্ববিদ আরলিন হারশ নিরবচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত কর্মীদের কীভাবে কাজের ফিডব্যাক দিতে হবে তার কিছু উপায় বাতলে দিয়েছেন। তা সংক্ষেপে তুলে ধরছি।
কলেবরে ছোট, তবে দ্রুত :
নতুন এই প্রজন্মের পছন্দ কলেবরে ছোট ফিডব্যাক। ভুলে গেলে চলবে না যে জনপ্রিয় মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার এর ২৮০ অক্ষরের সীমাতেই অভ্যস্ত অমিলেনিয়ালরা। তাই ফিডব্যাক রাখতে হবে ছোট এবং সুনির্দিষ্ট। তাছাড়া ফিডব্যাক দিতে হবে যথাসময়ে, চটজলদি। ফিডব্যাককে একটা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে না ফেলে, অনেকটা নিয়মিত আলাপচারিতার ঢংয়ে নিয়ে যেতে পারলে ভাল। নিয়মিত আলাপচারিতার সুবিধা হল এতে প্রশংসামূলক এবং নেতিবাচক উভয় ফিডব্যাকই খুব সহজভাবে দেয়া যায়। নিয়মিত ফিডব্যাক কিন্তু অনেক আনুষ্ঠানিকতার সময় বাঁচিয়ে দেয় বলে অনেকে মনে করেন। এক্ষেত্রে প্রযুক্তির সহায়তা নিলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়।
গঠনমূলক , কিন্তু বৈচিত্র্য ভুললে চলবে না :
আমরা গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া কথাটার সাথে বেশ পরিচিত। কিন্তু এটা আসলে কী? সোজাসাপ্টা উত্তর হল, এটা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন। ব্যক্তি ভেদে এটা প্রশংসা, উৎসাহ, গঠনমূলক সমালোচনা, বৈধতা প্রদান, মনোযোগ প্রদান, পেশা ভিত্তিক উপদেশ ইত্যাদি প্রকারের হতে পারে। কিন্তু গড়পড়তা কিছু না বলে, বরং ব্যক্তির প্রয়োজন অনুসারে ফিডব্যাককে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলতে হবে। না হলে ফিডব্যক দেয়াই হবে, তাতে যিনি ফিডব্য্যক পেলেন তিনি তা এক কান দিয়ে শোনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিতে পারেন। তাছাড়া, প্রশংসামূলক ফিডব্যাকের পাশাপাশি সংশোধনমূলক ফিডব্যাকও দিতে হবে।
ফিডব্যাক নয়, বরং ফিড ফরোয়ার্ড, অর্থাৎ ভবিষ্যৎমুখী প্রতিক্রিয়া :
ফিডব্যাক বেশিরভাগই ময়নাতদন্তের মতো, অর্থাৎ অতীতের উপর নির্ভর। কিন্তু, লেখক মার্শাল গোন্ডস্মিথের মতে অতিমাত্রায় অতীত নির্ভরতা ফিডব্যাককে অকার্যকর করে ফেলে। কারণ অতীত যাই হোক না কেন, তা ভবিষ্যতে অনুরূপ পুনরাবৃত্তি নাও হতে পারে। কিন্তু অতীত আর ভবিষ্যতের মধ্যে একটা সরল পার্থক্য হল বর্তমানের কাজকর্মে আমরা অতীত পাল্টাতে না পারলেও ভবিষ্যৎ পাল্টাতে পারি কিছুটা হলেও। তাই, ফিডব্যাক হতে হবে ফিড ফরোয়ার্ড, অর্থাৎ ভবিষ্যৎমুখী। ভবিষ্যতের সুযোগ, সুবিধা অসুবিধার বিবেচনাতেই ফিডব্যাক দিলে তা ব্যক্তিকে উৎসাহিত করে আস্থার সাথে, দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সামনে এগিয়ে যাবার। শুধু অফিস আদালত, স্কুল-কলেজে নয়, ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও আমরা এই বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে কার্যকরী ফিডব্যাক বা প্রতিক্রিয়া আদান-প্রদান করতে পারি।
লেখক: পিএইচডি গবেষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, কর্নেল ইউনিভার্সিটি, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র