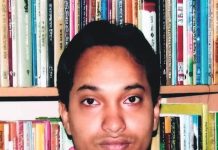প্রবৃদ্ধি শব্দটি অর্থনীতিতে বহুল ব্যবহৃত হয়। একই সাথে এ শব্দটির সমার্থক আর একটি শব্দ আছে ‘উন্নয়ন’। এ শব্দ দুইটির অর্থ সাধারণ মানুষের কাছে প্রায় একই হলেও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করলে এ দুইটি শব্দের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। অর্থনীতির গভীর তত্ত্বগত বিশ্লেষণে না গিয়ে সহজে বুঝার জন্য বলা যায়, প্রবৃদ্ধি হচ্ছে একটি অর্থনীতির খাত ভিত্তিক প্রসারতা যা অর্থনীতিতে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়। অপরপক্ষে ‘উন্নয়ন’ হচ্ছে অর্থনীতির সামগ্রিক প্রসারতা যা অর্থনীতিকে বিবেচিত সকল খাতকে বিবেচনা করা হয়। এদিক থেকে বলা যায়, প্রবৃদ্ধির বিষয়টি হয় তুলনামূলক ছোট পরিসর। আর উন্নয়ন বিষয়টি হয় তুলনামূলক বড় পরিসর। এ কারণে রাজনীতির মাঠে বক্তব্য রাখার সময় কোনো নেতা দেশের উন্নয়নের কথা তেমন বলে না। বরং প্রবৃদ্ধির কথাই বলে।
এখন উন্নয়নকে বিশ্লেষণ না করে যদি প্রবৃদ্ধি বিশ্লেষণের কথা বলি তবে বিশ্বের প্রতিটি দেশের কোনো না কোনো খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বিশেষ করে একবিংশ শতাব্দীর সিকি ভাগে পৌঁছে এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু দেশ ছাড়া অধিকাংশ দেশে কিছু না কিছু প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। যদি মাথাপিছু আয়কে বিবেচনা করি, তবে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মাথাপিছু আয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, প্রবৃদ্ধির অংশ হিসেবে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি কি একটি দেশের সকল জনগণ সমভাবে ভোগ করতে পেরেছে? অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির ধারা থেকে আগত আয় দেশের অভ্যন্তরে সকল মানুষ কি সমভাবে ভোগ করতে পেরেছে? এখানেই রয়ে গেছে বিশাল অভিঘাত তথা বৈষম্য। বিশ্বের অধিকাংশ দেশ পুঁজিবাদী ধারার মাধ্যমে পরিচালিত। এসব পুঁজিবাদী দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র মনে করে, মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। পৃথিবীর সকল মানুষ সমান যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। কাজেই কর্মক্ষেত্রে আয়ের বৈষম্য থাকা স্বাভাবিক। পুঁজিবাদী অর্থনীতির এরূপ চিন্তাধারা মানুষ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছে বলে এটাকে কোনো অপরাধ বলে মনে করে না। পুঁজিবাদী দেশের কেন্দ্র রাষ্ট্রটি অন্ততঃ তাই মনে করে। তাই এ দেশেও দেখা যায়, একাধারে রয়েছে বিশাল বিশাল অট্টালিকা, আর এ অট্টালিকার ছায়াতে শুয়ে থাকে গৃহহীন নরনারীরা। অবশ্য এ দেশগুলোতে কিছু মানবতাবাদী লোকও আছে যাঁরা এরূপ ব্যবস্থার বা বৈষম্যের প্রতিবাদ করে। কিন্তু এ প্রতিবাদ কোনো কাজে আসে না। বরং বৈষম্যের গতি দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পায়। কারণ বিত্তশালীরা রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে। এ সম্পর্ক যেমন আর্থিক তেমন পারিবারিকও বটে। কাজেই কোনো অবস্থায় এ সম্পর্কের বৃত্ত কেউ ভাঙতে পারে না। ফলে অপ্রতিরোধ্যভাবে এগিয়ে যায় আয় বৈষম্য।
২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল– ‘সারভাইভাল অব দ্যা রিচেস্ট’– নামক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এ প্রতিবেদনটি ‘ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম’– এর বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপিত হয়। উক্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়, বিশ্বের ধনী ও অতি ধনীদের সম্পদ বেড়েই চলেছে। ২০২০ সালের পর সারা বিশ্বে যত সম্পদ তৈরি হয়েছে, তার দুই–তৃতীয়াংশ বিশ্বের শীর্ষ ১ শতাংশ ধনীর ঘরে গেছে। একই সময়ে বাকী ৯৯ শতাংশ মানুষের ঘরে গেছে অবশিষ্ট এক–তৃতীয়াংশ সম্পদ। এখানে শেষ নয়। বিগত এক দশকে সমগ্র বিশ্বে যত সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, তার অর্ধেকের মালিক হয়েছে শীর্ষ ১ শতাংশ ধনী।
অক্সফামের প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ২০২০ সালের পর বিশ্বে ৪২ ট্রিলিয়ন বা ৪২ লাখ কোটি ডলারের সম্পদ তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে ৬৩ শতাংশ বা ২৬ ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদ দখল করেছে বিশ্বের ১ শতাংশ শীর্ষ ধনী। বাকী ৩৭ শতাংশ বা ১৬ ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদ ভাগ হয়েছে পৃথিবীর অবশিষ্ট ৯৯ শতাংশ মানুষের মধ্যে। আরো আশ্চর্যতম তথ্য হচ্ছে, বিশ্বে তৈরি হওয়া সম্পদ থেকে সমাজের নিচের দিকের ৯০ শতাংশ মানুষের ১ ডলার আয়ের বিপরীতে ধনীদের আয় ১৭ লাখ ডলার। এরূপ বৈষম্যের কথা চিন্তা করলে, পুঁজিবাদ যে সমাজকে তথা সমাজের বৈষম্যকে কোথায় নিয়ে গেছে তা কল্পনাও করা যায় না। যারা সমাজের সচেতন ব্যক্তি নয় তাদের কাছে এ তথ্য কিছু যায় আসে না। আর যারা এ সব বিষয় নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করে তারা এ তথ্যকে সপ্ত আশ্চার্য্যের ন্যায় মনে করবে।
২০২০ সালে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের কোম্পানিগুলো কয়েকগুণ মুনাফা করেছে। মহামারির এ সময়ে মানুষের প্রযুক্তি নির্ভরতা বেড়ে যাওয়ার কারণে কোম্পানিগুলো অধিক মুনাফা করতে সক্ষম হয়েছে। ঘরে বসে অফিস করা, ভার্চ্যুয়াল বৈঠক ও ক্লাসের কল্যাণে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো রমরমা ব্যবসা করেছিল। ওয়ালমার্টের মালিক ওয়ালটন পরিবার এ সময়ে মুনাফা করেছে ৮৫০ কোটি ডলার। ২০২২ সালে শীর্ষ ধনীদের সম্পদ বৃদ্ধির প্রধান দুইটি কারণ হচ্ছে খাদ্য ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি। ৯৫টি খাদ্য ও জ্বালানি কোম্পানি স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে দ্বিগুণ মুনাফা করেছে। এ দ্বিগুণ মুনাফার পরিমাণ হয় ৩০৬ বিলিয়ন বা ৩০ হাজার ৬০০ কোটি ডলার। অবশ্য এর মধ্যে ২৫ হাজার ৭০০ কোটি ডলার তারা শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসেবে বিতরণ করেছে। প্রতিবেদনে আরো দেখা যায়, যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ মূল্যস্ফীতি হয়েছে করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর অতি মুনাফার কারণে। স্পেনের অন্যতম বৃহৎ ট্রেড ইউনিয়ন সিসিওও মনে করে, ২০২২ সালের প্রথম প্রান্তিকে দেশটির মূল্যস্ফীতির ৮৩ দশমিক ৪ শতাংশ হয়েছে করপোরেটদের উচ্চ মুনাফার কারণে। আর এ মূল্যস্ফীতির ফলে তাদের তথা শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরী কমেছে। এ সময়ে বিশ্বে প্রায় ৮২ কোটি মানুষ পেটে ক্ষুধা নিয়ে ঘুমাতে গেছে। আর এই জনগোষ্ঠীর সিংহভাগই হলো নারী ও মেয়ে শিশু। এই কারণে বিশ্বব্যাংক বলেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে সম্ভবত ২০২০, ২০২১, ২০২২ সালে আয় বৈষম্য সবচেয়ে বেশি হারে বেড়েছে।
করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর এ অতিমুনাফাকে বলা হয় ‘উইন্ডফল প্রফিট’। এরূপ উইন্ডফল প্রফিটের ওপর ‘উইন্ডফল ট্যাক্স’ বা উচ্চ হারে কর আরোপ করা প্রয়োজন। অথচ দেখা যায়, বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক ২০১৪ থেকে ২০১৮ সালে কর দিয়েছে ৩ শতাংশ হারে। আর উগান্ডার আটা বিক্রেতা অ্যাবার ক্রিস্টিন মাসে ৮০ ডলার আয় করলেও আয়কর দিয়েছেন ৪০ শতাংশ হারে। এ কারণে অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল, অতি মুনাফালোভীর অবসান ঘটাতে সম্পদ কর ও উইন্ডফল কর আরোপের সুপারিশ করেছে।
বাংলাদেশে গত পাঁচ দশকে মাথাপিছু জিপিডি তিন গুণ বেড়েছে। ১৯৯০ এর দশক থেকে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি বাড়তে থাকে ২০০০ ও ২০১০ দশকে প্রবৃদ্ধির হার দ্রুত হয়। একদিকে প্রবৃদ্ধি বাড়লেও অন্যদিকে বেড়েছে বৈষম্য। ১৯৯১ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে বৈষম্য বেড়েছে বেশি। বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, মালদ্বীপ ও নেপাল– দক্ষিণ এশিয়ার এ ছয়টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কায় গত আড়াই দশকে ব্যাপক বৈষম্য বাড়লেও ভুটান, মালদ্বীপ ও নেপালে বৈষম্য কমেছে। বাংলাদেশে যদি বৈষম্য কমানো সম্ভব না হয় তবে কেন্দ্র পুঁজিবাদী দেশের ন্যায় বৃহৎ অট্টালিকার ছায়াতে দেখা যাবে বস্ত্রহীন, গৃহহীন নরনারী। এতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।
লেখক: পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ইউএসটিসি।