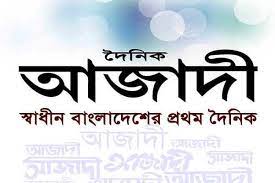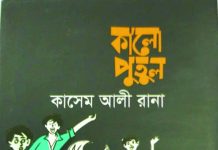একটি গণতান্ত্রিক কল্যাণমুখী রাষ্ট্র টিকে থাকে তিনটি অঙ্গের ওপর। এগুলো হলো বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও আইন বিভাগ। এর মধ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে নির্বাহী বিভাগ ও সংসদের (আইন বিভাগ) প্রধান একই ব্যক্তি হয়ে থাকে। বিচার বিভাগের প্রধান হন সেই বিভাগ থেকে উঠে আসা একজন ব্যক্তি। তাই রাষ্ট্রের ইক্যুলিব্রিয়াম রক্ষায় স্বাধীন বিচার বিভাগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরোধপূর্ণ অনেক সমস্যা এই বিভাগের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়। তাই এই বিভাগটি সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকার কোন বিকল্প নাই। আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উচ্চারিত মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম মূলনীতি হলো ‘জনগণকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদান’ করা। এই নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ শাসন হিসেবে আমরা শুরুতে গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছিলাম। চলনসই একটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, কিন্তু সেটা স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন করা যায়নি। প্রায়ই হোঁচট খেয়েছে, এসেছে নানা রকমের অগণতান্ত্রিক শাসন। লে জনগণকে বারবার রাজপথে নেমে গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে হয়েছে। এসব প্রক্রিয়ায় বিচার বিভাগকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ভূমিকাতেই দেখা গেছে। এমন মিশ্র অভিজ্ঞতার আলোকে দেশে একটি কার্যক্ষম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও তা অব্যাহত রাখার স্বার্থে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। যার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের অধীনে বিচার বিভাগের জন্য একটি পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। তবে এই বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত না থাকলেও বিগত ৫৪ বছরে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। যা সত্যিই দুঃখজনক!
৫ই আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে দেওয়া প্রথম ভাষণে বিচার বিভাগের সংস্কারকে সরকারের অন্যতম প্রতিশ্রুতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। সে লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন। যদিও সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। শুরুতে ১৯৭২ সালের সংবিধানে ১১৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল, ‘বিচার–কর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ(কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি দান, ছুটি মঞ্জুরিসহ) ও শৃঙ্খলাবিধান সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত থাকিবে।’ পরে ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর পর ১১৬ অনুচ্ছেদ দাঁড়ায়, ‘বিচার–কর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি দান, ছুটি মঞ্জুরিসহ) ও শৃঙ্খলাবিধান রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত থাকিবে। পরবর্তীতে পঞ্চম ও পঞ্চদশ সংশোধনীর পর বর্তমানে ১১৬ অনুচ্ছেদ যা আছে তা হলো, ‘বিচার–কর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি দান, ছুটি মঞ্জুরিসহ) ও শৃঙ্খলাবিধান রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সুপ্রিম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে।’
বর্তমান সংবিধান অনুসারে, প্রধান বিচারপতি ও প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ছাড়া রাষ্ট্রপতি আর কোনো কিছু স্বাধীনভাবে করতে পারেন না। তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর বাধ্যতামূলক পরামর্শ অনুসারেই অন্য সব নির্বাহী দায়িত্ব পালন করতে হয়। ফলে বিচারকদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সংক্রান্ত ‘রুলস অব বিজনেস’ এবং ‘অ্যালোকেশন অব বিজনেস’ অনুসারে সরকারের আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী এই নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন। মাঝখানে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে এই ক্ষমতা প্রয়োগের বিধান থাকলেও এবং মাসদার হোসেন মামলার রায়ে এ ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সেই পরামর্শই প্রাধান্য পাবে বলে সাব্যস্ত হওয়ার পরেও বিগত দিনে সেটি বাস্তবায়িত হয়নি। আসলে বিচারক ও বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটদের সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার এই কাজ সম্পন্ন হয়েছিল ১৯৭৫ সালের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে। তার আগে এই ক্ষমতা ছিল সুপ্রিম কোর্টের হাতে। তখন সাংবিধানিকভাবে নিয়ন্ত্রণের পুরো ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব সুপ্রিম কোর্টের হাতে ছিল। তবে সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ সুপ্রিম কোর্টের হাতে থাকলেও, ফৌজদারি কার্যবিধিতে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বিচারিক কর্মকর্তাকে নয় বরং নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তাদেরই নিয়োগ দেওয়ার বিধান বহাল রাখা হয়েছিলো। এভাবে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিয়ে বিচার বিভাগে পরোক্ষভাবে আংশিক দ্বৈত শাসনব্যবস্থাই চালু রাখা হয়। কিন্তু এই জোড়াতালির বন্দোবস্তও বেশি দিন সহ্য করেনি দেশের রাজনীতিবিদেরা। সব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক বিন্দুতে ঘনীভূত করতে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে ১১৬ অনুচ্ছেদে ‘সুপ্রিম কোর্ট’ এর জায়গায় ‘রাষ্ট্রপতি’ লিখে দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটদের তো বটেই, তার সঙ্গে সঙ্গে বিচারকদের নিয়ন্ত্রণও নিজের হাতে তুলে নেয়। বলা যায় একটিমাত্র শব্দ বদলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যবনিকাপাত ঘটে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বা পৃথকীকরণ নিশ্চিত করার যাবতীয় রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রথম অধ্যায়ের। এভাবে পৃথকীকরণের বদলে একীভূতকরণ হয়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় নীতি। যদিও এই সংশোধনী দিয়ে কার্যত সংবিধান ‘পুনর্লিখন’ করে তার মাধ্যমে কায়েম করা একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা বেশি দিন টেকেনি। পরবর্তী আমলে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে আরেক দফায় সংবিধানের পুনর্লিখন করা হয়। তবে আশার কথা হলো, এই সরকারের আমলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার্থে উচ্চ আদালতের বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাত থেকে নিয়ে দেশের শীর্ষ তিন বিচারকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে ন্যস্ত করা হয়।
আসলে শুধু একটি পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করলেই পৃথকীকরণ বা স্বাধীনতা সম্পন্ন হয়ে যাবে না। আরো কিছু অত্যাবশ্যকীয় অনুষঙ্গ যুক্ত আছে এর সঙ্গে। যেমন আদালতে রাজনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসা কত দূর পর্যন্ত হতে পারে। উচ্চ আদালতে নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণ। অবসরের পর বিচারকদের লাভজনক সরকারি পদে নিয়োগের প্রশ্ন। স্বতন্ত্র অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা। বিচারকদের নিয়োগ, পদায়ন, কর্মকাল, পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলাসংক্রান্ত নীতিমালা স্থির করা। আর্থিক স্বাধীনতা, জবাবদিহি নিশ্চিত করাসহ আরো অনেক বিষয় এর সঙ্গে জড়িত আছে। তবে এই সবকিছুর কেন্দ্রে রয়েছে পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি। এদিকে মাসদার হোসেন মামলায় দেওয়া আদালতের নির্দেশনা অনুসারে আইনসভা বা সংসদের ক্ষমতাবলে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ভিত্তিতে ১১৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন যে কোন সময়ই করা যাবে। তাই বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলই হলো ১১৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন ও পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার মোক্ষম সময়।
একটি রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক, জবাবদিহিমূলক ও কল্যাণমূখী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে হলে তার প্রতিটি অংগ ও প্রতিষ্ঠানকে নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হতে হয়। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সেই চাওয়াটি আরো বেশি ব্যাপক। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে কোনো সরকারই এসব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার দিকে নজর দেয়নি। তারা নিজেদের পছন্দের লোকজনকে এসব প্রতিষ্ঠানে পদায়িত করেছে, প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের কব্জায় রাখার জন্য। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান নিরপেক্ষ ও কার্যকরভাবে সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারেনি ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রর প্রায় সব প্রতিষ্ঠান ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থার জায়গাটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে রাষ্ট্রটি কার্যকরভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠেনি। তাই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসাবে বিচার বিভাগ শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী করা আরো বেশি জরুরি। এদিকে সমপ্রতি সুপ্রিম কোর্টের জন্য পৃথক সচিবালয় তিন মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়ে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। রায়ে অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলাসংক্রান্ত ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করেছেন হাইকোর্ট। তাই এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে অতিদ্রুত রায়টি বাস্তবায়ন করা জরুরি। যা রাষ্ট্র ও দেশের কল্যাণ এবং নিরপেক্ষতার স্বার্থে।
লেখক: প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট।