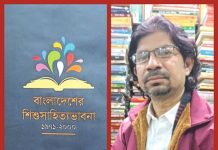একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং অনুন্নয়নে জনসংখ্যা যে কত বড় ভূমিকা রাখতে পারে তা শুধুমাত্র অর্থনীতিবিদরা জানে। জনসংখ্যা যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে তেমনি অতিরিক্ত জনসংখ্যা দেশে অনুন্নয়নেও ঋণাত্মক ভূমিকা পালন করে। সুতরাং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে লাগানোর ভেতর দিয়ে দেশের প্রবৃদ্ধির হারকে বাড়ানো যেমন সম্ভব তেমনি জনশক্তিকে কাজে লাগাতে না পারলে তার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় প্রবৃদ্ধির হার কমে যাওয়াও সম্ভব। অর্থনীতি বিষয়ের একটি শাখা হয় জনসংখ্যা অর্থনীতি যা অনার্স ও মাষ্টাস–এর পাঠ্য। যেহেতু আমার লিখিত ‘জনসংখ্যা অর্থনীতি’ – দুইটি পাঠ্য বই আছে সেহেতু পাঠ্যক্রমে জনসংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই দুইটি বইতে রয়েছে।
কোন দেশের জনসংখ্যা যদি সম্পদের তুলনায় কম হয় তবে জনশক্তির অভাবে প্রাপ্য সম্পদকে যথাযথ ব্যবহার করা যায় না। বর্তমান বিশ্বে এরূপ অনেক দেশ আছে যে সব দেশের জনসংখ্যা, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় অনেক কম। বর্তমান রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশ এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশ, তাদের প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম। তাই এসব দেশগুলো এশিয়ার উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার দেশগুলো থেকে প্রতিনিয়ত জনশক্তি আমদানি করে। এমন কি মালয়েশিয়াতেও প্রাপ্ত সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম হওয়ার কারণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে থাকে।
বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। এদেশে দারিদ্র্যের হার সরকারি হিসেবে ২০ শতাংশ। অবশ্য বেসরকারি হিসেবে ৩০ শতাংশ বা এর কিছু বেশি। আবার দরিদ্র রেখার ওপরে যাদের অবস্থান তাদের আর্থিক আয়ের মধ্যে কোন সমতা নেই। যে কারণে আর্থিক দিক দিয়ে তাদের শ্রেণিগত অবস্থানও সমান নয়। আয়কে যদি সামাজিক অবস্থানের ভিত্তি হিসেবে মনে করা হয় তবে সামাজিক অবস্থানকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন– উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র। সামাজিক স্তর ভিত্তিক দারিদ্র্য রেখা যদি কল্পনা করা হয় তবে দরিদ্রদের অবস্থান দারিদ্র্য রেখার নীচে থাকে। তাহলে বলা যায়, দারিদ্র্য রেখার ওপরে তিনটি স্তর রয়েছে। নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত। দারিদ্র্য রেখার নীচে যাদের অবস্থান তাঁরা অতি স্বল্প আয়ের মানুষ বলে তাদেরকে গ্রামে বা অতি গন্ডগ্রামে বসবাস করে জীবন প্রবাহ নির্বাহ করতে হয়। এসব দরিদ্র শ্রেণির লোকদের দুপুরে কোন রকমে খেতে পারলেও বিকালে বা রাত্রে খাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই। জীবন প্রবাহ পরিচালনার জন্য তাদেরকে প্রতিনিয়ত প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করতে হয়। এ দরিদ্র শ্রেণি যদি উচ্চ জীবনযাত্রা নির্বাহ করার জন্য কোন প্রকারে নগরে আসে তবে তাকে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে বস্তিতে অবস্থান করতে হয়। নিম্নবিত্তদের অবস্থাও প্রায় একই। আর সম্পূর্ণ নগর জুড়ে রয়েছে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের আবাসস্থল কিন্তু আলাদা। ঘটনাচক্রে কোন উচ্চবিত্ত যদি মধ্যবিত্তের সাথে একই এলাকায় বসবাস করেও পরবর্তীতে উচ্চবিত্ত সেখান থেকে স্থানান্তর হয়ে উচ্চবিত্তদের এলাকায় চলে যায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এ অবস্থা দেখা যায়।
জনসংখ্যার নিরিখে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম দেশ। এ দেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লাখ। (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনশুমারি ও গৃহগণনা– ৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৩)। ২০৫০ সালে বাংলাদেশ হবে জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের দশম বৃহত্তম দেশ। এ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যাওয়ার পরেও ২০৫০ সালে জনসংখ্যা হবে ২০ কোটি ৪০ লাখ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এ দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২ দশমিক ৬৪। আর ২০২২ সালে এ হার নেমে এসেছে ১ দশমকি ২২ শতাংশে। আর ২০৩০ সালে এ হার হবে শূন্য দশমিক ৮ শতাংশে। ২০৫০ সালে এ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হবে শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমলেও আয়তনে ছোট বাংলাদেশের জন্য বর্তমান জনসংখ্যা ও ঘনবসতি বড় সমস্যা। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব এখন প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১ হাজার ১১৯ জন। ২০৫০ সালে এই ঘনত্ব হবে ১ হাজার ৫৬৬ জন। বর্তমানে বিভাগ হিসেবে ঢাকার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। এ বিভাগে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২ হাজার ১৫৬ জন মানুষ বসবাস করবে। এর পরেই ময়মনসিংহ। এই বিভাগে বাস করে ১ হাজার ১৪৬ জন। নগর হিসেবে সবচেয়ে বেশি মানুষ বসবাস করে ঢাকায়। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৭ শতাংশ মানুষ ঢাকায় বসবাস করে।
এরপর চট্টগ্রাম নগরে, যেখানে ২০ শতাংশের বেশি মানুষ বাস করে। বাংলাদেশে নগরায়ণ প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নগরায়ণের শর্ত হচ্ছে, নগরে বসবাসের সুযোগ তৈরি, নগর দারিদ্র্য হ্রাস, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রন এবং মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। অথচ নগরায়ণে শুধুমাত্র ঢাকাকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। জনশুমারীর সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার ৩১ দশমিক ৫১ শতাংশ মানুষ নগরে বসবাস করে। ২০৫০ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার ৫৮ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষ নগরবাসী হবে। ১৯৭৪ সালে নগরে বাস করা মানুষের হার ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ৯ শতাংশ। ১৯৭৪ সাল থেকে ২০২২ সময় ব্যবধানে নগরবাসীর সংখ্যা বেড়েছে সাড়ে ২২ শতাংশ। বাংলাদেশে এরূপ নগরায়ণের সবচেয়ে বড় চাপ পড়েছে ঢাকার ওপর। এখন ঢাকা জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বের নবম বৃহত্তম নগর। জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিভাগের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে ঢাকার অবস্থান হবে বিশ্বে তৃতীয়। এ সময়ের মধ্যে ঢাকা ব্রাজিলের সাওপাওলো ও ভারতের মুম্বাইকে ছাড়িয়ে যাবে। অপরপক্ষে বাংলাদেশে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শূন্য থেকে ১৪ বছর এবং ৬৪ বছরের উর্ধ্বে জনগোষ্ঠীকে নির্ভরশীল বলে ধরা হয়। আর ১৫ থেকে ৬৪ বয়সী মানুষ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বলে বিবেচিত। বাংলাদেশে এখন ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়স্ক জনগোষ্ঠী ৬৫ দশমিক ৫৩ শতাংশ। জনমিতির ভাষায় অর্থনীতির এ অবস্থাকে ‘জনমিতিক লভ্যাংশ’– বলা হয়। এ সুবিধাকে যদি যথাযথ ব্যবহার করা যায় তবে অথনৈতিক প্রবদ্ধি হবে দ্রুত। তবে এ সুবিধা ২০৩৫ থেকে ২০৩৭ সাল পর্যন্ত পাওয়া যাবে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ষাটোর্ধ্ব জনগোষ্ঠীর পরিমাণ ৯ দশমিক ২৮ শতাংশ। আর ৬৫ বছরের উর্ধ্ব জনগোষ্ঠীর হার ৫ দশমিক ৮৯ শতাংশ। ২০৫০ সালে ষাটোর্ধ্ব মানুষের হার দাঁড়াবে মোট জনসংখ্যার ১৬ দশমিক ৫ শতাংশ। আর তখন ৬৫ বছরের বেশি বয়সী মানুষের হার দাঁড়াবে মোট জনসংখ্যার ২১ দশমিক ৩ শতাংশ। ২০৬০ সালে বাংলাদেশ হবে সবচেয়ে বেশি বয়সী জনসংখ্যার সপ্তম বৃহত্তম দেশ।
২০২২ সালের জনশুমারিতে দেখা যায়, দেশে প্রথমবারের মতো পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি। দেশে প্রতি ১০০ নারীর অনুপাতে পুরুষের সংখ্যা ৯৮ দশমিক ৪ জন। ২০৫০ সালে তা হবে ৯৫ দশমিক ২৩ জন। কোন কোন অর্থনীতিবিদ মনে করেন, নারী ও পুরুষের এরূপ অনুপাত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর প্রভাব ফেলবে। এ কথা সত্য নাও হতে পারে যদি বর্তমান থেকে সেভাবে জোরালো প্রস্তুতি নেয়া হয়।
বাংলাদেশের জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও আস্তে আস্তে বাড়ছে। ফলে মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। এ শহরমুখীতাকে কমানোর জন্য জেলা ও উপজেলায় মিনি শহর বা উপশহর তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ শুধুমাত্র ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো বড় বড় শহর নগরায়ণ করলে হবে না। অন্যান্য শহরগুলোকেও নগরায়ণের আওতায় আনতে হবে। এতে বড় বড় শহরের বস্তি এলাকা যেমন হ্রাস পাবে তেমনি নগরায়ণের মধ্যেও সমতা আসবে।
লেখক : শিক্ষাবিদ; পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ইউএসটিসি; সাবেক অধ্যক্ষ, গাছবাড়িয়া সরকারি কলেজ।