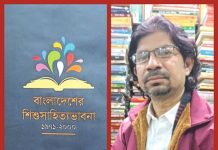দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮০–৮২ শতাংশই হলো পোশাক। আমাদের পোশাক মূলত রপ্তানি হয় ইউরোপ–আমেরিকায়। এ দুটি বাজারে অস্থিতিশীলতা তৈরি হলে তার বিরূপ প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে। আশংকা অনুযায়ী এখন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্ক নির্ধারণের কারণে অশনি সংকেত দেখা যাচ্ছে। দেশের রপ্তানি খাতে সুপারস্টার এখন পর্যন্ত একটাই, তৈরি পোশাক। কেন আমরা অন্য কোনো বিকল্প রপ্তানি পণ্য সুযোগ থাকাও সত্ত্বেও রপ্তানি করতে পারিনি। কারণগুলো হলো, পোশাক শিল্পের ওপর অতিরিক্তি নির্ভরশীলতা, সরকারগুলোর রাজনীতি–অপরাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকা, আর যারা এ বিষয়গুলো পরামর্শ দিয়ে থাকে, তাদেরকে গুরুত্ব না দেওয়া। যেমন, পোশাক শিল্প ছাড়াও আরো সম্ভাবনাময় যে খাতগুলো ছিল বা এখনো আছে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, পাট ও পাটজাত পণ্য ইত্যাদি। কিন্তু পোশাক ছাড়া অন্যান্য খাতগুলো থেকে এক থেকে দেড় বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ে সীমাবদ্ধ। এছাড়া আছে আইটি খাত। এগুলো কোনোটিই সুপারস্টার দূরের কথা স্টারও হতে পারেনি। অর্থনীতির জন্য একটি খাতের ওপর নির্ভরতা ভালো না, এটা এখন টের পাওয়া যাচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের রপ্তানি পোশাকের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণায় দেশের পোশাক শিল্পের ব্যবসায়ীরা দিশেহারা। এই যে এখন পোশাক খাতে শুল্ক নির্ধারণ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যে সমস্যাগুলো হলো তা নিয়ে দেশের বিশেষজ্ঞরা অনেক আগে থেকেই বলেছিল কিন্তু কোনো সরকারই পাত্তা দেয়নি। অথচ আজ আমরা এই সংকটে পতিত। এখন যদি যুক্তরোষ্ট্রর পর ইউরোপিয়ন ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশগুলো বাংলাদেশের সাথে একই শুল্ক নির্ধারণ করে তাহলে পোশাক শিল্পের কী অবস্থা হবে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য এক কঠিন সময় আসন্ন।
এই উচ্চ শুল্ক কেবল পোশাক খাতকেই নয়, এর সঙ্গে জড়িত চট্টগ্রাম বন্দর, ব্যাংকিং খাত এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্পকেও বড় ধরনের সংকটে ফেলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই খাতে আমারা যাদের সাথে প্রতিযোগিতা তাদের ওপর শুল্ক কেমন তাও বিবেচনায় নিতে হবে। এখন আমাদের প্রতিযোগী দেশ ভারত, চীন, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া। তাদের ট্যারিফ অনেক কম। ফলে যদি আমাদের শুল্ক তাদের সমপর্যায়ে না নেওয়া যায়, তাহলে তো প্রতিযোগিতায় টিকতে বেগ পেতে হবে। বাংলাদেশের শুল্কহার তো তাদের তুলনায় ১৫–২০ শতাংশ বেশি হবে। এরইমধ্যে পোশাকের অর্ডার হারাতে শুরু করেছে ব্যবসায়ীরা। যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক নির্ধারণে চট্টগ্রামের গার্মেন্টস শিল্প সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ চট্টগ্রাম থেকে পোশাক রপ্তানির ৪০ শতাংশেররই গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র। এ কারণে ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক এই অতিনির্ভরতাকে বড় ঝুঁকিতে ফেলেছে চট্টগ্রামের উদ্যোক্তাদের। আশি–নব্বই দশকে যুক্তরাষ্ট্রের কোটাসুবিধা নিয়ে চট্টগ্রামের উদ্যোক্তারা ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছিলেন। যোগাযোগব্যবস্থাসহ নানা কারণে চট্টগ্রামে সে সময় অন্য দেশের ক্রেতারা আসতে চাইতেন না। ফলে ঢাকার কারখানাগুলো শুধু কোটার ওপর নির্ভরশীল ছিল না, অন্য দেশের ক্রেতাদের কার্যাদেশ পাওয়ার সুযোগ ছিল। চট্টগ্রামের সে সুযোগ কম থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা বেড়েছে।
প্রধান এই রপ্তানি খাতের সঙ্গে জড়িত প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক–কর্মচারী। যুক্তরাষ্ট্রের এই পাল্টা শুল্কের ধাক্কায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে এ কর্মসংস্থানে। আলোচনার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত শুল্ক ঠিক হবে। কিছু দেশ তো শুল্ক কমিয়ে নিয়েছে, তাহলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যারা নেগোসিয়েশনে করেছেন বা করছেন, তাদের তুলনায় আরও অধিকতরযোগ্য লোক দেশে ছিল, কেন তাদেরকে নেওয়া হয়নি। বিদেশের বাজারে আরেকটি সম্ভাবনাময় খাত হলো জুতা শিল্প। এটি দ্বিতীয় বৃহৎ রফতানিমুখী শিল্প খাত না হয়ে ওঠার কারণ হচ্ছে, রপ্তানিতে আমাদের একটা নিরীহ ব্যবস্থা ধরে রাখা। বিদ্যমান ব্যবস্থায় রপ্তানি করলে মুনাফার হার বেশি হয় না। দেশীয় বাজারে বিক্রি করলে যে লাভ হয় রপ্তানি তা হয় না। কিন্তু রপ্তানি বাজারে প্রবেশ করলেই আমাদের জুতা শিল্প বড় হওয়ার সুযোগ তৈরি হতো এবং এতে তৈরি পোশাক খাতের মতো কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতো। প্রথমত কথা হলো, বাণিজ্য শুল্ক দিয়ে দেশীয় বাজারকে লাভজনক করে রাখার ব্যবস্থাটা ভালো নয়। এতে রপ্তানি করার প্রণোদনা হারান উৎপাদকরা। দ্বিতীয়ত, দেশীয় বাজার আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় অনেক ছোট। এখানে শিল্পের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শুধু মুনাফা করা নয়। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। রফতানিমুখী শিল্পে যেমন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, দেশীয় শিল্পে এ রকম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা যায় না। বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার অনেক বড় হয়েছে। এখন তা ৪৬০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি। স্বাধীনতা–পরবর্তী সময়ের তুলনায় দেখলে বেশ বড়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজার হচ্ছে ১০০ ট্রিলিয়ন ডলারের। আমাদের তাই আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের লক্ষ্য নিয়েই এগোনো উচিত। এতে যেমন অসংখ্য কর্মসংস্থান হবে তেমনি বড় হবে আমাদের অর্থনীতির আকার।
বাংলাদেশে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য মোট রপ্তানির ৫০ শতাংশ ছিল। যা সেই সময়ের সব পণ্য রপ্তানির শীর্ষে ছিল পাটের অবদান। তবে আশির দশকের শেষার্ধে পোশাক শিল্পের রপ্তানির গতি বৃদ্ধি পায়। এবং পোশাক শিল্প রপ্তানি খাতের শীর্ষে চলে আসে। ১৯৯৯ সালে এই শিল্পের ব্যাপক উত্থান ঘটে। পাট শিল্পের সবচেয়ে ইতিবাচক দিকটি ছিল আমাদের দেশে এর ব্যাপক ফলন হয়। অর্থাৎ এ শিল্পের কাঁচামাল দেশেই পাওয়া যায়। আমাদের জুট মিলগুলোও ছিল অনেক বড়। আদমজী জুট মিলস পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাট কারখানা ছিল। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের শিল্প খাত বলতে ছিল পাট শিল্প। বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী খাত হিসেবে গুরুত্বের কারণে পাটকে বলা হতো সোনালি আঁশ। অথচ এই সম্ভাবনাময় খাততে আমরা অবহেলায় শেষ করে দিয়েছি। শুধুমাত্র তৈরি পোশাক শিল্পের উপর নির্ভরশীলতা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি ঝুঁকিপূর্ণ দিক। অনেক আগে থেকে বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে বারংবার সতর্ক করলেও কোনো সরকারই আমলে নেয়নি। তৈরি পোশাক শিল্প দেশের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু এর উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতকে অবহেলা করার দিকে পরিচালিত করেছে।
পোশাক শিল্পের বাইরে, বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে নিম্নলিখিত খাতগুলিতে মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ: খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিনিয়োগ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে রফতানি বাড়ানো সম্ভব। তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) ও ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিস: আইটি খাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও উন্নয়নশীল প্রযুক্তি যেমন– আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিক্স, ব্লকচেইন ইত্যাদিতে মনোযোগ দিলে নতুন কর্মসংস্থান ও রফতানি সুযোগ তৈরি হবে। ফার্মাসিউটিক্যালস: ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল (এপিআই) উৎপাদনে মনোযোগ দিলে, আমদানিনির্ভরতা কমে আসবে এবং রপ্তানি আয়ও বাড়বে। হালকা প্রকৌশল শিল্প: হালকা প্রকৌশল শিল্পের উন্নতি ঘটিয়ে যন্ত্রাংশ, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি তৈরি করে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ এবং রপ্তানি করা যেতে পারে। পর্যটন : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহাসিক স্থান ও সংস্কৃতি পর্যটকদের আকর্ষণ করতে পারে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি: সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎ–এর মতো নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ করে পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ সংকট মোকাবিলা করা যেতে পারে। এই খাতগুলোতে মনোযোগ দিলে, পোশাক শিল্পের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমে আসবে এবং কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।
লেখক : কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক