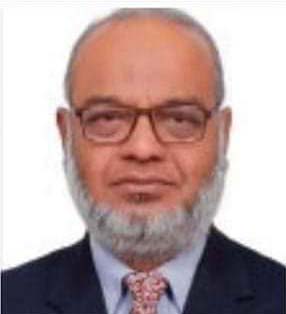কয়েকদিন আগে মিরসরাইয়ের কাছাকাছি একটি জায়গায় যাত্রা বিরতি করে দেখি, সেটি একটি জুট মিলের সামনে। সাইন বোর্ডে জুট মিল লেখা দেখে কৌতুহল বশত ভিতরে ডুকে দেখি জরাজীর্ণ সব অবকাঠামো।বিল্ডিংয়ের পলেস্তার খসে পড়েছে। ছাদের টিন ফুটো। মনে হয় ভূমিকম্পে বিধস্ত কোনো স্থাপনা। খালি জায়গায় আগাছায় ভরা। এখানে সেখানে পরিত্যক্ত বিভিন্ন কলকব্জা। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম চারিদিকের অনেক জায়গায় সব্জি চাষ হচ্ছে, এক পাশে গরুর খামার করা হয়েছে। দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো।এইটি শুধু এই জুট মিলের অবস্থা নয়। দেশের প্রায় সব সরকারি জুট মিলের একই অবস্থা। ভাবছি একসময় দেশের প্রধান ঐতিহ্যবাহী রপ্তানি খাত, এখনো দেশের প্রধানতম রপ্তানি পণ্য পাট ও পাটজাত পণ্যের কারখানার কেন এই জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা? কেন এমন হলো?
পাটের ইতিহাস বড়ই করুণ। ব্রিটিশ আমলে বাংলার উৎপাদিত পাট দিয়ে কলকাতার পাটকলগুলো চলত। বাংলার দায়িত্ব ছিল পাট ফলিয়ে তা সস্তায় পাঠানো। দেশ ভাগের পর সেসব পাটকলের কোনটিই পূর্ব বাংলায় পড়েনি। এরপর পাকিস্তান আমলে পাটকল গড়ে উঠল ঠিকই কিন্তু তার সুফল পেল পশ্চিম পাকিস্তান।দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভাবা হয়েছিলো পাটই হয়ে উঠবে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী পণ্য। পাটের টাকা দিয়ে দেশ এগিয়ে যাবে উন্নতির শিখরে। কিন্তু এখন বাংলাদেশ হচ্ছে বিদেশী পাটকলের কাঁচামালের জোগান দাতা। পাকিস্তান আমলে সোনার ডিম পাড়া হাঁস ছিল বাংলাদেশের পাটশিল্প। পাট রপ্তানির টাকা দিয়ে ইসলামাবাদ, করাচি শহর গড়ে উঠলেও অবহেলিত রয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তান। এ প্রেক্ষিতে ‘সোনার বাংলা শ্মশান কেন’ দাবি তুলে দানা বাঁধে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। পাট রপ্তানির ন্যায্য হিস্যা না পাওয়া ছিল আঞ্চলিক বৈষম্য। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনের এক পর্যায়ে রূপ নেয় স্বাধিকার আন্দোলন। বলা যায়, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পেছনে পাটের অবদান অপরিসীম।
শুধু তাই নয়, বাঙালি মুসলমানের বিকাশের পেছনেও ছিল পাটের বিশেষ ভূমিকা।উনিশ শতকের শেষ দিকে জমিদারি আইনে সংস্কার হলে বাংলায় পাটের উৎপাদন বাড়ে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় বিশ্ব বাজারে পাটের চাহিদা বেড়ে যায়।পাটের আয়ে গ্রামের কৃষক, ফড়িয়া ও পাটের আড়তদারের সন্তানেরা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু করে।ফলে কৃষকের সন্তানের শিক্ষিত হওয়ার পিছনে পাটের ভুমিকা অপরিসীম। যে পাটের বঞ্চনার কথা বলে ছয় দফা জয়যুক্ত হলো। স্বাধীনতার পর জাতীয়করণের ফলে পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া পাটকলগুলো নেতা ও আমলাদের লুটপাটের আখড়ায় পরিণত হলো। আশা ছিল, স্বাধীন দেশে বাঙালিদের দায়িত্বে ও কর্তৃত্বে পাটশিল্পের জয়জয়কার হবে। দুর্নীতির ব্যাপকতার ফলে সরকার গেলো বেসরকারী করণের পথে। বেসরকারীকরণ হয়ে উঠলো সরকারি সম্পদ সরকারের ঘনিষ্ঠদের হাতে তুলে দেওয়ার শর্টকাট পথ।এর ধারাবাহিকতায় ১৯৮২ সালে বিশ্বব্যাংকের কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি মেনে সরকার শিল্পনীতি ঘোষণা করলো। সরকারি মালিকানাধীন ৬৫০টি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমালিকানায় ছাড়া হলো।এটাই ছিল এযাবৎকালে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেসরকারীকরণ।এতে ৬২টি পাটকলের মধ্যে ৩৩টি বিক্রি করা হয় এমন লোকদের কাছে,যাঁদের শিল্প চালানোর কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে শিল্পগুলো রুগ্ন হয়ে পড়ে। এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে সরকার এশিয়ার সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজীকে বন্ধ করে দেয়। ১৯৭২ সালের ‘জাতীয়করণ’, ১৯৮২ সালের ‘বেসরকারীকরণ’ আর ২০০২ সালে আদমজীর ‘গোল্ডেন হ্যান্ডশেক’,সবই ছিল পাটশিল্প সর্বনাশের এক একটি অধ্যায়।তখন ১ হাজার কোটি টাকা খরচ করে পাটকলগুলোর আধুনিকায়ন করা সম্ভব ছিল।কিন্তু সরকার সেই পথে না গিয়ে শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের তহবিলে রেখেছিলো ৫ হাজার কোটি টাকা!
স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ৭৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের সমন্বয়ে গঠন করা হয় বিজেএমসি। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে বিজেএমসি আরও ৪টি পাটকল স্থাপন করলে সংখ্যা দাঁড়ায় ৮২তে। তবে পরের বছর ১৯৮২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বেসরকারীকরণ নীতিমালার আওতায় ৩৫টি পাটকল সাবেক বাংলাদেশি মালিকদের কাছে শর্তসাপেক্ষে হস্তান্তর, ৮টির পুঁজি প্রত্যাহার এবং ৭টি বিক্রি করে দেওয়া হয়।এরপরও বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণে ছিল ৩২টি পাটকল।২০০২ সালে সরকার আদমজী জুট মিলস লিমিটেড ও এবিসি লিমিটেডকে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) কাছে হস্তান্তর করে।পরে শর্ত ভঙ্গের কারণে ২০১৪ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে মালিকানায় দেওয়া পাটকলগুলোর মধ্যে ছয়টিকে পুনঃগ্রহণ করে আবার বিজেএমসিকে দেয়া হয়।দুই বছর পর ২০২০ সালে ২৫টি পাটকল বন্ধ করে দেয়া হয়। গত বছরের মাঝামাঝি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের জুটো ফাইবার গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ কারখানাটি বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কাছে হস্তান্তর করে সরকার। বর্তমানে বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণে আছে ৩৫টি পাটকল, সব কারখানা বন্ধ। এগুলো বন্ধ করার সময় বিজেএমসিতে কর্মরত ছিলো ২,৯৪১ কর্মকর্তা কর্মচারী এবং এখনো কর্মরত আছে ২,৫১৭ কর্মকর্তা কর্মচারী। এরমধ্যে রাজধানীর মতিঝিলে বিজেএমসির প্রধান কার্যালয়ে ১৫৪ কর্মকর্তা ও ১১০ কর্মচারী আছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, বিজেএমসির সব কারখানা বন্ধ থাকলেও প্রধান কার্যালয়ের উৎপাদন বিভাগে এখনো কর্মরত আছে ১০ কর্মকর্তা। লোকসানের অজুহাতে কারখানা বন্ধ ও শ্রমিক ছাঁটাইয়ের পরও প্রতিবছর লোকসান দিচ্ছে বিজেএমসি।এরমধ্যে গত অর্থ বছরে বিজেএমসির লোকসান দেয় ২৬০ কোটি টাকার বেশি। কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন, সম্পত্তি মেরামত, তদারক ও রক্ষণাবেক্ষণ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি খাতে এই লোকসান হয়।এর মধ্যে কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বাবদ সবচেয়ে বেশি ১৪০ কোটি টাকার বেশি ব্যয় হয়।বিজেএমসি এখন বন্ধ পাটকল ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।সে লক্ষ্যে ২০২১ সালের এপ্রিলে ১৭টি (মূলত ২১টি, নরসিংদীতে তিনটি কারখানা মিলে ইউএমসি জুট মিলস লিমিটেড এবং চট্টগ্রামে তিনটি মিলে কেএফডি নামে পরিচিত) ভাড়ার অনুমোদন দেয় মন্ত্রণালয়। গত নভেম্বরে অনুমোদন দেয় আরও দুটি কারখানা। এখন পর্যন্ত বিজেএমসি মাত্র ছয়টি (মূলত আটটি) পাটকল ভাড়া দিয়েছে। ভাড়া ছয় পাটকলের মধ্যে চারটি চালু করা হয়েছে। তবে যাদের কাছে এসব পাটকল ভাড়া দেওয়া হয়েছে,তাদের কেউই পাট ব্যবসায় সম্পৃক্ত নয়। বিজেএমসির শর্ত ছিলো এসব পাটকল ভাড়া নিয়ে পাট ও টেঙটাইল পণ্য উৎপাদন করতে হবে।এসব পাটকল সর্বোচ্চ ৩০ বছরের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। মাসে সর্বনিম্ন ২২ লাখ ৫০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৪২ লাখ ৬০ হাজার টাকায় কারখানা ভাড়া দিয়েছে বিজেএমসি। তবে যারা পাটকলগুলো ভাড়া নিয়েছেন তারা কেউ কেউ আংশিকভাবে পাটের বস্তা বানাচ্ছে। তবে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের অভিমত হলো বিজেএমসির কারখানা বেসরকারি পাটকল মালিকেরা নিতে চান না। কারণ সরকারের সহযোগিতার অভাবে বেসরকারি পাটকল মালিকেরা আন্তর্জাতিক বাজারে টিকতে পারে না। তার উপর যন্ত্রপাতি পুরোনো,এগুলো আধুনিকায়নে অনেক টাকা খরচ করতে হবে। সেজন্য তারা সরকারকে একটি তহবিল গঠনের অনুরোধ করেছিলো। কিন্তু সরকার এতে সাড়া দেয়নি। তবে ভাড়া দেওয়ার পরেও এখনো ২৭টি পাটকল অলস পড়ে আছে।এতে যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছে। ভবনগুলোতে ময়লার স্তূপ, গাছ লতা পাতায় ছেয়ে আছে। সংশ্লিষ্টরা বলেন, পাটকলগুলোকে এভাবে বসিয়ে রেখে যন্ত্রপাতি সচল রাখা কঠিন। এভাবে চলতে থাকলে আর কিছুদিন পর এসব যন্ত্রপাতি স্ক্রেপ লোহা হিসাবে বিক্রি করতে হবে। এর ফলে পাটকলগুলোর যবনিকাপাত ঘটে একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে।
লেখক : প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট