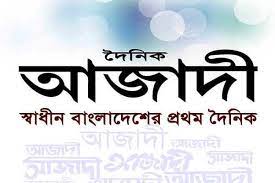চিয়াং কাইশেক, মাও এবং লং মার্চ
অপমানের শতবর্ষ পেরিয়ে সবাইকে নিয়ে এ মুহূর্তে যাদুঘরের যে অংশে এসে পৌঁছেছি, সেটিকে বলা চলে মূলত ভাস্কর্য আর পেইন্টিং এর গ্যালারী। অবশ্য ছবি, মানে ফটোগ্রাফও আছে বেশ এখানে। এদিকে ছোঁয়াফোনের পর্দায় চকিত চোখ যেতেই ঘোষণা করল তা যে বরাদ্দকৃত সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত! খুব বেশী নেই সময় হাতে। দ্রুতই দেখতে হবে সব এরকম মনস্থ করে দেয়ালে সাঁটানো নানান চিত্রকর্ম আর ফটোগ্রাফগুলো দেখতে, মানে দৌড়ের উপর চোখ বোলানো শুরু করতেই , দলের বাকীরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল নানান ভাস্কর্য ঘিরে ছবি তোলায় ।
ঐসব ছবি আর ফটো হাঁটতে হাঁটতে দেখতে দেখতে এখানকার প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু যে মনে হলো, তা হল প্রথমত এক সময়ের আধা উপনিবেশিক পুরোসামন্ত চায়নার নানান দেশী বিদেশী শ্ত্রুদের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই। দ্বিতীয়ত চায়নিজ কমিউনিস্ট পার্টির সেই বিখ্যাত লং মার্চ, এবং সবশেষে সাংষ্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক চায়নার গোড়াপত্তনের সচিত্র কাহিনী দর্শকের সামনে তুলে ধরা । এই যেমন এইমাত্র যে সব ছবি আর পেইন্টিংয়ে চোখ বুলিয়ে পেরিয়ে এলাম, ওগুলোর বিষয়বস্তু ছিল, চায়নার একসময়ের জাতিয়াবাদী নেতা চিয়াং কাইশেকের জাতীয়তাবাদী সৈন্যদলের সাথে চায়নিজ কম্যুনিস্ট পার্টির রেড আর্মির লড়াই ।
ছাত্রবস্থায় পাঠ্যপুস্তকে যেভাবে ইতিহাস পড়তে বাধ্য হয়েছিলাম, তাতে ইতিহাসের ব্যাপারে একটা চরম অরুচি তৈরি হয়েছিল। ফলে পাঠসূচি থেকে ইতিহাস বাদ হয়ে যেতেই মহা আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে বুঝেছিলাম ইতিহাস জানাটা কতোটা গুরুত্বপূর্ণ, অতএব আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম তাতে, আছে যা বজায় এখনও। তবে সমস্যা হল যে কোন ইতিহাসেরই সঠিক হদিস পেতে গেলে পড়তে হবে, জানতে হবে নানান উৎসের বইপত্র, খোঁজ নিতে হবে ঐই সময়ের দলিল দস্তাবেজের। এইরকম আগ্রহ যতদিনে তৈরি হয়েছিল ভেতরে, ততোদিনে তো জীবন জীবিকার লড়াইয়ে এতোই ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, পরিকল্পনা করে প্রকৃত ইতিহাসের বই খুঁজে পেতে পড়ার ইচ্ছা থাকলেও, পড়া হয়নি তা তেমন ভাবে। পড়েছি যা, তা হল বলা চলে আধখেঁচড়া ভাবে, ফলে বুঝেছি সব খামচে খামচে।
যৎসামান্য চায়নার ইতিহাস যা জানি ঐ রকম আধখেঁচড়া, খামচা খামচা, সেইরকম খালি কলসির ঠনঠনা জ্ঞানে এখানকার নানা ছবির বিষয়বস্তু মেলাতে গিয়ে পড়লাম এক্কেবারে বিষম বিভ্রাটে । গোলক ধাঁ ধাঁয় পড়লাম বেশী চায়নার তিরিশ আর চল্লিশ দশকের, মানে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তি সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি মেলাতে গিয়ে। আবছা ভাবে ধোঁয়াশার মতো বেড়িয়ে আসছে যা ঐ খালি কলসি থেকে তাতে মনে হচ্ছে, ঐ সময় নানান বিদেশী আগ্রাসনে বহুধাবিভক্ত মহাচীনকে একসুতায় বাঁধার জন্য, চিয়াং কাইশেকের কুন মিং টাং আর চায়নিজ কম্যুনিস্ট পার্টি গাঁটছড়া বেঁধেছিল একসাথে। কিন্তু তাদের সেই দোস্তিতে কি কারনে কখন যে চিড় ধরেছিল তা আর মনে করতে পারছি না, মেলাতেও পারছি না।
তবে এটা মনে পড়ছে যে, গাঁটছড়া ভেঙ্গে যাবার পর চিয়াং কাইশেক চায়নিজ সামন্ত প্রভুদের দিকে তাক করা তার কামান বন্দুক সব ঘুরিয়ে দিয়েছিল কম্যুনিস্টদের দিকে। অতএব শুরু হয়ে গিয়েছিল চায়নিজ জাতিয়াতবাদি আর সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ। সেই গৃহযুদ্ধেরই এক পর্যায়ে কম্যুনিস্টরা তাদের রেড আর্মি নিয়ে শুরু করেছিল বিখ্যাত লং মার্চ , যার পুরোভাগে চলে এসেছিলেন মাও সে তুং একসময়। অবশেষে সেই লং মাচের্র বিজয়ের সুচনা হতেই , চিয়াং কাইশেককে পালাতে হয়েছিল তাইওয়ানে। পত্তন করতে হয়েছিল আরেকটি নতুন রাষ্ট্রের, অথচ চিয়াং ও তো চায়নার এই বিভক্তি চান নি। কিন্তু কি আর করা? ইতিহাসের গতিপথ তো এভাবেই সময়ের পরিক্রমায় নিয়েছে এমন এক ভিন্ন দিকে মোড় যা হয়তো ঐসব ইতিহাসের নির্মাণকারীরা চাননি আদৌ শুরুতে। ঘটেছে এমন এ গ্রহের নানান অংশেই। কেউ মানুন আর না মানুন, সভ্যতা নিয়ে বড়াই করা মানুষের ইতিহাসের পথ কিন্তু বড়ই রক্তপিচ্ছিল।
দেখতে দেখতে, ভাবতে ভাবতে, হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়িয়েছি এক্ষণে লাল পতাকা উঁচিয়ে ক্ষেত খামার, ঝোপঝাড়, পাহাড় পর্বতের বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে সদর্পে এগিয়ে যাওয়া রেড আর্মির একটা বড় ছবির সামনে। একই রকম আরো বেশ কটা ছবি আছে এখানকার, ডানে, বাঁয়ে, উপরে, নীচে। ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার অনুভব করতে পারছি যাবতীয় বাধাবিপত্তি, ঝড়ঝঞ্ঝা তুচ্ছ করে সামনে এগিয়ে যাবার যে জীবনমরণ দুমর্র প্রতিজ্ঞাটি ছিল এই লালবাহিনীর, তা! অর্থাৎ যে এক বা একাধিক শিল্পীরই আঁকা হয়ে থাকুক না কেন এই ছবিগুলো, সার্থক হয়েছেন তাঁরা।
এক লাখের কিছু বেশী সৈন্য আর লোকবল নিয়ে শুরু করা বিশাল আকারের লং মার্চটি নিয়ে সামনে এগুতে গিয়ে এক বছরেরও বেশী সময় ধরে, প্রতিপক্ষের আক্রমণের জবাবে আত্মরক্ষার সাথে সাথে পাল্টা আক্রমণ করতে গিয়ে যেমন হয়েছিল সেই মিছিলটির লোকক্ষয়; তেমনি নানান প্রাকৃতিক বৈরিতার ভেতর দিয়ে হেঁটে, সুদীর্ঘ ৯০০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে গিয়ে মারা পড়েছিল আরো অনেকেই! ফলে শেষ পর্যন্ত নাকি বেঁচেছিল ঐ মিছিলের মাত্র হাজার আটেক লোক। যাবতীয় রকম চরম বৈরি পরিস্থিতির মোকাবেলা করে দীর্ঘ ও বিপদসংকুল এই পদযাত্রায় যে হাজার আটেক লোক বেঁচেছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টির জন্য পরবর্তীতে হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা সবাই, যাকে বাংলায় বলে এক্কেবারে আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনা হওয়া, তা। আর সেই লং মার্চের নেতৃত্বে তখন ছিলেন যেহেতু মাও, ফলে সেই আট হাজার জনই হয়ে উঠেছিল তাঁরই একনিষ্ঠ ভক্ত ; তাতে চায়নিজ কমিউনিস্ট পার্টিতে মাওয়ের নেতৃত্ব হয়ে উঠেছিল শক্ত ও পাকাপোক্ত।
“মুক্তির মন্দির সোপান তলে, কতো প্রাণ হলো বলিদান “লেখা আছে তা এই দেয়ালে; লং মার্চের ছবিগুলো দেখতে দেখতে অবচেতনের সেই দ্বিতীয়জন বিখ্যাত ঐ গানকে প্যারোডি করল। কিন্তু সেই প্যারোডিতে গলা না মিলিয়ে প্রথমজন বলে উঠলো শোন, সেই যে লক্ষপ্রাণ যাঁরা অকাতরে দিয়েছিল নিজ নিজ শোণিত ও জীবন সেই দুর্গম আর অনিশ্চিত যাত্রায়, তাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে তো অবশ্যই জানাতে হয় লাল সালাম, এবং আমি জানাই ও তা। তবে আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করো, তাবৎ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা আর মনুষ্যসৃষ্ট হিংগ্র বৈরিতা সামলে, প্রতিনিয়ত সহযোদ্ধা কমরেডদের জীবনহানীর তুমুল দুঃখ, বেদনা, ক্রোধ মোকাবেলা করে; যে কোন সময়ে প্রত্যেকের অতিসম্ভাব্য জীবনহানীর ভয়কে জয় করে সে মিছিলটি যে এগিয়ে গেল বিজয়ের দিকে, অবশিষ্ট মাত্র হাজার আস্টেক যোদ্ধাকে নিয়ে, লক্ষে তাদেরকে স্থির রাখার ব্যাপারে মাও যে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে রাখতে পেরেছিলেন শেষ পর্যন্ত, সেটা অতিঅবশ্যই এক বিরাট, বিরাট ব্যাপার! নেতৃত্বের শুধু এই দুর্লভ ক্ষমতাটির জন্যে হলেও মাওয়ের ঘোরতর শত্রুকেও মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম ঠুকতে হবে মাওকে।
ঐ তো দেখছি বাঁয়ের দেয়ালের বেশ কিছুটা উপরের দিকে লাগানো বড় তৈলচিত্রটি। আচ্ছা এটা কি তৈল চিত্র ? হউক তা যে কোন চিত্রই , তাতে কিছু যায় আসে না। আসে যায় যা আমার মতো শিল্পনির্বোধের কাছে ,তা হল ঐ চিত্রকর্মটির বিষয়বস্তু। ফলে এগিয়ে গিয়ে ঘাড় পেছনে কাত করে উপরে লটকে থাকা সেই চিত্রকর্মটি গভীর মনোযোগে জরীপ করতে লাগলাম।
ছবিটি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করার কারণ হল, এর নীচে লেখা আছে যে এই ছবিটিতে মাওয়ের সাথে যাঁরা আছেন, তাঁরা সবাই হলেন মাওয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর। লং মার্চে তাঁরা সবাই ছিলেন কি না জানি না , তবে যতোটুকু বুঝতে পারলাম, আমরা যাঁকে ঈসা নবী (আঃ) বলি আর বাকী বিশ্ব যাঁকে চেনে যেসাস নামে ,তাঁর যেমন ১২ জন ছিল ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সহচর , এই ছবিতে যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই মাওয়ের ঐরকমই সহচর। তবে তফাৎ নিশ্চিত একটা আছে! আর তা হলো যিশুর সেই ১২ জন ঘনিষ্ঠ সহচরের মধ্যে একজন ছিল বিশ্বাসঘাতক। তিনি তা যে জানতেনও, তাঁর সেই বিখ্যাত “লাস্ট সাপার” এ সেই ১২ জনকে নিয়ে খেতে বসে, কাউকে নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত না করলেও, পরিষ্কার বলেছিলেন তা যিশু! সে জায়গায় মাওয়ের এই দলটির ভেতর নিশ্চয় কোন বিশ্বাসঘাতক ছিল না। কারণ যদি সে থাকতোই, তবে তাঁর ছবি নিশ্চয় এখানে লটকানো থাকতো না। জানা থাকা সত্বেও যিশু যেমন সজ্ঞানে তাঁর সেই বিশ্বাসঘাতক অনুচরের ব্যাপারে নিরুদ্বেগ থেকে , নিয়তি কে জয়ী করে এগিয়ে গেছেন ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার জন্য, এ ব্যাপারে মাও ছিলেন অত্যন্ত ভয়ংকর কঠোরহস্ত। যে কোন বিরুদ্ধতাকে মাও দমন করেছেন সবসময়ই কঠিন হস্তে, কঠোর নিষ্ঠুরতায়।
ছবিতে চোখ বুলিয়ে মাওকে খুঁজে বের করতে পারলাম সহজেই। কারণ সকলের মধ্যমণি হিসাবে ছবিতেও আছেন উনি এক্কেবারে মাঝামাঝি জায়গাতেই। কিন্তু বাকীদের কার নাম যে কি? তা তো জানি না, আবার চিনিও না তাদের। পোশাকে আশাকে চেহারায় বাকী সবাইকেই তো চায়নিজই, মানে একই চেহারা যমজই মনে হচ্ছে শুধু! আচ্ছা আছে ক’জন এ ছবিতে?
ঘাড় পেছনে হেলিয়ে উরধ্মুখে চোখ চালিয়ে ঐ ছবির মানুষের সংখ্যা গুনতে গিয়ে দেখছি, বারবারই খেই হারিয়ে ফেলছি। অতএব অচিরেই বাদ দিলাম সে চেষ্টা। তারচেয়ে বরং খুঁজতে শুরু করলাম এই দলে ক’জন মহিলা সদস্য আছেন তা? যদিও খুব একটা কথা হয় না এ ব্যাপারে, তারপরও মাওয়ের নারীপ্রীতি ও যৌনস্বেচ্ছাচারিতার বিষয়টি জানেন অনেকেই। তবে এ মুহূর্তে যে কারনে ছবিতে নারীর উপস্থিতি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি, তার সাথে মাওয়ের একান্ত ব্যাক্তিগত ঐসব বিষয়ের কোন যোগ নেই। বরং বুঝতে চেষ্টা করছি, সমাজতন্ত্রে যেহেতু নারী পুরুষের সমানাধিকারের ব্যাপারটি খুব উঁচু গলায় ঘোষণা করা হয়, এবং করেছিলেন তা মাও নিজেও, সে রকম একটা অবস্থায়, তাঁর এই ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের মধ্যে আসলেই ক’জন ছিলেন মহিলা!
“বৃথা এ সাধনা ধীমান” মনের দ্বিতীয়জন বলে উঠলো হেসে প্রথমজনকে; যেহেতু ছবিতে হদিস করতে পারলাম না আছে কি না কোন নারীনেত্রী। ছবির সকলের চুলের কাট, পোশাকের ছাট, আর চেহারার ধাঁচ সব একই রকম ঠেকছে বলে, ছবি দেখে লিংগ নির্ধারণ করার চেষ্টা, গেল বিফলেই এক্কেবারে।
লেখক : প্রাবন্ধিক, ভ্রমণ সাহিত্যিক