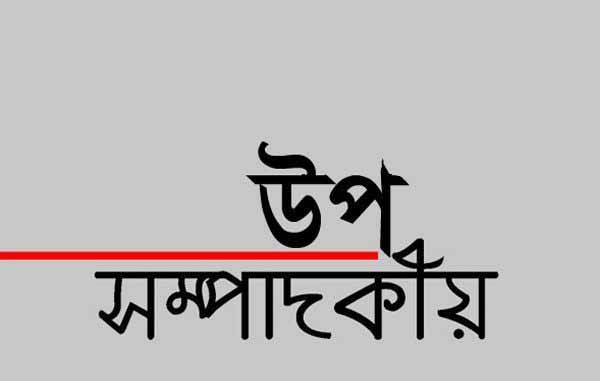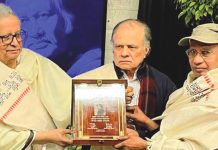আচ্ছা কেনাকাটা তো হবে পরে। আগে দেয়া যাক চক্কর একটা গোটা হলঘরটায়। চৌকোনাএই বিশাল হলঘরের চারদিকেই যেমন আছে নানান আকারের স্টল, তেমনি এর মাঝখানটা জুড়ে কোমড় সমান উঁচু একটা বেদি মত আছে, এ মাথার ও মাথার অনেকটা জুড়েই। তাতে ঐ উঁচু বেদিটাকে বিশাল হলঘরের মাঝে পিঠ তুলে রাখা দ্বীপের মতোই লাগছে। এই দ্বীপটাও খালি নয়। এখানেও আছে আচার, মোরব্বা ক্যান্ডির স্টল। আমাদের দেশের নানান জেলা শহরে সরকারীভাবে তৈরি করা মাছ বাজারের মাঝখানেও এরকম উঁচু বেদি থাকে দেখেছি, যেখানে মাছ বিক্রেতারা মাছের পসরা সাজিয়ে বসে। এখানেও তেমনি দেখছি স্তুপাকারে সাজানো আছে এদের পণ্যের পশরা। হাবেভাবে কেন জানি মনে হচ্ছে এই দ্বীপের স্টলগুলোই বুঝি এখানকার রাজা। অতএব ঠিক করলাম এক সন্ধ্যায় ঘুরে ঘুরে চারদিকের সব স্টলের স্যাম্পল তো টেস্ট করা যাবে না, তারচেয়ে বরং থাকি এই দ্বীপ নিয়েই।
কিন্তু এই দ্বীপে তো দেখছি একই স্টলেরই পাশাপাশি রাখা,দেখতে অনেকটা একই রকমের সেলোফেন মোড়া আঁচার/মোরব্বা/ ক্যন্ডিরে দামে বিস্তর তফাৎ। আগে না হয় ঐপাশের ভিন্ন দুই স্টলে, কম বেশী দুই রকম দাম দেখেছিলাম, বাহ্যিকভাবে মোটামুটি একই রকম দেখতে এই খাদ্যবস্তুসমূহের। এখন তো দেখছি একই ঘটনা এই দ্বীপের একই স্টলের পণ্যেই। তাতে তো বুঝতে পারছি না আরও, যে নেবো কোনটা? মানে কম দামেরটা নেব? নাকি বেশী দামেরটা? যৌক্তিক হিসাবি মন বলছে আমার, কম দামের একই পণ্য থাকতে বেশী দাম গোনে কোন বেকুবে?
অন্যদিকে আবেগি মন বলছে, আরে দূর বেশী দামেরটা আসলে ভাল; তাই তো ঐটির বেশী দাম। বাইরে থেকে দেখেই কি বোঝা যায় নাকি আছে কি ভেতরে? বেইজিং কিম্বা চায়নাতেই আবার কবে যে আসবে তুমি, তার কি আছে নাকি ঠিক ঠিকানা কোন? নেবেই যখন ভালোটাই নাও।
ভালো টা মানে? এ পর্যন্ত বেশ ক’টাই তো স্যাম্পলই চেখে দেখলাম। ওগুলোর প্রতিটিরই স্বাদে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও কোনটা যে খারাপ আর কোনটা ভাল, তা তো বলা যাচ্ছে না। তদুপরি পর পর কয়েকটা স্যাম্পল চাখার পর, এখনতো আর আলাদাই করতে পারছি না, কোনটার স্বাদ কই রকম। হয়েছে অবস্থা এখন আমার ঐ রকম, হয় যেরকম পারফিউম কিনতে গিয়ে। প্রথম দু তিনটা পারফিউম পরখ করার পর, তারপর আর যে পারফিউমই শুঁকি না কেন, আলাদা কিছু বুঝতে পারি না। এ কারণে পারফিউমের দোকানে তো জানি কফি বীজ রাখে পারফিউম বিক্রেতারা। কোন ক্রেতা দুয়েকটা পারফিউম শোঁকার পর তুমুল সুগন্ধে যখন তার নাক ভির্মি খেয়ে গিয়ে বাকি সব সুগন্ধিকে আলাদা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তখন সেই ক্রেতাকে ঐ কফির বীজ শোঁকালে, নাকের নাকি হুঁশ ফিরে। এখানেও এদের তেমন কিছু রাখা দরকার ছিল , যাতে দু তিনটা স্যম্পল চাখার পর, জিহবা ভির্মি খেয়ে যাবার পর সেটির ঐ ভির্মিবস্থা কাটানো যায়। যৌক্তিক মনের এই দীর্ঘ বক্তব্য শুনে , আবেগি উঠলো
আরে মিয়া, এতো লম্বা চওড়া কথাবার্তায় কাম কী তোমার? এসব তো বেশীরভাগই কিনছে এখানকার চায়নিজরাই। তোমার মতো বাংগাল বা বিদেশী ক্রেতা আছে ক’জন দেখো তো? বেশী দামের গুলো ভাল না হলে কী আর এগুলো বিক্রি হতো এখানে?
যদিও এর আগেও এই গোটা হলঘরটা ঘুরতে ঘুরতে দেখেছে এর ক্রেতাদের তারপরও আবারো চোখ বোলালাম চারদিকে।
নাহ, কথা সত্য এই অধম ভিন্ন অন্য কোন ভিনদেশী ক্রেতা নেই এখানে এখন। বিক্রেতা হিসেবে চায়নিজরা যতোই চিকন বা মোটা ত্যাঁদড়ামি মার্কা বুদ্ধিরই হোক না কেন, এদের ক্রেতারাও তো সেই রকমই হবার কথা। ফলে দেখতে যতোই কাছাকছি রকমের হউক না কেন , ভেতরের জিনিষ যদি একই হয়েই থাকে তবে বেশী দামেরগুলো তো বিক্রিই হবা কথা নয় । অতএব নিশ্চিত ধরে নেয়া যায়, পার্থক্য আছে এগুলোর স্বাদে যতোটা না , তারচে ঢের হয়তো মাল মশলায় । যেমন আমাদের দেশে চিনি দিয়ে বানানো মিষ্টি আর স্যাকারিনের মিষ্টি দুটো যদি কেউ খায়, তবে স্বাদে তো দুটোই মিষ্টিই মনে হবে। ঐ স্বাদ চেখে কেউ কি বলতে পারবে কোনটা চিনির আর কোনটা স্যাকারিনের? এখনতো ঐ স্যাকারিনের চেয়েও নাকি উচ্চ মাত্রার কী কী সব মিষ্টি রাসায়নিকের বহুল ব্যবহার চলছে মিষ্টিতে। শুধু চিনি, স্যাকারিন বা অন্য মিষ্টি রাসায়নিক পদার্থই বা কেন? আমাদের দেশে কদাচিৎই আজকাল কোন ময়রা যেমন খাঁটি দুধের ছানা দিয়ে সন্দেশ বানায়। বেশীর ভাগই তো জানি সন্দেশ বানায় ময়দা মিশিয়ে , সেগুলো খেয়েই বা ক’জন ধরতে পারে কোনটা কিসের তৈরি? এইসব ভেজাল মিশানোতে আমাদের দেশের গ্রামগঞ্জের মানুষেরা যে আজকাল অত্যন্ত কাবিল হয়ে উঠেছে , তার সবগুলোর ভেজালেরই তো যোগানদার হল এই চায়না।
আরে দূর মিয়া কী শুরু করছ এতোসব গবেষণা ! কিনলে তো কিনবা না হয় এক, দেড় বা দুই কেজি চায়নিজ মোরব্বা, আচার বা হারবাল ক্যান্ডি এখান থাইক্কা। প্লেন,রকেট, সবামেরিন কিনতে যাইয়াও তো মানুষ এতো চিন্তা করে না। তুমি কি না পাঁচ দশ রেন মেন বি বাঁচানোর জন্য করতাছো এতোসব হিসাব আর গবেষণা। লইয়া লও, চার পাঁচ রকমের জিনিষ মিলাইয়া ঝিলাইয়া। কমদাম, বেশী দাম নিয়া অতো হিসাব নিকাশ কইরা কী আর হইব?
আরে বলছ এ কী তুমি ? পেশাগত জীবনে বেচাবিক্রির নানান গুরুগম্ভীর মনস্ততাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া ঘাটাঘাটি করে এখন তুমি এইটা কী কইলা? জানো না ক্রেতা মাত্রেই জিততে চায় । ক্রেতার জগতে কোন ক্রেতাই হারতে চায় না। হউক সে ক্রেতা সাবমেরিন বা উড়োজাহাজের ক্রেতা কিম্বা নিতান্তই পান বিড়ি সিগারেট বা আচার কেনার ক্রেতা। তদুপরি রকেট, সাবমেরিন, উড়োজাহাজ নিজের পকেটের টাকায় কিনে কী কেউ। ঐসব কেনাকাটায় তো থাকে নানান ধরনের ডান হাত বাম হাতের হিসাব। ঐটার সাথে এইটা মিলাইলা তুমি কোন যুক্তিতে? শোন নিজের ঘাম ঝরানো পয়সা খরচ করতে গিয়ে খুব কম জনাই বেহিসাবি হতে পারে।
নিজ মনের দুই জনের এইসব কথাবার্তা আর তর্ক বিতর্কের ফাঁকে এরই মধ্যে দেয়া হয়ে গেছে চক্কর গোটা হল ঘরটাই । যদিও বেশ আগেই মুখ আর জিহ্বা বিবস হয়ে গেছে তিন চারটা স্যাম্পল চাখার পর পরই, তারপরও চাখছিলাম যখনই পড়ছিল সামনে ফ্রি স্যাম্পল। এই মুহূর্তে যখন ফের সেই তিলের খাঁজার স্তুপের সামনে এসে পড়লাম দেখেছিলাম যা ঢুকেই প্রথম, তাতে ওটারও স্যাম্পল চেখে দেখার বদলে মনে জাগল প্রশ্ন ,আচ্ছা এই তিলের খাঁজা বানানোটা কে শিখেছে কার কাছ থেকে? আর শিখলই বা কবে তা? রাজশাহি নওগাঁ নাটোরের তিলের খাজার কারিগরেরা এটা শিখেছে চায়নার কারিগরদের কাছ থেকে? নাকি চায়নিজরা শিখেছে এটা বাংলার কাছ থেকে? অতিশ দীপঙ্কর আর হিউয়েন সাং ছাড়াও দুই ভূখণ্ডের এই ধরনের কারিগরেরাও কী আসা যাওয়া করেছিল নাকি প্রাচীনকালে? না হয় একদম একই ধরনের এই খাবার কিভাবে তৈরি হল এই দুই মুল্লুকে? না কি কেউ কারো কাছ থেকেই শিখেনি এটা? সম্পূর্ণ আলাদাভাবে আপাত বিচ্ছিন্ন দুই ভূখণ্ডের মানুষেরা তৈরি করতে শুরু করেছিল নিজেরা নিজেরাই নিজেদের মতো করেই এ মিষ্টান্ন । এই মিলে যাওয়া ব্যাপারটি নিতান্তই কাকতালীয়।
জীবনের কতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেরই তো উত্তর মিলে না মানুষের ! সে হিসাবে এ মোটেই কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন না । অতএব এ নিয়ে বৃথা আর মাথা ঘামানো। এছাড়া তিলের খাজা এমন কোন রাজকীয় খাবার নয় যে, এটির জন্ম ইতিহাস লিখে রাখার দরকার মনে করেছিল কখনো, কেউ । থাক তবে বাদ ওই ভাবনা। শুরু করা যাক এবার কেনাকাটা ।
কিন্তু কিনবো যে, কি হিসাবে কিনব? তা তো বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ প্রতিটা স্তুপেই যদিও পরিষ্কার ইংরেজিতে ১৮/২০/২৫/৩৫ এমন কি ৫৫ লেখা থাকতে দেখলেও , ঐ গুলি কী , হালি, ডজন নাকি কুড়ি হিসাবের দাম তা তো জানি না । তদুপরি বিক্রেতারা যারা বসে আছে তাদের নিরাবেগ চেহারার দিকে তাকিয়েও বুঝতে পারছিলাম না, বাৎচিত চালাবো কিভাবে । অবশ্য এখান থেকে সামান্য দূরের ঐ হুতং মানে গলির বাজারের বিক্রেতারা যেমন নো নো , ওকে ওকে এসব বলে বেচাবিক্রির কাজ চালিয়ে যেতে পারছে, এরাও তা পারারই কথা । আবার দামগুলো যেহেতু ইংরেজিতে লেখা, নিশ্চয়ই অন্ততপক্ষে ওটুকু তারা জানে । তবে জিগাই কেমনে তারে যে, এই দামে দিবা কয়টা?
এমন ভাবতে ভাবতেই দেখতে পেলাম এক চায়নিজ, আমার ডান দিকের স্টলের স্তুপের পাশে ভাঁজ করে রাখা নীল রঙ্গয়ের ছোট্ট একটা পলিথিন ব্যাগ তুলে , তাতে ঐ স্তুপ থেকে মুঠো ভর্তি করে সেই আচার / মোরব্বা / ক্যান্ডি নিয়ে ঐ ব্যাগ ভর্তি করে স্তুপের ওইপাশে উঁচু টুলে বসে থাকা বিক্রেতার হাতে তুলে দিতেই সে ঐ প্যাকেটটাকে অতিচেনা আজকালকার ওজন মাপার যন্ত্রে বসাতে। আর তাতেই বুঝে গেলাম, এ হল এক কেজির দাম।
ফলে সেই চায়নিজকে অনুসরণ করে একটা মোটামুটি আকারের পলিথিন হাতে নিয়ে তাতে ঐ একই ঢিবি থেকে কেজি খানেক আন্দাজ ক্যান্ডি ঢুকিয়ে সেটিকে মোটামুটি ভর্তি করে, বিক্রেতার হাতে তুলে দিতে দিতে “গিভ মি ওয়ান কেজি , প্লিজ‘ বলতে বলতে হাতের এক আঙ্গুল তুলেও বোঝালাম যে নেবো এক কেজি।
বিনাবাক্যব্যয়ে আমার হাত থেকে বিক্রেতা এইমাত্র ভর্তি করে দেয়া প্যাকেটটি হাতে নিয়ে তাতে হাত ঢুকিয়ে বেশ অনেকগুলো ক্যান্ডি বের করে স্তূপে ফেরত রেখে, বাকিটা ওজন করার যন্ত্রে বসিয়ে ওটার পর্দায় চোখ বুলিয়ে, ক্যান্ডির স্তূপ থেকে একটামাত্র ক্যান্ডি তুলে প্যাকেটে ঢুকিয়ে আমার তা হাতে ফেরত দিতেই, ভাবলাম–
আরেহ! এ কয়টাতেই এক কেজি হয়ে গেল নাকি? নাহ হাতের ওজনেও তো মনে হচ্ছে না যে এটাতে এক কেজি আছে। আমি তো মুখে বলার সাথে, হাতের ইশারায়ও দেখালাম যে এক কেজি নেব । সে তার থেকে কমালোই বা কেন? এটাতে তো আছে বড় জোর আধা কেজি হবে হয়তো।
লেখক : প্রাবন্ধিক, ভ্রমণ সাহিত্যিক।