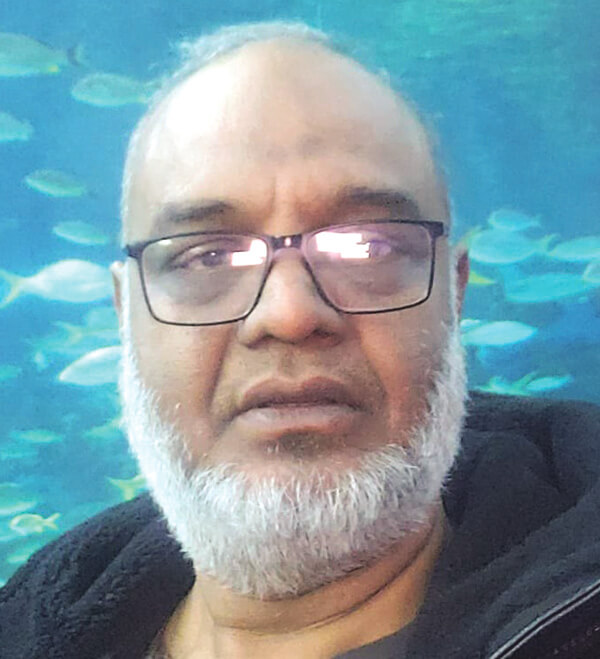বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সুপেয় পানির অপ্রতুলতা। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো গ্যাস। গ্যাস দিয়ে উৎপাদন করা হয় সার ও বিদ্যুৎ। বিভিন্ন শিল্পপণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় গ্যাস। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে গ্যাসের অবদান অপরিসীম। তবে নানান সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে পারলে এই বাধাগুলো অতিক্রম করা সম্ভব। আর সেজন্য প্রয়োজন সময়মত সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও অজ্ঞানতার জন্য আমরা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। দেশে প্রচুর নদনদী ও বৃষ্টি হলেও, সেই পানিকে সংরক্ষণ করে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছি না। ভূগর্ভস্থ পানির উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা আমাদেরকে বড় বিপদের মুখোমুখি করছে। এতে দ্রুত পানির লেয়ার নিচে নেমে পরিবেশকে ভয়াবহ বিপদের মুখোমুখি করেছে। অথচ সঠিক ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা নিয়ে এগুলে ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা কমানো সম্ভব। চট্টগ্রামের মীরসরাই থেকে ভাটিয়ারী পর্যন্ত দীর্ঘ পাহাড়ি এলাকায় পাহাড়ের ঢালে বাধ দিয়ে পানি সংরক্ষণ করলে, সেই পানি দিয়ে মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত স্থাপিত ইন্ডাস্ট্রিগুলোর পানির সমস্যার সমাধান করা যায়।
অন্যদিকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের তথ্যমতে দেশের গ্যাসের ব্লকগুলোতে প্রচুর গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলেও সিদ্ধান্তহীনতায় ত্রিমাত্রিক জরিপ, খনন ও উত্তোলনের ব্যবস্থা করতে পারছি না।
যদিও একই ভৌগোলিক অবস্থানের আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করে তাদের অংশে গ্যাস উত্তোলনে সফল হয়েছে। আবার দেশের অনেক এলাকায় গ্যাস পাওয়া গেলেও সেই গ্যাসকে সঠিকভাবে উত্তোলন ও ব্যবহার করতে পারছি না। দেশে প্রতিবছর কমছে গ্যাসের উৎপাদন। তাই চড়া দামে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করেও চাহিদা মেটানো যাচ্ছে না। ফলে চাহিদামতো গ্যাস পাচ্ছে না গৃহস্থালি ও শিল্পকারখানা। এতে আটকে আছে নতুন বিনিয়োগ। যদিও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে দক্ষিণের দ্বীপজেলা ভোলার গ্যাস। এ গ্যাস ব্যবহার নিয়ে দীর্ঘ আড়াই দশক পরও কার্যকর পরিকল্পনা নিতে পারেনি সরকার।
বাংলাদেশ তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ করপোরেশন পেট্রোবাংলার মতে, ভোলায় উৎপাদিত গ্যাস জেলার বাইরে আনার কোনো ব্যবস্থা নেই। জেলার ভেতরেও উৎপাদন সক্ষমতা অনুসারে গ্যাসের ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়নি। শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র থেকে দিনে ১৫ কোটি ঘনফুট উৎপাদন সক্ষমতা থাকলেও উৎপাদন হচ্ছে মাত্র সাড়ে ৭ কোটি ঘনফুট গ্যাস। আরো দুটি গ্যাসক্ষেত্র থেকে উৎপাদন শুরুই হয়নি। ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় ১৯৯৫ সালে শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি (বাপেক্স)। শাহবাজপুর থেকে গ্যাস উৎপাদন শুরু হয় ২০০৯ সালে। একই সংস্থা ২০১৮ সালে আবিষ্কার করে ভোলার দ্বিতীয় গ্যাসক্ষেত্র ভোলা নর্থ, ২০২৩ সালে আবিষ্কার করে ইলিশা গ্যাসক্ষেত্র। এই দুটি গ্যাসক্ষেত্র থেকে এখনো উৎপাদনও শুরু হয়নি। পেট্রোবাংলা সূত্র অনুযায়ী, ভোলার তিনটি গ্যাসক্ষেত্র মোট ১,৪৩২ বিলিয়ন ঘনফুট (বিসিএফ) গ্যাসের মজুত থাকতে পারে। যদিও নতুন কূপ খননের পর মজুত আরো বাড়তে পারে। এরমধ্যে এখন পর্যন্ত গ্যাস উত্তোলিত হয়েছে ২০০ বিলিয়ন ঘনফুটের (বিসিএফ) কম।
অথচ দেশে প্রতিদিনের গ্যাসের চাহিদা ৩৮০ কোটি ঘনফুট। সরবরাহ করা হচ্ছে ২৭০–২৮০ কোটি ঘনফুট। এর মধ্যে দেশে উৎপাদিত হচ্ছে ১৭৭ কোটি ঘনফুট। ঘাটতি মেটাতে ২০১৮ সাল থেকে চড়া দামের এলএনজি আমদানি শুরু করে সরকার।
গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের পর নব্বইয়ের দশকে ভোলার গ্যাস জেলার বাইরে আনার প্রস্তাব দিয়েছিল বহুজাতিক কোম্পানি ইউনিকল। ১২০ কিলোমিটার পাইপলাইন করার কথা বলেছিল তারা। এ গ্যাস ব্যবহার করে ভোলা, বরিশাল ও খুলনায় বিদ্যুৎকেন্দ্র করার প্রস্তাব দিয়েছে ইউনিকল। এটি লাভজনক হবে না ভেবে এগোয়নি তৎকালীন সরকার। এত বছর পরেও এটি লাভজনক হবে কি না, তার সম্ভাব্যতা যাচাই শেষ হয়নি, যা সত্যি দুঃখজনক!
বর্তমানে পেট্রোবাংলার অভিমত, ভোলার গ্যাস নিয়ে গভীরভাবে ভাবা হচ্ছে। সিএনজির বড় সিলিন্ডারে করে মেঘনাঘাট পর্যন্ত এনে শিল্পে সরবরাহ করার কথা ভাবছে তারা। এলএনজি করার বিষয়টিও বিবেচনায় আছে। পাইপলাইনের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনটি পেলে এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হবে। এদিকে ভোলার গ্যাস বাইরে নিতে পাইপলাইন নির্মাণে গত সরকারের সময় মার্কিন কোম্পানি এক্সিলারেট এনার্জির সঙ্গে আলোচনা করে পেট্রোবাংলা। ভোলা থেকে বরিশাল হয়ে খুলনায় যাওয়ার কথা একটি পাইপলাইন। আরেকটি পাইপলাইন বরিশাল থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা ছিল। ভোলার গ্যাস বরিশাল পর্যন্ত আনতে একটি সম্ভাব্যতা যাচাই করেছে গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)।তবে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সময় পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। বরিশাল থেকে সরাসরি ঢাকায় পাইপলাইন আনার সম্ভাব্যতা যাচাই চলছে এখন। ডিসেম্বরে এ প্রতিবেদন পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া ভোলার গ্যাস রূপান্তর করে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) হিসেবে বাইরে আনার চিন্তাও আছে জ্বালানি বিভাগের। এতে একাধিক কোম্পানি আগ্রহ দেখিয়েছে। পাইপলাইনের সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে যেটি সবচেয়ে লাভজনক হয়, সে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার।
এদিকে গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বাড়াতে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে উন্নয়ন, সংস্কার ও অনুসন্ধান মিলে ৫০টি কূপের কাজ শেষ করার কথা। যদিও এখন পর্যন্ত শেষ হয়েছে মাত্র ২০টির কাজ। বাংলাদেশ তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) সূত্র বলছে, চার বছরে ৫০টি কূপে কাজ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয় ২০২২ সালে। বিগত সরকারের সময় থেকে এটি ধীরগতিতে এগোয়। অন্তর্বর্তী সরকার আসার পর গতি বাড়ালেও প্রকল্প অনুমোদন ও দরপত্রে পিছিয়ে যায় কাজ। এটি শেষ করার আগেই আরো ১০০টি কূপ খনন প্রকল্পের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।
খনন শুরুর পর অনুসন্ধান বা উন্নয়ন কূপের কাজ শেষ করতে লাগে অন্তত সাড়ে তিন মাস। সংস্কার কূপ খননে লাগে দুই মাস।একাধিক বিদেশি কোম্পানিকে দিয়ে কাজ করাতে পারলে হয়তো বেশি কূপ খনন করা সম্ভব।
পেট্রোবাংলা বলছে, ৫০টি কূপের কাজ শেষে দিনে নতুন করে ৬২ কোটি ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনে যুক্ত হওয়ার কথা। তবে ২০টি কূপের খনন শেষে দিনে ২১ কোটি ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের সুযোগ তৈরি হলেও যুক্ত হয়েছে মাত্র ৯ কোটি ঘনফুট। ছয়টি কূপের কাজ চলছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানির পাঁচটি রিগ (খননযন্ত্র) ও চুক্তিতে নিয়োজিত কোম্পানির দুটিসহ সাতটি রিগ কাজ করছে। ডিসেম্বরের মধ্যে চুক্তিতে নিয়োজিত কোম্পানির আরো তিনটি রিগ যুক্ত হবে। এরপর একসঙ্গে ১০টি রিগ খননের কাজ করবে। দেশের খনিজ সম্পদ উত্তোলনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা পেট্রোবাংলা। তাদের অধীন থাকা তিনটি কোম্পানি গ্যাস উত্তোলনে যুক্ত বাপেক্স, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড। এর মধ্যে বাপেক্সের কূপ খননের সক্ষমতা আছে। বাকি দুটি কোম্পানি ঠিকাদার নিয়োগ করে কাজ করায়। আসলে বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে দেশকে শিল্পায়নের হাব হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। সেক্ষেত্রে যেসব বাধা আছে তা দ্রুততার সহিত দূর করতে হবে, না হলে পিছিয়ে পড়তে হবে আমাদেরকে। যা কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না। তাই এসব বিষয়ে সরকারের সর্বোচ্চ মহলের কার্যকর সুদৃষ্টি ও পদক্ষেপ নিতে হবে। না হয় আমাদেরকে পস্তাতে হবে বহুকাল ও বহুসময়।
লেখক: প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট।