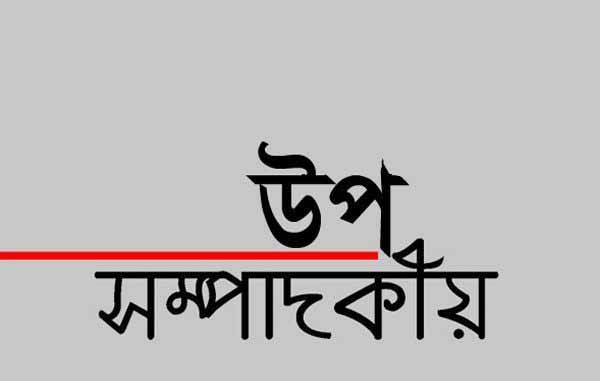৭ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশে আরেকটি একতরফা সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ বেশিরভাগ বিরোধীদল নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ৭ জানুয়ারির নির্বাচন বয়কট করেছে। এবারের একতরফা নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২২৪টি আসনে জয়ী হয়েছে। কিন্তু, ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী যাঁরা জয়ী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ৬ জন ছাড়া ৫৬ জন আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মী হওয়ায় ২৮০টি আসনে আওয়ামী লীগই বিজয়ী হয়েছে বলা চলে। (জাতীয় পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ এবং কল্যাণ পার্টির বিজয়ী প্রার্থীরাও আওয়ামী লীগ–সমর্থিত)। নির্বাচনের দিন বিকেল তিনটায় নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছিল তখন পর্যন্ত ২৭.১৫ শতাংশ ভোট পড়েছে, যা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। মিডিয়ার কল্যাণে দেখা গেছে, দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে প্রায় সারাদিন ভোটের কেন্দ্রগুলো জনবিরল ছিল। ২০০৮ সালের নির্বাচনে যে দীর্ঘ ভোটার লাইন দেখা গিয়েছিল এবার তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি। ভোটের পর এখন তারা বলছে, নির্বাচনে ৪১.৯৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। শেষের এক ঘন্টায় ১৪.৮৪ শতাংশ বৈধ ভোট পড়ার বিষয়টি একেবারেই অবিশ্বাস্য। নির্বাচন কমিশনের দাবি তাদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে কি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেনি? বিরোধী দলসমূহের নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি অদূর ভবিষ্যতে পূরণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, অদূর ভবিষ্যতে দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনেরও কোন আশা নেই বলা চলে। এ–পর্যায়ে যে প্রশ্নটা সামনে চলে আসে তাহলো গত ১৫ বছরে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করা সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সুষ্ঠু নির্বাচনকে ভয় পাচ্ছে কেন? সুষ্ঠু নির্বাচন হলে তারা হেরে যাওয়ার ভয় করছে কেন? সব দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ২০১৮ সালের নির্বাচনে তারা তো এমনিতেই জয়ী হতে যাচ্ছিল, এরপরও কার্ বুদ্ধিতে আগের রাতে সিল মেরে ব্যালট বাক্স ভরাতে হয়েছিল? বক্ষ্যমাণ কলামে এই প্রশ্নটির জবাব দিতে চেষ্টা করবো আমি।
বর্তমানে ক্ষমতাসীন শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশে ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত যে মেগা–প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত করেছে কিংবা বাস্তবায়ন করছে তার তালিকাটা দেখুন: পদ্মা বহুমুখী সেতু, ঢাকা মেট্রোরেল, ঢাকা শাহজালাল বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, কর্ণফুলী টানেল, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর, মাতারবাড়ি ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প, পায়রা বন্দর, পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প, রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প, বাঁশখালী বিদ্যুৎ প্রকল্প, ঢাকা বিআরটি প্রকল্প, ঢাকা–আশুলিয়া উড়ালসড়ক, ঢাকা–চট্টগ্রাম চার লেইনের মহাসড়ক, মিরসরাই–ফেনীতে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরী, কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা–মাওয়া–ভাঙা–পায়রা–যশোর রেলপথ, যমুনা রেলসেতু, পতেঙ্গা নিউমুরিং টার্মিনাল, আখাউড়া–লাকসাম ডবল লাইন রেলপথ এবং চট্টগ্রাম–দোহাজারী–কক্সবাজার রেলপথ। এই মেগা–প্রকল্পগুলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে অভূতপূর্ব গতি–সঞ্চার করেছে তা অস্বীকার করা যাবে না। এগুলো ছাড়াও সারাদেশের গ্রাম ও শহরগুলোতে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে গত পনেরো বছরে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ জনগণের বৃহদংশের মন জয় করতে পারেনি। কারণ, এই প্রকল্পগুলোকে জনগণ পুঁজি–লুন্ঠনের মেগা–মওকা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। গত ১৫ বছরে শেখ হাসিনার আত্মীয়–স্বজন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত দেশের কয়েক শত পুঁজি–লুটেরা পুঁজিপতির ধন–সম্পদের যে অভাবনীয় স্ফীতি জনগণ পর্যবেক্ষণ করছে তার পেছনে মেগা–প্রকল্পের এই পুঁজি–লুন্ঠন প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। বলতে গেলে, গত ১৫ বছর ছিল দেশে দুর্নীতি ও পুঁজি–লুন্ঠনের মোচ্ছব–কাল। সেজন্যই এতসব মেগা–প্রকল্প বাস্তবায়ন সত্ত্বেও শেখ হাসিনা জনগণের মন জয় করতে পারেননি।
দৈনিক বণিক বার্তা ৫ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে খবর প্রকাশ করেছে যে ২০২৩ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ১০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। আমাদের সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে সততা, জনপ্রিয়তা, জনমত ও জবাবদিহিতার যে কোন মূল্য নেই তারই জলজ্যান্ত প্রমাণ খামখেয়ালিভাবে গৃহীত নানা প্রকল্পে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের হিড়িক, যার মাধ্যমে তিন বছরের মধ্যেই বিদেশী ঋণকে ১০০ বিলিয়ন ডলারে উল্লম্ফন করানো হয়েছে। অর্থনীতি বিপদে পড়বে যখন ২০২৫ সাল থেকে এই খামখেয়ালিপনার খেসারত হিসেবে ঋণগুলোর সুদাসলে কিস্তি পরিশোধ শুরু হয়ে যাবে। দেশের প্রধান ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা ‘দি ডেইলি স্টার’ জানিয়েছে, বৈদেশিক ঋণের সুদাসলে কিস্তি পরিশোধ ২০২২–২৩ অর্থ–বছরের ২.৭৬ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে আগামী ২০২৫–২৬ অর্থ–বছরের বাজেটে ৪.৫ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে দাঁড়াবে। বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের এহেন উচ্চ–প্রবৃদ্ধি ২০২৯ সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। আরো দুঃখজনক হলো, এসব ঋণের অর্থে চলমান প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন যখন সম্পন্ন হবে তখন প্রকল্পগুলোর আয় থেকে ঋণের কিস্তির অতি সামান্য অংশ পরিশোধ করা সম্ভব হবে। বাকি অর্থ জনগণের উপর দীর্ঘমেয়াদী বোঝা হিসেবে চেপে বসবে।
বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ কিংবা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মত আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে এখনো ‘সফট লোন’ পাওয়া গেলে আমরা নিতে আগ্রহী হই, কিন্তু আমাদের বৈদেশিক ঋণের সিংহভাগই এখন ‘সাপ্লায়ার’স ক্রেডিট’। সাপ্লায়ার’স ক্রেডিটের অসুবিধে হলো যোগানদাতারা প্রকল্পের প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ঋণ হিসেবে দেওয়ার সময় প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাজার দামের চাইতে অনেক বেশি দাম ধরে ঋণের পরিমাণকে বাড়িয়ে দেয়। উপরন্তু, সাপ্লায়ার’স ক্রেডিটের সুদের হারও সফট লোনের সুদের হারের চাইতে বেশি, ঋণ পরিশোধের সময়সীমাও কম থাকে। আরো গুরুতর হলো, সাপ্লায়ার’স ক্রেডিটে রাজনীতিবিদ, ঠিকাদার ব্যবসায়ী ও আমলাদের ‘মার্জিনের হার’ অনেক বেশি হয়ে থাকে। সেজন্য সাপ্লায়ার’স ক্রেডিটকে লুটপাটের অর্থনীতির সবচেয়ে বহুল–ব্যবহৃত মেকানিজম অভিহিত করা হয়। দুঃখজনকভাবে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে সাপ্লায়ার’স ক্রেডিট শাসকমহলের দুর্নীতি ও পুঁজিলুন্ঠনের সবচেয়ে মারাত্মক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সেজন্য বাংলাদেশের মেগা–প্রজেক্টগুলোর ব্যয় বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক হয়ে যাচ্ছে, কারণ এসব প্রকল্প থেকে পুঁজি–লুন্ঠন এখন শাসক দলের নেতা ও প্রধানমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের লোভনীয় ধান্দা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে হলে যেহেতু তাদের অনেক কঠিন শর্তগুলো পরিপালনে শাসকরা জটিলতার সম্মুখীন হন তাই বাংলাদেশে ২০০৯ সাল থেকে বর্তমান সরকার প্রধানত সাপ্লায়ার’স ক্রেডিটের প্রতি অতিমাত্রায় ঝুঁকে পড়েছে। বিশেষত, গত পাঁচ বছর বেলাগামভাবে অনেকগুলো অত্যন্ত বাজে প্রকল্পে ঋণ গ্রহণে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিকটু আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে।
চীনা সাপ্লায়ার’স ক্রেডিটে যেসব মেগা–প্রকল্প এদেশে বাস্তবায়িত হয়েছে বা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে সেগুলো হলো পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা–যশোর–পায়রা রেলপথ প্রকল্প, কর্ণফুলী টানেল প্রকল্প এবং ঢাকা–গাজীপুর বিআরটি প্রকল্প। জাপানের জাইকার সাপ্লায়ার’স ক্রেডিটে অর্থায়িত যেসব মেগা–প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে বা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে সেগুলো হলো ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্প, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর, মাতারবাড়ি কয়লা–চালিত বিদ্যুৎ প্রকল্প, ঢাকা শাহজালাল বিমান বন্দরের থার্ড টার্মিনাল, যমুনা রেলসেতু এবং চট্টগ্রাম আউটার রিং রোড। ঢাকা–যশোর রেলপথ এবং ঢাকা–গাজীপুর বিআরটি প্রকল্প নিঃসন্দেহে নিকৃষ্ট প্রকল্প। কিন্তু, বাংলাদেশের নিকৃষ্টতম ‘সাপ্লায়ার’স ক্রেডিট প্রকল্প’ ১২ বিলিয়ন ডলার রাশিয়ান ঋণে নির্মীয়মাণ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প। এটি আক্ষরিকভাবেই ‘সাদা হাতি প্রকল্প’। দুই ইউনিটের এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় হবে ১৩৫০ কোটি ডলার। এর দুটো ইউনিট থেকে নাকি ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। প্রাক্কলিত নির্মাণ ব্যয় ১৩৫০ কোটি ডলারের মধ্যে ১২০০ কোটি ডলার ঋণ দেবে রাশিয়া। রাশিয়ার ঋণের সুদের হার হবে ৪ শতাংশ, যা ১০ বছরের গ্রেস পিরিয়ড সহ ২৮ বছরে বাংলাদেশকে সুদাসলে পরিশোধ করতে হবে। অনেকেরই জানা নেই যে মাত্র ৬ বিলিয়ন ডলার রাশিয়ান ঋণে ভারতের তামিলনাড়ুর কুদান কুলামে ২০০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট স্থাপিত হয়েছে কয়েক বছর আগে। অথচ, আমাদের ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ প্ল্যান্টের জন্য ১২ বিলিয়ন ডলার রাশিয়ান ঋণ নিতে হচ্ছে কেন? উল্লিখিত মহলগুলোর পুঁজি–লুন্ঠন কি এর জন্য দায়ী?
স্বল্প–প্রয়োজনীয় প্রকল্পে যথাযথ ফিজিবিলিটি স্টাডি ছাড়া খামখেয়ালিভাবে বিনিয়োগের হিড়িকের ব্যাপারে আপত্তি জানানোয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্যঙ্গ করে আমাকে ‘অর্বাচীন অর্থনীতিবিদ’ আখ্যা দিয়েছিলেন। ২০২২ সালের মে মাসে জার্মান টিভি ডয়শে ভেলে আমাকে এ–ব্যাপারে মন্তব্য করতে বলায় আমি বলেছিলাম,‘২০১২ সালে যখন বিশ্ব ব্যাংক পদ্মা সেতুর অর্থায়ন বাতিল করেছিল তখন বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে আমিই প্রথম তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিলাম নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য। আবার, তাঁর হাত থেকেই আমি ‘একুশে পদক’ নিয়েছি। এখন তিনি আমাকে অর্বাচীন অর্থনীতিবিদ বলছেন! তা তিনি বলতেই পারেন, কিন্তু আমি আমার অবস্থান বদলাবো না’। আমার এই সাবধান বাণীকে আমলে না নেয়ায় এখন আমাদের অর্থনীতি যে চরম টালমাটাল অবস্থায় পৌঁছে গেছে তা সামাল দিতে পারছে না সরকার। গত ১২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে আইএমএফ এর ৪.৭ বিলিয়ন ডলার ঋণের দ্বিতীয় কিস্তির প্রায় ৬৯ কোটি ডলার পাওয়ায় এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ৪০ কোটি ডলার ঋণ পাওয়ায় রিজার্ভ কয়েকদিনের জন্য ২১ বিলিয়ন ডলারের উপরে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে রিজার্ভ আবার ২০.১৯ বিলিয়ন ডলারে নেমে গেছে। কঠোরভাবে আমদানি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভের পতনকে থামাতে চেষ্টা করেও এখনো সফল হতে পারেনি। ইতোমধ্যে দেশের আমদানি নিয়ন্ত্রণের নানাবিধ ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় ২০২২ সালের আগস্ট মাস থেকে সতের মাসে এল/সি খোলা ১৬ শতাংশ কমে এসেছে, কিন্তু হুন্ডি ব্যবস্থায় রেমিট্যান্স প্রেরণকে কোনমতেই নিরুৎসাহিত করা যাচ্ছে না। হুন্ডি ব্যবসার রমরমা অবস্থা দিনদিন বাড়তে থাকার প্রধান কারণ আন্তঃ–ব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ডলারের দামের সাথে হুন্ডি মার্কেটের ডলারের দামের পার্থক্য ৭–৮ টাকায় স্থির থাকা। এই পার্থক্য বজায় থাকলে ডলারের দামের ক্রম–বাজারিকরণের সিদ্ধান্ত তেমন সুফল দেবে না, হুন্ডি ব্যবসা চাঙাই থেকে যাবে শক্তিশালী চাহিদার কারণে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে সরকারের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) এর বরাত দিয়ে দেশের পত্র–পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল যে শুধু হুন্ডি প্রক্রিয়ায় দেশ থেকে বছরে ৭৫ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে। এর সাথে আমদানির ওভারইনভয়েসিং, রফতানির আন্ডারইনভয়েসিং এবং রফতানি আয় দেশে ফেরত না আনার মত মূল সমস্যাগুলো যোগ করলে দেখা যাবে প্রত্যেক বছর এখন কমপক্ষে দেড় লাখ কোটি টাকার সম–পরিমাণের বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হচ্ছে। এর মানে, বাংলাদেশ থেকে বছরে কমপক্ষে ১৫/১৬ বিলিয়ন ডলার পুঁজি এখন বিদেশে পাচার হয়ে চলেছে (অথবা ডলার দেশে আসছে না), যার অর্ধেকের মত পাচার হচ্ছে হুন্ডি প্রক্রিয়ার বেলাগাম বিস্তারের মাধ্যমে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স গত ২০২০–২১ অর্থ–বছরের ২৪.৭৪ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০২২–২৩ অর্থ–বছরে ২১.৬১ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে, যার প্রধান কারণ হুন্ডি প্রক্রিয়ায় রেমিট্যান্স প্রেরণ আবার চাঙা হওয়া।
আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধার করতে হলে ক্ষমতাসীন সরকারকে দুর্নীতি, পুঁজি–লুন্ঠন এবং পুঁজিপাচারের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর দমননীতি গ্রহণ করতে হবে। এজন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে অবিলম্বে কঠোরভাবে হুন্ডি ব্যবস্থাকে দমন। কারণ, হুন্ডি পদ্ধতিতে বিদেশে থেকে যাওয়া ডলার বা অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রা কেনার ক্ষেত্রে চাহিদার প্রধান অংশটাই আসছে দুর্নীতিবাজ আমলা ও রাজনীতিবিদ এবং ব্যাংকঋণ লুটেরাদের পক্ষ থেকে, যাদেরকে লালন করছে আওয়ামী লীগ। গত পাঁচ বছরে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম একেবারেই ‘বাত্ কা বাতে’ পর্যবসিত হয়েছে। কঠোরভাবে দুর্নীতি দমন না করলে পুঁজিপাচার নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।
লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ ও অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়