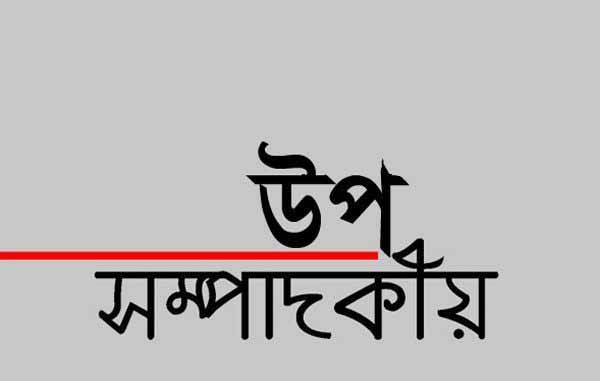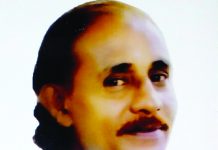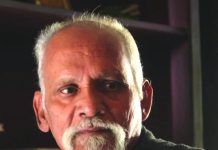সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ওপর ৩৫ শতাংশ আমদানি–শুল্ক আরোপ করেছে। এর ফলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের তৈরী পোশাক রফতানি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। এর আগেও অবশ্য বাংলাদেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানির ক্ষেত্রে প্রায় ১৬ শতাংশ শুল্ক প্রদান করতে হতো, এখন তা বেড়ে যদি ৩৫ শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায় তাহলে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ অনেক বেশি বৈষম্যের সম্মুখীন হবে। বর্তমানে বাণিজ্য উপদেষ্টার নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দল শুল্ক কমানোর উদ্দেশ্যে মার্কিন কর্তাব্যক্তিদের সাথে আলোচনার জন্য ওয়াশিংটন ডিসি গমন করেছেন, কিন্তু তাঁদের এই সফরের সময় উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্য আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বিশেষত, ভারত, পাকিস্তান ও ভিয়েতনামের ওপর আরোপিত শুল্কহার বাংলাদেশের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় বাংলাদেশ এসব প্রতিযোগী দেশের কাছে বাজার হারাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ খুব বেশি পণ্য আমদানি না করায় বাংলাদেশের বাণিজ্য–ভারসাম্য একতরফাভাবে বাংলাদেশের অনুকূলে থাকে। তাই, বাংলাদেশকে শাস্তিমূলক শুল্কহারের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে যাচ্ছে বলে পত্র–পত্রিকায় সম্প্রতি খবর প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে ২৫টি বোয়িং বিমান কেনা, গম আমদানি–বৃদ্ধি এবং কাঁচা–তুলা আমদানি–বৃদ্ধির কথা শোনা যাচ্ছে।
অবশ্য, এসব যুক্তির চাইতেও শুল্কবৃদ্ধির অন্য কারণ রয়েছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয়বার দায়িত্ব গ্রহণের পর সারা বিশ্বের বিরুদ্ধে বাণিজ্য–যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছেন। তাঁর কথায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাণিজ্যের মাধ্যমে তার বাণিজ্য–সহযোগীরা শোষণের শিকার করে চলেছে, যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য–ঘাটতি দিনদিন বেড়েই চলেছে। বিশেষত, চীন মুক্ত–বাণিজ্যের সুবিধা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রায়–একচেটিয়া দখল প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। এই অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না, সেজন্যই নাকি এবারের শুল্কযুদ্ধ। ডোনাল্ড ট্রাম্পের এহেন যুক্তি আসলে ধোপে টেকে না। আসল কথা হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন একটি ক্ষীয়মান বিশ্ব–পরাশক্তিতে পরিণত হওয়ার চক্রে প্রবেশ করেছে। আগামী চার–পাঁচ বছরের মধ্যে চীন তাদেরকে ডিঙিয়ে বিশ্বের ‘এক নম্বর অর্থনৈতিক পরাশক্তিতে’ পরিণত হবে। এই বাস্তবতা ট্রাম্প এবং রিপাবলিকানরা মেনে নিতে অপারগ। সেজন্য তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দ্রুত একটি ‘প্লুটোক্রেটিক রাষ্ট্রে’ পরিণত করার মিশন নিয়ে সারা বিশ্বের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন’ স্লোগান দিয়ে এই মিশনকে এগিয়ে নিচ্ছেন ট্রাম্প। বিশ্বের প্রথম সাংবিধানিক গণতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন অত্যন্ত নগ্নভাবে একটি ‘প্লুটোক্রেসিতে’ পরিণত হয়েছে।
গণতন্ত্রের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ১৮৬৩ সালে, তাঁর বিশ্বখ্যাত গেটিসবার্গ বক্তৃতায়,‘Democracy is government of the people by the people and for the people. ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই স্বাধীনতা ঘোষণাকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৭৮৩ সালে গ্রেট বৃটেনকে স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত করে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল। ১৭৮৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংবিধান অনুমোদন করে বিশ্বের প্রথম সাংবিধানিক গণতন্ত্র হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে। কিন্তু, এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই ফেডারেল রিজার্ভের একজন কিংবদন্তী প্রাক্তন–চেয়ারম্যান পল ভলকার কিছুদিন আগে ঘোষণা করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন প্লুটোক্রেসিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই নূতন অভিধাটি বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছে বিশ্বখ্যাত নোবেল পুরস্কার–বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজও আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্লুটোক্রেসি অভিহিত করায়। স্টিগলিজ বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন কেন তিনি এই অভিধাকে যথার্থ মনে করেন। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে প্লুটোক্রেসির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ‘government by the richest people of the country। ঐ ডিকশনারিতে প্লুটোক্রেট বলা হচ্ছে ঐ ব্যক্তিকে যিনি তাঁর সম্পদের কারণে শক্তিধর (a person who is powerful because of his wealth )। অক্সফোর্ড ডিকশনারির এই সংজ্ঞা মোতাবেক ইতিহাস বিবেচনা করলে ১৯৫০ এর দশক থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশ একটি প্লুটোক্রেসিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা অনেকেই হয়তো জানি না যে ১৯৪৫ সালে প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট মৃত্যুবরণের পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আয়বৈষম্যের দিক্ থেকে পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাজ্যের তুলনায় অনেকখানি ‘কম বৈষম্যপূর্ণ’ ছিল, কিন্তু ২০২৫ সালে এসে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সকল উন্নত–শিল্পায়িত ওইসিডি সদস্য দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আয়বৈষম্যমূলক দেশে পরিণত হয়েছে। আরো গুরুতর হলো, ১৯৭০ এর দশক থেকে এই আয়বৈষম্য দিনদিন মারাত্মক দ্রুতগতিতে ক্রমবর্ধমান। গত ৫৫ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার নিম্নতর আয়ের ৫০ শতাংশ মানুষ তাঁদের প্রকৃত আয় স্থবির থেকে ক্রমশ নিম্নগামী হয়ে যেতে দেখেছে, অথচ দেশের ১০ শতাংশ ধনাঢ্য জনগোষ্ঠীর আয় ও সম্পদ ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলেছে। ১৯৭৯ সালে ‘মুক্তবাজার অর্থনীতির’ আদলে চরম–দক্ষিণপন্থী বাজার মৌলবাদ মার্কিন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতির কেন্দ্রীয় মঞ্চ দখল করার পর গত ৪৬ বছরে সেদেশে আয় ও সম্পদবৈষম্য যেমনি অপ্রতিহত গতিতে বেড়ে চলেছে তেমনি রাষ্ট্রপরিচালনা ও ভোটের রাজনীতিতেও অর্থ–বিত্ত প্রধান ফলদায়ক উপাদানে পরিণত হয়েছে। ২০২৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিম্ন আয়ের ৫০ শতাংশ জনগণ জাতীয় আয়ের মাত্র ২.৫ শতাংশের মালিক হতে পেরেছে। এর পরের ৪০ শতাংশের দখলে রয়েছে জাতীয় আয়ের ৩০ শতাংশ। এর মানে জনগণের ৯০ শতাংশের দখলে রয়েছে জাতীয় আয়ের মাত্র ৩২.৫ শতাংশ। আর, ১০ শতাংশ উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠীর দখলে চলে গেছে জাতীয় আয়ের ৬৭.৫ শতাংশ। অন্য কোন উন্নত–শিল্পায়িত দেশে আয় ও সম্পদবৈষম্য এত গুরুতরভাবে বাড়তে পারেনি। ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ইটালি, জাপান, কানাডার মত জি–সেভেন দেশগুলোতে যেরকম পুঁজিবাদ প্রচলিত রয়েছে তার তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদ অনেক বেশি কট্টর–দক্ষিণপন্থী ও বাজার–মৌলবাদী। মার্কিন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পুরোপুরি মুনাফাবাজ ইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর করায়ত্ত। মার্কিন শিক্ষাব্যবস্থাও ক্রমেই বাজারীকরণের অসহায় শিকারে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। মার্কিন ‘ফুডস্টাম্প’ কর্মসূচিকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্রমেই সংকুচিত করে চলেছেন। এর ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সালের জুলাই মাসে সমাজের ধনাঢ্য জনগোষ্ঠীকে আরেক দফা কর হ্রাসের সুবিধা দিয়ে আইন পাশ করা হয়েছে ২০১৭ সালের মত। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেহেতু শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠির বিপুল জনসমর্থনে ২০২৪ সালের নভেম্বরে দ্বিতীয়বারের মত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন তাই নিম্নআয়ের অশ্বেতাঙ্গ ও ল্যাটিনো জনগোষ্ঠীর প্রতি তাঁর বিদ্বেষ তিনি কখনোই লুকানোর চেষ্টা করেন না। প্রেসিডেন্ট হিসেবে ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি দায়িত্বগ্রহণের পর তিনি সারা বিশ্বের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব ‘শুল্কযুদ্ধ’ শুরু করে দিয়েছেন, অভিবাসীদেরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাড়ানোর জোরদার তৎপরতা শুরু করেছেন এবং নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের নানা ধরনের সুবিধা কাটছাঁটের উদ্যোগ নিয়েছেন। ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন’ (ম্যাগা) স্লোগানকে পুঁজি করে তিনি চীনের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বাণিজ্য–যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা অনেকেই হয়তো জানি না যে ক্রয়ক্ষমতা সাম্য নীতির ভিত্তিতে হিসাব করে চীনের জিডিপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপিকে ২০১৪ সালেই ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল আইএমএফ। বর্তমানে দু’দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বিবেচনায় নিয়ে আইএমএফ বলছে ২০২৯ সাল কিংবা ২০৩০ সালে চীনের নমিনাল জিডিপি মার্কিন নমিনাল জিডিপিকে অতিক্রম করে যাবে। এর মানে, ২০২৯ কিংবা ২০৩০ সাল নাগাদ নমিনাল জিডিপি এবং ক্রয়ক্ষমতার সাম্যের উভয় নিক্তিতেই বিশ্বের ‘এক নম্বর অর্থনীতি’তে পরিণত হবে চীন। বিশ্ব অর্থনীতির এই আসন্ন অবশ্যম্ভাবী পালাবদলকে নস্যাৎ করার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন মরিয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছেন একের পর এক।
প্রথম দৃষ্টিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি সাংবিধানিক গণতন্ত্র মনে হলেও এর গভীরে গেলে মার্কিন গণতন্ত্রের অনেকগুলো ‘অগণতান্ত্রিক চারিত্র্য’ মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে ধরা দেয়। জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন না, ইলেকটোরাল কলেজের ভোটের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে তাঁকে নির্বাচিত হতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি স্টেটের মধ্যে এই ইলেকটোরাল কলেজের ভোট ভাগ করে দেওয়া আছে। যে প্রেসিডেন্ট–প্রার্থীর দল যে স্টেটের ‘হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভস’ এর বেশি আসনে জয়লাভ করেন তিনি ঐ স্টেটের সকল ‘ইলেকটোরাল কলেজ ভোট’ নিজের ভাগে নিয়ে নেন, অন্য দলের প্রেসিডেন্ট–প্রার্থী একটিও ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পান না। এই নিয়মের কারণে ৫০টি স্টেটের মধ্যে মাত্র ৬/৭টি স্টেটের নির্বাচন সত্যিকারভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঐ স্টেটগুলোকে ‘সুইং স্টেট’ অভিহিত করা হয়। ওহাইয়ো, ফ্লোরিডা, মিশিগান, পেনসিলভানিয়া, উইসকনসিন, অ্যারিজোনা, মিনেসোটা– এই সাতটি স্টেটকে প্রতিটি প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে ‘ক্রুশিয়াল সুইং স্টেট’ বিবেচনা করা হয়। ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ ইয়র্ক, ম্যাসাচুসেটস্ কিংবা ইলিনয়ের মত জনবহুল স্টেটে প্রতিবার ডেমোক্রেটিক পার্টি জয়লাভ করলেও তা ঐ দলের প্রার্থীর জয়ে কোন অবদান রাখে না। সাড়ে তেত্রিশ কোটি মার্কিন জনগণের মধ্যে প্রায় সাত কোটি অশ্বেতাঙ্গ এবং ল্যাটিনো জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই বড় বড় নগরীতে বসবাস করায় তাঁদের সমর্থন ডেমোক্রেটিক পার্টিকে তেমন একটা সুবিধা দিতে পারে না। অন্যদিকে, নির্বাচনে সমাজের ধনাঢ্য জনগোষ্ঠীর আর্থিক শক্তি এবং বহুজাতিক কর্পোরেট পুঁজির দাপট ক্রমেই ফলাফলকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে চলেছে। একইসাথে, জায়নবাদী আইপ্যাক এবং ইভানজেলিক্যাল ক্রিস্টিয়ানদের সংঘবদ্ধ আর্থিক প্রোপাগান্ডা নির্বাচনে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হচ্ছে প্রায়শ। এসব কারণে, মার্কিন নির্বাচনগুলোতে দক্ষিণপন্থী রিপাবলিকানদের দাপট অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে চলেছে বলা যায়। ২০২৪ সালের নির্বাচনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের দুই কক্ষ ‘হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভস’ এবং সিনেট রিপাবলিকান পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধীনে চলে গেছে। এর বেশ কিছু বছর আগে থেকেই মার্কিন সুপ্রিম কোর্টও রিপাবলিকান পার্টির কট্টর সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল। এর ফলে, বর্তমান ২০২৫–২৯ মেয়াদে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতা প্রয়োগে মার্কিন কংগ্রেস কিংবা সুপ্রিম কোর্টের লাগাম টেনে ধরার সম্ভাবনা একেবারেই নেই বললে অত্যুক্তি হবে না।
ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেও একজন বিলিয়নিয়ার, দেশের বিলিয়নিয়ারদের ৯০ শতাংশেরও বেশি তাঁকে অন্ধভাবে সমর্থন করে। অতএব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার আগামী চার বছর ধরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্লুটোক্রেটিক নীতির ধারাবাহিকতা চালিয়ে যেতে কোন বাধার সম্মুখীন হওয়ার আশংকা নেই বললেই চলে। ট্রাম্পের চলমান ‘শুল্কযুদ্ধ’ মার্কিন সাধারণ ভোক্তাদের জীবনকে অদূর ভবিষ্যতে আরো বেশি বিপর্যস্ত করলেও ট্রাম্প তাঁর এই অযৌক্তিক নীতি থেকে সরে আসবেন বলে মনে হয় না। অবশ্য, এই নীতিমালা যদি মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দাবস্থা ডেকে আনে তাহলে ট্রাম্প এবং রিপাবলিকান পার্টি আগামী ২০২৬ সালের কংগ্রেস নির্বাচনে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তেও পারে। তবে, ২০২৪ সালের নির্বাচনী বিপর্যয়ের ফলে বিরোধী ডেমোক্রেটিক পার্টি বর্তমানে প্রচন্ড নেতৃত্বের সংকটে পড়েছে। উপরন্তু, মার্কিন নির্বাচন ব্যবস্থার শ্বেতাঙ্গ–তোষণ চারিত্র্য আগামী কয়েকটি নির্বাচনে ঐ দলটির জেতার সম্ভাবনাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষত, ডেমোক্রেটিক পার্টির সোশ্যাল ডেমোক্রেটরা তাঁদের দলে আগামী কয়েক বছর ধরে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবেন কিনা সে প্রশ্ন এখন সামনে চলে এসেছে। এর মানে দাঁড়াচ্ছে, মার্কিন প্লুটোক্রেসি আগামী কয়েকটি নির্বাচনেও শক্তিশালী থাকার সম্ভাবনাই বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জনগণ অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের প্রকৃত–আয় ও জীবনযাত্রায় কোন ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না।
লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ এবং অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়