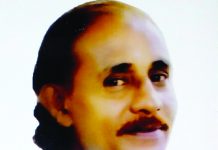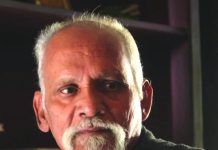গত এক দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বড়সড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিদেশে পুঁজিপাচার। যদিও এসময়ে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে বেড়েছে তবুও জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার প্রতি বছর যা হওয়ার কথা তার চাইতে এক শতাংশ বা দেড় শতাংশ কম হচ্ছে পুঁজিপাচার ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায়। এই ক্রমবর্ধমান পুঁজিপাচারের কারণে প্রাইভেট সেক্টরে বিনিয়োগ-জিডিপি’র অনুপাত ২৩-২৪ শতাংশের আশেপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, অথচ সরকারী বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত গত এক দশকে বেড়ে সাত শতাংশ ছাড়িয়ে যাওয়ায় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার তেমন কমছে না। এই পুঁজিপাচারকারীরা জাতির ‘এক নম্বর দুশমন’। তারা যদি ব্যাপকভাবে বিদেশে পুঁজিপাচার না করতো তাহলে এদ্দিনে বাংলাদেশ শুধু ভারত নয় শ্রীলংকাকে পেছনে ফেলে দক্ষিণ এশিয়ায় মাথাপিছু জিডিপি’র বিচারে সবচেয়ে অগ্রগামী দেশে পরিণত হতো। সেজন্যই, শুধু সরকার নয় দেশে-বিদেশে অবস্থানকারী সকল বাংলাদেশী বাঙালির কর্তব্য এদেরকে ঘৃণা, বয়কট এবং প্রতিহত করা।
অনেকেরই হয়তো জানা নেই, বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৫৭ সালে বাংলাকে উপনিবেশ করার আগে কয়েক’শ বছর ধরে ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচুর্যময় অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত ছিল তদানীন্তন বাংলা। এই স্বীকৃতি প্রথম দিয়েছিলেন বিশ্বখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা, যিনি বাংলার সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের আমলে এদেশে এসেছিলেন। দ্বিতীয় স্বীকৃতিটি এসেছিল মোগল সম্রাট আকবরের ‘নবরত্ন’ সভার খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ আবুল ফজলের লিখিত ইতিহাসে। তাঁর রচিত আকবরনামায় তিনি স্বীকার করেছেন, আকবরের শাসনাধীন ভারতবর্ষে সবচেয়ে প্রাচুর্যময় প্রদেশ ছিল ‘সুবা বাংলা’। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, আকবরের আমলেই বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তা-ও ঈসা খানের সাথে সন্ধির কারণে তখন পুরো বাংলা মোগলদের করতলগত হয়নি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে বাংলা-দখল সম্পন্ন হয়েছিল,যার রাজধানী নির্বাচিত হয়েছিল ঢাকা। তৃতীয় যে স্বীকৃতি, সেটা দিয়েছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের ফরাসী ‘কোর্ট ডাক্তার’ ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার। বার্নিয়ারের মতে সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশ্বে সবচেয়ে প্রাচুর্যময় অঞ্চল হিসেবে মিশরের যে সুনাম ছিল সে সুনামের প্রকৃত দাবিদার ছিল বাংলা। কিছুদিনের মধ্যেই আরেকজন ফরাসী ব্যবসায়ী ট্যাভারনিয়ার বার্নিয়ারকে এ-বিষয়ে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ট্যাভারনিয়ার চামড়ার ব্যবসার জন্য বেশ কয়েকবার বাংলায় আসার কারণে এই অঞ্চল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। কার্ল মার্ঙ বার্নিয়ারের এই স্বীকৃতির উদ্ধৃতি দেওয়ায় বিশ্বে তা বহুলপরিচিতি অর্জন করেছে। ১৭৫৭ সালে বাংলা দখল করার পর এক’শ বছর ধরে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনির কর্মকর্তা-কর্মচারী-সিপাহসালার এবং সিপাহীরা জাহাজের পর জাহাজ বোঝাই করে বাংলা থেকে ধন-সম্পদ ও সোনা-রুপা লুন্ঠন করে ইংল্যান্ডে নিয়ে গেছে। তাদের এই পুঁজিপাচারের পরিমাণ এতই বেশি ছিল যে লন্ডন বন্দরে লুন্ঠিত সামগ্রীবাহী জাহাজগুলো খালাস করার জন্য তিন মাসের একটি জাহাজ-জট সৃষ্টি হয়েছিল বলে প্রমাণ করেছেন ব্রুক এডামস নামের একজন মার্কিন ইতিহাসবিদ। আরো অনেক ঐতিহাসিকের গবেষণার মাধ্যমে এই বাংলা-লুন্ঠনের কাহিনী সপ্রমাণিত হওয়ায় এখন ইতিহাসে এই লুন্ঠনপর্বকে ‘দি বেঙ্গল লুট’ নামে অভিহিত করা হচ্ছে। ১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক বৃটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতার নামে আবার ২৪ বছরের জন্য পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে পরিণত হওয়ায় আরেকদফা লুন্ঠন, বঞ্চনা ও পুঁজিপাচারের শিকার হয়েছিল তদানীন্তন পূর্ব বাংলা/পূর্ব পাকিস্তান। সেজন্যই স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে হেনরী কিসিঞ্জারের কল্যাণে বাংলাদেশের কপালে তকমা জুটেছিল ‘ইন্টারন্যাশনাল বাস্কেট কেস’ এবং ‘বটমলেস বাস্কেট কেস’। এই দুটো ঔপনিবেশিক লুন্ঠনপর্বের ২১৪ বছর পার হয়ে এসে ভারতবর্ষের ‘একদা সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ’ বাংলার কপালে কেন এই অপমানতিলক জুটল সেটা বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে কেন বর্তমান সময়ের পুঁজিপাচারকারীদেরকে আমি ‘জাতির এক নম্বর দুশমন’ অভিহিত করছি। তাদেরকে আমি লুটেরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পাঞ্জাবী-পাকিস্তানীদের ‘ভাবাদর্শিক দোসর’ মনে করি।
স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা দুর্নীতি ও পুঁজিলুন্ঠন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭৩ সাল থেকে দুর্নীতি ক্রমেই বিস্তার লাভ করলেও বঙ্গবন্ধুর শাসনকালে দুর্নীতি ছিল ব্যাতিক্রমী আচরণ, রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রে তখনো ওটা নিয়মে পরিণত হয়নি। কিন্তু সমরপ্রভু জিয়া নিজেকে সততার পরাকাষ্ঠা হিসেবে জাহির করলেও তাঁর সচেতন আশকারা পেয়েই তাঁর শাসনামল থেকে দুর্নীতি ও পুঁজিলুন্ঠন বেড়ে বর্তমানে সর্বনাশা স্তরে পৌঁছে গেছে। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি স্বৈরাচারী এরশাদ আমলে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। ১৯৯১ সালে ভোটের রাজনীতি চালু হওয়ার পর গত ৩১ বছর একই প্রক্রিয়াগুলো আরো জোরদার হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশকে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পুঁজিপাচার গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠেনি। বঙ্গবন্ধুর আমলে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে অভিবাসন তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, যদিও যুক্তরাজ্যে পাকিস্তান আমলের পঞ্চাশের দশক থেকেই সিলেটীদের অভিবাসন শক্তিশালী হচ্ছিল বলা চলে। প্রবাসীদের রেমিট্যান্সও বঙ্গবন্ধুর আমলে অর্থনীতির জন্য বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠেনি। ১৯৭৩ সালের প্রথম বিশ্ব তেল সংকটের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের তেল-রফতানিকারক দেশগুলোতে যখন নগর-উন্নয়নযজ্ঞ শুরু হয় সেখানে সস্তা শ্রমিক যোগানের অন্যতম আকর্ষণীয় সূত্র হিসেবে সত্তর দশকের শেষদিকে বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমিক-অভিবাসনে গতিসঞ্চারিত হয়, গত সাড়ে চার দশক ধরে এই অভিবাসন-ধারা বেগবান রয়েছে। নব্বই দশক থেকে মধ্যপ্রাচ্যের পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশে বাংলাদেশীদের অভিবাসন দ্রুত বাড়তে শুরু করে, যার ফলে গত ত্রিশ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইতালী, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশীদের গন্তব্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ২০২১ সালের শেষে বিশ্বে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংখ্যা এক কোটি ত্রিশ লাখে পৌঁছে গেছে বলে প্রাক্কলন করা হচ্ছে, যদিও অবৈধ অভিবাসনের কারণে এক্ষেত্রে একটা ‘গ্রে জোন’ রয়েছে।
সত্তর দশকে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর অবস্থা ছিল খুবই সংকটাপন্ন, তখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়-জিডিপি’র অনুপাত ছিল মাত্র আট শতাংশ। ঐ সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ছয়টি ব্যাংকে আমানতের প্রবৃদ্ধি ছিল খুবই শ্লথ, যার বিপরীতে ব্যাংকঋণের জন্য হাহাকার ছিল নিত্যসঙ্গী। ঋণের জন্য এই হাহাকারের সুবিধা নিয়ে ১৯৭৩ সাল থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর উচ্চপদের কর্মকর্তাদের একাংশ ক্রমেই দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হচ্ছিল, যাদের সাথে বখরার সুবিধাভোগী হয়ে তথাকথিত ‘ব্রিফকেস ব্যবসায়ীরা’ ক্রমেই পুঁজিপতি বনতে শুরু করে। সমরপ্রভু জিয়া তাঁর শাসনামলে ব্যাংকঋণকে অপব্যবহার করেছেন বেচাকেনার রাজনীতির সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে। অপরদিকে, ব্যবসায়ী, সামরিক ও সিভিল আমলা এবং রাজনীতিকদের মধ্যে যারা জিয়ার কাছে বিক্রিত হয়ে বিএনপি’র রাজনৈতিক ঝান্ডাতলে সমবেত হয় তারা ব্যাংকঋণের সহায়তায় অতিদ্রুত কোটিপতির কাতারে স্থান করে নেয়। এভাবেই শুরু হয়েছিল বাংলাদেশে ব্যাংকঋণ লুন্ঠনের মহাযজ্ঞ। ১৯৮২ সালে স্বৈরাচারী এরশাদ দেশে ছয়টি বেসরকারী ব্যাংক স্থাপনের লাইসেন্স প্রদানের পাশাপাশি দুটো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংককে প্রাইভেট ব্যাংকে রূপান্তরিত করেন। অতএব, রাষ্ট্রায়ত্ত এবং প্রাইভেট উভয় প্রকারের ব্যাংক থেকে ব্যাংকঋণ লুন্ঠনকে প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জনের সুযোগ প্রদানকে এরশাদ আমলের অন্যতম প্রধান কীর্তি বলা উচিত, কারণ জিয়ার আমলেও ব্যাংকের আমানতের প্রবৃদ্ধির শ্লথগতি বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের মত ব্যাংকঋণ প্রদানের পথে বাধা হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের রেমিট্যান্স ক্রমেই দ্রুত বাড়তে শুরু করে। কিন্তু তখন এরশাদ সরকারের আমদানি উদারীকরণ নীতিমালা ভারতের তুলনায় প্রায় ছয় বছর আগে বাস্তবায়িত হওয়ায় দেশের অর্থনীতিতে চোরাচালান গুরুতর সমস্যায় পরিণত হয়, যার ফলশ্রুতিতে চোরাচালানের অন্যতম সুবিধাজনক পেমেন্ট সিস্টেম হিসেবে ‘হুন্ডি সিস্টেম’ জনপ্রিয় হতে শুরু করে। হুন্ডি পদ্ধতিতে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স প্রেরণ অতিদ্রুত ফরমাল পদ্ধতিগুলোর প্রধান বিকল্প হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ফরমাল পদ্ধতিতে রেমিট্যান্স প্রেরণকে প্রবাসী-বান্ধব করার ব্যাপারে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের ব্যর্থতাও হুন্ডি সিস্টেমের জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। ঐ সময়ে ব্যাংকের জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রেরণের হয়রানির অভিজ্ঞতা যাদের হয়েছে তাঁরা হয়তো বিকল্প পদ্ধতি খুঁজে নিয়েছেন ভোগান্তির কারণেই। বলতে গেলে, আশির দশক ও নব্বই দশকে মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ থেকে হুন্ডি পদ্ধতিতে রেমিট্যান্স প্রেরণ প্রবাসীদের বৃহদংশের জন্য একমাত্র বাস্তবসম্মত বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হতো।
গত ৪০ বছরে বিদেশে বাংলাদেশীদের অভিবাসনের সাথে পাল্লা দিয়ে বিদেশে পুঁজিপাচারও ক্রমশ বেড়ে এখন অর্থনীতির অন্যতম প্রধান সমস্যায় পরিণত হয়েছে। ২০২১ সালে এক কোটি ত্রিশ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশী বৈধপথে ২২ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন, যার বিপরীতে গ্লোবাল ফাইনেন্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির প্রাক্কলন মোতাবেক বাংলাদেশ থেকে বিদেশে ২০১৮ সালেই পুঁজিপাচারও প্রায় ৭-৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গেছে। (হুন্ডি পদ্ধতিতে বিদেশে রয়ে যাওয়া রেমিট্যান্স-ডলারের পরিমাণ কখনো প্রকাশিত হয়নি)। পুঁজিপাচারের এই রমরমা অবস্থা সৃষ্টিতে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত সবচেয়ে বেশি ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে। এ-পর্যায়ে বলা প্রয়োজন, বৈধপথে হোক্ কিংবা হুন্ডি সিস্টেমে হোক্ যেভাবেই দেশে রেমিট্যান্সের টাকা আসুক্ এই টাকার সিংহভাগ প্রধানত নিরাপত্তার জন্য ব্যাংকগুলোতে আমানত হিসেবে জমা পড়বেই। সেজন্যই আমরা দেখছি, বাংলাদেশে ব্যাংকের সংখ্যা বেড়ে এখন ৬১ হলেও ব্যাংকগুলোতে আমানতের ঢল অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক হিসাব মোতাবেক ব্যাংকগুলোতে প্রায় এগার লক্ষ কোটি টাকার আমানত রয়েছে, অথচ খেলাপিঋণের প্রকৃত পরিমাণও হয়তো এখন চার লক্ষ কোটি টাকার বেশি হবে। এর ফলে ‘উদ্বৃত্ত আমানত’ এদেশের ব্যাংকিং খাতের প্রধান সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, এত বিপুল খেলাপিঋণ সত্ত্বেও ব্যাংকঋণের জন্য এদেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কোন হাহাকার চার দশকে মারাত্মক আকার ধারণ করেনি। যে সমস্যাটা মারাত্মক হয়ে উঠেছে সেটা হলো, ধাপে ধাপে এদেশে নূতন নূতন ব্যাংক স্থাপনের লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে সরকারগুলো এদেশে কয়েক হাজার ‘রবার ব্যারন’ সৃষ্টি করেছে। ব্যাংকঋণের ওপর এসব রাঘববোয়ালেরা একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে ফেলেছে। বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সেটা বিদেশে পাচার করার যে সনাতন-সংস্কৃতি আমদানি বাণিজ্যের ‘ওভার ইনভয়েসিং’ এবং রফতানি বাণিজ্যের ‘আন্ডার ইনভয়েসিং’ পদ্ধতির প্রায় একচেটিয়া দখলে ছিল তার সাথে জোরেসোরে যুক্ত হলো দুর্নীতিবাজ সামরিক-সিভিল আমলা, রাজনীতিবিদ, পেশাজীবী এবং নব্য ব্যাংক-মালিকদের পুঁজিপাচারের মহাযজ্ঞ। ফলে, আমদানিকারক ব্যবসায়ী, রফতানিকারক গার্মেন্টস মালিক, দুর্নীতিবাজ সামরিক-সিভিল আমলা,পেশাজীবী এবং রাজনীতিবিদদের সাথে পাল্লা দিয়ে ব্যাংক-মালিক ও ব্যাংকঋণ-লুটেরারাও বিদেশে পুঁজিপাচারকারীদের সামনের কাতারে উঠে এসেছে গত চার দশকে। ব্যাংকের ঋণ যতই খেলাপি হোক্ নানা পন্থায় ঐ খেলাপিঋণ লুকিয়ে ফেলার ব্যবস্থায় মেতে উঠেছে সরকার। অন্যদিকে, পুঁজিপাচার দমনে সরকারের কোন তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না।
সাম্পতিক কালে ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রেরণের জটিল পদ্ধতি অনেকখানি সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিপ্লবের কারণে রেমিট্যান্স প্রেরণের হুন্ডি সিস্টেমও একেবারেই সহজ হয়ে গেছে। উপরন্তু, এই চার দশকে হুন্ডি ডলারের একটা বিশাল চাহিদা কাঠামো সম্প্রসারিত হয়ে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে জালের মত ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে, এক ডলারের বৈদেশিক মান বাংলাদেশী টাকায় বৈধ বাজারে যতই হোক হুন্ডি ডলারের বাজারে ডলারের দাম তার চাইতে এক/দুই টাকা বেশি পাওয়া যাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রেমিট্যান্স উৎসাহিত করার জন্য দুই শতাংশ প্রণোদনা ঘোষণা ও বাস্তবায়নের সাথে পাল্লা দিয়ে হুন্ডি ডলারের বাজারে এক ডলারের বিনিময়ে প্রায় অষ্টাশি টাকা পাওয়া যাচ্ছিল। সম্প্রতি যখন সরকার প্রণোদনা বাড়িয়ে আড়াই শতাংশ করেছে , তখন হুন্ডি ডলারের বাজারে এবং কার্ব মার্কেটে ডলারের দাম নব্বই-একানব্বই টাকায় পৌঁছে গেছে। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদেরকে বিদেশে বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন, এতে নাকি বিদেশে পুঁজিপাচার কমবে। আসলে পুঁজিপাচারকে আড়াল করবে এই সিদ্ধান্ত। প্রাইভেট সেক্টরের বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত ২৩-২৪ শতাংশে স্থবির রয়েছে, এই হারকে বাড়ানোই অর্থমন্ত্রীর অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। দেশীয় পুঁজিলুটেরাদেরকে বিদেশে বিনিয়োগে উৎসাহিত করলে এই স্থবিরতা কাটবে না।
লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ ও অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়