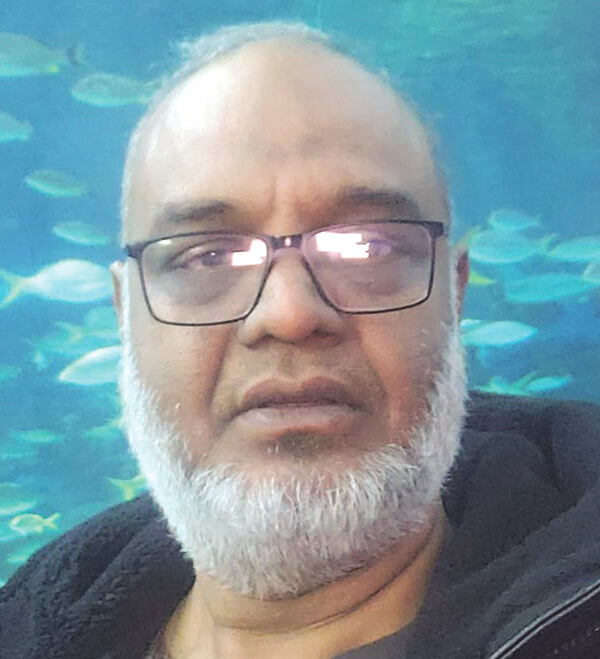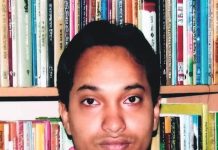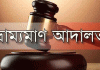সদ্য প্রকাশিত ২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় সারাদেশে গড় পাসের হার ৫৮.৮৩%, যা গতবছরের তুলনায় ১৮.৯৫% কম। জিপিএ–৫ পেয়েছে ৬৯,০৯৭ জন শিক্ষার্থী। ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট ১২,৫১,১১১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে ৬,১৮,০১৫ জন ছেলে ও ৬,৩৩,০৯৬ জন মেয়ে শিক্ষার্থী। সাধারণ শিক্ষা বোর্ডগুলোর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৬৪.৬২%, রাজশাহীতে ৫৯.৪০%, কুমিল্লায় ৪৮.৮৬%, যশোরে ৫০.২০%, চট্টগ্রামে ৫২.৫৭%, বরিশালে ৬২.৫৭%, সিলেটে ৫১.৮৬%, দিনাজপুরে ৫৭.৪৯%, ময়মনসিংহে ৫১.৫৪%। অন্যদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৭৫.৬১% ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ৬২.৫৭%। এবারের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকেই এটি নিয়ে আফসোস করেছেন এবং বিগত বছরগুলোর তুলনায় খারাপ বলে আখ্যায়িত করেছেন।
গত এক বছরে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন ও চ্যালেঞ্জ এসেছে। নতুন শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে। যা নিয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মধ্যে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। এছাড়া শিক্ষার মান উন্নয়ন, পরীক্ষার পদ্ধতি এবং শিক্ষা খাতে বরাদ্দ নিয়ে সারাবছর চলেছে আলোচনা ও বিতর্ক। এই শিক্ষাক্রমে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে এবং শিক্ষার্থীদের মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে সমস্যা সমাধান ও ক্রিয়াশীলতার উপর বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।
নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, তবে এই প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত কিনা এবং শিক্ষকরা নতুন পদ্ধতি কতটা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।
পূর্বের সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি (creative question system) নিয়ে বিতর্ক ছিল, নতুন শিক্ষাক্রমে এর পরিবর্তন আনা হয়েছে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা পদ্ধতির এই পরিবর্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেমন প্রভাব ফেলবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে শিক্ষার মান উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং নতুন শিক্ষাক্রম ও অন্যান্য পদক্ষেপ এই মান উন্নয়নের জন্য নেয়া হয়েছে। এ ব্যবস্থায় ৫ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা–৮ বছরে উন্নীত করা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যাতে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা যায়। সামগ্রিকভাবে গত এক বছরে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যপক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়েছে, তবে এই পরিবর্তন কতটা সফল হবে, তা সময়সাপেক্ষ।
বাংলাদেশে তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এগুলো হলো মাদ্রাসা (আলিয়া/কওমি), সাধারণ শিক্ষা (ন্যাশনাল ক্যারিকুলাম) ও ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা। এর মধ্যে ব্রিটিশ কারিকুলাম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও উন্নত কারিকুলামের পর্যাপ্ত রিসোর্স থাকার ফলে বাংলাদেশে এটি ভালোভাবে চলমান আছে। এরপর আছে মাদ্রাসা (আলিয়া/কওমি) শিক্ষা ব্যবস্থা। এতে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী লেখাপড়া করে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রয়েছে এর বিস্তার। এতে অধ্যয়নরত জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সন্তান। যদিও এই শিক্ষা ব্যবস্থার পুরোটাই পরিচালিত হচ্ছে বেসরকারিভাবে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সরকারের যে পরিমাণ নজরদারি থাকার কথা, তার ছিটেফোঁটাও এতে নেই। ফলে এটি চলছে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে। যদি এটিকে যুগোপযোগী স্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে সমন্বয় করে তৈরি করা না হয়, তাহলে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী অনেকটা অদক্ষ থেকে যাবে। ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে বিদেশি কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্কের যে কাঠামো, সেই কাঠামো ন্যাশনাল কারিকুলামের সঙ্গে সমন্বয় করে দক্ষতা ও মানবিক মূল্যবোধ তৈরি করার উপযোগী বিষয় সংযুক্ত করে যদি সংস্করণ করা হয়, তাহলে বৃহৎ এই জনগোষ্ঠী কর্মশক্তিতে যুক্ত হবে। অধিকন্তু এতে যেসব দুর্বলতা রয়েছে, যেখানে উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে ও এই ব্যবস্থাকে কীভাবে সাজাতে হবে, উচ্চপর্যায়ের একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটির গবেষণালব্ধ ফলাফল এবং মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ অথরিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে। এর বাইরে আরেকটি বিশেষায়িত শিক্ষা চলমান আছে। যেটাকে হাফেজি শিক্ষা বলা হয়। হাফেজি মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীরা শুধু পবিত্র কোরআনের হাফেজ হয়। তাই কোরআনের হিফজ যেসব প্রতিষ্ঠানে থাকবে বা যেসব প্রতিষ্ঠান শুধু কোরআনের হিফজ করাবে, সেসব প্রতিষ্ঠানে কোরআনের হিফজের পাশাপাশি ন্যূনতম মৌলিক জ্ঞানের কিছু বিষয় যুক্ত করে একটি বিশেষায়িত শিক্ষাক্রম করা যেতে পারে। এর জন্য দরকার একটি একক রেগুলেটরি অথরিটি। যাতে এটা নিশ্চিত করা যায় যে, যারা এসব মাদ্রাসায় কোরআনুল করিমের হিফজ করবে, পড়া শেষে তারা যেন মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় পরিপূর্ণভাবে যুক্ত হতে পারে অথবা স্কুল–কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থায় এসে যুক্ত হতে পারে। এছাড়া হিফজুল কোরআন যেহেতু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এটির জন্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান না করে, যে কেউ চাইলে যাতে এই কোরআন অধ্যয়ন করতে পারে–কারিকুলাম বা শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই সুযোগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে বিশেষ করে সৌদি আরব, মিসরে প্রাইমারি স্কুলের কারিকুলামে আল কোরআনকে একটি বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কোরআনুল করিম পড়ছে বা হিফজ করছে। যারা স্কুল কলেজে পড়াশোনা করছে, তারাও কোরআনুল করিম পড়ার ও কোরআনের হাফেজ হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এমনকি ব্রিটিশ কারিকুলামেও বাধ্যতামূলক বিষয় গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞানের সঙ্গে আল কোরআনসহ যেকোনো জেনারেল বা বিশেষায়িত বিষয় যুক্ত করে পড়ানোর সুযোগ রয়েছে। একই ভাবে আমাদের দেশেও প্রাইমারি পর্যায়ে এগুলোকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা যেতে পারে।
এবার আসি সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার কথায়। বিগত বছরগুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনটি পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রথমটি আসে ১৯৯৬ সালে, দ্বিতীয়টি ২০১২ সালে এবং তৃতীয়টি ২০২১ সালে। দুঃখজনক ব্যাপার হলো ১৯৯৬ ও ২০১২ সালের দুটি পরিবর্তন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সর্বশেষ ২০২১ সালে যে পরিবর্তন হয়েছে, এ পরিবর্তনও অত্যন্ত সমালোচিত হয়েছে সুধী মহলে, শিক্ষক মহলে ও অভিভাবক মহলে। এই ক্যারিকুলামের অনেক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং কিছু ত্রুটি স্পষ্ট। যেমন কোনো দেশের ক্যারিকুলাম একসঙ্গে শতভাগ পরিবর্তন করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এই কারিকুলামটি সারা পৃথিবীতে প্রচলিত নয়। এই কারিকুলামটি পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে ইউরোপ ও কানাডার মতো দেশের কিছু কিছু প্রদেশে চলমান আছে, যদিও স্থায়ীভাবে নয়। এটি আন্তর্জাতিকভাবে বহুল ব্যবহৃত কারিকুলাম নয়। এই কারিকুলাম বাস্তবায়নের জন্য যে ধরনের অবকাঠামো, যে ধরনের শিক্ষা উপকরণ, নীতিমালা এবং যে ধরনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, সে ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো রিসোর্স বা ব্যবস্থাপনা আমাদের দেশে নেই। ফলে বাস্তবায়ন করতে চাইলেও পূর্ণাঙ্গভাবে করা যাবে না। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমরা কোনোভাবেই প্রস্তুত নই এই কারিকুলাম বাস্তবায়ন করার জন্য। এর মূল্যায়ন ব্যবস্থা যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। এছাড়া এই কারিকুলাম প্রণয়নের সময় যেসব গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে, সেগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।
আমরা যদি উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সত্যিকার অর্থে একটি টেকসই কারিকুলাম বা টেকসই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে একটি সভ্য, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন একটি সমাজ গঠন করতে চাই ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে মোকাবিলা করার উপযোগী নাগরিক তৈরি করতে চাই, তাহলে দক্ষতা ও নৈতিকতা এ দুইয়ের সমন্বয়ে সময়োপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অভিজ্ঞ, সৎ, যোগ্য, যাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে, এমন বিশেষজ্ঞদেরকে দিয়ে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করতে হবে এবং ধীরে ধীরে তাদের সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হবে।
আমরা যদি উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সত্যিকার অর্থে একটি টেকসই কারিকুলাম বা টেকসই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে একটি সভ্য, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন একটি সমাজ গঠন করতে চাই ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে মোকাবিলা করার উপযোগী নাগরিক তৈরি করতে চাই, তাহলে দক্ষতা ও নৈতিকতা এ দুইয়ের সমন্বয়ে সময়োপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অভিজ্ঞ, সৎ, যোগ্য, যাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে, এমন বিশেষজ্ঞদেরকে দিয়ে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করতে হবে এবং ধীরে ধীরে তাদের সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হবে।
লেখক: প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট।