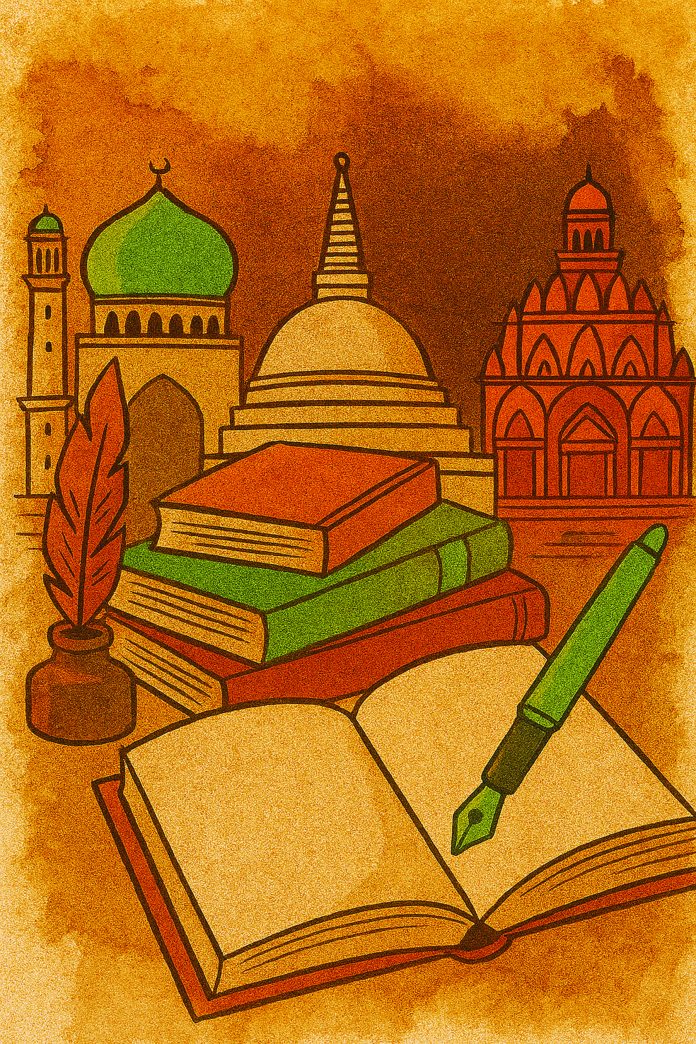চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। হাজার বছরের পুরনো নিজস্ব এক অনন্য ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক। প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যের কারণে স্মরণাতীত কাল থেকে চট্টগ্রামে এসেছেন পীর–আউলিয়া, ফকির–দরবেশ, সাধু–সন্যাসী, বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ নানা ধর্ম–বর্ণের ধর্মযাজক ও পর্যটক। যে কারণে এখানে হিন্দু–মুসলিম, বৌদ্ধ–খ্রিষ্টান এবং আদিবাসী পাহাড়ি জাতিসত্ত্বার ধর্মীয় ও আর্থ–সামাজিক আচার–আচরণে বহুমাত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ দৃশ্যমান। এ জেলা অসাম্প্রদায়িক সমাজ ব্যবস্থার এক অনন্য দৃষ্টান্ত বলে বিবেচিত হওয়ার নানাবিধ উপকরণে সমৃদ্ধ। ঐতিহাসিক বিবর্তনে চট্টগ্রামের জনজীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গৌড়ীয় এবং আরবীয় সংস্কৃতির যেমন অনুপ্রবেশ ঘটেছে তেমনি আরাকান ও বার্মিজ সংস্কৃতিও এখানকার সমাজ জীবনে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। চট্টগ্রামে আধুনিক শিক্ষার ক্রমবিকাশের ফলে ইউরোপীয় সংস্কৃতি এ অঞ্চলে স্থান করে নেয়। সকল অনুপ্রবেশের সম্মিলনের মধ্যেও বীর চট্টলার মানুষ হাজার বছরের জীবনযাপন ও প্রচেষ্টায় নিজস্ব ঐতিহ্যে যে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি নির্মাণ করেছে, বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি তাতে প্রভূত সমৃদ্ধ হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চট্টগ্রাম বহু কীর্তিমান মানুষের সৃষ্টিশীল কর্মে আলোকিত হয়েছে। তাঁদের যাদুকরী সৃষ্টিসহ দেশপ্রেমে নির্মিত হয়েছে চট্টগ্রামের ইতিহাস, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বর্ণিল প্রচ্ছদ।
চট্টগ্রাম ও আরাকান সুপ্রাচীনকাল থেকে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত একটি অখণ্ড রাজ্যরূপে চন্দ্রসূর্য রাজবংশের রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। ফলে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতে ছিল বর্মী প্রভাব। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম সমতট ও হরিকেল রাজ্যভুক্ত হয়। আরাকানের সাথে সমতট ও হরিকেল রাজ্যের প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকতো। ফলে চট্টগ্রামে কারোরই শাসন কন্টকশূণ্য হয়নি। তবে বিবদমান দু’পক্ষই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওয়ায় চট্টগ্রামে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। উপমহাদেশের প্রথিতযশা ঐতিহাসিক ড. আবদুল করিমের মতে, “খ্রিষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রামের সঙ্গে আরব মুসলমান বণিকদের যোগাযোগ ছিল। আরব বণিকরা চট্টগ্রামে স্বাধীন রাজ্য গঠন না করলেও আরবদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামের ভাষায় প্রচুর আরবি শব্দ ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় ক্রিয়াপদের আগে ‘না’ সূচক শব্দ ব্যবহারও আরবি ভাষার প্রভাবের ফল।” চট্টগ্রামের অনেক লোকালয়ের নাম আরবিতে এবং এ জেলার অধিবাসীদের আচার–ব্যবহার ও স্বভাবের মধ্যে আরবি সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্যণীয়। ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের চট্টগ্রাম বিজয়ের পর হতে ভাগ্যান্বেষী মুসলমানরা গৌড়ীয় এবং পশ্চিম মধ্য এশিয়ার দেশ থেকে চট্টগ্রাম এসে বসতি স্থাপন করে। তাদের চারিত্রিক গুণাবলী ও সংস্কৃতির প্রভাবে চট্টগ্রামের হিন্দু ও বৌদ্ধ অধিবাসীদের বৃহৎ অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হয়। এ সম্পর্কের মেলবন্ধনের কারণে সকল সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণের ফলে চট্টগ্রামে মুসলমান অধিবাসীর উদ্ভব হয় এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। যার ফলশ্রুতিতে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতে আরবীয় ও গৌড়ীয় সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ করে এবং তা প্রাধান্য লাভ করে। দশম শতকে চট্টগ্রামে পণ্ডিতবিহার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং চর্চা হয়েছে চর্যাগানের। মধ্যযুগে সুলতানি, আফগান ও মোগল আমল তথা ১৬৬৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত চট্টগ্রামে কারো শাসনই নিরঙ্কুশ হয়নি। কখনো ত্রিপুরা কখনো আরাকানের শাসক দ্বারা চট্টগ্রাম শাসিত হয়েছে। আবার আরাকানের সাথে বরাবরই যুদ্ধ করতে হয়েছে অন্যান্যদের। ফলে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতে আরাকানের প্রভাব যেমন দূরীভূত হয়নি, অন্যদিকে এর উপরই প্রলেপ পড়েছে নতুন নতুন সংস্কৃতির। এর প্রতিফলন ঘটেছে সাহিত্য–কলা–সংগীতে। রাজনৈতিকভাবে যেমন সংঘাত ঘটেছে, নানা ক্ষেত্রে আবার সমন্বয়ও ঘটেছে বেশ কিছু, যার মাঝে সংস্কৃতি অন্যতম নিয়ামক। বাংলা ভাষার চর্চা হয়েছে আরাকান রাজদরবারে। ‘চন্দ্রাবতী’ রচয়িতা মাগন ঠাকুরের অনুরোধে আলাওল রচনা করেন তাঁর অমর কাব্য ‘পদ্মাবতী’। আবার বাংলা ভাষার উপর আক্রমণও হয়েছে যার প্রতিবাদী প্রতিফলন ঘটে সন্দ্বীপের কবি আবদুল হাকিমের ‘বঙ্গবাণী’ কবিতায় – ‘যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/ সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।’
১৬৬৬ সালে মোগল সুবাদার শায়েস্তা খানের পুত্র বুজুর্গ উমেদ খান আরাকানী মগদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম জয় করেন। এই বিজয়ের ফলে চট্টগ্রাম মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বুজুর্গ উমেদ খান চট্টগ্রামের প্রথম মোগল ফৌজদার নিযুক্ত হন। ১৬৬৬ সালে চট্টগ্রামের উপর আরাকানী প্রাধান্য চিরতরে শেষ হয়ে যায় এবং মোগলরা হয়ে ওঠে চট্টগ্রামের প্রকৃত শাসক। এসময় চট্টগ্রামের সংস্কৃতির বিশেষ দিক পুঁথি রচনা উৎকর্ষতা অর্জন করে। ১৬৭৫ সালে পটিয়ার সুচক্রদণ্ডীর দ্বিজরতী দেব তাঁর বিখ্যাত পুঁথি ‘মৃগলুব্ধ’, বোয়ালখালীর কমর আলী ‘সরসালের নীতি’ কাব্য ও ‘ঋতুর বারোমাস’ নামে একটি গীতিকাব্য, ১৬৮৪ সালে সলিমপুরের কবি আবদুন নবী ‘আমীর হামজা’ পুঁথি, ১৭০৩ সালে বাঁশখালীর রামজীবন বিদ্যাভূষণ ‘মনসামঙ্গল’ এবং কক্সবাজারের রামুর শেখ মনসুর ‘ছিরিনামা’ ও ‘আমীর–জঙ্গনামা’ রচনা করেন।
১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ্দৌলা’র পরাজয়ের মাধ্যমে ইংরেজ বণিক গোষ্ঠী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের রাজনৈতিক আধিপত্যকে সুদৃঢ় করতে অর্থনৈতিক জোন হিসেবে চট্টগ্রামকে বেছে নেয় এবং মোগল আমলের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা বাতিল করে নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন স্বভাবতই অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রামে নতুন একটি ভূম্যধিকারী শ্রেণি ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ১৮৩৬ সালে সরকারিভাবে চট্টগ্রামে ইংরেজি স্কুল, ১৮৪৫ সালে বেসরকারি উদ্যোগে পটিয়ায় মিডল ইংরেজি স্কুল এবং ১৮৬৯ সালে চট্টগ্রামে এফ.এ. কলেজ (বর্তমান চট্টগ্রাম কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হয়। নব উদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে পাশ্চাত্যের জ্ঞান–বিজ্ঞান দর্শনের সংস্পর্শে আসে। ফলে সমাজে আধুনিক চেতনার প্রভাব উৎসারিত হয়।
চট্টগ্রামে বুদ্ধিবৃত্তিক সভা–সমিতি বা লেখক সাহিত্যিক গোষ্ঠী সৃষ্টিতে আধুনিক শিক্ষার অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। কলকাতায় ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’ বা ‘ভারত সভা’ গড়ে ওঠার দেড় বছর পূর্বে তথা ১৮৭৫ সালের ২৯ জানুয়ারি ‘চট্টগ্রাম অ্যাসোসিয়েশন’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চট্টগ্রামের জনগণের সকল প্রকার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অভিযোগ, দাবি–দাওয়া, প্রতিবাদ, আবেদন–নিবেদনের মুখপাত্র হিসেবে চট্টগ্রামের তৎকালীন স্বদেশপ্রেমী প্রগতিশীল ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় এই সংগঠন গড়ে উঠেছিল। সংগঠনের সভাপতি ছিলেন নলিনীকান্ত সেন এবং সম্পাদক বর্ষীয়ান উকিল দুর্গাদাস দস্তিদার। এই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার পর চট্টগ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, নারী সংগঠন, সাংস্কৃতিক তৎপরতা, প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন, সংবাদপত্র প্রকাশ ইত্যাদি সমাজ গঠনমূলক নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও প্রচার–প্রসারের লক্ষ্যে ১৮৯৩ সালে নলিনীকান্ত সেনের উদ্যোগে চট্টগ্রামে গঠিত হয় ‘জাতীয় শিল্প রক্ষিণী সমিতি’। তাঁর প্রচেষ্টায় ‘অধ্যয়নী সম্মিলনী’ নামে একটি পাঠাগার গড়ে ওঠে যেটি ছিল চট্টগ্রামের প্রথম পাঠাগার। সমসাময়িককালেই আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের উদ্যোগে প্রাচীন লুপ্ত পুঁথি উদ্ধার কাজ শুরু হয় এবং প্রাচীন সাহিত্য সংগ্রহ সমিতি গড়ে ওঠে ও প্রত্ন সাহিত্য লাইব্রেরি স্থাপনের চেষ্টা অব্যাহত থাকে।
১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার পূর্বেই চট্টগ্রামের রাজনীতি সচেতন বুদ্ধিজীবীগণ বাংলাকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র আঁচ করতে পেরে ‘চট্টল হিতসাধিনী সভা’ নামক একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। ‘চট্টগ্রাম অ্যাসোসিয়েশন’ ও ‘চট্টল হিতসাধিনী সভা’ এর যৌথ উদ্যোগে চট্টগ্রামে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। এ দুটি সংগঠন ১৯০৫ সাল থেকে পর পর তিন বছর স্বদেশী মেলার আয়োজন করে। স্বদেশী আন্দোলনে চট্টগ্রামের সম্পৃক্ততা অবিভক্ত বাংলায় উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল, যা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণেও সমর্থ হয়। মূলত ১৯০৭ সালের ১৭ জুন রবীন্দ্রনাথের চট্টগ্রামে আসার অন্যতম কারণ চট্টগ্রামের স্বদেশী আন্দোলন ও স্বদেশী মেলার সাফল্য। এছাড়া চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠায় কবি সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করেন। রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ আন্তরিকতার সাথে লোকসাহিত্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। এর প্রমাণ মেলে তাঁর সংগৃহীত ছড়া ও ধাঁধা’র পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশনা। প্রায় দশ বছরের প্রচেষ্টা ও শ্রমের ফসল তাঁর সংগৃহীত চট্টগ্রাম অঞ্চলের ছড়া–ধাঁধা–সংগ্রহ। ১৩০৯ সনের পরিষৎ পত্রিকায় (নবম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা) ছাপা হয় সাহিত্যবিশারদের ‘চট্টগ্রামী ছেলে–ভুলানো ছড়া’ শীর্ষক প্রবন্ধ এবং ১৩১২’র মাঘ সংখ্যায় ছাপা হয় ‘চট্টগ্রামী ছেলে ঠকান ধাঁধা’ শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত ১৯৮টি ছড়া এবং শেষোক্ত প্রবন্ধে ১৫০টি ধাঁধা মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথের আগমনের বছর চারেক পর চট্টগ্রামে সাহিত্য পরিষদ গঠিত হয়। ‘চট্টল সাহিত্য পরিষদ’ ১৯১৩ সালের ২২ ও ২৩ মার্চ চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করে। অন্যদিকে ১৯০৬ সালে স্বদেশী সঙ্গীত শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় ‘আর্য্য সঙ্গীত সমিতি’। এই সমিতির প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে ত্রিপুরা চৌধুরী ও যোগেন্দ্রলাল দত্ত। ১৯২০ সালে সঙ্গীতাচার্য সুরেন্দ্র লাল দাশের সময়েই চট্টগ্রামে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চা, যন্ত্র সঙ্গীতে পদ্ধতিগত শিক্ষণ এবং মেয়েদের জন্য সঙ্গীত শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। ১৯৩৬ সালে নিখিল বঙ্গ কংগ্রেস সম্মেলনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘আওয়ার অর্কেষ্ট্রা’ এর বাদন গুণীজনদের মুগ্ধ করেছিল। চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সাংস্কৃতিক তৎপরতা এখানে সহাবস্থানে থেকে এগিয়েছে। কখনও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে আসন্ন রাজনৈতিক সংকটের পূর্বলক্ষণ দেখে, আবার কখনও বা রাজনৈতিক আন্দোলনের সহযোগী শক্তি হিসেবে বেগবান হয়েছে। বঙ্গভঙ্গের পর অসহযোগ–খিলাফত আন্দোলনের সময়েও চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক তৎপরতা জোরদার ছিল। ১৯৩০ সালে যুব বিদ্রোহের শুরু থেকেই চট্টগ্রামের শহর ও গ্রামে গড়ে ওঠে ক্লাব, পাঠাগার ও ব্যায়ামাগার।
বাংলার প্রতিভাদীপ্ত কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্যে চট্টগ্রাম আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে কংগ্রেস নেতা অধ্যাপক হেমন্ত সরকারের সাথে কবি নজরুল প্রথমবারের মতো চট্টগ্রাম আসেন। চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্র সংসদের তৎকালীন নেতা মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার ও কলেজ অধ্যক্ষ কামাল উদ্দীনের আমন্ত্রণে চট্টগ্রাম কলেজের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নজরুলের চট্টগ্রামে আগমন। প্রথমবার চট্টগ্রাম এসে খুব খুশি হয়েছিলেন কবি নজরুল যা চট্টগ্রামের বেগম শামসুন নাহার মাহমুদের কাছে ১১ আগস্ট ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে লেখা চিঠিতে তিনি অকপটে স্বীকার করেছিলেন, ‘ফুল যদি কোথাও ফুটে, আলো যদি কোথাও হাসে, সেখানে আমার গান গাওয়ার শোভা পায়, গান গাই। সেই আলো, সেই ফুল পেয়েছিলাম এবার চট্টলায়, তাই গেয়েছি গান… তোমরা আমায় বলেছ লিখতে! সে বলা আমায় আনন্দ দিয়েছে, সৃষ্টির বেদনাও জেগেছে অন্তরে। তোমাদের আলোর পরশে শিশিরের ছোঁয়ায় আমার মনের কুড়ি বিকচ হয়ে উঠেছে। তাই চট্টগ্রামে লিখেছি।’ ১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে দ্বিতীয়বার চট্টগ্রামে এসেছিলেন কবি। চট্টগ্রাম ভিক্টোরিয়া ইসলামী হোস্টেল ও মুসলিম শিক্ষা সমিতির ৩০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে যোগদান করেন। ১৯৩৩ সালে তৃতীয়বার চট্টগ্রাম আসেন কবি নজরুল ইসলাম। এ সময় রাউজানে কবি তরুণ কনফারেন্স ও শিক্ষা সম্মিলনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। চট্টগ্রামে কবি তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘সম্মানের গান’, ‘বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি’, গীতিনাট্য ‘মধুমালা’ ছাড়াও চক্রবাক, শীতের সিন্ধু, শিশু যাদুকর, সাত ভাই চম্পার বেশ কিছু কবিতা লিখেছেন। কবিতার পাশাপাশি চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে তাঁর রচিত রচনা দিয়ে গেছেন চট্টগ্রামের সংস্কৃতিকে। এখানে বসে তিনি রচনা করেছেন– ‘আমার সাম্পান যাত্রী না লয়/ভাঙা আমার তরী/আমি আপনারে লয়েরে ভাই/এপার ওপার করি।’ ‘তোমায় কূলে তুইলা বন্ধু আমি/নামছি জলে/আমি কাঁটা হইয়া রই নাই বন্ধু/তোমার পথের তলে।’ নজরুলের চট্টগ্রাম আগমন এবং তাঁর এ সকল কর্মযজ্ঞ বরাবরই চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রেরণা যুগিয়েছে।
১৯৩০ সালের যুব বিদ্রোহের পরে ব্রিটিশ সরকার চট্টগ্রাম বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। ১৯৪০ সালের পর ভারতের রাজনীতিতে মুসলিম লীগ গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সমসাময়িক চট্টগ্রামে বামপন্থী রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল লক্ষণীয়। যা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও প্রভাব পড়ে। চট্টগ্রামে ‘প্রগতি লেখক সংঘ’ প্রতিষ্ঠা, ‘কবিয়াল সমিতি’ গঠন, নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলন উপলক্ষে মানিক বন্দেপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ কবি–সাহিত্যিকের আগমন, ১৯৪৬ সালের অস্থিতিশীল পরিবেশে জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভাব জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে নজরুল জয়ন্তী উদযাপন, প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকা ‘সীমান্ত’ প্রকাশের উদ্যোগ ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে।
১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম হলেও বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির উপর পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ শুরু হয়। চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক কর্মীরা বাঙালি সংস্কৃতির প্রগতিশীল ধারাকে এগিয়ে নিতে শিল্পী সাহিত্যিকদের নিয়ে ‘সাংস্কৃতিক বৈঠক’, ‘প্রান্তিক নব নাট্য সংঘ’ প্রভৃতি সংগঠনের জন্মলাভ, আণবিক বোমার ধ্বংসকারিতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক স্বাক্ষর অভিযানে অংশগ্রহণ করে ৭ লক্ষ মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। সারাদেশের ন্যায় চট্টগ্রামেও প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে। চট্টগ্রামের ছাত্র–বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মীরা আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সভাপতিত্বে জে.এম. সেন হলে প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়ে ভাষা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পটভূমি গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। কিন্তু ১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে চট্টগ্রামের সচেতন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীরা দাঙ্গা প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন। মাদারবাড়ি ক্লাব, নন্দনকানন শক্তি সংঘ, দেওয়ানজী পুকুর পাড়ের অগ্রণী সংঘের সদস্যবর্গ ও প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিকদের উদ্যোগে জে.এম. সেন হলে শেখ রফি উদ্দিন সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে দাঙ্গা প্রতিরোধের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা–বিরোধী দীর্ঘ এক মিছিল বের হয়। মিছিলে শিল্পীরা দাঙ্গা–বিরোধী গান গেয়ে পুরো শহর প্রদক্ষিণ করেন। তৎকালীন ঔপনিবেশিক সরকার আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ‘সাংস্কৃতিক বৈঠক’ এবং ‘প্রান্তিক নব নাট্য’ সংঘ যৌথভাবে ১৯৫১ সালের ১৬–১৯ মার্চ হরিখোলার মাঠে দেশের প্রথম সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। এর মূল সভাপতি ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। অফিস ও সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে চৌধুরী হারুনুর রশিদ ও মাহবুবুল আলম চৌধুরী। সম্মেলনের আবেদনপত্র সায়দুল হাসান ও শওকত ওসমানের যুগ্ম স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্মেলন উদ্বোধন করতে ঢাকা থেকে এসেছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল। এছাড়া সলিল চৌধুরীর নেতৃত্বে ‘ভারতী নাট্যসংঘ’ এবং সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস (জর্জ বিশ্বাস), হেনা বর্মন প্রমুখ অংশগ্রহণ করেছিলেন। কবিয়াল রমেশ শীল ও ফনি বড়ুয়া সারারাত উপস্থাপন করেছিলেন শান্তি ও যুদ্ধ বিষয়ক কবি গান। সাংস্কৃতিক সম্মেলনে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের কন্ঠে উচ্চারিত হয় বাঙালির মাতৃভাষা, বাঙালির সংস্কৃতি এবং সমাজের রূপ ও স্বরূপের কথা। সাহিত্য বিশারদের ভাষণে ছিল ৫২’র আসন্ন দুর্যোগের আভাস, তাই এই সম্মেলন একদিকে তখনকার পূর্ববাংলার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করে, অন্যদিকে বাঙালি–সংস্কৃতির প্রতি যে কোন হামলা প্রতিরোধে সংগ্রামী চেতনার জন্ম দেয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষনে হত্যার প্রতিবাদে চট্টগ্রামের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক মাহবুব–উল–আলম চৌধুরী ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ১৭ পৃষ্ঠার দীর্ঘ একটি কবিতা ‘কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি’ লিখেন, যেটি ছিল একুশ নিয়ে লেখা প্রথম কবিতা। চট্টগ্রামের এ সকল সাংস্কৃতিক তৎপরতার হাত ধরে ১৯৫৩ সালের ১৭–১৮ এপ্রিল জে.এম. সেন হল প্রাঙ্গনে ‘চট্টগ্রাম কবিয়াল সমিতি’ ও ‘প্রান্তিক নাট্য সংঘ’ দেশের প্রথম লোক সংস্কৃতি সম্মেলনের আয়োজন করেন। ১৩৫৮ (১৯৫১ সাল) বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রবর্তক প্রেস থেকে রেলওয়ের একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘পরিচিতি’ প্রকাশিত হয়। ১৯৫৯ সালের ২২ নভেম্বর চট্টগ্রামের বুদ্ধিজীবীরা মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের সংগঠক আবুল ফজলকে নাগরিক সংবর্ধনা দেন। সংবর্ধনায় বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা চট্টগ্রামের তরুণ সমাজকে কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে মুক্তবুদ্ধির চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে।
ষাটের দশকের শুরুতেই তৎকালীন সরকার রবীন্দ্র সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। চট্টগ্রামের সংস্কৃতি–কর্মীরা ১৯৬০ সালে এনায়েত বাজারস্থ ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউটে নজরুল হীরক জয়ন্তী পালন করে। এরপর বৈরী পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ চট্টগ্রামের সেন্ট প্লাসিডস স্কুল প্রাঙ্গনে সপ্তাহব্যাপী রবীন্দ্র শত জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ স্পষ্ট কন্ঠে জানিয়ে দেন, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি বাঙালির মহৎ উত্তরাধিকার। ষাটের দশক চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে স্মরণীয় দশক। ১৯৬২ সালের শুরুর দিকে চান্দগাঁও এর (কালুরঘাট) ১০ কিলোওয়াট শক্তি সম্প্রচার যন্ত্র স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয় এবং জুলাই মাসে পরীক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়। ১৯৬৩ সালের ১ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। এই বেতার কেন্দ্র হতে নিয়মিত বিভিন্ন ঘরানার অনুষ্ঠান প্রচার করা হতো। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ করলে এর বিরুদ্ধে আবুল ফজলের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম থেকে কয়েকজন বুদ্ধিজীবী তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দেন যে, ‘রবীন্দ্রনাথকে মুছে দেওয়ার মতো সামর্থ্য পাকিস্তান কেন, সমগ্র ভূমণ্ডলেরও নেই’। সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রবীন্দ্র শিল্পীগণ তখন চট্টগ্রাম বেতার বয়কট করেন। ষাটের দশকের পুরো সময় ধরে চট্টগ্রামের প্রগতিশীল ছাত্র –ছাত্রীরা বাংলা প্রচলন, বাঙালি সংস্কৃতির বহিরঙ্গ রূপকে জনসমক্ষে তুলে ধরা, লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ, চারুকলা চর্চাসহ বিভিন্ন কাজে আত্মনিয়োগ করে। চট্টগ্রাম কলেজ ছিল এ সকল কর্মকাণ্ডের সূতিকাগার। তাদের এ সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চট্টগ্রামে প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।
ষাটের দশকের শেষে ‘লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে মানে না কাহারো ঋণ’ – বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম শুরু হয়। ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চের সংগীতানুষ্ঠান, মমতাজ উদ্দীন আহমদের নাটক ‘এবারের সংগ্রাম’ এবং ১৬ মার্চ থেকে ট্রাকে করে রাস্তার মোড়ে মোড়ে অনুষ্ঠান পরিবেশন জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র–ছাত্রী সমিতির উদ্যোগে ২৪ মার্চ প্যারেড ময়দানে মমতাজ উদ্দীন আহমদ রচিত ‘স্বাধীনতার সংগ্রাম’ নাটক অভিনীত হয়। এই নাটক দেখে ২০–২৫ হাজার উজ্জীবিত দর্শক মিছিল করে বন্দরের দিকে এগিয়ে যায় পাকিস্তানি ‘সোয়াত’ জাহাজ থেকে অস্ত্র–খালাস প্রতিরোধ করতে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। এ সময়ে সারা দেশের মতো চট্টগ্রামেও সংস্কৃতি ও রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে মিলে মুক্তিযুদ্ধের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।
১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় বাঙালির স্বাধীনতা। বাঙালির সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এটি ছিল নতুন সূর্যোদয়। ১৯৭২ সাল থেকে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি, মহান স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস পালনে এলো নতুন আঙ্গিক, নতুন আভরণ। গড়ে ওঠে গ্রুপ থিয়েটারের চেতনা। নতুন দেশের চট্টগ্রামেই প্রথম অভিনীত হয় পথ নাটক। বাঙালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক কর্মীরা গড়ে তোলে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক কর্মীরা তাদের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠায় সাংস্কৃতিক চর্চায় মনোনিবেশ করে। বর্তমানে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় জেলা শিল্পকলা একাডেমি, মুসলিম হল, থিয়েটার ইনস্টিটিউট ইত্যাদিতে। প্রজন্ম হতে প্রজন্ম সংস্কৃতির বার্তা পৌঁছে দিতে চট্টগ্রাম সম্মিলিত পহেলা বৈশাখ পরিষদ, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, আবৃত্তি সংসদ, রবীন্দ্র শিল্পী পরিষদ, দৃষ্টি চট্টগ্রাম, উদিচি, প্রমা, ফুলকি ও মোর্চাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন সাংস্কৃতিক চর্চা অব্যাহত রেখে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করতে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০১ সালের ১ জানুয়ারি চট্টগ্রামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে প্রকাশ, প্রচার ও গবেষণার মাধ্যমে তা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ‘চট্টগ্রাম একাডেমি’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠন চট্টগ্রামের লেখক ও প্রকাশনা শিল্পের স্বার্থ রক্ষা এবং লেখক, কবি, সাহিত্যিক সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। চট্টগ্রাম একাডেমির উদ্যোগে প্রতিবছর ‘স্বাধীনতার বইমেলা’ আয়োজন করা হয়। বইমেলার পাশাপাশি চট্টগ্রাম লেখক কোষ, সংগীত কোষ ইত্যাদি অনেক বই প্রকাশ করে নজর কেড়েছে চট্টগ্রাম একাডেমি।
প্রাচীনকাল থেকে চট্টগ্রামে কাওয়ালি, গজল, হামদ্, নাত্, মারফতি, মুর্শিদি ইত্যাদি ইসলামী সংস্কৃতির প্রচলন রয়েছে। যা বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। এই গানগুলোতে সাধারণত আল্লাহ্ এবং নবীর প্রশংসা, ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। গজলের সুরেলা এবং কাওয়ালির ছন্দবদ্ধ পরিবেশনা চট্টগ্রামে খুব জনপ্রিয়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে শিল্পী আবু কাওয়ালের খ্যাতি সুদূর কলকাতা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। আবু কাওয়ালের সমসাময়িক ছিলেন রশীদ কাওয়াল ও উকিল কাওয়াল। এছাড়া সেলিম নিজামী, ইসলাম কাওয়াল, আবদুল মান্নান কাওয়াল প্রমুখ কাওয়ালি পরিবেশন করতেন। বর্তমানে ওবায়দুল্লাহ তারেক (জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী), এডভোকেট জুনায়েদ শিবলি, কাদের আল নেওয়াজ, হাফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী, আবু সাদেক নোমানী প্রমুখ কাওয়ালি পরিবেশন করে যাচ্ছেন।
চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের ইতিহাসও সমৃদ্ধ। আঞ্চলিক, মরমি ও মাইজভাণ্ডারী গানে নবযুগ সৃষ্টি করেছেন আবদুল গফুর হালী। ‘মনের বাগানে ফুটিল ফুল গো’, ‘পাঞ্জাবিঅলা মনে বড় জ্বালারে’, অ শ্যাম রেঙ্গুম ন যাইও, কিংবা মাইজভাণ্ডারি গান ‘দেখে যারে মাইজভাণ্ডারি হইতাছে নূরের খেলা’ এমন অনেক জনপ্রিয় গানের স্রষ্টা আবদুল গফুর হালী। শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণব এবং শেফালী ঘোষকে বলা হয় চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী। শ্যামসুন্দর বৈষ্ণবের জনপ্রিয় ও কালজয়ী গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বানুরে ও বানু, আর বাইক্যা টেঁয়া দে, ও জেডা ফইরার বাপ প্রভৃতি। শেফালী ঘোষের চিরসবুজ গানের মধ্যে রয়েছে ‘ও রে সাম্পানওয়ালা/ তুই আমারে করলি দিওয়ানা’, ‘ছোড ছোড ঢেউ তুলি পানিত/ লুসাই পাহাড়ত্তুন লামি যারগই কর্ণফুলী’, ‘নাতিন বরই খা, বরই খা, আঁতে লইয়া নুন/ ঠেইল ভাঙ্গিয়া পইজ্জে নাতিন বড়ই গাছত্তুন’ ইত্যাদি। কিংবদন্তী এই তিন গুণী শিল্পী চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরেছেন।
চট্টগ্রামের সংস্কৃতি একটি সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য যা ঐতিহাসিক প্রভাব, ভূ–প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণে গঠিত। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত ও বিকশিত হচ্ছে। চট্টগ্রামের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুপরিচিত করতে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে দৃশ্যমান পদক্ষেপ নিতে হবে। এভাবে সংস্কৃতি চর্চা, বিকাশ ও প্রচার–প্রসারে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।
তথ্যসূত্র: আবদুল হক চৌধুরী, বন্দর শহর চট্টগ্রাম, ১৯৯৪; ওহীদুল আলম, চট্টগ্রামের ইতিহাস, ১৯৮২; নজরুল রচনাবলী, বাংলা একাডেমি, ২০০৯; Syed Ahaadul Huq, A short History of Chittagong, 1949 ; Suniti Bhushan Qamungo, A History Of Chittagong, 1988।
লেখক: পিএইচডি গবেষক, শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।