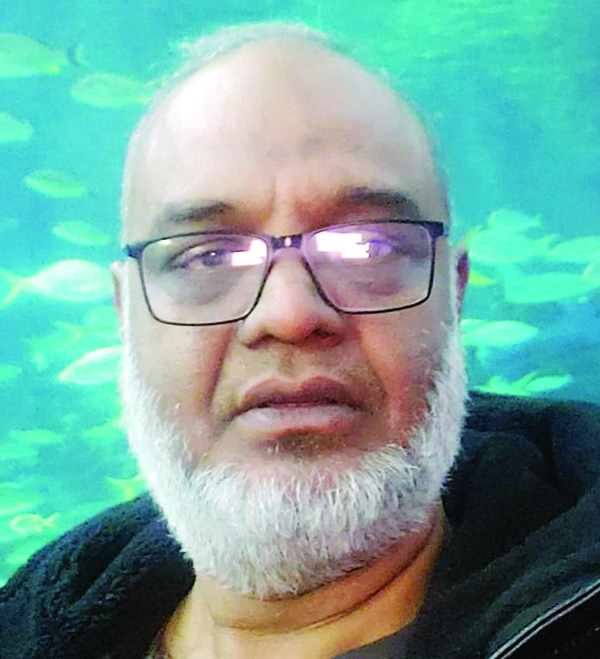১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র দু’টির মধ্যে ভারত মোটামুটি গণতান্ত্রিক ধারা ও পাকিস্তান গণতান্ত্রিক ধারার পরিবর্তে সেনা শাসন ও সেনা সমর্থিত শাসনে পরিচালিত হতে থাকে। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে পরিচালিত না হওয়ায় ও বৈষম্যের কারণে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে আলাদা রাষ্ট্রের মালিকানা লাভ করে। কিন্তু শুরু থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর একগুঁয়েমি ও ব্যক্তি বিশেষের একনায়কতন্ত্রিক মনোভাবের কারণে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারেনি। ফলে এদেশে গণতন্ত্র বার বার হোঁচট খেয়েছে ও লাইনচ্যুত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে আপামর জনগণ ১৯৯০, ২০০৬ ও ২০২৪ সালে রাস্তায় নেমে এসেছে ও সরকার পরিবর্তন করেছে এবং প্রতিবারই রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। যদিও গণতন্ত্রের বিকল্প গণতন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু নয় এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমেই গণতন্ত্র আদায় করতে হবে। সে প্রেক্ষিতে ৫ই অগাস্টের পট পরিবর্তনের পর বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্রের মূলনীতি সংশোধনের জন্য ঐকমত্য কমিশন গঠন করেছে। বর্তমানে সেখানেই রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি টেকসই রাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠনের লক্ষ্যে দফায় দফায় আলোচনা হচ্ছে। আশা করা যায় কয়েক মাসের মধ্যে এর একটা যৌক্তিক সমাধান আমরা অবলোকন করতে পারবো।
আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি গণতান্ত্রিক হবে, গণ–অভ্যুত্থানের পর এতে কারোরই দ্বিমত নেই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রয়েছে নানা ধরন। তবে রাষ্ট্র পরিচালনায় কোন পদ্ধতির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমাদের জন্য অধিকতর প্রযোজ্য হবে সেটি নিয়েই চলছে আলোচনা। গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতি দুই ধরনের। এক সংসদীয় বা ওয়েস্ট মিনস্টার ধাঁচের সরকার পদ্ধতি এবং দুই রাষ্ট্রপ্রধান দ্বারা পরিচালিত সরকার পদ্ধতি।
ওয়েস্ট মিনস্টার নামটি এসেছে লন্ডনের হাজার বছরের প্রাচীন ওয়েস্ট মিনস্টার প্রাসাদের নাম থেকে। যা ৫০০ বছর ধরে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সংসদীয় পদ্ধতির সূতিকাগার এবং বড় উদাহরণ হলো ইংল্যান্ডের সরকারব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় একজন আলঙ্কারিক রাষ্ট্রপ্রধান (রাজা) আছেন, যাঁর কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নেই। তিনি নির্বাচিত হন না, বংশানুক্রমিক ভাবে পদটিতে অধিষ্ঠিত হন। ক্ষমতা থাকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত আইনসভার হাতে।
আইনসভার সাধারণত দুটি কক্ষ থাকে। নিম্নকক্ষ গঠিত হয় জনগণের ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে আর উচ্চকক্ষ গঠিত হয় প্রধানত মনোনীত/বংশানুক্রমিক খেতাবধারী ব্যক্তিদের নিয়ে। আইন সভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে, মন্ত্রী হন সংসদ সদস্যদের মধ্যে থেকে, দলের নেতা হন প্রধানমন্ত্রী। অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগ ও আইনসভার মধ্যে কোনো ফারাক থাকে না। তবে সরকারপ্রধান আর রাষ্ট্রপ্রধান আলাদা হন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় আইনসভার নিম্নকক্ষের বিরোধী দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়।
অন্যদিকে রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত সরকার ব্যবস্থার উদাহরণ হলো যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতি। মার্কিন সংবিধান গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে এমন এক পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়। যেখানে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন, যিনি একই সঙ্গে সরকার প্রধানও বটে।
ফরাসি আইনবিদ মন্টেস্কুর ‘ক্ষমতার পৃথককরণ তত্ত্ব’ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে যেভাবে সরকার, আইনসভা ও বিচার বিভাগে ভাগ করার কথা বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সেই রকমের পৃথকীকরণ আছে। সেখানে সংসদ সদস্যরা মন্ত্রী বা সরকারের কোন পদাধিকারী হতে পারেন না। একইভাবে মন্ত্রীরা সংসদ সদস্য থাকতে পারেন না। এই পদ্ধতিতে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান একই ব্যক্তি হন। তিনি নির্বাচিত হন সরাসরি জনগণের ভোটে। তিনি মন্ত্রীদের নিয়োগ দেন, তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী মন্ত্রীরা পদে থাকেন এবং তাঁদের দিয়েই রাষ্ট্রপ্রধান সরকার চালান। অন্যদিকে আইনসভার সদস্যরাও নির্বাচনী আসন থেকে সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন।
শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নকক্ষ সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলেও উচ্চকক্ষ বা সিনেটে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল না। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের জন্য দুজন করে সিনেটর নির্বাচন করতেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আইনপ্রণেতারা। তবে ১৯১৩ সালে মার্কিন সংবিধানের ১৭তম সংশোধনীর মাধ্যমে সিনেটে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়।
মার্কিন রাষ্ট্রকাঠামোতে সিনেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আইন প্রণয়ন ও বৈদেশিক চুক্তি অনুমোদনের ক্ষমতা ছাড়াও সিনেটে শুনানি এবং অনুমোদন ছাড়া প্রেসিডেন্ট তাঁর মন্ত্রীদের (সেক্রেটারি) নিয়োগ করতে পারেন না। সুপ্রিম কোর্টসহ ফেডারেল বিচারকদের নিয়োগও সিনেটে অনুমোদিত হতে হয়। রাষ্ট্রপ্রধানসহ অন্য শীর্ষ পদাধিকারীদের চূড়ান্ত ভাবে অভিশংসিত করার ক্ষমতাও সিনেটের। এভাবে উচ্চকক্ষ মার্কিন রাষ্ট্রকাঠামোতে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রেখে উচ্চকক্ষ বা সিনেট স্বৈরতন্ত্রের উত্থান রোধসহ স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।
বাংলাদেশে ১৯৭২ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী শাসিত সংসদীয় পদ্ধতি চললেও ১৯৭৫ সালে বাকশালের মাধ্যমে চালু হয় রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার। সামরিক বেসামরিক শাসন মিলে সেটা বহাল থাকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত। সে বছরই সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে আবার চালু করা হয় সংসদীয় পদ্ধতির সরকার। তবে বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার পদ্ধতি যুক্তরাজ্যের সংসদীয় পদ্ধতি থেকে কিছুটা আলাদা। এই পার্থক্য হলো সংসদীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে। আমাদের দেশে সংসদ নয়, সংবিধানই সার্বভৌম। এই ব্যবস্থায় জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা সরকার গঠন করেন। তাঁদের নেতা একই সঙ্গে সংসদনেতা ও প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি সাধারণত অন্য সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রীদের মনোনীত করেন।
সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়া ব্যক্তিদের দ্বারাই সংসদ ও সরকার পরিচালিত হয়। অর্থাৎ সংসদ সদস্যরা আইন প্রণয়ন করেন এবং তাঁদের মধ্যকার কেউ কেউ সরকারের মন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতারও অংশীদার হন। সংসদ সদস্যদের নেতা ও মন্ত্রীদের ‘নিয়োগকর্তা’ হিসেবে আইন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের অধিপতি হয়ে ওঠেন প্রধানমন্ত্রী।
বাংলাদেশে একজন প্রধানমন্ত্রী কতটা ক্ষমতাবান এবং কতটা ক্ষমতার চর্চা করতে পারেন, তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো বিগত সরকার প্রধান। শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসক হয়ে ওঠার জন্য যেমন তাঁর রাজনীতির দায় আছে, তেমনি বাংলাদেশের বিদ্যমান সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভূমিকাও রয়েছে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এতো বেশি যে এখানে ব্যক্তির ভূমিকা অনেকটাই গৌণ হয়ে যায়। যিনি প্রধানমন্ত্রী হন, তিনি থাকেন সব ধরনের জবাবদিহির ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ আইন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের প্রধান হওয়ার কারনে প্রধানমন্ত্রী উপর অসহায়ভাবে জনগণকে নির্ভরশীল হতে হয়। এই ব্যবস্থা কোনোভাবে গণতন্ত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। ফলে কোন ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমাদের জন্য উপযোগী হবে, এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন। তবে একটা রাষ্ট্রে গণতন্ত্র আছে কি না, তা নির্ধারণ করার অনেক ধরনের মাপকাঠি আছে। আধুনিক যুগের অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন, কোনো দেশে গণতন্ত্র আছে কি না।সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে একটা ‘সাধারণ’ প্রশ্নের মাধ্যমে।
প্রশ্নটি হলো, রাষ্ট্রের একজন সাধারণ ব্যক্তির সরকার প্রধান হওয়ার পথ কতটা সহজ বা আদৌ সম্ভব কি না। অর্থাৎ নিজের যোগ্যতা, শ্রম আর ক্যারিশমা দিয়ে জনগণের সমর্থন আদায় করে কোনো একদিন তিনি দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন, এমন কোনো বৈধ পদ্ধতি সে দেশে আছে কি না। যদি সে রকম সুযোগ থাকে, তাহলে সেই দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক বলা যেতে পারে। যেমন কৃষ্ণাঙ্গ ও পূর্বপুরুষ অভিবাসী হওয়া সত্ত্বেও বারাক ওবামা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে পেরেছিলেন। এটা তিনি পেরেছিলেন তাঁর নিজস্ব যোগ্যতা এবং দেশটির গণতান্ত্রিক কাঠামোর জোরে। অন্যদিকে রাজতন্ত্র না থাকলেও অনেক দেশে পারিবারিক উত্তরাধিকার ছাড়া রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা চিন্তাই করা যায় না। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই ধরনের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি।
তাই এখনই মোক্ষম সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা কীভাবে চলবে তা ঠিক করার। এবার যদি আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত না নিতে পারি ও একটি টেকসই গণতান্ত্রিক স্থায়ী ব্যবস্থার দিকে না যাই, তবে বার বার স্বৈরাচার সৃষ্টি হবে ও বার বার জনগণকে রক্ত দিয়ে সেই স্বৈরাচারের পতন ঘটাতে হবে। তাই প্রয়োজনে ভেবেচিন্তে সময় নিয়ে হলেও রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি স্থায়ী সমাধান করা দরকার, যা দেশের জনগণ ও জনগণের গণতান্ত্রিক ধারা চালিয়ে নেওয়ার স্বার্থে জরুরি।
লেখক: প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট।