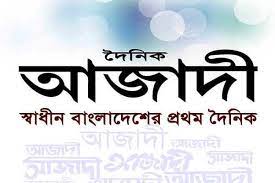গুমাই বিল। চট্টগ্রাম কাপ্তাই সড়কের উত্তর অংশ জুড়ে নয়নাভিরাম এক সবুজ সৌন্দর্যের নাম। যাকে বলা হয় বাংলাদেশের অন্যতম শস্যভাণ্ডার। চট্টগ্রাম একাডেমির পিকনিকে উয়াগ্গছড়া যাওয়ার পথে এই বিলের সৌন্দর্য উপভোগ করলেও কখনো এর সম্পর্কে বিস্তারিত জানা হয়নি। শুধু জানতাম এটি একটি ঐতিহাসিক ঐতিহ্যবাহী বিল। তাই এবার গন্তব্য স্থির করলাম শুধু গুমাই বিল। শরতের চটুলতা প্রকৃতিতে। এই রোদ, এই ঝুম বৃষ্টি। সোজাসুজি না গিয়ে অনন্যা আবাসিক এলাকার পথ ধরে যেতে যেতে দেখতে পাচ্ছিলাম কাশের বনে শুভ্রতার ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে। কাপ্তাই সড়কের দু‘পাশে ইউক্যালিপটাস, মেহগনি, শিরীষ, রাধাচূড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রহরীর মতো। রাঙ্গুনিয়া এলাকায় প্রবেশ করতেই হাতের বামদিকে বিস্তীর্ণ সবুজের হাতছানি। বিলের প্রান্ত ছুঁয়ে ধূসর রঙের পাহাড়। গুমাই বিল যেন পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা একটি সবুজ নদী। স্থানীয়দের ভাষায় ‘গুঁয়ার বিল’। প্রায় সাড়ে চার হাজার হেক্টর আয়তনের গুমাই বিলের আয়তন কমে গিয়ে এখন তিন হাজার হেক্টরে এসে ঠেকেছে। এই বিলের আলে, জমিতে গেঁথে রয়েছে ইতিহাস।
১৯৭৬ সালের এক গবেষণায় বলা হয়, গুমাই বিলের এক মৌসুমের উৎপাদিত ফসলে বাংলাদেশের আড়াই দিনের খাদ্য চাহিদা মেটানো সম্ভব। বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতিতে কেউ কেউ গুমাই বিলকে দেশের ‘হৃদপিণ্ড’ অভিহিত করেন। যেখানে থেমেছি এলাকাটার নাম কাটাখালি। মরিয়ম নগর ইউনিয়ন। টং চায়ের দোকানটি বেশ খোলামেলা। গুরা মিয়ার দোকান নামে এলাকাবাসীর কাছে পরিচিত এই দোকানও একটি ইতিহাস সমৃদ্ধ চায়ের দোকান। ছোট্ট একটি চালাঘরের মতো করে এটি গড়ে ওঠে সত্তর দশকের আগে। দোকানী ফরিদুল ইসলাম চমৎকার শুদ্ধ ভাষায় কথা বলেন। তাঁর কাছে জানতে চাইলাম তাঁর দেখা গুমাই বিল সম্পর্কে। তিনি বললেন, ছোটবেলায় আমরা দেখেছি চাষ মারা (পুরো মৌসুমের ফসল নষ্ট হওয়া) যেতো। তখন কাপ্তাই বাঁধ তৈরি হয়নি। ফলে বর্ষায় বৃষ্টির পানি আর পাহাড়ি ঢলে ডুবে যেতো বিল। আর একবার পানি হলে দুই তিনবার রোপন করেও ধান পাওয়া যেত না। এক কানি (বিশ গণ্ডা) জমিতে কুড়ি, তিরিশ আড়িও ধান পেতাম না। এখন খাল কাটা হয়েছে। বিলে পানি জমে থাকে না। তাই পঁচিশ থেকে তিরিশ মণ ধান প্রতি কানিতে পাওয়া যায় এখন। তখনকার দিনের সৌন্দর্য আর এখনকার বিলের সৌন্দর্যের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। তখন বিলের তারুণ্য ছিল। ঝাঁক বেঁধে টিয়ে পাখি আসতো। বিলে সোনালী ধান আর আকাশে সবুজ টিয়ের ঝাঁক। যদিও আমাদের ফসলের ক্ষতি হতো তবুও এই সৌন্দর্য ছিল এক কথায় অপূর্ব! তখন চাষের মধ্যেও একটা উৎসব ছিল। আমরা লাঙ্গল, গরু নিয়ে চাষ করতাম। এখন ধরণ বদলেছে। লাঙ্গল, গরুর পরিবর্তে ইঞ্জিন চালিত মেশিন এসেছে। উন্নত মানের চাষাবাদ পদ্ধতিতে আমরা চাষ করছি। আগের সেই সনাতনী ধান নেই। ঊনপঞ্চাশ, ইরিটন, একপঞ্চাশ এরকম বিভিন্ন জাতের ধান চাষ হচ্ছে এখানে। কিছুক্ষণ পর সেখানে উপস্থিত হলেন আশি বছর বয়সী জলিল সওদাগর। এক সময় নিজে ছিলেন কৃষিকাজের সাথে সরাসরি জড়িত। বর্তমানে জমি বর্গা দিয়ে চাষ করেন। জানতে চাইলাম তার দেখা গুমাই বিল সম্পর্কে। তিনি নজরটিলা ওয়ার্ডের বাসিন্দা। বললেন, পাকিস্তান আমল থেকেই এই বিল দেখে আসছি। জন্ম যেহেতু এখানে, তাই এই বিলের কাদামাটি মেখেই আমাদের বড় হওয়া। তিনি বললেন, টিয়ে পাখির যে ঝাঁকের কথা আপনি বলছেন এদিকে আসলে ওরকম আসে না। যখন ধান পাকে তখন টিয়া পাখিসহ বিভিন্ন রকমের ছোট পাখি আসে, অতিথি পাখি আসে। পাকিস্তান আমল থেকে এই জমিতে আমার দাদা, আমার বাবা, পরে আমিও চাষ করেছি। বয়সের কারণে এখন নিজে না করতে পারলেও চাষা দিয়ে চাষ করাই। কিন্তু এখানে আমাদের পানির সমস্যা অনেক। বর্ষার মৌসুমে বেশি পানি, শুকনো মৌসুমে পানি না পাওয়ার কষ্ট। বিলের জন্য পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা করতে হলে খাল কাটা প্রয়োজন। বর্ষার মৌসুমে ঝড়–বৃষ্টি, বন্যায় জমিতে পানি জমে যায়। তখন পাম্প মেশিনও পাওয়া যায় না, যাতে পানি সেচে জমিতে চাষের কাজ শুরু করবে। যদি বড় খালটা খনন করে পানি যাওয়ার রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হয় তাহলেও আমাদের চাষাবাদে অনেক সুবিধা হয়। তাছাড়াও এই বিলের আশেপাশে অনেক খাল আছে। কিন্তু বেশিরভাগ খাল ভরাট হয়ে গেছে। যার জন্য চাষাবাদে আমাদের ভীষণ অসুবিধা ভোগ করতে হয়। ঐতিহ্যবাহী এই বিলটাকে রক্ষা করতে হলে খালগুলো কেটে পানি যাওয়ার রাস্তা তৈরি করে দিলে ফসলের উৎপাদন আরো অনেক বেশি হবে। শুকনো মৌসুমে পাম্প মেশিনের পানি সব জমিতে যায় না। নিশ্চিন্তপুর এলাকার রেশম বাগানে একটি ছড়া আছে যেখানে রাঙ্গামাটি থেকে পানি আসে। তখন সেই ছড়ায় বাঁধ দিয়ে জমিতে পানির ব্যবস্থা করা হয়। তবুও আমাদের অনেক জমি খালি পড়ে থাকে শুধুমাত্র পানির অভাবে। পাশে একটি নতুন খাল কাটা হচ্ছে। রাস্তাও হচ্ছে। এই খাল আর রাস্তা দুটোই আমাদের অনেক বেশি উপকারে আসবে। তিনি জানালেন, তবুও বর্তমানে আগের তুলনায় ধানের পরিমাণ অনেক বেশি পাওয়া যায়। তাঁর ভাষায়, পাকিস্তান আমলে কী ধান ছিলো? এখন তো ধানের পরিমাণ অনেক বেশি। এখন দশ কানির ধান এককানিতে হয়। যদিও লিচু বাগানের ওদিকে অনেক জমি ভরাট হয়ে ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দালান কোঠা উঠেছে। আগেকার দিনে ওদিকে সব মানুষ চাষাবাদ করতেন। পরবর্তীতে প্রায় হাজারের মতো জমিতে বিল্ডিং হয়ে গেছে। কিন্তু ধানের ফলন কমেনি বরং অনেক বেশি বেড়েছে। তিনি বললেন আমি কিন্তু চাষাবাদের পাশাপাশি ব্যবসা–বাণিজ্য করেছি। ব্যবসার কাজে ঢাকা হয়ে বর্ডার পর্যন্ত গেছি। গুমাই শুধু ধান চাষের জমির জন্য বিখ্যাত নয়, এখানে যে খাল গুলো আছে সেখানে কিন্তু প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। ভরা বর্ষায় যখন জমি পানিতে তলিয়ে যায় তখন মাছের গ্রোত বসে। একটা সময় আমরা কাঁধে করে ধানের মত মাছ বয়ে নিয়ে গেছি। বর্তমানেও এসব খালে যে মাছগুলো পাওয়া যায় ওগুলোর দাম কেজিপ্রতি বারো থেকে পনেরো’শ টাকা। এই বিলে আছে কাজীর দিঘি। যেখানে বাণিজ্যিকভাবে মাছের চাষ হয়। স্থানীয়ভাবে খালগুলোকে আমরা গুমাই খাল বলি। ওই যে পাহাড় দেখতে পাচ্ছেন আপনি সেখান থেকে শুরু হয়ে এই খাল রাঙ্গামাটির হ্রদে গিয়ে মিশেছে। দেখতে পাচ্ছিলাম, জমিতে ধানের নতুন গাছ। জানতে পারলাম ওগুলো একপঞ্চাশ, বায়ান্ন ধানের চারা। বছরে দুই মৌসুমে এখানে ধানের চাষ হয়। আলাপ চলাকালে সেখানে এসে উপস্থিত হন এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠ আলকাজ মিয়া। তিনি বলেন, যখন ধান কাটা হয় সেই সময়ে বিলে চলাচলের সমস্যার কথা। বলেন, এখানে অনেক রাস্তার দরকার। একজন কামলার বেতন বারোশত থেকে পনেরোশত টাকা। সে পাঁচবার ধান নিয়ে জমি থেকে আসার কথা। সেজয়গায় তিনবারও সে আসতে পারে না চলাচলের অসুবিধার কারণে। সরকারিভাবে রাস্তা সংস্কার বরাদ্ধ হলেও জমি পর্যন্ত সেই সংস্কার এসে পৌঁছুয় না। যদি নদীর পার ধরে রাস্তা তৈরি করে দেয়া হয় তাহলে চাষাদের অনেক সুবিধা হবে। গরমের মৌসুমে বৃষ্টি হয়। তখন কাদার জন্য হাঁটাচলায় অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। আমন মৌসুমে বৃষ্টি হয় না। পথঘাট শুকনো থাকে। তখন আবার আমাদের সেই সমস্যা হয় না। বর্তমানে ছোটো ছোটো গাড়ি আছে। সেই গাড়িতে জমির ফসল সহজে আনা যায়। সেই সুবিধা নেয়ার জন্যে তো রাস্তার দরকার। যদি হরিণাখালের পাশ দিয়ে একটা কাঁচা ইটের মাইল তিনেক রাস্তা আমাদের অনেক দরকার। এখানে পর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা নেই। আগে একটা মোটর দিয়ে চাষ করতাম তিনশ কানি জমি। এখন দেড়শো কানিও করতে পারি না। কারণ গর্ত। মাটির তৈরি ড্রেন কুঁইচা আর কাঁকড়া নষ্ট করে দেয়। যার জন্যে জমিতে ঠিক মতো পানি যায় না। কোনো কোনো জায়গায় সরকারিভাবে পাকা ড্রেন বসানো হয়েছে। এদিকেও যদি সেভাবে ড্রেন করে দেয়া হয় আমাদের জন্য বেশি উপকার হয়। কাটাখালী হচ্ছে গুমাই বিলের নাভী। অথচ এই জায়গাটাই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। গুমাইয়ের দুঃখ হলো ঐতিহাসিক এই বিলে চলাচলের পর্যাপ্ত রাস্তা নেই আর ড্রেনেজ সিস্টেম নেই। জানতে চাইলাম নবান্ন উৎসবের কথা। দু‘জন খুব উৎফুল্ল হয়ে বললেন, সেটা তো আছেই। ঘরে ঘরে পিঠা–পুলি বানানো এটা এতো সাধারণ বিষয় আমাদের আলাদা করে চোখে পড়ে না। ঘরে ঘরে ভাপা পিঠা, জালি পিঠা, চিতই পিঠা বানানো হতো। অনেক খেজুর গাছ ছিলো। রস দিয়ে সেই পিঠা খেতাম আমরা। তাঁকে সেই আড়াই দিনের খাবারের প্রবাদ মনে করিয়ে দেয়ায় বললেন, এটা আমিও শুনেছি। কিন্তু আজ আপনাকে আমি নতুন একটি তথ্য দিতে চাই। এই যে রওজার হাটের গুমাই মার্কেট এখান থেকে গুমাই বিল শুরু হয়ে চন্দ্রঘোনা লিচু বাগানে গিয়ে শেষ হয়েছে। যদি তখনকার সময়ে আড়াই দিনের খাদ্যের যোগান হয়ে থাকে এখন হবে পনেরো দিনের। আমার বাবা–চাচাদের মুখে শুনেছি তখন এককানি জমিতে পাওয়া যেতো দুই কুড়ি, দেড় কুড়ি আড়ি ধান। তাঁরা চল্লিশ বলতেন না। এখন সেই জমিতে আমরা পাচ্ছি আশি–পঁচাশি মণ ধান। কতগুণ বেড়েছে খেয়াল করে দেখেন। জমি কিছু কমলেও ফলন বেড়েছে। এই যে আইয়ুব খান সরকার চিনা ধান এনেছে, ইরি ধান এনেছে, জিয়া সরকার খাল কেটেছে সেসবের কারণে আমাদের চাষা, যাদের ঘরে দশ আড়ি ধান থাকতো তাদের ঘরে এখন দশ শতক মণ ধান আছে। আমরা পেট ভরে খাচ্ছি। এই যে চৈত্র–বৈশাখ মাস, আমরা বলতাম অভাবের দিন। দূর–দূরান্ত থেকে ধান এনে রোদে শুকিয়ে চালকলে দিতাম। সেই চাল বাজারে বিক্রি করতাম। শবজি এনে বিক্রি করেছি। কোনোমতে চলেছি। কিন্তু এখনকার অবস্থা ভিন্ন। এই যে পাশে বসে আছে, সে একজন দরিদ্র কৃষক। কিন্তু তারঘরেও চারশ মণের উপরে ধান আছে। এর কারণ বাইরে থেকে যে উন্নতমানের বীজ নিয়ে আসা হয়েছে সেই ধান অনেকবেশি ফলনশীল। এই জমিতে বর্তমানে ছয় সাত আট ধরনের ধানের চাষ হয়। আবার দুই তিন বছর পরপর নতুন জাতের ধান আসে। আমাদের শৈশবে দেখেছি গুমাইয়ের বন্যা। তখনও কাপ্তাই বাঁধ তৈরি হয়নি। আড়াই তিনমাস পর্যন্ত বন্যার পানি রয়ে যেতো। বিস্তর মাছ হতো সেই পানিতে। আমরা মাছ ধরে সেই মাছ বিক্রি করতাম। এই যে বাইলা মাছ, আমরা এক কেজি পর্যন্ত দেখেছি। এখন যেভাবে পুটি মাছ পায়, তখন সেভাবে বিভিন্ন রকমের বড় বড় মাছ পাওয়া যেতো। এই যে ভাদ্র মাস, আগস্ট মাসে যখন বন্যার পানি কমে যেত তখন মাছের যে লাফালাফি আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। ঢাকা থেকে পর্যন্ত লোক এসে এই গুমাই বিলে মাছ ধরতো। আমাদের এই দোকানটা করেছি ১৯৭৩ সালে। বাঁশের চালা দিয়ে টং করছি। তখন দেখেছি ঢাকাসহ এখানকার বিভিন্ন এলাকার মানুষ এদে মাছ ধরছে। রাতের বেলায় তারা যখন টর্চ জ্বালিয়ে মাছ ধরতো মনে হতো অনেকগুলো জোনাকি বিলে জ্বলছে। অনেকে গাড়ি থামিয়ে মাছ কিনে নিয়ে যেতো। এই যে দোকানের পাশে খাল আছে? এই খালে আমার বাবা–চাচারা অড়বড়ই গাছ বসিয়ে দিতেন। ওরে মাছের ডেলা! আপনি বিশ্বাস করবেন না, এক একটি মাছের ওজন তিরিশ, পঁয়ত্রিশ কেজি, একমণ হতো। মাছগুলো দশ বিশজনে ধরে জমিতে টাল মারতাম। এগুলো ভাগ করে টুকরি ভরে ভরে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হতো। আমি এই গ্রামে গুরা মিয়া নামে পরিচিত। সেই সময়ের দিনগুলোতে ভালো পোশাক না পরেও, কম খেয়েও দিনভরে ছিলো আনন্দ। তখন কোনো মেয়ে স্কুলে গেছে, পাড়ায় বেড়াতে গেছে আমাদের চিন্তা ছিলো না। আমরা জানতাম নিশ্চয় সে নিরাপদে ফিরে আসবে৷ আমরা যখন মাঠে যেতাম, গাঙে নেমে গরুকে গোসল করাতাম, নিজেরা স্নান করতাম, ডুব দিয়ে মরিচ খেলা খেলতাম। তখন দেখতাম আমাদের মা বোনেরাও বিভিন্ন গৃহস্থালি কাজে কিংবা গোসল করতে নামছে। কিন্তু আমাদের মনে কোনো বাজে চিন্তা আসেনি। কারো গাছ থেকে একটা কাঁঠাল নামানো হয়েছে। বাড়ির সবাইকে ডেকে বলছে, কাঁঠাল খেয়ে যা। বিচিগুলো রেখে যাবি। এটাতে তরকারি হবে। বর্তমান সময়ে সেই পরিবেশ কি আছে? আমাদের নজরটিলা গ্রাম শিক্ষিত মানুষের গ্রাম হিসেবে পরিচিত। পাকিস্তান আমলেও এখানে চল্লিশজন করে শিক্ষিত লোক পাওয়া যেতো। এখানে ডাক্তার, ডক্টরেট করা মানুষ আছে। পাশের গ্রামে সেই তুলনায় কিছুই ছিলো না। কথাটা বললাম এই কারণে ওখানে বিলের মধ্যে যে নালা, যে ইট বসানো পাকা রাস্তা–দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। তারা পড়ালেখা করেনি কিন্তু নিজেদের এলাকার জমি সংস্কার করেছে। অথচ এগুলো হওয়ার কথা আমাদের। হয়নি, কারণ দুর্নীতি। তারা লেখাপড়া করে নিজের কথা ভেবেছে মানুষের কথা ভাবেনি। এগুলো এখানে বলার কথা না। কিন্তু কথা প্রসঙ্গে এসে গেলো। তবে সবকিছু মিলিয়ে যদি বলি, আমাদের একটা বিশুদ্ধ জীবন ছিলো। এই বিল, বিলের ধান, বিলের মাছ, খাল, নদী, পাহাড় সবকিছু আমাদের অনেক আপন। শুনেছেন নিশ্চয় মাছে–ভাতে বাঙালি। আমরা ঠিক সেই মাছ ভাতের মানুষ। এই গুমাই বিল আমাদের জীবনের সাথে মিশে আছে। এখানে ধান কাটার উৎসব হয়। মাছ ধরার উৎসব হয়, মধুমাসে ফলের উৎসব হয়। তাঁর কাছে এতোগুলো উৎসবের নাম শুনে বললাম পিঠা উৎসব করেন না? তিনি হেসে বললেন, আমাদের তো প্রতি মৌসুম উৎসব। তবে কয়েকবছর আগে একবার এখানে সরকারি উদ্যোগে পিঠা উৎসব হয়েছিলো। অনেক লোকজন এসেছিলেন। প্যান্ডেল করে বেশ জাঁকজমকভাবে এই উৎসব হয়েছিলো। ফেব্রুয়ারি মাসে যখন ধান রোপণ করা হয়, তখন পাখিরা সেই জ্বলায় সাঁতার কেটে কিছু ক্ষতি করে। তিনি হেসে বললেন, ওটা পাখিদের উৎসব। গুমাইয়ের অন্যকোনো দিকে টিয়ার ঝাঁক আসে কি–না আমরা জানি না। তবে এদিকে অতিথিপাখিসহ বিভিন্ন রকমের পাখি আসে সেখানে টিয়েও থাকে। আলকাজ মিয়ার সাথে কথা শেষ করে যখন বেরিয়েছি তখন বিকেল পাহাড়ের ওপাশে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা নামার ইঙ্গিত দিচ্ছে। কিছু সাদা বক ওড়াউড়ি করে বিলের পানিতে মাছের সন্ধান করছে হয়তো।
পুরনো ইতিহাস থেকে জানা যায়, সংস্কার হওয়ার আগে গুমাই বিল ছিলো বিরাট এক জলাভূমি। বৃটিশ পার্লামেন্টের সিনেটর রবার্ট মুন্দার ১৯৪৩ সালে এবং তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের কৃষি উপদেষ্টা হাশেম মাহফুজ গুমাই বিল পরিদর্শন করে কর্ণফুলী নদী থেকে খাল খননের কাজ শুরু করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৫ সালে আবদুল বারি তালুকদার স্থানীয় লোকজন নিয়ে গুমাই বিলের পতিত জমিকে চাষের উপযোগী করে তোলেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান গুমাই বিল পরিদর্শন করে আব্দুল বারী তালুকদারকে গুমাই পিতা উপাধি দেন। সেই সময় গুমাই বেইল সংস্কার কমিটির সভাপতি ছিলেন মরহুম আব্দুল ওহাব সিকদার তিনি অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের রাঙ্গুনিয়ার সভাপতি গান্ধীবাদী নেতা ছিলেন। এছাড়া কারণ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান গুমাই বিল পরিদর্শন করেন বলে জানা যায়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গুমাই বিলে ধান উৎপাদনে বিপ্লব সাধিত হয়। এই বিল ঘিরে রয়েছে মুন্দরী খাল, কুরমাই খাল, হাসেম খাল, হ্রদ খাল, কালাপানি খাল, বাইনালার ছড়া, বারঘোনিয়া ছড়া। কৃষি কাজের পাশাপাশি মাছ ধরে বিক্রি করাও এদের জীবিকার অংশ। ‘গোলা ভরা ধান আর খাল–বিল ভরা মাছ’ কথাটি এখানকার জনজীবনের সাথে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। এখানে হেমন্তের বিকেলের সোনালি আলোয় বিলের সোনালি ধান আরো উজ্জ্বল হয়ে কৃষকের মুখে হাসি ফোটায়। ‘আজ জীবন খুঁজে পাবি, ছুটে ছুটে যায়। হাসি নিয়ে আয় আর বাঁশি নিয়ে আয়‘- ভূপেন হাজারিকার এই গান যেন মজুরদের ডাক দিয়ে আনে গুমাইয়ে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা এই মজুরদের দেখেই হয়তো কেউ শত বছর আগে সেই প্রবাদটি লোকমুখে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন– ‘হাতত হাঁচি, কোঁরত দা, ভাত হাইলি রইন্যা যা’।
লেখক: গল্পকার; সম্পাদক–অনন্যধারা।