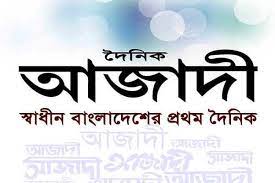কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের কিছু ধারণা আছে। বলাবাহুল্য তার অধিকাংশই প্রশংসার নয়, অনেকটা নিন্দার। তারমধ্যে কয়েকটি হচ্ছে, ‘ওরা প্রচণ্ড কিপ্টা। না খাইয়ে অতিথিকে বলে, “আজ কিন্তু না খেয়ে গেলে আবার আসলে খেতে হবে।” ওরা মিষ্টি কেনে এক পিস, দুই পিস, তিন পিস। মিষ্টির দোকানে এমন প্যাকেটও থাকে। ওরা মাছ কেনে দুই টুকরা, মাংসও কেনে ২ শ গ্রাম, তিন শ গ্রাম। খায়-দায়, জীবনযাপন করে অত্যন্ত আড়ম্বরহীন। ওপার থেকে ঘুরে আসা ব্যক্তিরা বলে ওখানে একসঙ্গে কয়েককেজি মিষ্টি কিনলে নাকি দোকানি জিজ্ঞেস করে, দাদা কি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? এই যে অভিযোগ বা নিন্দা তা কোনোটিই মিথ্যে নয়। কিন্তু কেন এবং কোন ক্ষেত্রে ঘটে তা জানলে বা বোঝার চেষ্টা করলে নিন্দাগুলো প্রশংসনীয় বলে মনে হবে।
প্রথমে বলি কলকাতার জীবনযাত্রার সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসবের মিল নেই। কলকাতার প্রকৃত চিত্র তা নয়। কলকাতার যেসব এলাকায় পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুরা ঠাঁই নিয়েছে সেসব এলাকার বাসিন্দাদের থেকে অন্যদের জীবনযাত্রা পৃথক। অর্থাৎ কলকাতার আদি বাসীদের জীবনযাপনের সঙ্গে এদের মিল নেই। যদিও কালের পরিক্রমা ও এদেশ থেকে যাওয়া মানুষগুলোর টিকে থাকার প্রবল সংগ্রামের কারণে এখন শিক্ষাদীক্ষাসহ জীবনের নানা ক্ষেত্রে তারা অনেক এগিয়ে গেছে।
এসব ব্যাপক অর্থে বুঝতে গেলে পেছনে তাকাতে হবে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে এই উপমহাদেশে বড় মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করার ফলে প্রায় দেড় কোটি মানুষ রাতারাতি উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছিল। এটি বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মাইগ্রেশনের ঘটনা। দাঙ্গায় নিহত হয়েছিল লাখের কাছাকাছি। ও সময়ে পূর্ববঙ্গে বাপদাদার ভিটেমাটি ছেড়ে কলকাতা, আসাম ও ত্রিপুরায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল লাখ লাখ হিন্দু। তো সেই উদ্বাস্তু বা রিফিউজি জীবন কাটাতে তাদের অনেক লড়াই করতে হয়েছে। পূর্ববঙ্গে জমিদারি বা স্বচ্ছতা থাকলেও ওপারে গিয়ে তাদের পড়তে হয়েছিল নিদারুণ অনিশ্চয়তার মধ্যে। মানবেতর সে জীবন পেরিয়ে আসা লোকরা স্বাভাবিকভাবেই জ্যাক লন্ডনের সেই গল্পের চরিত্রের মতো সবসময় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে ফলে জীবনযাপনে মিতব্যয়ী না হয়ে তাদের উপায়ও নেই। একবার দেশহীন, ঠিকানাবিহীন না হলে ৪৭-এর সে উদ্বাস্তু হয়ে পড়া মানুষদের মর্মবেদনা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এপার বাংলা থেকে যারা যায় তারা আত্মীয়তা বা পরিচয় সূত্রে যায় তো ওই একসময়ে রিফিউজি হয়ে পড়া এপার বাংলার দুখী মানুষগুলোর কাছেই ফলে হয়ত এমন একটি ধারণা নিয়েই অনেককে ফিরতে হয়েছে।
এরাই দুটোর প্রয়োজন হলে দুটো, চারটির প্রয়োজন হলে চারটি মিষ্টি নিয়ে ঘরে যায়। এরাই আজকের প্রয়োজন অনুযায়ী তিন টুকরো মাছ কেনে। তাতে ক্ষতি তো নেই বরং সেটাই আধুনিকতা, সেটাই মানবতা। এই অনুশীলনকে বিদ্রুপ করা মোটেও ঠিক নয়। এপার বাংলার মানুষের সঙ্গে ওপার বাংলার মানুষের ব্যবহার ও জীবনযাপনে প্রভেদ আছে। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এপার বাংলার মানুষের মধ্যে লোকদেখানো, বড়লোকি দেখানো এবং অপচয় করার প্রবণতা আছে। এই প্রবণতা কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে খুব বেশি নেই। প্রায় ২৫/২৬ বছর আগে বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব, লেখক রণজিৎ বিশ্বাস লিখেছিলেন বাংলাদেশের একজন উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা কতটা জৌলুশপূর্ণ জীবনযাপন করেন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় একই পদমর্যাদার কর্মকর্তার চেয়ে। এখনো পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই ভারত সরকারের কর্মকর্তাদের চেয়ে, ওদের এমপি, মন্ত্রীদের চেয়ে আমাদের দেশের একই পদের ও মর্যাদার লোকজনের জীবনযাপন অনেক অনেক আড়ম্বরপূর্ণ, পূর্বেই উল্লেখ করেছি কলকাতার এই অনুশীলন আমার কাছে মানবিক, আধুনিক ও নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি হিসেবেই বিবেচিত। যার যতটুকু দরকার বা যতটুকু কেনার সামর্থ্য আছে ততটুকু কেনার অধিকার থাকা প্রয়োজন। সমাজে সে অনুশীলন থাকা প্রয়োজন।
ধরুন, একজন শ্রমিক বা খেটে খাওয়া মানুষের লিচু খেতে ইচ্ছে করছে। তার দরকার দশটি বা বিশটি, তার সামর্থই আছে ততটুকু কেনার। বাংলাদেশে কি সে পরিমাণ লিচু কেনা সম্ভব? লিচুবিক্রেতারা ৫০টির কমে বিক্রি করতে চায় না, বিক্রি করে না। অনেক ফুসলিয়ে ২৫টি পর্যন্ত কেনা যেতে পারে তবে তা সব স্থানে নয়। কোনো শ্রমিক বা খুব সীমিত আয়ের কারো ইলিশ মাছ খেতে ইচ্ছে করছে। সে কি কিনে তা খেতে পারবে? এক হাজার টাকার নিচে একটি ইলিশ মাছ পাওয়া যাবে? মোটামুটি খাওয়ার যোগ্য রুই কিংবা কাতলা মাছের কেজি ২৫০ টাকার নিচে নয়। এক কেজি থেকে কম ওজনের এই মাছ কাঁটার জন্য খাওয়াও মুশকিল। ভালো মান ও বড় সাইজের রুই-কাতলার দাম ৪০০ টাকা কেজি। তিন কেজি ওজনের একটি মাছ কিনতে হলে দাম পড়বে অন্তত ১২০০ টাকা। এই দামে একটি মাছ কিনতে পারবে কত পার্সেন্ট মানুষ? একজন দিনমজুর, রিকশা বা বেবিট্যাক্সিচালক অথবা ওই শ্রেণির কারো কি কোনোদিন এত বড় একটি মাছের এক টুকরা খাওয়ারও সুযোগ হবে না? এখন যদি দুই শ গ্রামের ইলিশ মাছের এক বা দুই টুকরা কেনার সুযোগ থাকতো তাহলে ক্ষতি কী হতো?
আমরা কি কখনো তাদের কথা ভেবেছি? ৭০০-৮০০ টাকা কেজি গরুর মাংস একসঙ্গে এককেজি কেনার সামর্থ্য যাদের নেই তারা কি গরুর মাংস খাবে না? যদি দুই শ গ্রাম কেনার সুবিধা থাকতো, বাজারে সে নিয়ম থাকতো তাহলে এই মানুষগুলো মাসে-দুই মাসে একবার অন্তত গরুর মাংস খাওয়ার স্বাদ পেতো।
এক্ষেত্রে একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। চট্টগ্রামে গরুর মাংস বিক্রির সঙ্গে ঢাকার মিল নেই। ঢাকায় চট্টগ্রামের চেয়ে দাম কম তবে সঙ্গে হাড়ও নিতে হয়। চট্টগ্রামে দুই দামে গরুর মাংস বিক্রি হয়। শুধু রানের মাংস একদাম, হাড়সহ মাংসের একদাম। বলাবাহুল্য শুধু রানের মাংসের দাম তুলনামূলক বেশি। একদিন মাংস কিনে দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে আছি তা কুটানোর জন্য। এমন সময় এক বয়স্ক নারী এলেন মাংস কিনতে। তার বেশভূষায় বোঝা যাচ্ছিল তিনি সচ্ছল পরিবারের নন। তিনি দামটাম জেনে অনেক দ্বিধা-সংকোচ নিয়ে দোকানিকে বললেন আধা কেজি মাংস দিতে। একেতো নারীর বেশভূষায় দারিদ্র্যের ছাপ তার ওপর মাত্র আধা কেজি মাংসের কথা শুনে দোকানের কর্মচারী, যে মাংস কাটছিল সে খুব রা করল না। কয়েকবার বলার পর কর্মচারীটি খুব বিরক্ত হয়ে রানে ছুরি বসাতে বসাতে গজগজ করে বলল, ঝামেলা করতে কেন আসো? আধা কেজি কি বেচা যায়? বলে সে যে পরিমাণ মাংস কাটল স্কেলে দেওয়ার পর দেখা গেল তার ওজন হয়েছে তিন শ গ্রামের কম। এবার সে এখান থেকে এক টুকরা, ওখান থেকে এক টুকরা এবং শেষে একটি হাড় তুলে দিয়ে ৫০০ গ্রাম বা আধা কেজি মাংস মেপে পলিথিনে ভরলো। তার এই ব্যবহারে বারবার আপত্তি জানাচ্ছিলেন মহিলা। একপর্যায়ে কর্মচারীটি উল্টো খেপে গিয়ে বললেন, এমন বিরক্ত করো বলেই তো তোমাদের কাছে বেচি না।
এতক্ষণ তার এই তামাশা অবলোকন করে মুখ খুললাম আমি। বললাম, সকাল থেকে অনেক মাংস বিক্রি করছো এবং সবাইকে ঠকিয়েছো ওজনে এবং এখান থেকে ওখান থেকে মাংস দিয়ে। এই মহিলা হয়ত অনেক কষ্ট করে আধা কেজি মাংসের টাকা জোগাড় করে এনেছে তাঁকে না ঠকালে কি নয়? সে মাথা নিচু করলো। বুঝলাম সেটা লজ্জা বা অনুতাপে নয়। আমার মতো পরিচিত কাস্টমারের কথা বলে।
এটা শুধু মাংসের ক্ষেত্রে নয়, সর্বক্ষেত্রে গরিবদের এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। যেমন ধরুন ওষুধ বা চিকিৎসাসেবার ক্ষেত্রে। গরিবের জন্য উন্নত বাদ দিন মানসম্মত চিকিৎসাসেবাই নেই। সরকারি হাসপাতালের অধিকাংশ নার্স ও চিকিৎসক তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যেন তাদের চিকিৎসাসেবা নয় তাদের করুণা করছেন, দয়া করছেন। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের বড় লোকরা(?) এ দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে আচরণ করেন প্রজাসুলভ। ভেজাল, মানহীন, পচা-বাসি খাবার খেয়ে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে রোগাক্রান্ত হয়ে কোনোপ্রকার চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে অনেক পরিশ্রমের টাকা দিয়ে এই গরিবদেরই কিনতে হয় মানহীন, ভেজাল-নকল ওষুধ। ওষুধবিক্রেতারা চেনাজানা, প্রভাবশালী বা পরিষ্কার কাপড়চোপড় পরিধানকারীদের কাছে সহজে নকল ওষুধ বিক্রি করে না। তাদের টার্গেট হলো সহজ-সরল ও গরিব কিসিমের ক্রেতারা। ফলে অকালে জীবনপ্রদীপ নিভে যায় গরিবের। এদের প্রতিটি মাথা হিসাবে ধরলেও মাথাপিছু আয় এবং ৭৩ বছর গড় আয়ুর কোনোটারই সুবিধাভোগী নয় এরা।
রাষ্ট্রটি এখন বড়লোকদের হয়ে পড়েছে। গরিবের স্বার্থ দেখার যেন কেউ-ই নেই। বর্তমান সরকার দারিদ্র্য দূর করার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে বটে তবে সেসবের সব সুবিধা তাদের কাছে পোঁছানোর আগেই ভাগবাটোয়ারা করে নেয় বড়লোকরা। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে দেশে, ভিটেমাটিহীন মানুষদের বাড়ি করে দেওয়া হচ্ছে, একটি বাড়ি একটি খামার, বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, পড়ালেখার খরচসহ অনেক অনেক কার্যক্রম পরিচালনা করছে সরকার তারপরও কিছু বিত্তশালী লোভীদের কারণে অনেক সময় গরিবরা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়।এসবকিছুর পাশাপাশি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যদি না বদলায় তাহলে প্রকৃত উপকারটি হবে না।
আমাদের বিয়েশাদি থেকে শুরু করে সামাজিক নানা উৎসবে যেভাবে খাদ্যের অপচয় হয় তা দেখে যেকোনো বিবেকবান মানুষের আহত হওয়ার কথা। যেদেশে এখনো অনেক মানুষ দুবেলা ভালো করে খাবার খেতে পারে না সেদেশে এমন অপচয়কে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। এই আচরণ অসভ্যতা, অমানবিকতা। এটা বন্ধ করা দরকার।
কলকাতার মানুষের যে আচরণকে আমরা বিদ্রুপ করি মানুষ ও মানবতার স্বার্থেই সে অভ্যাসই আমাদের রপ্ত করা উচিত। বিক্রেতাদের বাধ্য করা উচিত যার যতটুকু দরকার ততটুকু বিক্রি করতে। এটা ভোক্তা অধিকারের অন্যতম। দেশে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর আছে। তারা মাঝেমধ্যে নকল-ভেজাল ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজারে অভিযান পরিচালনা করে। সেটি ভালো উদ্যোগ। এর সঙ্গে তাদের এটাও দেখা উচিত একজন ভোক্তা তার চাহিদামতো পণ্য কিনতে পারছে কিনা।
লেখক : কবি-সাংবাদিক