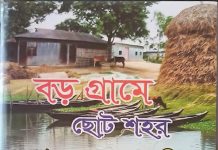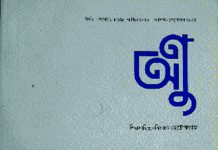বিশাল ও বর্ণিল প্রতিভার অধিকারী কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের একজন বড়ো মাপের কবি। অসম্ভব ঘটনাবহুল, বৈচিত্র্যময়তা আর সৃষ্টিশীলতায় ভরা তাঁর জীবন। তাঁকে নিয়ে আজ নানা কৌতূহল। তাঁর কবিতা, গান ও ব্যক্তিজীবনের চর্চা আজ বাঙালির নিত্যবিষয়। তিনি আমাদের সচল জীবনের সজীব সঙ্গী। কালান্তরে তিনি জেগে উঠেছেন নতুন নতুন পরিচয়ে। তিনি যেন কবিতার ফিনিক্স পাখি, উত্তরোত্তর উদ্ভাসিত হচ্ছেন বিচিত্র ও নবতর মাত্রায়।
কাজী নজরুল প্রকৃতই সাহিত্যের এক অনন্য সাধারণ প্রতিভা। তাঁর কাব্য চৈতন্যে নানা বাঁক পরিবর্তন ও বিচিত্র গতিধারার প্রাধান্য লক্ষ করা গেলেও তা ছিল এক অখণ্ড সৌন্দর্যানুভূতিতে ভরপুর। তিনি স্বভাবজাত কবির মতোই সৃষ্টি সুখের উল্লাসে তাঁর আপন কাব্য ভুবনে বিচরণ করতেন। এক্ষেত্রে তাঁর ছিল ‘অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস’। তিনি একই বৈঠকে বসে বিভিন্ন আঙ্গিক, ছন্দ ও ভাববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ কবিতা ও গান লিখতে পারতেন। কিন্তু তিনি শব্দের আড়ালে কখনো নিজেকে লুকোননি। তাঁর ভেতরের অস্থির চিত্ত সর্বদা প্রকাশে উন্মুখ ছিলো বিধায় তিনি মুক্ত বিহঙ্গের মতো তাঁর সৃষ্টির নীলিম আকাশে অবাধ বিচরণ করতেন কোনো লুকোচুরি ছাড়াই। এ কারণে তিনি কখনো জেল খেটেছেন, কখনোবা তাঁর কবিতা বাজেয়াপ্ত হয়েছে, আবার কখনোবা তিনি ‘কাফের’ ফতোয়ায় অভিষিক্ত হয়েছেন। কিন্তু তিনি এসবের থোড়াই পরোয়া করেছেন। সচেতনভাবে নিজের মতোই চলেছেন, নিজের মতোই বলেছেন এবং নিজের মতোই লিখেছেন। আসলে তিনি নিজ মাত্রা বা প্রবণতার স্রষ্টা। তিনি ‘নজরুলী’য় ধরনের কবিতা ও গানের প্রবক্তা, যা আপন স্বাতন্ত্র্যে অনন্য।
সাহিত্যে নজরুল এক অসামান্য শক্তিধর প্রতিভাবান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও দুরারোগ্য ব্যধির কারণে তাঁর সক্রিয় সাহিত্য–চর্চার কাল ছিলো মাত্র ২৩ বছর। এই সময়ে তিনি রচনা করেছেন ২২টি কাব্যগ্রন্থ, ৩টি অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ, ৫টি প্রবন্ধগ্রন্থ, ৩টি গল্পগ্রন্থ, ৩টি উপন্যাসংগ্রহ, ৩টি নাটকগ্রন্থ, ৩ (তিন) হাজারেরও বেশি গান, কিছু অভিভাষণ, শিশু সাহিত্যের কাব্যগুণ উচ্ছলিত এক বিশাল সাহিত্যভান্ডার, যা বাংলা সাহিত্যে তো বটেই, বিশ্বসাহিত্যেও দুর্লভ। এছাড়াও তিনি সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ, অর্ধ– সাপ্তাহিক ধূমকেতু, সাপ্তাহিক লাঙ্গল–এর মতো পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনা এবং গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানি, বেতার, মঞ্চ ও ছায়াছবির সাথে যুক্ত থেকে–এসবকে তাঁর সৃষ্টি বৈচিত্র্যে ধন্য করেছেন। কিন্তু তাঁর এই সৃষ্টি সক্রিয় জীবন, বিশেষত ১৯৪৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত নজরুলকে নিয়ে আলোচনা–সমালোচনা প্রচেষ্টা তেমন কোথাও দেখা যায় না।
১৯৪৪ সালে কবির এক সময়কার বন্ধু বুদ্ধদেব বসু তাঁর ‘কবিতা’ পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা ‘নজরুল সংখ্যা(কার্তিক–পৌষ ১৩৫১)’ নামে নজরুলকে উৎসর্গ করেন। এতে তিনি ‘নজরুল ইসলাম’ শীর্ষক প্রবন্ধে নজরুলকে নিয়ে কিছু তীর্যক মন্তব্য করেন, যাতে নজরুলের প্রবণতাকে খাটো করে দেখা হয়। তিনি লিখেন, ‘নজরুল চড়া গলার কবি, তাঁর কাব্যে হইচই অত্যন্ত বেশি। অনেক লেখা তিনি লিখেছেন, যাতে শুধু হইচই আছে, কবিত্ব নেই। …অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততা নজরুল রচনার প্রধান গুণ এবং প্রধান দোষও। যা কিছু তিনি লিখেছেন, লিখেছেন দ্রুতবেগে– ভাবতে, বুঝতে, সংশোধন করতে কখনো থামেননি, কোথায় থামতে হবে দিশে পাননি।’ তখন বুদ্ধদেব বসু নজরুলকে এভাবে মূল্যায়ন করলেও এখন আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলা কবিতায় মহাসমুদ্রের উত্থাল তরঙ্গের মতো বেগবান প্রবাহ আমদানি করে, একে বাঙালির সম্পদে পরিণত করেন নজরুলই। কবিতায় শব্দ ব্যবহার ও ধ্বনি–চেতনা গতির আবেগকে কতটা তীব্রতর করতে পারে, নজরুল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি শব্দকে ভাবের বাহন করে বাংলা কবিতায় ওজস্বিতা বাড়িয়ে দিয়েছেন।
প্রথমদিকে নজরুল তেমন আলোচনায় না আসলেও ভারত–বিভাগ পরবর্তী বিশেষত বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নজরুলকে নিয়ে আলোচনা– সমালোচনা হয়েছে এন্তার। একসময় তাঁকে নিয়ে গবেষণার বিষয়টি কারোর বিবেচনায় না থাকলেও বর্তমানে নজরুল–চর্চা, নজরুল–গবেষণা বাংলা সাহিত্যের এক অপরিহার্য অঙ্গ। যতই দিন যাচ্ছে, তাঁর বহুধাবিস্তৃত ও সর্বগ্রাসী প্রতিভা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হচ্ছে। ফিনিক্স পাখির মতো তিনি নতুন করে জাগছেন আপন স্বাতন্ত্র্যে। একসময়ের বিদ্রোহী কবি, সাম্যের কবি, প্রেমের কবি, গণজাগরণের কবি, মানবতার কবির সাথে যুক্ত হচ্ছে চিত্রকল্পের কবি, প্রান্তিক শ্রেণির কবি, সংগীতের কবি, পুনঃনির্মাণের কবি ইত্যাকার নানা অভিধা।
নজরুল খুব দ্রুত কবিতা রচনার সাথে সাথে শব্দের আলঙ্কারিক প্রয়োগ ও চিত্রময়তায় ছিলেন সমান স্বাচ্ছন্দ্য ও পারঙ্গম। নজরুলের কালোত্তীর্ণ কবিতাগুলোর প্রধান কারুকাজ হলো এর চিত্রকল্প। তাঁর প্রথাবিরোধী অবিস্মরণীয় কাব্য ‘বিদ্রোহী’ কবিতার প্রতিটি চরণই যেন এক একটি চিত্রকল্প। তেমনি বিখ্যাত ‘খেয়াপারের তরণী’ কবিতায় দুর্যোগময় রাত্রির পটভূমিকায় শব্দালঙ্কার ও শব্দ ঝংকারে অপূর্ব চিত্রকল্প তৈরি করেন তিনি। তার অন্যান্য কবিতায়ও চিত্রকল্প দৃষ্ট হয়। নজরুল আকণ্ঠ বিষয়বাদী হয়েও কবিতায় চিত্রকল্পের ব্যবহার করেন নির্দ্বিধায়। তিনি কাব্যের স্বাভাবিক ও অন্তর্গত তাগিদে আশ্রয় নেন অভাবিত–পূর্ব চিত্র ও রূপকের তথা চিত্রকল্পের। এদিক বিবেচনায় আজকাল অনেকেই নজরুলকে চিত্রকল্পের কবি বলতে আগ্রহী।
নিপীড়িত মানবতার কবি নজরুলকে আজকাল অনেকে প্রান্তিকশ্রেণির কবি বলতেও সচেষ্ট। তাদের মতে, পারিবারিক বলয় ও বিত্তে নজরুল প্রান্তিক শ্রেণিভুক্ত ছিলেন। এ কারণেই তিনি মাজারের খাদেম, মসজিদের ইমামতি, মোল্লাগিরি, মক্তবের শিক্ষক, লেটো কবিদলের কবিয়াল, রেলগার্ডের বাবুর্চি, রুটির দোকানের বয়, লজিং বাড়িতে পড়াশোনা, সৈনিক, সাংবাদিক, সম্পাদক, প্রকাশক, গ্রামোফোন কোম্পানি ও কোলকাতা বেতারে যোগদান ইত্যাকার বিভিন্ন পেশা ও অবস্থানে থেকে চিরজীবন অস্তিত্বের সংগ্রাম করেছেন। তিনি যে জীবনে স্থায়ী পেশা বেছে নেননি, তা তাঁর বাউণ্ডুলেপনা নয়, বরং আপন শ্রেণিগত অবস্থানেরই পরিচায়ক। তিনি নিজেই বলছেন, ‘আমি উঁচু বেদির উপর সোনার সিংহাসনে বসে কবিতা লিখিনি। যাদের মূক মনের কথাকে আমি ছন্দ দিতে চেয়েছি, মালকোঁচা মেরে সেই তলার মানুষের কাছে নেমে এসেছি।’ তাঁর ভেতরের দ্রোহ চেতনা, অহমের সাধনার নেপথ্যে ক্রিয়াশীল ছিল সমাজের প্রান্তিক অবস্থানের নিপীড়িত–লাঞ্চিত–সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মুক্তি ও শান্তির অন্বেষণ।
নজরুল সংগীত স্রষ্টাও। তিনি একাই তিন হাজারের বেশি বিশুদ্ধ সংগীত রচনা করে সংগীতের ইতিহাসে এক গৌরবদীপ্ত অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। তাঁর মতো এত অধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ গান রচনা একজনের পক্ষে দুঃসাধ্য বটে। নজরুল গানে এত বৈচিত্র্য আছে যে, বছরের প্রতিটি দিন, প্রতিক্ষণেই তা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তিনি নিজেই তাঁর গানের সুরকার। তাঁর গানের একটা নিজস্ব স্টাইল আছে। তাঁর গানের সুর, তাল, লয়, ছন্দ–সবকিছুতেই নজরুলীয় স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হয়। সৃজনশীল মৌলিক সংগীত প্রতিভার অধিকারী নজরুল ১৯২৮ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যভাগে অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ১৪ বছরে গ্রামোফোন, বেতার, মঞ্চ, সিনেমা–এসব বিভিন্ন মাধ্যমে স্বরচিত অগণিত সংগীতের স্রষ্টা ছিলেন। তাঁর সংগীতের সংখ্যাগত বহুত্ব, রচনা রীতিগত বৈচিত্র্য ও আপাত–স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও, এতে যে কালজয়ী উপাদান আছে, তা উৎকর্ষ বিচারে অনবদ্য। প্রতিভাময়ী শিল্পীকণ্ঠ যে নির্ভরতা, স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য পায় নজরুলের গানে তা অতুলনীয়। সঙ্গত কারণেই ইদানীং নজরুলকে ‘সংগীত স্রষ্টা নজরুল’ বলা হচ্ছে।
নজরুলের সাহিত্য সাধনার মূল সময় ঔপনিবেশিক শাসন ও দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকাল সময়ে বলে তাঁর কবিতায় বিদ্রোহ, ধ্বংস ও ভাঙনের শব্দই শোনা যায় বেশি। ঔপনিবেশিকতার কাব্যিক মোকাবেলায় তিনি আক্রমণাত্মক, সরাসরি ও তেজদীপ্ত। কিন্তু একটু কান পাতলেই বোঝা যায়, তাঁর বিদ্রোহ, ধ্বংস ও ভাঙনের মাঝেও রয়েছে পুননির্মাণের অদম্য এক অনুপ্রেরণা। আসলে নজরুলের সমগ্র সাহিত্য সাধনার মূলে রয়েছে এক ইতিবাচক জীবনবোধ। এক সময় তা উদাসীনতার কুয়াশার আড়ালে ঢাকা থাকলেও পর্যায়ক্রমে তা স্পষ্ট হচ্ছে, উঠে আসছে ভিন্ন এক বিস্ময়কর নজরুল।
কালোত্তীর্ণ কবি নজরুলের কবিতা কালান্তরে খুলে দিচ্ছে সৃষ্টির নতুন নতুন দ্বার। আধুনিক নজরুল গবেষকরা, তাঁর কবিতায় এক ধরনের প্রান্তমুক্ততা লক্ষ করছেন, যা বর্তমান শতকের নয়া কাব্যভাষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এখানে এসে আমরা অবাক বিস্ময়ে অন্য এক নজরুলকে খুঁজে পাই। এখন এটা স্পষ্ট যে, নজরুল ব্যতিক্রমী ও বড়ো মাপের কবি ছিলেন বলেই, রবীন্দ্রনাথ ও তিরিশের কবিদের সময়কালে থেকেও তৈরি করে নিয়েছিলেন নিজের স্বতন্ত্র মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। তিনি আজীবন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থান করেও আমাদের দিয়ে গেছেন এক বিশাল ও বর্ণিল সৃষ্টিসম্ভার, যা বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের মতো কালান্তরে নজরুলকে আমাদের সামনে উপস্থিত করছে নব নব পরিচয়ে, নতুন নতুন বিস্ময়ে। এটা সম্ভব হয়েছে এজন্য যে, তাঁর লেখনীতে রয়েছে এক ধরনের চিরকালীন উপাদান, কালতীত ভাব–যা আমাদের নিত্য প্রেরণা যোগায়। কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে, অভিভাষণে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, যা সৃষ্টি করেছেন, নজরুল গবেষকরা তা থেকে নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছেন, অন্য এক কাছের নজরুল বেরিয়ে আসছে ফিনিক্স পাখির মতো, বারে বারে পুনঃজন্ম হচ্ছে নজরুলের। ঔপন্যাসিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক বছর আগে বলা কথায়ও আমরা সেই প্রতিধ্বনিই শুনি, ‘যত দিন যাচ্ছে, নজরুলের জীবন ও তাঁর গান ততই বেশি বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।’ (জল প্রপাতের অন্তর্লীন বিষাদ, দেশ– ১২ জুন ১৯৯৯ ইংরেজি)।